
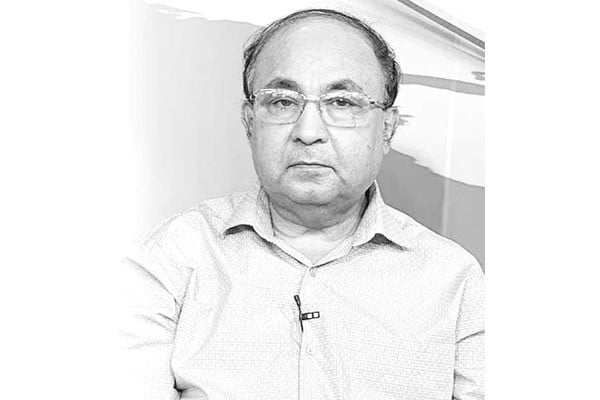
সামরিক শাসক এরশাদের শাসনামলে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর এবং সিলেটে হাই কোর্ট বিভাগের ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিল ও অকার্যকর ঘোষিত হলেও সংসদ অদ্যাবধি বিষয়টি নিয়ে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কিন্তু সংশোধন বাতিল পরবর্তী বাতিলের সপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান বিচারপতি হিসেবে অস্থায়ী সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালনকালীন সংবিধান পুনর্মুদ্রণকালীন সংশোধিত ১০০ অনুচ্ছেদটিকে এর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সংসদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংবিধান পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায় কি না, এ প্রশ্নটির সুরাহা হওয়া প্রয়োজন।
 সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ দফা (২)-এর আলোকে আইন প্রণয়নপূর্বক জেলা জজ আদালতসমূহকে নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন স্থানীয় সীমার মধ্যে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন সব বা যে কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হলে হাই কোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি দেশের সর্বত্র বিচারপ্রার্থী জনমানুষের স্বল্প ব্যয়ে তাদের কাক্সিক্ষত প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। এটি কার্যকর করা হলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০-এর অনুবলে বিভাগীয় বা জেলা শহরে হাই কোর্ট বিভাগের বেঞ্চ স্থাপনের আবশ্যকতা থাকবে না। আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ আদালত অবমাননা বিষয়ে হাই কোর্টের দন্ড প্রদানের ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণকল্পে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ পাক-ভারত উপমহাদেশের অংশ হিসেবে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকাবস্থায় উক্ত সালে প্রণীত হয়। এ আইনটিতে আদালত অবমাননার দণ্ডের উল্লেখ থাকলেও আদালত অবমাননার ব্যাখ্যা দেওয়া না থাকায় এর সীমারেখার ব্যাপ্তি প্রায়শই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ দফা (২)-এর আলোকে আইন প্রণয়নপূর্বক জেলা জজ আদালতসমূহকে নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন স্থানীয় সীমার মধ্যে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন সব বা যে কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হলে হাই কোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি দেশের সর্বত্র বিচারপ্রার্থী জনমানুষের স্বল্প ব্যয়ে তাদের কাক্সিক্ষত প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। এটি কার্যকর করা হলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০-এর অনুবলে বিভাগীয় বা জেলা শহরে হাই কোর্ট বিভাগের বেঞ্চ স্থাপনের আবশ্যকতা থাকবে না। আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ আদালত অবমাননা বিষয়ে হাই কোর্টের দন্ড প্রদানের ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণকল্পে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ পাক-ভারত উপমহাদেশের অংশ হিসেবে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকাবস্থায় উক্ত সালে প্রণীত হয়। এ আইনটিতে আদালত অবমাননার দণ্ডের উল্লেখ থাকলেও আদালত অবমাননার ব্যাখ্যা দেওয়া না থাকায় এর সীমারেখার ব্যাপ্তি প্রায়শই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।
পৃথিবীর সব সভ্য, উন্নত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আদালত অবমাননা সংজ্ঞায়িত হওয়ায় বিগত কয়েক দশক ধরে আদালতের রায় ও বিচারকদের বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ এবং আলোচনা লেখক, প্রকাশক ও আলোচক কারও জন্য কোনো ধরনের হয়রানির কারণ হয়ে দেখা দেয়নি। আমাদের আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬-কে যুগোপযোগী করার মানসে ২০০৮ সালে আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ এবং ২০১৩ সালে আদালত অবমাননা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। অধ্যাদেশ ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আদালত অবমাননার সীমারেখার ব্যাপ্তি নির্ধারণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। অধ্যাদেশ ও আইন উভয়ই অনেকটা সমরূপ বিধানসংবলিত ছিল। অধ্যাদেশ ও আইনটির বৈধতা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের মাধ্যমে আপত্তি উত্থাপিত হলে শুনানি-অন্তে হাই কোর্ট বিভাগ অধ্যাদেশ ও আইন উভয়টিকে অবৈধ ঘোষণা করে।
আমাদের সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে ‘কোর্ট অব রেকর্ড’ উল্লেখপূর্বক এর অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ দান বা দণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সব ক্ষমতার অধিকারী করেছে। সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদ অবলোকনে প্রতীয়মান হয়, আদালতের বাইরে সংঘটিত যে কোনো ধরনের আদালত অবমাননা বিষয়ে আদালত অবমাননা-সংক্রান্ত আইন কার্যকর থাকার আবশ্যকতা রয়েছে।
২০১৩ সালে আদালত অবমাননা আইন প্রণয়নকালে ওই আইনের ২০ ধারা বলে আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ রহিত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩-এর ৮টি ধারা বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনপূর্বক ধারাসমূহের বাতিল চাওয়া হলেও শুনানি-অন্তে হাই কোর্ট বিভাগ সম্পূর্ণ আইনটি বাতিল করে দেয়। সম্পূর্ণ আইনটি বাতিল করার কারণে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বর্তমানে কোনো আদালত অবমাননা আইন কার্যকর আছে কিনা? এ বিষয়ে অধিকাংশ আইনজ্ঞের মতামত আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩ বাতিল ঘোষণার সময় আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ অস্তিত্ববিহীন থাকায় একটি অস্তিত্বহীন আইনকে কার্যকর বলার কোনো সুযোগ নেই।
পৃথিবীর সর্বত্র বিচার বিভাগকে বলা হয় মানুষের অধিকার সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের কতিপয় বিচারকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ, বেআইনি ও অসাংবিধানিক আচরণের কারণে বহু সম্ভ্রান্ত নাগরিককে আদালতের মাধ্যমে অপমান, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার দলিল, ১৯৪৮-এ স্বাক্ষরকারী দেশ। উক্ত দলিলের অনুচ্ছেদ ৫ এবং আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫ দফা (৫) সমরূপ। এ দফাটিতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানসিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না কিংবা কারও সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না।
দফাটি অবলোকনে প্রতীয়মান হয় আদালতে ডেকে নিয়ে আদালত অবমাননার নামে কোনো ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে কারও সঙ্গে অবমাননা বা লাঞ্ছনাকর আচরণ করা যাবে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের উচ্চ আদালতের আপিল ও হাই কোর্ট বিভাগের কতিপয় বিচারক সংবিধান ও আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার ব্যত্যয়ে আদালত অবমাননার খড়গের অপপ্রয়োগে সমাজের গণ্যমান্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিকে অপমান ও অপদস্থ করে জাতির সামনে হেয়প্রতিপন্ন করার প্রয়াস নিয়েছেন। আমাদের উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদে বিবৃত সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের নামে আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ বহাল থাকাকালীন আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের সীমারেখাকে অতিক্রম করে একজন পত্রিকার সম্পাদককে যে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছিল এর মাধ্যমে কী আসলেই সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা হয়েছিল! আদালতের এহেন অন্যায় আচরণে ভুক্তভোগীদের মহান আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অপর কারও কাছে প্রতিকার চাওয়ার পথ রুদ্ধ ছিল বা বর্তমানেও রুদ্ধ।
১ নভেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ বিচার বিভাগ আংশিক পৃথকীকরণ পরবর্তী চারটি বিধিমালা যথা-বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরি, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলাবিধান এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা, ২০০৭ এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণীত হলেও অদ্যাবধি পৃথকীকরণকে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদানে সুপ্রিম কোর্টে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক অধস্তন বিচার বিভাগের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রম সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।
’৭২-এর সংবিধান প্রণয়নকালীন বিচারকর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান, ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্বপূর্বক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল কার্যকর করা হলেও অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টকে আর ফেরত দেওয়া হয়নি। প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরিসংক্রান্ত বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সর্বমোট ৭টি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং ১টি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল কার্যকর রয়েছে। চাকরিসংক্রান্ত বিষয়াবলি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালকে একক স্বতন্ত্র এখতিয়ার প্রদান করায় এসব বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট ডিভিশনে রিটের মাধ্যমে প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ বারিত করা হলেও তা প্রায়শই উপেক্ষিত হচ্ছে। এতে করে একই বিষয়ে দুটি পৃথক বিচারালয়ের কার্যক্রম বিদ্যমান থাকায় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।
এ কথাটি অনস্বীকার্য যে সুপ্রিম কোর্টের ওপর অধস্তন বিচার বিভাগের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলাবিষয়ক কার্যক্রমের পদক্ষেপের বাস্তবায়নে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা-পূর্ববর্তী উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে বিচারক নিয়োগ আইন প্রণয়ন অতীব জরুরি। এর পাশাপাশি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬, ৯৯, ১১৫ ও ১১৬ ’৭২-এর সংবিধানে যে অবস্থায় ছিল তাতে প্রত্যাবর্তন করা হলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অনেকাংশে সব ধরনের লোভলালসার ঊর্ধ্বে থাকার অবকাশ ঘটবে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করার আগে অবশ্যই উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের বিচারকদের প্রবেশ পদে নির্ধারিত যোগ্যতার চেয়ে আরও উচ্চতর যোগ্যতাধারীদের নিয়োগের বিষয়টি বিচারক নিয়োগ আইনে অন্তর্ভুক্তি যৌক্তিক বিবেচিত। আদালত অবমাননা বিষয়েও সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদের অভিপ্রায়ের আলোকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আদালত অবমাননা আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগী আদালত অবমাননা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
♦ লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক
Email: [email protected]