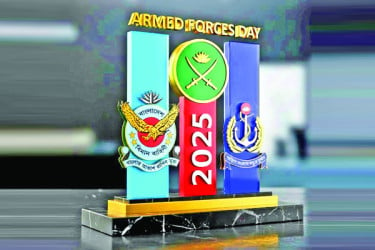পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট- একদিকে ৩২ নম্বরের বাসার মেঝে-সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্বজনদের লাশ তখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে। শোকে কাতর দেশবাসী হতবিহ্বল। অন্যদিকে সারা দেশে কারফিউ, সেনা তৎপরতার মুখে যখন টুঁশব্দটি করার উপায় ছিল না, তখন একদল প্রতিবাদী যুবক গর্জে ওঠে। তারা অস্ত্রহাতে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে সীমান্তবর্তী জনপদ। বঙ্গবন্ধুভক্তরা দলে দলে জড়ো হয় গারো পাহাড়ের গহিন জঙ্গলে, আসাম-মেঘালয় সীমান্ত এলাকায় শুরু হয় প্রতিরোধযুদ্ধ।
প্রথম দিকে গজারির ডাল কেটে বিশেষ কায়দায় বানানো লাঠিই ছিল তাদের সম্বল আর ছিল অদম্য মনোবল।
প্রতিবাদ-প্রতিরোধ শুধুই প্রতীকী মেজাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতির পিতাকে হারানোর শোকে মুহ্যমান একেকজন বীর যোদ্ধা জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে গেরিলা যুদ্ধে। তারা টহল পুলিশ ও বিডিআরের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলা পরিচালনার মাধ্যমে কব্জা করতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র। তা দিয়েই শুরু করে প্রতিরোধযুদ্ধের প্রাথমিক যাত্রা। প্রতিরোধযোদ্ধারা গারো পাহাড়ঘেঁষা ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা জেলা সীমান্তের বিরাট এলাকাজুড়ে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। তারা সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী পাঁচটি বিডিআর ক্যাম্প ও দুটি থানা দখল করে প্রায় ৩০০ বর্গমাইল এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গেও। প্রশিক্ষিত সেনা দলের হেলিকপ্টার, গানশিপ আর সাঁজোয়া বহরের বিপরীতে এমএমজি, মর্টার, এসএলআর নিয়েই লড়াই চালায়। একবার সেনাবাহিনী হটেছে তো অন্যবার পিছিয়ে গেছে প্রতিরোধযোদ্ধারা। যুদ্ধকালে ৪ শতাধিক প্রতিরোধযোদ্ধা শহীদ হয়। এ ছাড়া প্রতিরোধযুদ্ধে ১৪ জন বিডিআর-পুলিশ নিহত হয়, ক্রসফায়ারে সাধারণ গ্রামবাসীও মারা যায় তিনজন। গুলিবিদ্ধ হয় উভয় পক্ষের সহস্রাধিক ব্যক্তি। এভাবে প্রায় ২২ মাস যুদ্ধ চালিয়ে প্রতিরোধযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গেই টিকে থাকে। কিন্তু ওই সময় রাজনৈতিক নির্দেশনার অভাবে অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে প্রতিরোধযুদ্ধ। পাশাপাশি ভারতে জাতীয় নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় হলে প্রতিরোধযোদ্ধাদের শিবিরগুলো একে একে গুটিয়ে নিতে হয়।
প্রতিরোধযুদ্ধে বহু মানুষ সর্বহারা : দুর্গাপুর মহিলা কলেজের অধ্যাপক গারো আদিবাসী নেতা রেমন্ড আড়েং বলেন, ‘জাতির পিতা হত্যার প্রতিবাদে আমাদের আদিবাসী অগ্রজরা যুদ্ধ করেছে এটা আমাদের গৌরব। তবে এ যুদ্ধে আমরা অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছি।’ তিনি বলেন, ‘১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গারো পাহাড়ি এলাকার ১০ হাজারের বেশি গারো-হাজং-কোচ-বানাই-ডালু আদিবাসী তাদের জমিজিরেত, সহায়সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এর মাত্র পাঁচ বছর না পেরোতেই শুরু হয় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। তখন সমগ্র দেশবাসীর মতো আমরাও স্বজন-পরিজন সহায়-সম্পদ হারিয়ে পথে এসে দাঁড়ানোর উপক্রম হই। আবার চার বছর পার না হতেই শুরু হয় প্রতিরোধযুদ্ধ। ফলে আবার ৫ সহস্রাধিক আদিবাসী পরিবার শরণার্থী হয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়।’ আরেক আদিবাসী নেতা অধ্যাপক অঞ্জন ম্রং বলেন, ‘তৎকালীন প্রশাসনও প্রতিরোধযুদ্ধে যাওয়ার অভিযোগ তুলে আদিবাসী পল্লীগুলোয় বেপরোয়া লুটপাট চালাতে থাকে। পানির দামে জমি বিক্রি করে সে টাকা পুলিশ-বিডিআরের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে আদিবাসীরা। এর পরও নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে রেহাই মেলেনি।’ অধ্যাপক অঞ্জন বলেন, ‘বারোমারী গ্রামের শেখর হাগিদক ও তার ভাই শংকর হাগিদক প্রতিরোধযুদ্ধে যাওয়ার কারণে তার বাবাকে আড়াই শ একর জমি বিক্রি করতে হয়েছে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই। এত জমিজমার মালিক হওয়া সত্ত্বেও আজ শেখর-শংকরকে প্রায় ভূমিহীন অবস্থায় অমানবিক জীবনযাপন করতে হচ্ছে।’ বিরিশিরি উপজাতি কালচারাল একাডেমির পরিচালক স্বপন হাজং পঁচাত্তরের প্রতিরোধযুদ্ধে আদিবাসীদের ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার অপরাধে ৭৮টি আদিবাসী গ্রামের ৩ হাজারের বেশি অধিবাসী তাদের সহায়সম্বল সব হারিয়েছে। একের পর এক আক্রোশমূলক মামলার শিকার হয়েছে আরও ৫ শতাধিক মানুষ। অনেকে বিনা অপরাধেও জেলে থেকে জীবনের মূল্যবান সময় হারিয়ে এখন অথর্ব মানুষে পরিণত হয়েছে। ফসলি জমি হাতছাড়া হয়েছে ৫ সহস্রাধিক একর।
প্রতিরোধযুদ্ধের কমান্ডাররা : বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে যুদ্ধের জন্য সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয় নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার ভবানীপুরে। ছিটমহল স্টাইলের পাহাড়ি উপত্যকা ভবানীপুরের যে স্থানটিতে সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয় সেখানে যাতায়াত করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। বাংলাদেশের মূল ভূখ- থেকে ভবানীপুরের ২০-২২ একর আয়তনের ওই ছিটমহলটুকুতে ভারতের সীমানা ডিঙিয়ে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল। ফলে দেশের ভিতরে থেকেও বাংলাদেশের সেনা, বিডিআর, পুলিশসহ প্রশাসনিক অন্যান্য সংস্থার প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল প্রতিরোধযোদ্ধাদের হেডকোয়ার্টার এলাকাটি। সেক্টরের জিওসি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন টাঙ্গাইলের বাসিন্দা সেলিম তালুকদার। এখানে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন প্রশান্ত কুমার সরকার। কোয়ার্টার গার্ডের অধিনায়ক ছিলেন শরীফুল ইসলাম খান (ধামরাই উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান)। ডিফেন্স কমান্ডার হিসেবে ঘাঁটি করা হয় সোমেশ্বরী নদীঘেঁষা সুউচ্চ পাহাড়চূড়ায় (বর্তমানে বিজিবির ভবানীপুর বিওপি), দায়িত্বে ছিলেন সাইদুর রহমান, যিনি এলাকায় মহারাজ হিসেবে পরিচিত। হেডকোয়ার্টারের আওতায় বেশ কয়েকটি সাবসেক্টর গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরেই, দুর্গম পাহাড়-অরণ্যে। এগুলো হলো- নেত্রকোনা-সুনামগঞ্জ জেলা সীমান্তবর্তী বেতগড়া (কমান্ডার : সুকুমার সরকার), কলমাকান্দা থানা এলাকায় রংরা (কমান্ডার : জিতেন্দ্র ভৌমিক), দুর্গাপুর থানা এলাকায় ভবানীপুর (কমান্ডার : প্রশান্ত কুমার সরকার-বিল্লাবিন), নেলুয়াগিরি (কমান্ডার : সুনীল অধিকারী), ধোবাউড়া থানাধীন দাবরাং (কমান্ডার : দীপংকর তালুকদার), হালুয়াঘাট থানা এলাকায় গোবরাকুড়া (কমান্ডার : অতুল সরকার), ঝিনাইগাতী থানা এলাকার উত্তর গজনী। এসব সাবসেক্টর আওতায় ছোট বড় আরও বেশ কয়েকটি ক্যাম্প ছিল প্রতিরোধযোদ্ধাদের।
আরও যারা প্রতিরোধযুদ্ধে যান : প্রতিরোধযুদ্ধের শুরুতেই রাঙামাটি থেকে দীপংকর তালুকদার হাজির হয়েছিলেন মেঘালয়ের সীমান্তে, কাদের সিদ্দিকীর ঘাঁটিতে। সেখানে যান কাদের সিদ্দিকীর বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী এমপি, নারায়ণগঞ্জের নাসিম ওসমান, ধামরাইয়ের শরীফুল ইসলাম খান, কুলাউড়ার সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, মানু মজুমদার, মালেক উকিল, শেখ নওসের আলী নসু প্রমুখ। কেমন আছেন সেই প্রতিরোধযোদ্ধারা? ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়া সেদিনের যুবকরা আজ কেউ আর ভালো নেই। যুদ্ধকালেই তাদের সহায়সম্পদ সবকিছু কেড়ে নিয়েছে খুনি মোশতাকের দোসররা। যুদ্ধ সমাপ্ত ঘোষণার পর অনেকেই প্রায় তিন যুগ ধরে আসাম-মেঘালয়ের পাহাড়-জঙ্গলে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। যারা জিয়াউর রহমান সরকারের পুনর্বাসনের ঘোষণায় বিশ্বাস করে দেশে ফিরেছেন তাদের বছরের পর বছর জেলজীবন কাটাতে হয়েছে।
সব শেষে এলাকায় ফিরে প্রতিরোধযোদ্ধারা একেকজন হয়ে পড়েন পরিবারবিচ্ছিন্ন, সবার সীমাহীন অবজ্ঞা-অবহেলারও শিকার হন। প্রতিরোধযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে বারবার ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া গেরিলা কমান্ডার জিতেন্দ্র ভৌমিক বলেন, ‘পিতার (বঙ্গবন্ধু) রক্তের বদলা নিতে ছেলেদের যা করণীয় তা-ই করেছি। যে কারণে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ নিতেও ঘৃণাবোধ করেছি।’ অসমাপ্ত প্রতিরোধযুদ্ধের পর থেকেই টানা ৩৭টি বছর আসামের বিভিন্ন স্থানে নির্বাসনে ছিলেন তিনি। তার অনুপস্থিতিতে বাবা গজেন্দ্র ভৌমিক প্রশাসনিক নির্যাতনে রোগে শোকে মারা যান। মা চিত্র ভৌমিক এখনো বেঁচে আছেন প্যারালাইজ্ড অবস্থায়। জিতেন্দ্র ভৌমিক চোখের কোণে জমে ওঠা পানি মুছতে মুছতে বলেন, ‘আমি সেসব সন্তানতুল্য সহযোদ্ধার সঙ্গে প্রতারণা করে চলছি, মিথ্যা সান্ত¡না দিচ্ছি তাদের। বলি, কাল যাব ঢাকায়, পরশু যাব ঢাকায়। সব জানাব জায়গামতো। একটা কিছু করবই। একটা কিছু হবেই হবে।’ কিন্তু সেই একটা কিছু আর করা হয়ে ওঠে না জিতেন্দ্র ভৌমিকের, তাই তো নিজেই অনেকটা গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকেন বিরিশিরি এলাকায়। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মুখোমুখি হলে খুবই ব্যস্ততার ভান ধরে দিগ্বিদিক ছুটে চলেন। জিতেন ভৌমিক ক্ষোভে দুঃখে বলে ওঠেন, ‘আর পারি না। ভাবছি নিজেই আবার ভারতে পালিয়ে যাব। সেখানে শুধু আমার আর পরিবারের কান্না শুনি। এখানে এসে শুনছি হাজারো কণ্ঠের আর্তনাদ।’
ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে ফেরা বিশ্বজিৎ নন্দী : বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক, মুজিবভক্ত হিসেবে জীবন বাজি রাখা বিশ্বজিৎ নন্দীর জীবন কাটছে আজ সীমাহীন অবহেলায়, চরম কষ্টে। ফাঁসি থেকে প্রাণ বাঁচলেও তার জীবনচাকা আর যেন ঘুরছে না। টাঙ্গাইলের আকুরটাকুরপাড়ায় এক ছেলে, এক মেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে গড়ে তোলা ছোট্ট পরিবারে অভাব-যন্ত্রণার চাপা আর্তনাদ থাকলেও বিশ্বজিৎ নন্দী মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। একগাল হেসেই বলে ওঠেন, ‘বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হওয়ার পর থেকেই আনন্দে আছি।’