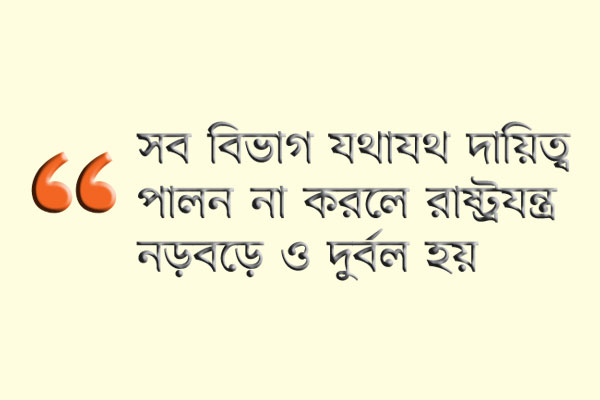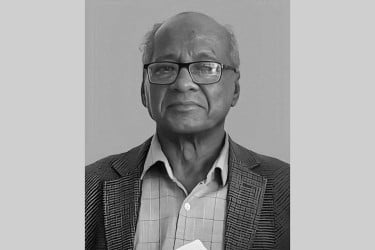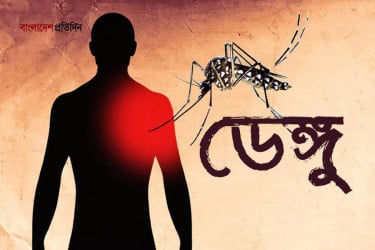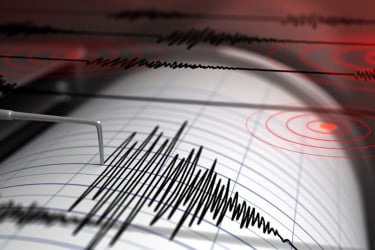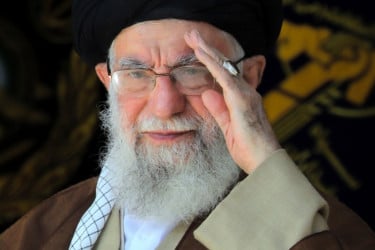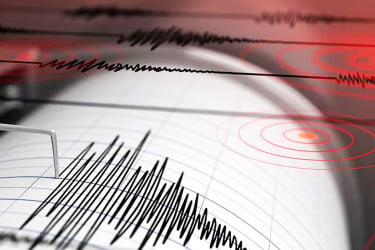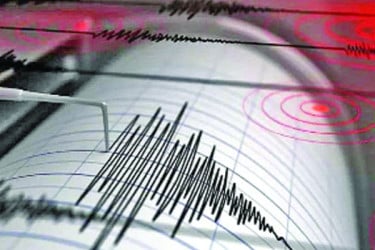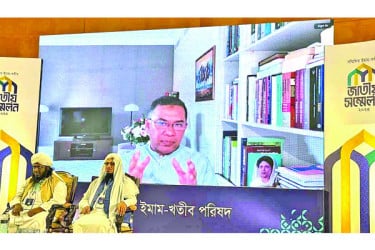প্রায় অকার্যকর হতে বসেছে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও সরকারের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পাওয়া যায় না সোচ্চার সংসদ, স্বাবলম্বী নির্বাচন কমিশন বা মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকাও বলিষ্ঠ নয়। রাষ্ট্রের আর্থিক হিসাব-নিকাশের নিরীক্ষা নিয়েও তৈরি হচ্ছে উদ্বেগ। প্রশ্ন রয়েছে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিয়েও। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার কথা যে কমিশনের তার নিজের চেহারাই জীর্ণ। আইনে প্রবল ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকার পরও তার ছিটেফোঁটা দেখা যায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আচরণে। একই চিত্র পানি, বিদ্যুৎ বা গ্যাস সংশ্লিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও। মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতিকীকরণে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে জনসাধারণের মৌলিক সেবা পাওয়াটাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বত্রই চলছে নির্বাহী বিভাগের দাপট। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক-বিশ্লেষক ও সাবেক শীর্ষ সরকারি কর্তারা বলছেন, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গাছের পাতাও নড়ছে না নির্বাহী বিভাগের আদেশ ছাড়া। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক বলয় বা দুর্নীতি ছাড়া সেবা দিচ্ছে না। যুগে যুগে দেখা গেছে যখন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে বা দুর্বল হয়ে পড়ে তখন রাষ্ট্রই অকার্যকর হয়ে যায় বলে মন্তব্য তাদের। কলামিস্ট ও অধিকার কর্মী সৈয়দ আবুল মকসুদের মতে, ভৌগোলিক আকার ও জনসংখ্যা যা-ই হোক রাষ্ট্র একটি মস্তবড় জিনিস। মানব দেহের মতো তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। শুধু হাত আর পা থাকলেই একজন মানুষকে সুস্থ মানুষ বলা যায় না। তার চোখ, কান, হৃদযন্ত্র, কিডনি, লিভার প্রভৃতি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, তার ওপর নির্ভর করছে মানুষটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক কিনা। দেহযন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন, রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রেও তা-ই। তাই শুধু নির্বাহী বিভাগ নয়, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করলে সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র নড়বড়ে ও দুর্বল হয়ে যায়। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদারের মতে, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন চলছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সুবিধা ও ইচ্ছামতো। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান যদি আত্মমর্যাদাশীল ও তীক্ষè ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে তিনি নির্বাহী বিভাগের চাপ কিছুটা প্রতিহত করতে পারেন। তবে তার ফলে তাকে মূল্যও দিতে হতে পারে। সেই ভয়ে অনেকে কোনো রকম বিবাদে জড়ান না। নির্বাহী প্রধানের বিরাগভাজন না হয়ে যতটুকু করা সম্ভব তাই করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. আতাউর রহমান বলেন, উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে নাইজেরিয়া একসময় এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, বাংলাদেশি অধ্যাপকরাও তখন সেখানে চাকরির জন্য যেতেন। উচ্চ বেতন ও সুবিধাদি দিয়ে তারা চমক সৃষ্টি করেছিল। ধরা হতো নাইজেরিয়ার অর্থনীতি বিশ্বে বড় শক্তি হিসেবে দেখা দেবে। আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতিও তেমন চমক ও আগ্রহের সৃষ্টি করছে। কিন্তু সাংবিধানিক বা গণতান্ত্রিক কাঠামো থেকে দূরে সরে মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতিকীকরণ ও জনবিচ্ছিন্ন প্রশাসন দিয়ে সরকার পরিচালনায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা ভালো লক্ষণ নয়। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদের মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান, তার অন্তরাত্মা গণতান্ত্রিক কিন্তু দেহ কাঠামো কলের পুতুলের মতো। সব কলের পুতুলের সক্রিয়তার জন্য প্রয়োজন পজেটিভ-নেগেটিভ দুটি ব্যাটারি। এ দুটি ব্যাটারির একটি হচ্ছে, কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংস্থা জাতীয় সংসদ। দ্বিতীয়টি হলো, রাষ্ট্রীয় জনকর্তৃক সংস্থা আমলাতন্ত্র। স্থানীয়ভাবে এ দুটি সক্রিয়তার প্রধান উপাদানের প্রধিনিধিত্ব করেন এমপি ও ডেপুটি কমিশনাররা। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচকম লী পরিবর্তন হয়। বাছাইকৃত নির্বাচকম লীর স্থলে জনগণকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপদ্ধতি এমনভাবে বিন্যস্ত হয়ে যায়, তাতে জাতীয়-স্থানীয় সর্বত্র নির্বাচিত স্বৈরশাসক তৈরির পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের বড় কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নিরীক্ষক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হাফিজ উদ্দিন খান মনে করেন, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বসানো হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। এ বিবেচনাটাও কে কতটা জনসেবা বা দলীয় আদর্শ বাস্তবায়নে পারঙ্গম সে হিসেবে নয়। ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে থাকা একটা বলয় চায়, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কে কতটা দুর্নীতি করে সেই বলয়কে দিতে পারবে তাকেই নিয়োগ দেওয়া হয়। এমন চললে সেবা পাওয়া মুশকিল থেকে দুরূহ হবে এটাই স্বাভাবিক।