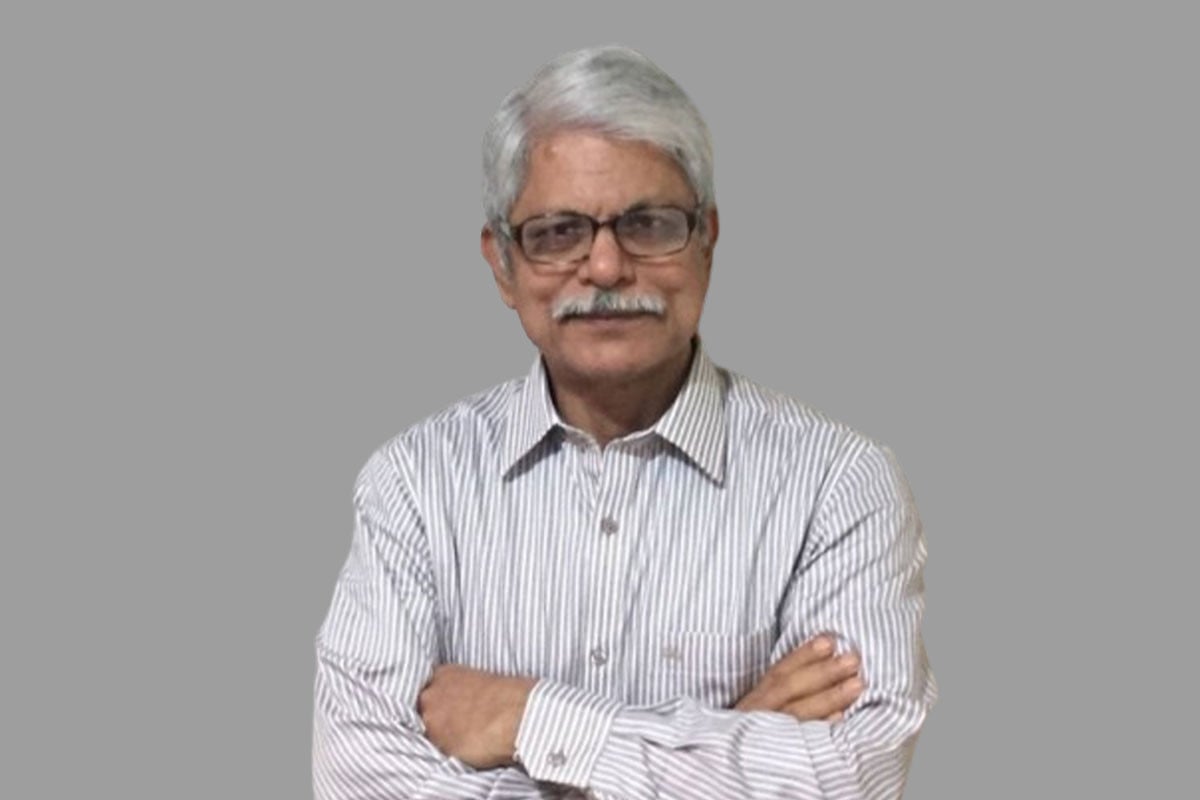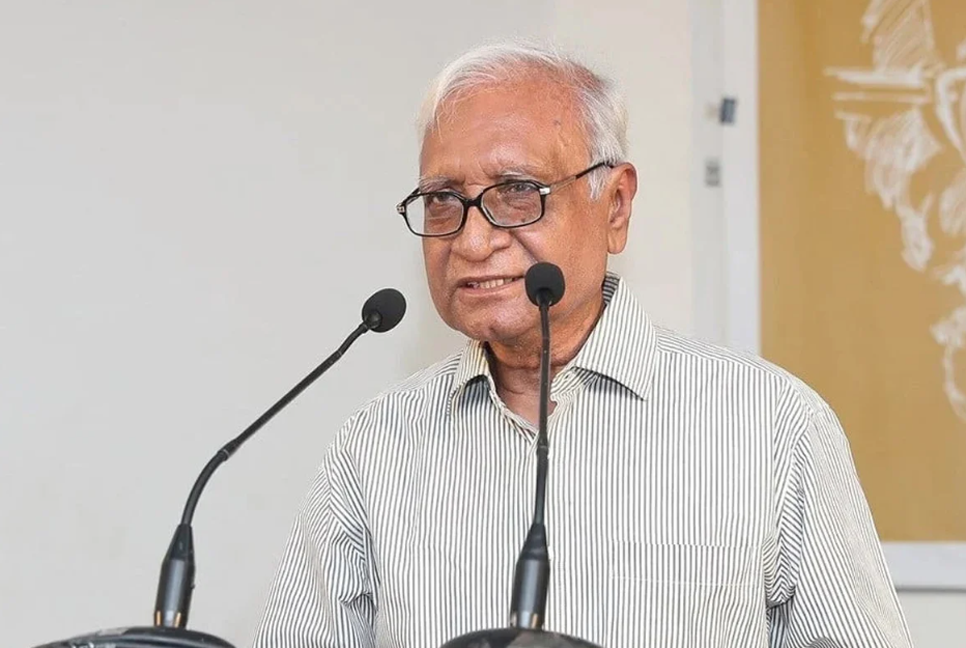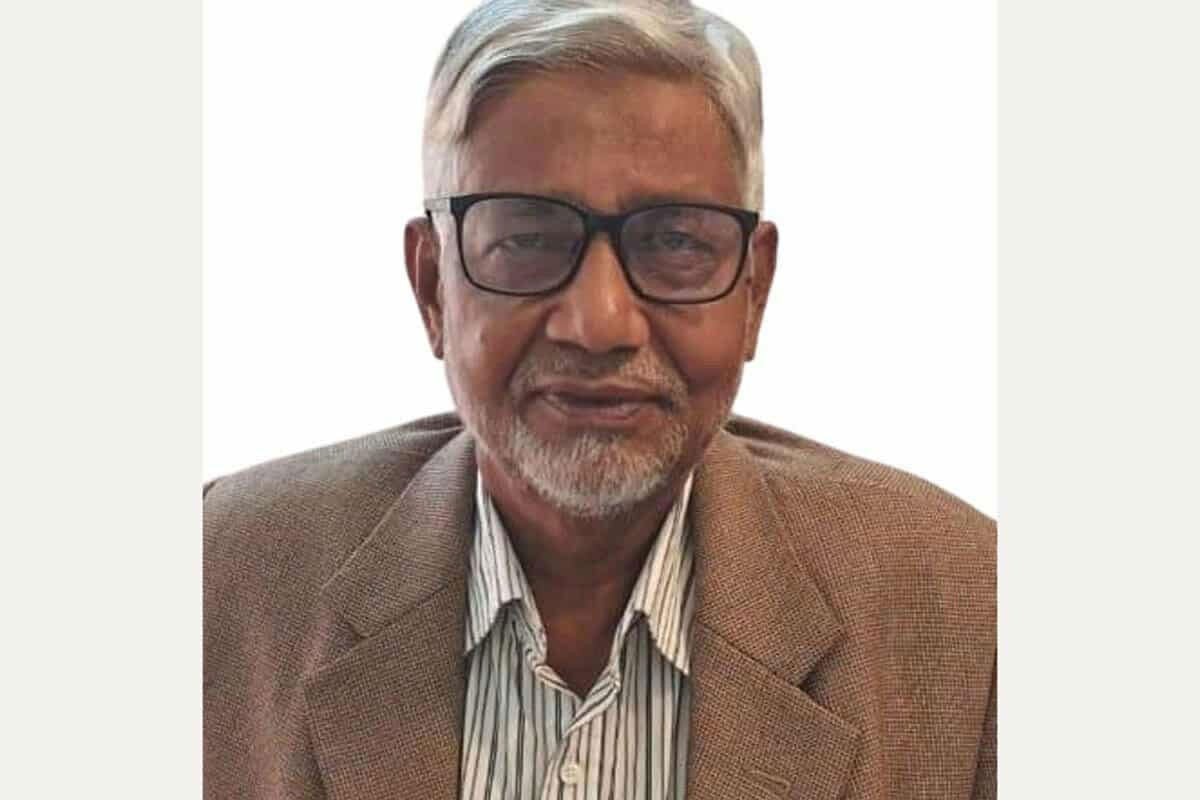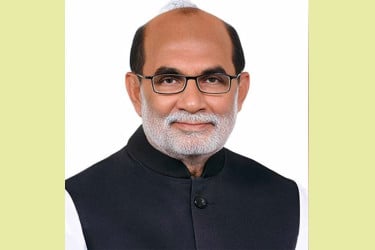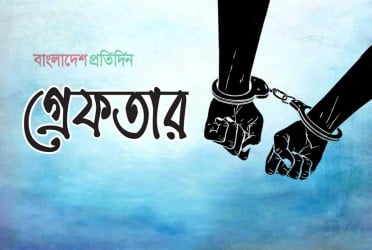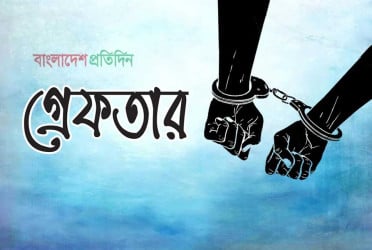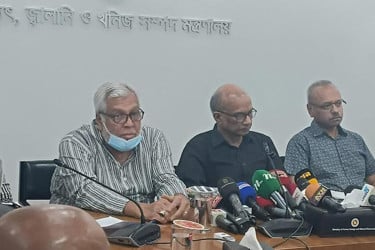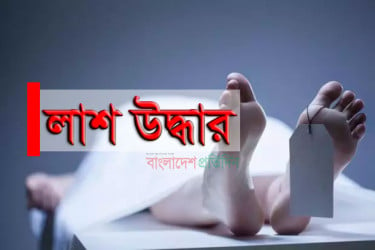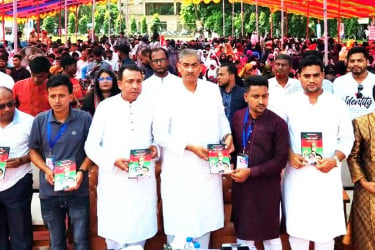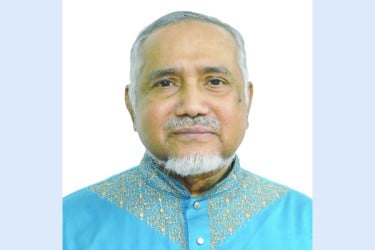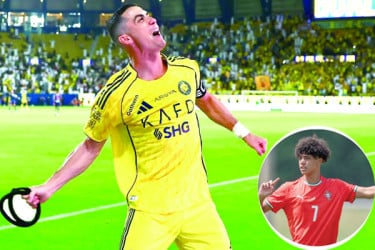সম্প্রতি এক আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন উদ্যোক্তা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে বিদ্যমান বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁরা বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ বোধ করছেন না। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন যদি সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।
তখন উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তাঁদের মতে, বিনিয়োগ আহরণের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একমাত্র শর্ত না হলেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে বিনিয়োগ নীতিমালার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। সেই অবস্থায় ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তারা নতুন করে বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।
বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে কথাটি আরো বেশি প্রযোজ্য। স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা নানা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে চাইলেই বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন না। তাঁরা নিজ দেশে বিনিয়োগে বাধ্য হন। কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই।
বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কোনো দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁরা চাইলে একটি দেশে বিনিয়োগ করতে পারেন কিংবা না-ও করতে পারেন। অর্থাৎ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা ইচ্ছা করলেই নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি নিয়ে যেতে পারেন না। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা হচ্ছেন ‘শীতের অতিথি পাখি’র মতো।
শীতের অতিথি পাখি কোনো জলাশয়ে প্রচুর খাবারের সন্ধান এবং জীবনের নিরাপত্তা না পেলে আশ্রয় গ্রহণ করে না। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও ঠিক তেমনই। কোনো দেশে বিনিয়োগ করে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন এবং বিনিয়োগকৃত পুঁজির নিশ্চিত নিরাপত্তা না পেলে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। একজন বিদেশি বিনিয়োগকারী চাইলেই তাঁর বিনিয়োগ গন্তব্য পরিবর্তন করতে পারেন। আর কোনো দেশে যদি স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ না করেন, তাহলে সে দেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহী হন না। বিদেশি বিনিয়োগ সাধারণত দুইভাবে হতে পারে। প্রথমত, সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করা এবং দ্বিতীয়ত, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যৌথভাবে বিনিয়োগ করা। যৌথভাবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত বিশ্বাসযোগ্য স্থানীয় উদ্যোক্তা খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যদি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব থাকে, তাহলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কোনো দেশে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সেই দেশটির বিনিয়োগ পরিবেশ, আইনিকাঠামো, মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় খুব ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রণীত বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা প্রতিবেদনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন খুব একটা সুখকর নয়।
বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ ‘ইজ অব ডুয়িং বিজনেস’ সূচকে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশকে অত্যন্ত নিম্নমানের বলে মন্তব্য করা হয়। সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৬তম। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস সূচক প্রকাশ বন্ধ আছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ‘বিজনেস রেডি’ শীর্ষক একটি নতুন সূচক প্রকাশ করেছে। এতে ৫০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হয়েছে চতুর্থ সারিতে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার পরিবেশ এখনো উন্নত হয়নি।
বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ ভালো নয়, এটি নানাভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জিডিপি-প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট রেশিও ২৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অনেক দিন ধরেই জিডিপি-প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট রেশিও ২৩-২৪ শতাংশে ওঠানামা করছে। যেমন—২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি-প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট রেশিও ছিল ২৪.৯৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এটি ছিল ২৩.৭০ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি-প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট রেশিও আরো কিছুটা কমে দাঁড়ায় ২৩.৬৪ শতাংশ। নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনোভাবেই ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো যাচ্ছে না। গত সরকারের আমলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সরকারি খাতে বিনিয়োগ বেড়েছিল। নানা ধরনের মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করতে না পারার কারণে ঢালাওভাবে বিদেশি ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ঋণকৃত অর্থ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটে নেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই বিদেশি ঋণনির্ভর একটি দেশে পরিণত হতে চলেছে। বিগত সরকার আমলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার অতিক্রম করে যায়। অবস্থা এমন হয়েছে যে ভবিষ্যতে নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে পুরনো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।
বিদেশি বিনিয়োগ একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশি বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে চায়। কিন্তু বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির স্বল্পতা থাকায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তি খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ না হলে সে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় না। শিল্প-কারখানা গড়ে না উঠলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হলে একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে, যারা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেই একটি দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা গেলেই কেবল টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটানোর জন্যও বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। বিদেশ থেকে যে বিনিয়োগ আসে, তা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে যুক্ত হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ গঠনে পণ্য রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের পাশাপাশি সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ আহরিত হলে উদ্যোক্তারা তাঁদের দেশ থেকে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ নিয়ে আসেন। বিদেশি বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।
বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় দেশ হলেও এ ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন চোখে পড়ার মতো নয়। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, পৃথিবীতে এত দেশ থাকলে বিদেশি উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত কেন নেবেন? ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় গেটওয়ে। বাংলাদেশে রয়েছে ১৭ কোটিরও বেশি মানুষের বসবাস। বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে দু-তিনটি দেশ মিলেও ১৭ কোটি মানুষ নেই। বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কয়েক বছর আগের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিস্ময়কর উত্থান ঘটেছে। তিন দশক আগে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারের হার ছিল ১২ শতাংশ। এখন তা ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ভোগপ্রবণতা ও সামর্থ্য উভয়ই বেড়েছে। বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গমনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাঁরা বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁরা রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। এই রেমিট্যান্সের অর্থ দিয়ে লোকাল বেনিফিশিয়ারিরা নিজেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাচ্ছে। আগে শহরে যেসব বিলাসজাত সামগ্রী ব্যবহৃত হতো, এখন গ্রামে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন করে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করা হলে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে শুল্ক রেয়াত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন—ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা প্রদান করে। বলা হয়, বাংলাদেশে সস্তায় বিপুলসংখ্যক শ্রমশক্তির নিশ্চিত জোগান রয়েছে। এটি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার অন্যতম কারণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, সস্তা শ্রমিকের চেয়ে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত শ্রমিকের চাহিদা বেশি।
নানা ধরনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারছে না। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ১১৪ কোটি মার্কিন ডলার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ করতে সক্ষম হয়। ২০২২ সালে ১০২ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ৭১ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ করে। গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশ ১০ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এটি গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ। বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি গন্তব্য হওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগ তেমন একটা আসছে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা খাতের অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অভাব বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নির্বাচন যাতে গ্রহণযোগ্য এবং সুষ্ঠু হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর স্থানীয় ও বিদেশি উদ্যোক্তারা বর্ধিত মাত্রায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিত করা, যাতে একজন বিনিয়োগকারীর কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হতে না হয়।
লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়