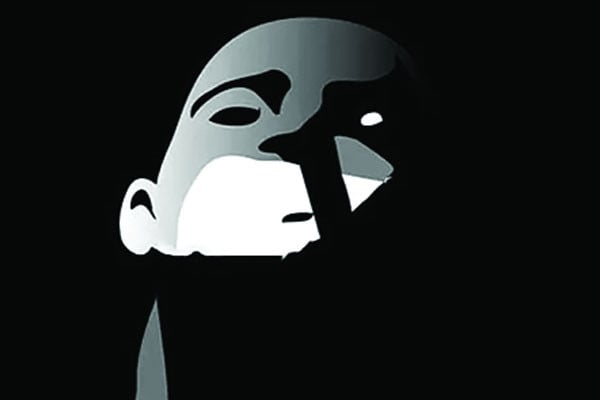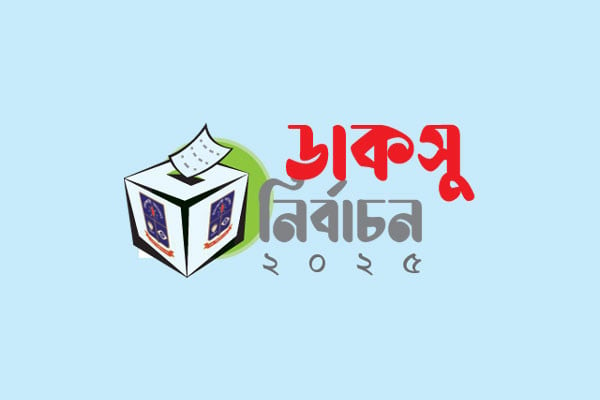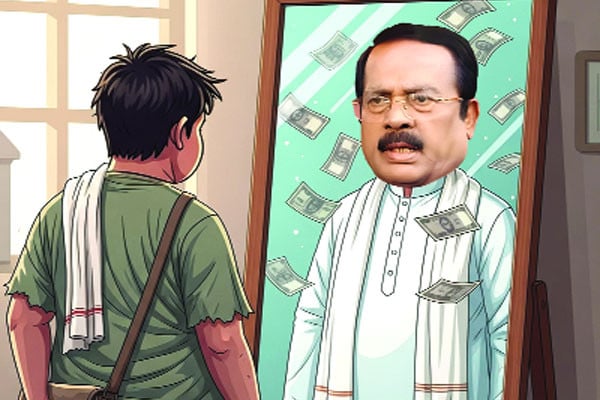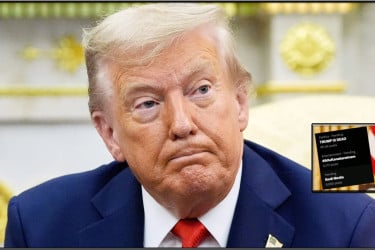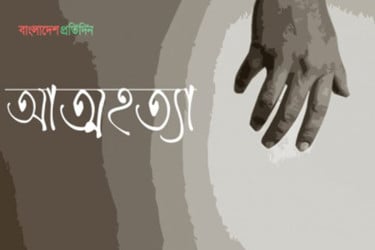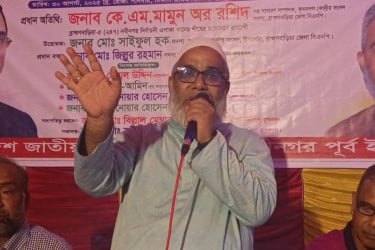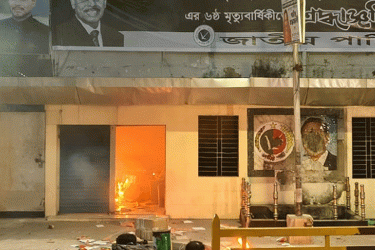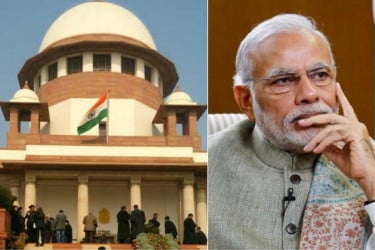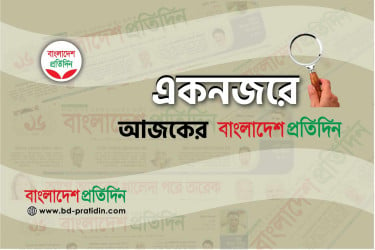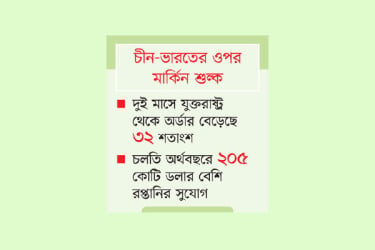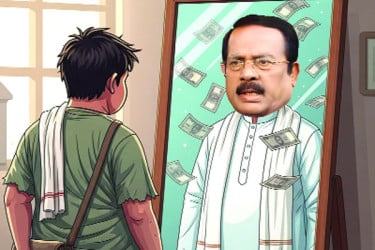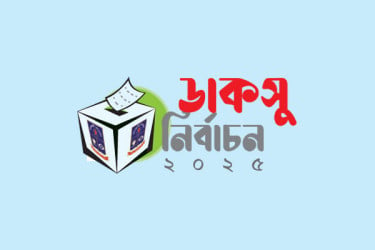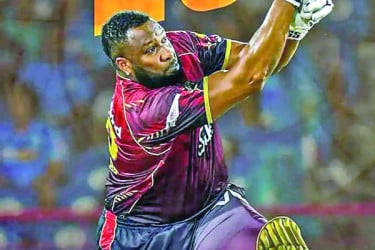জুলাই বিপ্লবের এক বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে, এক বছর পর সেই আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে যেন হাঁটছে বাংলাদেশ। জুলাই বিপ্লবের স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে মলিন হয়ে যাচ্ছে। এক বছর আগে যে ইস্পাতকঠিন ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঐক্য এবং সংহতিতে এখন ফাটলের ক্ষতচিহ্ন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে- জুলাই কি ব্যর্থ হতে চলেছে? জুলাই বিপ্লবের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈষম্যহীন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ। একটি কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা থেকে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। আর তা অর্জনের জন্য সবচেয়ে
প্রধান এবং প্রথম কাজ হলো গণতন্ত্রে উত্তরণ। জনগণের নির্বাচিত একটি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের পথে যেন কাঁটা বিছানো, পায়ে পায়ে নানারকম প্রতিবন্ধকতা। নির্বাচন নিয়ে যখনই কথাবার্তা শুরু হয়, তখনই দেশে শুরু হয় অস্থিরতা। গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে যেন ষড়যন্ত্রের জালে বন্দি করা হয়। ষড়যন্ত্র হচ্ছে চারপাশ থেকে। একটি ষড়যন্ত্র শেষ হতে-না হতেই আরেকটি নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হচ্ছে। যেন গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ বন্ধ হয়ে যায়, জুলাই বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জিত না হয়।
জুলাই বিপ্লবের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গণতন্ত্রের কথাই বলেছিলেন। তিনি সব রাজনৈতিক দল এবং অভ্যুত্থানের সূর্যসন্তানদের এক বাক্যে বলেছিলেন, জনগণ গত ১৫ বছর অধিকার বঞ্চিত হয়েছেন। জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল। কোনো মানুষ ভোট দিতে পারেনি। এটি ছিল স্বৈরাচারী সরকারের সবচেয়ে বড় অপরাধ। ক্ষমতা দখল করে তারা দেশে একটি লুণ্ঠনতন্ত্র কায়েম করেছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতার এক নজিরবিহীন ব্যবস্থাপনা। সেই ব্যবস্থাপনা থেকেই মুক্তি চেয়েছিল এ দেশের মানুষ। সেই ব্যবস্থাপনা থেকে মুক্তির পথ একটাই, তা হলো জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো এবং জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা। যেটি ড. মুহাম্মদ ইউনূস বারবার বলছেন। কিন্তু সে লক্ষ্যে আমরা গত এক বছরে আদৌ কি এগোতে পেরেছি?
অন্তর্বর্তী সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মূলত তিনটি কাজ করার জন্য। প্রথমত, জুলাই বিপ্লবের সময় যে গণহত্যা, নিপীড়ন, নির্যাতন সংঘটিত হয়েছিল তার অবাধ, সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন করা। এ বিচার যেন দ্রুত হয়, স্বচ্ছ হয় এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেন সে বিচার নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ওঠে।
দ্বিতীয়ত, সংস্কার। যেমন- নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কিছু জরুরি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রসঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য দরকার। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেন ভবিষ্যতে কোনো সরকার নিজের ইচ্ছামতো কুক্ষিগত করতে না পারে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেন দলের ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ইত্যাদি। রাষ্ট্র সংস্কারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন, যা সরকার বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।
অন্তর্বর্তী সরকারের তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আমরা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো ইঙ্গিত পাচ্ছি না। বরং জনগণের অধিকারের পথ যেন ক্রমশ বন্ধুর এবং জটিল হয়ে পড়ছে। গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রবল এক প্রতিপক্ষ যেন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।
দেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দাবি করেছে। যে তিনটি কাজ অন্তর্বর্তী সরকারের করার কথা, সে তিনটি কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। এক বছর রাষ্ট্র সংস্কার প্রশ্নে একটি অভিন্ন ঘোষণা প্রণয়নের জন্য যথেষ্ট সময়। কিন্তু এ নিয়ে যেন কালক্ষেপণের প্রতিযোগিতা চলছে।
গণহত্যার বিচারের বিষয়টি ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যার বিচারের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। এ বিচারকে তার আপন গতিতে চলতে দেওয়া উচিত। কিন্তু সারা দেশে শুরু হয়েছে মামলাবাণিজ্য। যে যার মতো যেভাবে পারছে মামলা করছে।
চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের পর এখন দেশে মামলাবাণিজ্য একটি রমরমা ব্যবসা। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য, ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাজেহাল করার জন্য, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার জন্য, এমনকি প্রতিবেশীকে শায়েস্তা করার জন্য হত্যা মামলা হচ্ছে। গত এক বছরে এসব মামলার তদন্ত হয়নি, বিচার তো দূরের কথা। প্রায় ১৬ হাজার মামলায় ১ লাখের বেশি আসামি হয়েছেন। অধিকাংশ আসামি নিরীহ। বাদী জানে না আসামি কে, আসামি বাদীকে চেনে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলাগুলো হয়েছে নানারকম মতলবে, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশায়। ফলে জুলাই গণহত্যার বিচারের বিষয়টি ক্রমশ একটি রাজনৈতিক খেলায় পরিণত হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ বিরক্ত। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি থেকে শুরু করে সাংবাদিক, সরকারি চাকরিজীবী থেকে শুরু করে নিরীহ শ্রমিক, মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মী কেউই মামলার তালিকা থেকে বাদ যাননি। মামলাবাণিজ্য বন্ধে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। মামলাবাণিজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে মব সন্ত্রাস। মব সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল, চাঁদাবাজি, দখলের সংস্কৃতি চলছে দেশজুড়ে।
দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়ংকর অবনতি ঘটেছে। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, লুটতরাজ এখন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অন্তর্বর্তী সরকার যেন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। তাদের যেন কিছুই করার নেই। এরকম একটি পরিস্থিতিতে সুযোগ নিচ্ছে গণতন্ত্রবিনাশী শক্তি। ফ্যাসিবাদী শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে নতুন করে। যখনই এ ধরনের সহিংসতা ঘটছে, তখনই শুরু হচ্ছে ‘ব্লেইম গেম’।
সর্বশেষ গত ৯ জুলাই বুধবার মিটফোর্ডের ঘটনাটির কথাই উল্লেখ করা যায়। একজন রাজনৈতিক কর্মী সোহাগকে নির্মমভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এ ঘটনা যখন ঘটছিল তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোথায় ছিল? খুব কাছেই আনসার ক্যাম্প ছিল, সেই আনসার ক্যাম্পের আনসাররা কী করল? ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দীর্ঘক্ষণ ধরে এ বর্বরতা ঘটেছে। অথচ সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন তামাশা দেখেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এগিয়ে আসেনি। সাধারণ নাগরিকরাও সাহসে বুক বেঁধে এই নৃশংস পৈশাচিক ঘটনাকে রুখতে এগিয়ে আসেনি। ফলে একটি মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশ। এ ঘটনার পরপরই বেশ কিছু রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পরপরই জুলাই বিপ্লবের যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি তার মধ্যে সুস্পষ্ট ফাটল দেখা দিয়েছে। একটি পক্ষ অন্যপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য যেন মাঠে নেমেছে।
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ একে অন্যের সমালোচনা করতেই পারে। এটাই গণতান্ত্রিক রীতি। কিন্তু এ সমালোচনা যেন শিষ্টাচারবহির্ভূত না হয়, অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ না হয়, সে বিষয়টি সবার লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো সোহাগ হত্যার পর গত রবিবার থেকে রাজনীতির মাঠে যেন তৃতীয় শক্তির অদৃশ্য ছায়া দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ সৃষ্টি করে কেউ কেউ পানি ঘোলা করে সেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো- এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ যারাই করুক না কেন, তারাই অপরাধী। তাদের রাজনৈতিক কোনো পরিচয় নেই। অপরাধীকে শুধু অপরাধী হিসেবে দেখতে হবে। কিন্তু সেটি না করে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে তার দায়দায়িত্ব একটি রাজনৈতিক দলের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা এক ধরনের রাজনৈতিক কূটকৌশল। এ ধরনের রাজনৈতিক কূটকৌশল দেশের জন্য ভালো নয়, গণতন্ত্রের জন্য অশুভসংকেত। এটিই হলো বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া।
আমরা লক্ষ্য করেছি, এ ঘটনাটি প্রথম নয়। জুলাই বিপ্লবের পর এ ধরনের বেশ কিছু মব সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। অনেকেই এ ধরনের মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তোফাজ্জলের কথা ভুলে যাইনি। ধানমন্ডিতে একজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে মব বাহিনী আক্রমণ করেছিল। পুলিশ সেখানে তাকে রক্ষা করেছিল। এ ধরনের ঘটনা যখন নিরন্তর ঘটতে থাকে এবং সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন তার বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তখন এ ঘটনাগুলো বাড়তেই থাকবে। আর তারই একটি ধারাবাহিকতা হলো সোহাগ হত্যাকাণ্ড। এ হত্যাকাণ্ডকে কখনই একটি রাজনৈতিক রং দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ রাজনৈতিক রং দেয় সেটি এক ধরনের ষড়যন্ত্র। আর এ ষড়যন্ত্র হচ্ছে খুব পরিকল্পিতভাবে। এমন এক সময় এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে, যে সময় লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকের মধ্য দিয়ে সরকার এবং দেশের রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুত গণতন্ত্রে উত্তরণের ব্যাপারে একটি সমঝোতায় পৌঁছে। প্রধান উপদেষ্টা এবং তারেক রহমান একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে সারা দেশে স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল। কিন্তু সে অনুযায়ী দেশে ফিরে প্রধান উপদেষ্টা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে দৃশ্যমান হয়নি। এ নিয়ে যখন আবার রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা আলাপ-আলোচনা শুরু হলো, তখন প্রধান উপদেষ্টা ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিলেন।
লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো- সোহাগ হত্যাকাণ্ড এ ঘটনার পরপরই ঘটেছে। তাহলে কি নির্বাচনের সঙ্গে মব সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক রয়েছে? প্রধান উপদেষ্টা যখনই ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতির ঘোষণা দিলেন, তার পর থেকে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়ংকর অবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় মব সন্ত্রাস আবার বেড়ে গেছে। এ মব এবং সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলকে দোষারোপ করছে। রাজনীতিতে আবার একটি মাইনাস ফর্মুলা নিয়ে গুঞ্জন ও আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। তার মানে কী, বাংলাদেশে কোনো কোনো মহল আছে যারা চান না দেশে নির্বাচন হোক?
আমাদের জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘদিন ধরে আলাপ-আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করছে। এত দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ করা আদৌ দরকার কি না, সে প্রশ্ন উঠেছে। তাহলে তারা কি নির্বাচন পিছিয়ে দিতে চান? দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন ছড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশে কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে চান কেউ কেউ? সে প্রশ্ন এখন সামনে উঠে এসেছে। গণতন্ত্র যেন ষড়যন্ত্রের জালে আবার বন্দি হয়ে যাচ্ছে।