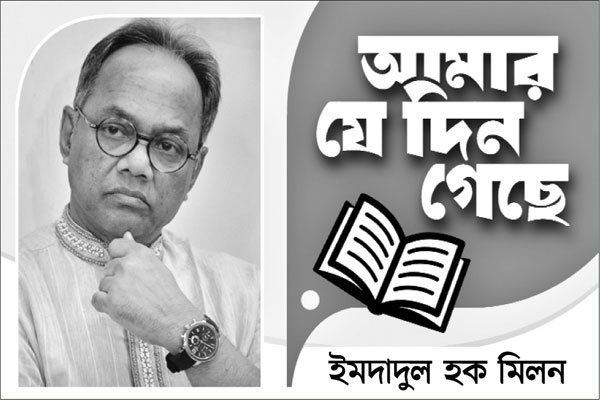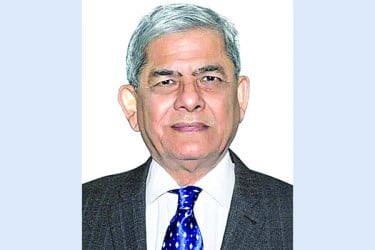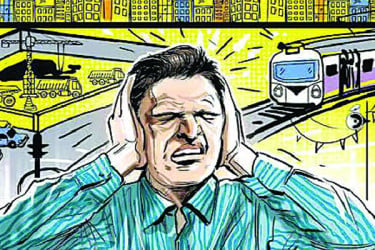চারজন তরুণ লেখক দাঁড়িয়ে আছেন শহীদ মিনারের সামনে। ২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলা, ১৯৭২ সাল। বুলবুল চৌধুরী, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সিরাজুল ইসলাম, ফিউরি খন্দকার। আমি আর আমার বন্ধু মুকুল মিলে একটা একুশে সংকলন বের করেছি। দুজনই এসএসসির ক্যান্ডিডেট। ’৭১ সালে পাকিস্তানিরা একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। সেই পরীক্ষা আমরা দেইনি। সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এপ্রিলের দিকে পরীক্ষা হবে। প্রিপারেশন সেভাবে নেওয়া হচ্ছে না। স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা আছি গভীর আনন্দে। মুকুলদের একটা প্রেস আছে লক্ষ্মীবাজারে। ‘মুকুল প্রেস’। সে বছর পাড়া-মহল্লা থেকে, বিভিন্ন ক্লাব আর সংগঠন থেকে একুশে সংকলন প্রকাশের হিড়িক পড়েছে। মুকুল আর আমি ঠিক করলাম, আমরাও একটা সংকলন করব। প্রেস কাগজ টাকা-পয়সা সবই মুকুল সামলাবে। আমি যেহেতু ছোটবেলা থেকেই বইপত্র পড়ি, সাহিত্যের খোঁজখবর রাখি, গল্প-উপন্যাস যা-ই হাতের কাছে পাই, গোগ্রাসে পড়ি। আমার আইডিয়াতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, সংকলনটা হবে শুধু গল্পের। ওসব ব্যাপারে মুকুলের কোনো কথা নেই। গল্পের সংকলনই হবে। গল্প জোগাড়ের ভার আমার ওপরে। গেন্ডারিয়ার রজনী চৌধুরী রোডে আমাদের বাসার প্রায় মুখোমুখি বাসায় থাকতেন তরুণ কবি মাহমুদ শফিক। নারায়ণগঞ্জে থাকেন শফিকের বন্ধু মুজিবুল হক কবীর। কবীরের বাবা সিরাজুল হক সাহেব ‘কালেরপাতা’ নামে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বের করেন। শফিকের সঙ্গে ’৭২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই কবীরদের সঙ্গে আড্ডা দিতে নারায়ণগঞ্জে যেতাম। আমি সংকলন বের করব শুনে, সংকলনের একটা নাম দিলেন শফিক। ‘কম্পাস’। কবীর বলল, ‘গল্প লেখক বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। বুলবুলের কাছে গেলে তিনি গল্প জোগাড় করে দেবেন। বুলবুল চৌধুরীদের বাড়ি নাকি বাংলাবাজারের ওদিকেই।’
কে যেন বলল, বাংলাবাজার থেকে ‘জোনাকী’ নামে একটি মাসিক সিনেমা পত্রিকা বেরোয়। বুলবুল সেই পত্রিকাতে কাজ করেন। এক বিকালে গেলাম বুলবুলকে খুঁজতে। ‘জোনাকী’র সম্পাদক আবদুল মতিন আসলে বইয়ের ব্যবসায়ী। প্রকাশনা সংস্থা আছে। প্রেসও আছে দোকানের কাছেই। সংস্কৃতিমনা মানুষ। অত্যন্ত সজ্জন, বিনয়ী, হাসিমুখের ভদ্রলোক। বাংলাবাজারের প্রত্যেকেই তাঁকে চেনে, সম্মান করে। এক মিনিটও লাগল না ‘জোনাকী’ অফিস বের করতে। গিয়ে দেখি অফিসটা আসলে বইয়ের গোডাউন। ঘরটা বেশ বড়। মাথার ওপর কাঠের পাটাতন দেওয়া। সেখানে ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির কাছে দু-তিনটি টেবিল চেয়ার পাতা। এক টেবিলে বসে আছে এক যুবক। মাথার লালচে চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে। চোখে ভারী লেন্সের চশমা। পরনের শার্ট-প্যান্ট দেখে বোঝা যায় পোশাকের ব্যাপারে তিনি একটু বেখেয়ালি। তাঁর এক হাতে সিগারেট জ্বলছে। আরেক হাতের কাছে চায়ের কাপ। বোধহয় চা শেষ হয়ে গেছে। চায়ের কাপেই সিগারেটের ছাই ফেলছেন। অতি নিবিষ্ট মনে লেখা এডিট করছেন। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। চোখ তুলে তাকালেন। গায়ের রং সামান্য ফ্যাকাশে ধরনের ফর্সা। চেহারা আদিবাসীদের মতো। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কবীরের রেফারেন্সে মনোবাসনা জানালাম। সামনের চেয়ারে আমাকে বসিয়ে চায়ের অর্ডার দিলেন বুলবুল। সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হলো বুলবুলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। প্রকৃত অর্থে কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বুলবুল চৌধুরীই আমার প্রথম বন্ধু। সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে বুলবুল আমার সংকলনের লেখা জোগাড় করে দিলেন। নিজেও আগ্রহ নিয়ে একটি গল্প লিখলেন। সেই গল্পের নাম এখনো আমার মনে আছে। ‘ঘর শালিকের ঘর’। ভারি মিষ্টি ধরনের গল্প। পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সিরাজুল ইসলামের গল্পও জোগাড় করে দিলেন। আরও কার কার যেন লেখা। ওই বয়সেই মুকুল খুব পাকা। মুকুলের বাবা গেছেন মানিকগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে। প্রেসের একমাত্র কর্মচারীটির সঙ্গে মুকুল প্রেসেই থাকে। প্রেসের সব রকমের কাজের ফাঁকে লোকটি মুকুলকে রান্না করে খাওয়ায়। আমিও প্রায় রাতে গিয়ে থাকি ওর সঙ্গে। সে অতি চটপটে বুদ্ধিমান ছেলে। নিজেও রান্নাবান্না করতে পারে। টাইপ কেস থেকে টাইপ তুলে তুলে কম্পোজ করতে পারে। কাঠের গ্যালিতে পৃষ্ঠার মাপে টাইপ সাজিয়ে মেশিনে সেট করে ছাপার কাজটাও পারে। দেখে দেখে শিখেছে।
দিনের বেলা প্রেসের স্বাভাবিক কাজ চলে। সংকলন বের করার জন্য রাতে গিয়ে আমি মুকুলের সঙ্গে থাকি। বাবা যেন না জানতে পারেন, সেভাবে মুকুল প্রেসের কর্মচারীটি ম্যানেজ করেছে। প্রেসের জমে থাকা কাগজ থেকে সেই লোক কাগজেরও ব্যবস্থা করে দিল। প্রচ্ছদের ব্লক ইত্যাদি সবই মুকুল তাকে দিয়ে করিয়ে ফেলল। যথাসময় সংকলন বেরিয়ে গেল। মুকুল আর আমি কাপড়ের থলিতে গাদাগাদি সংকলন নিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল বেলাতেই বিক্রি করতে বেরিয়ে গেলাম। দুজন দুদিকে। আমি গেলাম স্টেডিয়ামের দিকে, মুকুল গেল ঢাকা ইউনিভার্সিটির দিকে। দুজনের হাতেই বড় হরলিক্সের কৌটা। মুখ ঝালা করে আটকানো। মুখের মাঝখানে মাটির ব্যাংকের মতো করে কাটা। সংকলনের কোনো নির্দিষ্ট দাম নেই। যে যা দেবেন, তা ওই কাটা মুখ দিয়ে কৌটায় ফেলে দেবেন। টাকা-পয়সা আমরা হাত দিয়ে ধরব না। মনে আছে, সংকলনের খরচ তুলেও আমরা কিছু লাভ করেছিলাম। আর সেই সংকলন বিক্রি করতে গিয়েই চারজন তরুণ লেখককে পেয়ে গেলাম একসঙ্গে। বুলবুলকে চিনি, অন্য সবার নাম শুনেছি। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের লেখা পড়েছি। সেই প্রথম চাক্ষুষ দেখা। খুবই শিহরিত হয়েছিলাম। সেদিন কে জানত, আমিও একদিন তাঁদের পথেই হাঁটব। আমার লেখালেখির জগৎ হয়ে উঠবে ‘কথাসাহিত্য’। চারজনের হাতেই সিগারেট। সুকান্ত একটু উচ্চস্বরে কথা বলে। সিরাজের চোখেও চশমা। মেধাবী ধরনের লাজুক ছেলে। ফিউরি কথায় কথায় মিষ্টি করে হাসে। আমাকে পাত্তা দেওয়ার তাঁদের কোনো কারণ নেই। চারজন তুখোড় তরুণ লেখকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তাতেই আমি মুগ্ধ। সেই সময়কার তরুণ লেখকদের মধ্যে এ চারজনই বিশিষ্ট। ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠতে লাগল। এক দিন দুই দিন পরপরই বাংলাবাজারে চলে যাই বুলবুলের কাছে। আমি তখনো সিগারেট ধরিনি। বুলবুলের সঙ্গে বসে চা খাই। কখনো ‘জোনাকী’ অফিসে, কখনো তিনি আমাকে নিয়ে যান বাংলাবাজার পোস্ট অফিসের উত্তর-পশ্চিম পাশের বটতলার রেস্টুরেন্টটিতে। চা শিঙাড়া খাওয়ান। কথাসাহিত্যের নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তখনই বিখ্যাত কবি নির্মলেন্দু গুণ আর আবুল হাসান তাঁর বন্ধু। ওঁদের গল্প করেন। বলতে গেলে আমি বুলবুলের ন্যাওটা হয়ে গেলাম। প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বুলবুলের কথা বলার ধরন কারও সঙ্গে মেলে না। শব্দচয়ন অন্যরকম। গলার স্বর ভারী। যেন বুকের অনেক ভিতর থেকে কথা বের হয়। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনি।
এক বিকালে বুলবুল নিয়ে গেলেন নিউমার্কেটে। সেখানে ‘মনিকো’ নামের রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিতে আসেন তরুণ লেখকরা। সুকান্ত আর সিরাজ আসে নিয়মিত। ফিউরিও আসে মাঝে মাঝে। সুকান্ত ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র। সিরাজ বুয়েটের। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ফিউরি পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। এঁদের মধ্যে বুলবুল বয়সে বড়। তিনি বিএ পাস করে ওয়াপদায় কেরানির চাকরি করেন। পত্রিকা সম্পাদনার নেশা থেকে পার্টটাইম করেন ‘জোনাকী’তে। বাবা ভালো ব্যবসায়ী। গেন্ডারিয়া থেকে কলুটোলা কাঠেরপুল পেরিয়ে ডালপট্টির মোড় ছাড়িয়ে সোজা প্যারিদাস রোডের দিকে রওনা দিলে হাতের ডানদিকের গলিটির নাম পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জি লেন। সেই গলিতে গাড়ি ঢোকে না। রিকশা ঢোকে। সেখানে বুলবুলদের দোতলা বাড়ি। বুলবুলের সঙ্গে তারপর যাওয়া-আসা শুরু করলাম মনিকো রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিতে। সুকান্ত আর ফিউরির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায়, তেমনটা হলো না। যদিও অনেক পরে ফিউরির সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছিল তুই-তুকারি। বুলবুল আর সুকান্তের সঙ্গে আপনি আপনি, সিরাজের সঙ্গে তুই। সিরাজ ঢাকার ছেলে। দয়াগঞ্জের ওদিককার বেগমগঞ্জ লেনে বাড়ি। বুলবুলের সঙ্গে সঙ্গে সিরাজও হয়ে উঠল আমার প্রায় সারাক্ষণের বন্ধু। বুয়েটের হলে থাকে। ছুটিছাটায় বেগমগঞ্জের বাড়িতে আসে। সিরাজের বন্ধু হেলাল আহমেদদের বাড়িও একই গলিতে। হেলালের একটা চোখে খুত ছিল। জগন্নাথে বাংলায় পড়ে। সাহিত্যের তীক্ষè পাঠক। সিরাজের কারণে হেলালের সঙ্গে পরিচয় হলো। ওদের আরেক বন্ধুর নাম আরিফ। সে-ও সাহিত্যপড়া যুবক। পরিচয় হলো। সিরাজদের গলিতে ঢোকার পর আরেকটা গলি চলে গেছে ডানদিকে। সেখানে থাকেন আরেক তরুণ লেখক। তাঁর নাম নুরুল করিম নাসিম। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। ওদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কথাসাহিত্যের বিভিন্ন দিককার একেকটি দরজা আমার সামনে খুলে যাচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যের কোন কোন গল্প-উপন্যাস পড়া উচিত, সেসবের নির্দেশনা পাই ওদের কাছ থেকে। ওরা কেউ কেউ কোনো কোনো বই পড়তে দেয়। নিজেও জোগাড় করি কিছু। গেন্ডারিয়ার ‘সীমান্ত গ্রন্থাগার’ থেকে বই আনি। নিজের অজান্তেই যেন একটু একটু করে আমি ঢুকে যাচ্ছিলাম কথাসাহিত্যের জগতে।
বুলবুল আমাকে একবার ওঁদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ঢাকার কাছেই, কালীগঞ্জে। বেশ বড় বাড়ি। বাড়ির সামনে পুকুর। অনেক গাছপালা। গ্রামের এক পাশে খ্রিস্টানপাড়া। বুলবুলের বেশ কয়েকজন বন্ধু আছেন গ্রামে। গভীর আনন্দে কাটল তিন-চারটা দিন। বুলবুলের একটা প্রিয় বিষয় মাছ। মাছ ধরা থেকে শুরু করে মাছের টুকটাক অনেক কিছু তাঁর জানা। ‘মাছ বৃষ্টির দিন’ নামে ভারি সুন্দর একটা গল্প আছে তাঁর। গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা গল্প-উপন্যাসে বুলবুল খুবই মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘টুকা কাহিনী’, ‘নিরবধিকাল’, ‘জল কাদার প্রতিপালক’ এরকম বহু চমৎকার গল্প লিখেছেন। তাঁর ‘ইতু বউদির ঘর’ উপন্যাসটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক সবই পেয়েছেন। অকালেই চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। ফিউরিও চলে গেল। কোন মনোকষ্টে যে হেলাল আত্মহত্যা করেছিল তা আমি কখনো জানতে পারিনি। বুলবুল সেবার একদিন অদ্ভুত একটা কাজ করল। পুকুরে ডুব দিয়ে কেমন করে হাতিয়ে হাতিয়ে মাছ ধরতে হয়, আমাকে তা দেখাবে। আমি যে কিশোর বয়সে গ্রামে থেকেছি এবং নানাভাবে মাছ ধরার বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে, সে কথা আর বললাম না। নিজেদের পুকুরপাড়ে বুলবুল আমাকে একটা চেয়ার দিয়ে বসালেন। নিজে নেমে গেলেন পুকুরে। চশমা মুহূর্তের জন্যও খোলেন না। বিস্মিত হয়ে দেখি, চশমা পরেই মাছ ধরার জন্য ডুব দিচ্ছেন। অবিরাম ডুবোডুবি করে একটা মাছও ধরতে পারলেন না। আমি চেয়ারে বসে তাঁর কাণ্ড দেখে হাসছি। অনেকক্ষণ পর উঠে এলেন। এতক্ষণ সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারেন না। ভেজা হাতেই সিগারেট ধরালেন। মাছ ধরতে না পারার ব্যর্থতার চিহ্নও নেই মুখে। সিগারেট টানতে টানতে নির্বিকার গলায় বললেন, ‘মাছগুলো বড় চতুর’। আমি বললাম, ‘কিন্তু চশমা পরে ডুব দিলেন কেন?’ বুলবুলের নির্বিকার জবাব, ‘চশমা ছাড়া তো কিছু দেখতে পাই না। পানির তলার মাছ দেখব কেমন করে? চশমা ছাড়া আমি আসলে স্বপ্নও দেখতে পারি না। এ জন্য চশমা পরে ঘুমাই।’ আমি হাসব না কী করব, বুঝতেই পারছিলাম না। জাতীয় প্রেস ক্লাবে বুলবুলের জন্মোৎসব হচ্ছে। আমি বিশেষ অতিথি। তাঁকে নিয়ে কথা বলার একপর্যায়ে তাঁর ওই মাছ ধরার ইতিহাস আর চশমা কাহিনি বললাম। শ্রোতারা হাসতে হাসতে মরে। বুলবুলকে কিছুটা মাথায় রেখে সেই মাছ ধরার ঘটনার বহু বছর পর আমি একটা কিশোর চরিত্র তৈরি করেছি। প্রধান চরিত্রটির নাম বুলবুল চৌধুরী। আদরের ভাগ্নেটি তাঁর নাম সংক্ষেপ করেছে। ‘বুমা’। কত কত স্মৃতি আমার এই প্রিয় বন্ধুটিকে নিয়ে। কত ঋণ তাঁর কাছে। সাহিত্যের কত শিক্ষা।
অল্প বয়সেই গল্প-উপন্যাস লিখে সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় বেশ একটা সম্মানের জায়গা তৈরি করলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস থেকে শুরু করে বড় বড় কথাসাহিত্যিকরা, এমনকি কবিরাও সুকান্তর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ‘দৈনিক সংবাদ’-এর কোনো এক বিশেষ সংখ্যায় ছোট্ট একটি উপন্যাস লিখলেন সুকান্ত। ‘দেশ গেরামের মনিষ্যী’। আবুল হাসনাত ভাই অত্যন্ত যত্নে ছাপলেন সেই লেখা। পড়ে আমরা মুগ্ধ। ‘রাজধানী’ নামে গল্প লিখলেন একটি লিটল ম্যাগাজিনে। দারুণ। ‘জটাধারীর বান্নি’ নামের গল্পটিও অসাধারণ। তারপর সুকান্ত চলে গেলেন কলকাতায়। ডাক্তারি পেশায় অতি মনোযোগ দেওয়ার ফলে লেখালেখি থেকে অনেকটা সরে গেলেন। হঠাৎ হঠাৎ ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্প লেখেন। ‘ফিরিয়ে নেওয়া মুখ’ নামে পুজো সংখ্যায় উপন্যাসও লিখলেন। লেখা বদলে গেছে। আগের সেই সুকান্তকে আমি আর খুঁজে পেলাম না। ২০১২ সালে ‘আইআইপিএম সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার’ গ্রহণ করতে কলকাতায় গেছি। উঠেছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্বশুরপক্ষের রেস্ট হাউসে। সুকান্ত একদিন দেখা করতে এলেন। দীর্ঘক্ষণ পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করলাম দুজনে। সেদিনই জানতে পারলাম, কলকাতার অনেক বড় বড় লেখক কবি তাঁর রোগী। যেমন বিমল কর। সাহিত্য থেকে বলতে গেলে সরেই গেছেন সুকান্ত।
সিরাজুল ইসলামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সত্তরের দশকে তুখোড় তরুণ লেখক সিরাজুল ইসলাম। তখনকার দিনে দুজন সম্পাদকের হাত দিয়ে লেখা ছাপা হলে তরুণ লেখকরা লেখক হওয়ার স্বীকৃতি পেতেন। একজন ‘দৈনিক বাংলা’র সাহিত্য সম্পাদক কবি আহসান হাবীব, অন্যজন ‘দৈনিক সংবাদ’-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত। আহসান হাবীব দু-তিন সপ্তাহ পর পরই সিরাজের গল্প ছাপতেন। হাসনাত ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই। কত গল্প সিরাজের, ‘রাণী আসছেন’, ‘যাত্রার নায়ক’ ইত্যাদি। দিনে দিনে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল সে। অনেকটা নিঃশব্দে সরে গেল লেখালেখি থেকে। আমার এত প্রিয় বন্ধু! কত কত বছরের দিন-রাত কেটেছে সিরাজের সঙ্গে। শিল্পী কাজী হাসান হাবীবকে ঘিরে আমাদের পাঁচ বন্ধুর আলাদা একটা দল হয়েছিল। হাবীব, সিরাজ, মুহাম্মদ জুবায়ের, ফিরোজ সারোয়ার আর আমি। অতি অল্প বয়সে ক্যান্সারে চলে গেলেন হাবীব। জুবায়ের চলে গেল আমেরিকায়। তাকেও ছিনিয়ে নিল ক্যান্সার। ফিরোজ সারোয়ার এক সময় ছড়া লিখতেন। ‘একা’ নামে সুন্দর একটা গল্পও লিখেছিল ‘সংবাদ’-এর সাহিত্য পাতায়। সে চলে গেল বাংলা একাডেমিতে চাকরি করতে। লেখালেখির কলমটা আর ছুঁয়ে দেখল না। অনেক বছর পর সিরাজ আবার টুকটাক লিখতে শুরু করল। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো গল্প, স্মৃতিগদ্য কোনো কোনো কাগজে বেরোয়। একাত্তরে সে মাঝে মাঝে বুয়েটের হলে থাকত। সেই অবরুদ্ধ সময় নিয়ে চমৎকার একটি উপন্যাস লিখেছে, ‘গুহা’। ‘বেঙ্গল পাবলিশার্স’ থেকে বইটা বেরিয়েছে। পড়ে আমি মুগ্ধ। খুব ভালো লেগেছে আমাদের সেই পুরনো বন্ধু, এখন কলকাতার বাসিন্দা সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় সিরাজের বইটির সুন্দর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আমার এই বন্ধুদের কথা যখনই ভাবি, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দীর্ঘ একটি সময়ের কত টুকরো টাকরা স্মৃতি। কত দিন, কত রাতের কথা, কত আনন্দের কথা, তুমুল হইহল্লার কথা। চোখের পলকে যেন কেটে গেল জীবনের অনেকটা সময়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষায় বলতে হয়- ‘সেই সুখের দিন কে আমায় ফিরিয়ে দেবে’।
লেখক : কথাসাহিত্যিক ও প্রধান সম্পাদক, কালের কণ্ঠ