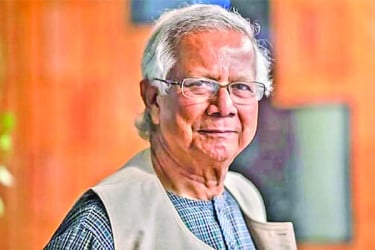জিন্দাবাহারের সে-ই বাড়ির জীবনটি ছিল বড় একঘেয়ে। এই একঘেয়ে জীবনের ভিতর হঠাৎ হঠাৎ ঘটত কোনো আনন্দের ঘটনা। দু-তিন মাস পর পর আব্বা আমাদের সবাইকে নিয়ে ছুটির দিনে সিনেমা দেখতে যেতেন। সে-ই সিনেমা দেখতে যাওয়া হতো সাধারণত ইভিনিং শোতে। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা। সেদিন দুপুরের খাওয়ার পর থেকেই প্রস্তুতি শুরু হতো আমাদের। আনন্দ উত্তেজনায় একেকজন ফেটে পড়ছি। আমার উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি। সাত-আট বছর বয়সেই গান-সিনেমার বই এসব আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। সিনেমা দেখতে যাওয়া হতো সাধারণত মাসের প্রথম সপ্তাহে। আব্বা বেতন পাওয়ার পর। ষাটের দশকের গোড়ার দিককার কথা। তখন পূর্ব পাকিস্তানেও ভারতীয় বাংলা সিনেমার খুবই রমরমা অবস্থা। উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা দেখার জন্য হল ভেঙে পড়ত। মধ্যবিত্ত বাঙালিরা নিয়মিত সিনেমা দেখতেন। পূর্ব পাকিস্তানে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে এ দেশের সিনেমা। কী সুন্দর নাম সিনেমাগুলোর। ‘কখনো আসেনি’, ‘কাঁচের দেয়াল’ ‘এ দেশ তোমার আমার’। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে যুক্ত হচ্ছেন মেধাবী সব পরিচালক, কলাকুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী। ভারতীয় হিন্দি সিনেমা আর পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সিনেমারও দর্শক ছিল অনেক। বিশেষ করে ঢাকার আদি বাসিন্দারা উর্দু-হিন্দি সিনেমার পোকা ছিলেন। সিনেমার গানগুলো তরুণদের মুখে মুখে ফিরত। ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে ‘ষোলওয়া সাল’ নামের একটি হিন্দি সিনেমা খুব জনপ্রিয় হলো। সে-ই সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হেমন্তের কণ্ঠে ওই সিনেমার ‘আয় আপনা দিল তো আওয়ারা’ গানটি জনপ্রিয়তায় নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল। রাস্তাঘাটে বেরোলেই তখনকার তরুণদের মুখে এই গান শোনা যায়। কোনো কোনো দোকানে রেডিও আছে। সেসব রেডিওতে এই গান বাজে। আমাদের বাড়ির পাশের লালুদের বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল। দুপুরের পরপর প্রায়ই গ্রামোফোনে হেমন্তের ওই গানের রেকর্ড বাজানো হতো। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বিক্রমপুরের কাজির পাগলা এ টি ইনস্টিটিউশনে পড়েছি আমি। সে-ই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন ‘উয়ারি’ গ্রামের রাধু কর্মকার। এই রাধু কর্মকার পরবর্তী জীবনে রাজকাপুরের ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করতেন। বাঙালি কণ্ঠশিল্পী আর অভিনেতারা তখনকার বোম্বাই জয় করে ফেলেছিলেন। শচীন দেববর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হিন্দিতে হলেন হেমন্তকুমার, সলিল চৌধুরী, মান্না দে, গীতা দত্ত, অভিনয় ও গানে কিশোর কুমার, তাঁর বড় ভাই নায়ক অশোক কুমার ব্যাপক জনপ্রিয়। সংগীত পরিচালক ও সুরকার হিসেবে শচীন দেববর্মণ আকাশছোঁয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হলেন দুই ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়। ‘নাগিন’ সিনেমার সংগীত পরিচালনা করলেন। গানে সুরারোপ করলেন। তাঁর সুরে লতা মঙ্গেশকার গাইলেন, ‘মেরা মান দোলে, মেরা তান দোলে’ সর্বকালের জনপ্রিয় হিন্দি গানগুলোর একটি হয়ে গেল। আর বাদ্যযন্ত্রের যে ব্যবহার এই গানটিতে করা হলো সেই বাজনা এই উপমহাদেশে কিংবদন্তি হয়ে গেল। যে বিন বাজিয়ে সাপ ধরে বেদেরা, সে-ই বিনের অসাধারণ ব্যবহার হলো এই গানে। অনেকের মনে সে-ই বিনের সুর এখনো দোলা দেয়। ‘নাগিন’-এ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেও গাইলেন ‘কাশি দেখা, মাথুরা দেখা’। এই গানও তুমুল জনপ্রিয় হলো। ‘ষোলওয়া সাল’ সিনেমার ‘আয় আপনা দিল’-এ মাউথ অর্গানের খুব সুন্দর ব্যবহার হয়েছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানের স্মার্ট তরুণদের মধ্যে মাউথ অর্গান বাজানো একটা বিশেষ গৌরবের ব্যাপার ছিল। জিনিসটার অন্য নাম ‘হারমোনিকা’। এই মাউথ অর্গানে দুটো গানের সুর খুব বাজানো হতো। একটা হেমন্তের ‘আয় আপনা দিল’, অন্যটি শ্যামল মিত্রের একটি বাংলা গান, ‘নাম রেখেছি বনলতা যখন দেখেছি’। শ্যামলের গানটা বাজারে এসেছিল আরও পরে।
আমার মায়ের একটা গ্রামোফোন ছিল। আমরা বলতাম ‘কলের গান’। নানা কলকাতা থেকে মেয়ের জন্য কিনে এনেছিলেন। জিনিসটা ছিল বিক্রমপুরের মেদেনীমণ্ডল গ্রামে, আমার নানাবাড়িতে। জিন্দাবাহারের বাসার আগে, সম্ভবত আমার বড় ভাইটি মাত্র জন্মেছে, তখন রোকনপুরে ছিল আমার মায়ের একমাত্র মামার ভাড়া করা বাড়ি। ওই বাড়িতেই মাকে নিয়ে থাকতেন আব্বা। আমার আপন নানাকে আমরা দেখিনি। মায়ের ওই মামাই আমাদের নানা। তাঁর ছেলেমেয়েরাই আমাদের মামা-খালা। বড় মামাটির নাম টুনু। পরে গেণ্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডে আমার নানা বাড়ি করেন। জিন্দাবাহার থেকে আমরা কখনো কখনো সে-ই বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। বাড়িটাকে আমরা বলতাম ‘টুনু মামাদের বাড়ি’। আমার মায়ের মামাতো বোন বিনা আমার বয়সি। সে-ই ছেলেবেলা থেকে এই খালাটি আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে আমেরিকার ফ্লোরিডাতে থাকে। একবার বিনা খালার ফ্লোরিডার বাড়িতে গিয়ে দিন বিশেক আমি ছিলাম।
আমার মায়ের কলের গানটা ছিল রোকনপুরের ওই বাড়িতে। জিন্দাবাহারের বাসায় আসার সময় কলের গানটা নানার কাছেই রয়ে গিয়েছিল। আর কখনো ফিরিয়ে আনা হয়নি। শুধু এক বাক্স রেকর্ড ছিল আমার মায়ের কাছে। আমি শিশু বয়স থেকেই গানপাগল। যে গান শুনতাম সেটাই চিৎকার করে গাইবার চেষ্টা করতাম। রেকর্ডগুলো মাঝে মাঝে বের করে হাতাতাম। সে-ই কলের গান মা আর কোনো দিন তাঁর মামার কাছ থেকে ফেরত আনেননি। আমি খুব চাইতাম মা ওটা ফিরিয়ে আনুক। মা আনেননি। আব্বা একবার আমাদের যাত্রা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মা-আব্বার সঙ্গে আমরা সব ভাইবোন। তখনো পর্যন্ত ছয়জন ভাইবোন। সঙ্গে পুলিশ কাকার ফ্যামিলিও আছে। যাত্রার আয়োজন হয়েছে হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির আঙিনায়। এখন পুরান ঢাকার যেখানে মহানগর মার্কেট, অর্থাৎ বলধা গার্ডেনের ঠিক উলটো পাশে ছিল হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি। রাত ৮টার দিকে শুরু হবে যাত্রা। আয়োজন করেছিল ‘মিউনিসিপ্যাল কমিটি’। আব্বা যেহেতু ওখানে চাকরি করেন সেই সুবাদেই তিনি আমাদের যাত্রা দেখাতে নিয়ে গেছেন। বিশাল খোলা আঙিনায় প্যান্ডেল করে আয়োজন। সেদিনকার আগে এত মানুষ আমি কখনো একসঙ্গে দেখিনি। হয়তো পাঁচ-সাত শ লোক হবে। এমন ধাক্কাধাক্কি আর হইচই চিল্লাচিল্লি বসার জায়গা নিয়ে, আমরা ছোটরা খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। আয়োজকরা লোকজন সামালই দিতে পারছে না। খড়-নারার ওপর চাদর বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা। ভয়ে আমি আব্বার কোলে ঘুমিয়ে পড়লাম। এক-দেড় ঘণ্টা পর ঘুম ভেঙেছে। আব্বার কোলে বসে অবাক বিস্ময়ে দেখি অদ্ভুত জামাকাপড় পরা, মাথায় পাগড়ি, হাতে তলোয়ার একজন রাজা দাঁড়িয়ে আছেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাজ পোশাকের রানি। রাজা চিৎকার করে করে কথা বলছেন। রানিও চিৎকার করছেন সমানে। কণ্ঠস্বর পুরুষের মতো। অর্থাৎ পুরুষই নারী সেজে অভিনয় করছে। সেই দিনের আগে এ রকম দৃশ্য দেখা তো দূরের কথা, কল্পনাও করিনি। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম।
আরেকটি ক্ষুদ্র যাত্রা হয়ে গেল এক রাতে আমাদের বারান্দায়। বাড়িটির একমাত্র দালানটিতে বিশাল বিশাল দুটি কামরা। কামরার সামনে আট-দশ হাত চওড়া বারান্দা। মাঝখানে বাঁশের বেড়া। সে-ই বেড়া তুলে দেওয়া হয়েছে। ট্রাংক, স্যুটকেস আর বোচকাবাচকি নিয়ে সন্ধ্যার পর বিচিত্র ধরনের কয়েকজন মানুষ এসেছে। সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলেও আছে। ঘটনা কী? পুলিশ কাকার ছেলে বাবুল বলল, ‘রূপবান’ যাত্রা হবে। সে-ই লোকগুলো ট্রাংক স্যুটকেস খুলে নানা রকমের পোশাক-আশাক বের করে পরল। কেউ-কেউ আলগা গোঁফ-দাড়ি লাগাল। লম্বা পরচুলা লাগিয়ে শাড়ি গহনা পরে চোখের সামনে পুরুষ হয়ে গেল নারী। বাচ্চা ছেলেটির পরনেও রাজার পোশাক। সে হচ্ছে রাজকুমার। তার নাম রহিম বাদশা। খাওয়াদাওয়া সাজপোশাক ইত্যাদি শেষ করার পর যাত্রা শুরু হবে। বাড়ির লোকজন উঠানে লাইন ধরে বসেছে। আমরা বসেছি বারান্দার এক কোণে। বাড়িটায় দিনেরবেলায়ও ঘাপটি মারা অন্ধকার। রাতে তো কথাই নেই। আমাদের আর পুলিশ কাকার ঘর ছাড়া কারও ঘরে হারিকেন নেই। ঘরে ঘরে পিতলের কুপি জ্বলে, টিনের ‘ডিবা’ জ্বলে। জিন্দাবাহারের গলিতে বিদ্যুৎ ঢোকেনি। ইসলামপুর মেইন রোডে দূরে দূরে টিমটিম করে জ্বলে দুয়েকটি বিদ্যুতের বাতি। যাত্রা উপলক্ষে সে-ই বাড়িতে সেদিন একটা হ্যাজাক বাতি ভাড়া করে আনা হয়েছে। সেটা শোঁ শোঁ শব্দে জ্বলছে। সাদা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে গেছে বাড়িটি। যাত্রা শুরু হয়ে গেল। পিনপতন নীরবতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে দর্শকরা। শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ আর গান শোনা যাচ্ছে। সিংগেল রিডের একটা হারমোনিয়াম থেকে থেকে বেজে উঠছে। বাজানদার লোকটির মুখ কঙ্কালের মতো। মুখের সঙ্গে খুবই বেমানান লম্বা মোটা গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। একসময় সে-ই বাচ্চা ছেলেটি, রহিম বাদশা খুবই করুণ সুরে একটা গান ধরল। ‘আমি যে গরিবের ছেলে, আমার কেহ নাই রে...’। রাজপোশাক পরা রাজকুমার বলছে, ‘আমি যে গরিবের ছেলে’? গানের সঙ্গে সে কাঁদতেও শুরু করল। অন্যদিকে বাড়ির নারীরা সবাই আঁচলে চোখ মুছতে লাগল। গরিবের ছেলে রাজকুমারের দুঃখে আমিও কাঁদছিলাম। কান্না অতি সংক্রামক। দ্রুত মানুষকে আক্রান্ত করে। আমার মাও কাঁদছিলেন। ও রকম আনন্দের রাত জিন্দাবাহারের সে-ই বাড়িতে আর কখনো আসেনি।
তারপর ঘটেছিল আরেকটি আনন্দের ঘটনা। আব্বা আর পুলিশ কাকা প্ল্যান করলেন আমাদের দুই পরিবারের সবাই মিলে মিরপুর মাজার জিয়ারত করতে যাবেন। আমার নানি আর খালা এসেছেন গ্রাম থেকে। তাঁরাও যাবেন। ভুঁইমালি আজিজ যাবে সঙ্গে। তখন ঢাকা থেকে মিরপুরে সড়কপথে যাওয়া খুব কঠিন। বাস যায় না। মাটির রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে হয়। আর যাওয়া যায় নৌকায় করে। আমরা যাব নৌকায়। বড় একটা নৌকা ভাড়া করা হয়েছে। বাদামতলী ঘাট থেকে ফজরের ওয়াক্তে সে-ই নৌকায় চড়েছিলাম। নৌকাতেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িপাতিলে করে ভাত-তরকারি নেওয়া হয়েছে। নৌকায় তিনজন মাঝি। হালমাঝি একজন, বাকি দুজন তালে তালে বৈঠা ফেলছে। বাদামতলী ঘাট থেকে পশ্চিম দিকে চলল নৌকা। সূর্য উঠল পূর্ব দিকে। বোধ হয় ফাল্গুন-চৈত্র মাস। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে নদীতে। সকালবেলার সূর্যের আলোয় বুড়িগঙ্গার পায়রার চোখের মতো স্বচ্ছ জল ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। নদীর উত্তর পাড়ে ঢাকা শহর। দক্ষিণ পাড়ে জিঞ্জিরা ও অন্যান্য গ্রাম। পশ্চিমে বহু দূর এসে নৌকার মুখ ঘুরে গিয়েছিল উত্তরে। হয়তো ঘণ্টা তিনেক লেগেছিল মিরপুরের মাজারঘাট পর্যন্ত যেতে। ওই এলাকাটি তখন বলতে গেলে পুরোপুরিই গ্রাম। বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি দালানবাড়ি আছে। বেশির ভাগ বাড়িই টিনের। কুঁড়েঘরও আছে কোনো কোনো বাড়িতে। ধান-পাটের খেত, গাছপালা, ঝোপঝাড়, মেঠোপথ। এ রকম পরিবেশেই মিরপুরের মাজার। মাজারের রাস্তার পাশে কয়েকটা দোকান। কিছু ভিখিরি আছে। মাজারের সেবকরা তো আছেনই। মনে পড়ে বড় বড় কয়েকটা গাছ ছিল মাজারের সঙ্গে। মাজার জিয়ারত করে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।
জিন্দাবাহার থার্ড লেনের সে-ই বাড়ি আর আশপাশের গলিগুলো ঘিরে আমার নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি হয়েছিল। পূর্ব দিককার গলিতে অনেকগুলো প্রেস ছিল। সকাল থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত ট্র্যাডেল বা গজ মেশিনের খটাখট শব্দ। কম্পোজিটাররা বসে বসে বাক্স থেকে টাইপ খুঁজে খুঁজে কম্পোজ করছে। প্রেসগুলোর সামনে কাগজ ও কালির মিশ্র গন্ধ। সামনের রাস্তায় ভাঙাচোরা সিসার টাইপ পড়ে থাকে। ভিখিরি ছেলেমেয়েরা সে-ই সব টাইপ কুড়াতে আসে। দিনে দিনে আমি জেনে গেলাম এই টাইপ একত্র করে লোহার ছোট কড়াইতে আগুনের তাপে গলানো হয়। তারপর সেগুলো কটকটিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করা হয়। সবকিছুতেই আমার অনেক কৌতূহল। দুই-তিন দিন সে-ই টাইপ কুড়িয়ে আমিও কিছুটা একত্র করলাম। এখন গলাই কী করে? এসব কাজে কেরামতের ছোট ভাইটা ওস্তাদ। সে নিয়মিতই টাইপ কুড়ায়। গলিয়ে কটকটিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে। দুই-এক আনা পয়সা পায়। কোত্থেকে অ্যালুমিনিয়ামের ভাঙাচোরা একটা ছোট গামলা জোগাড় করেছে সে। গেটের কাছে গিয়ে দুটো ইটের ওপর সে-ই গামলা বসিয়ে নিচে আগুন দিয়ে গলিয়ে ফেলে। আমিও সে-ই কায়দায় গলালাম। কিছুটা কটকটির সঙ্গে এক আনা পয়সাও পেলাম। তারপর বেশ কিছু দিন এই কাজটা আমি করেছি। জানতে পেরে মা একদিন খুব শাসন করেছিলেন। একটা কঞ্চি দিয়ে বড় ভাইকে একদিন খেলার ছলে মেরে বসলাম। ভাইয়ের চোখের কোনায় লেগে গেল বাড়িটা। চোখ ফুলে লাল। মা দুয়েকটা চড়-চাপড় মারলেন আমাকে। আব্বার ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। অফিস থেকে ফিরেই তো বড় ছেলের ওই চোখ তিনি দেখতে পাবেন। আব্বা আমাকে একটু বেশি ভালোবাসেন। কখনো তাঁর হাতে মার খাইনি। আজ নিশ্চয়ই রক্ষা নেই। মার খেতে হবে। আব্বা বাসায় ফেরার আগেই পুলিশ কাকির কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সে-ই কামরার দরজার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। একদিকে আব্বার ভয়, অন্যদিকে তীব্র গরম। দরদর করে ঘামতে লাগলাম। বড় ছেলের চোখের অবস্থা দেখে আব্বা খুবই চিন্তিত। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। চোখের মলম আর ট্যাবলেট ইত্যাদি দিলেন ডাক্তার। আমি তখনো লুকিয়ে আছি পুলিশ কাকার ঘরে। মা গিয়ে ডেকে আনলেন। ভয়ে থরথর করে কাঁপছি। আব্বা আমাকে কিছুই বললেন না। গভীর মমতায় গামছা দিয়ে শরীর মুখ মুছিয়ে দিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আর কখনো যেন এমন না করি এসব বোঝালেন। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। নিশ্চয়ই এক ধরনের অপরাধবোধ হচ্ছিল। সঙ্গে আব্বার স্নেহ। এই দুটো বিষয় মিলিয়ে হয়তো কেঁদেছিলাম। ঘুড়ি ওড়াবার দিনে বিহারি বাড়ি আর লালুদের বাড়ির ছেলেরা ছাদে উঠে নানা রঙের ঘুড়ি ওড়াত। আমি আমাদের ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। এক ঘুড়ি আরেক ঘুড়িকে কেটে দিচ্ছে। যে কাটতে পারছে আর তাকে ঘিরে আছে যারা তাদের আনন্দ চিৎকারে মুখর হয়ে যেত বিকেল বেলাটি। আমি তাকিয়ে থাকতাম কাটা ঘুড়িটির দিকে। হাওয়ায় ভেসে ভেসে কোনো অচেনা বাড়ি কিংবা রাস্তায় গিয়ে পড়বে সে-ই ঘুড়ি। পূর্ব-দিককার গলিতে লোহার বিশাল একটি পানির ট্যাংকি তৈরি হচ্ছে অনেক দিন ধরে। অত বড় পানির ট্যাংকি না কি ঢাকা শহরে আর নেই। তৈরি হতে দেড়-দুই বছর সময় লাগবে। সারা দিন লোহা পেটাবার শব্দ প্রচুর লোক কাজ করছে। বিশাল বিশাল গর্ত খুঁড়ে লোহার থাম বসানো হচ্ছে। প্রথম প্রথম দুয়েক দিন সে-ই এলাহি কাণ্ড দেখতে গিয়েছি। মা তারপর মানা করে দিলেন। আর যেন ও দিকটায় না যাই। কী কারণ? ওই পানির ট্যাংকি তৈরি করতে হলে না কি শিশুদের রক্ত দিতে হবে। একা কোনো শিশু পেলে তাকে জবাই করে রক্ত ঢেলে দেওয়া হবে থাম বসাবার গর্তে, শুনে এত ভয় পেলাম, ও দিকটায় আর কোনো দিন যাই-ই নি। চলে যেতাম পশ্চিমের গলিতে। লেপ-তোশকের দোকানগুলোর উলটো দিকে ড্রেনের ধারে একদিন দেখি ছোট্ট একটা ডালিম চারা। সবুজপাতা নিয়ে মাত্র জন্মেছে। সে-ই চারা তুলে এনে ছাদে ওঠার সিঁড়ির কোণে লাগিয়ে দিলাম। দুই বেলা পানি দিই। বারান্দায় বসে চারাটির দিকে তাকিয়ে থাকি। দুই-তিন দিনের মধ্যে সে-ই চারা বেশ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। কত যে স্বপ্ন এই চারাটিকে নিয়ে দেখতে শুরু করলাম আমি। চারা বড় হয়ে গাছ হবে। ডালিমের লাল ফুলে এক দিন ভরে যাবে গাছ। চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দেবে। ডালে ডালে ঝুলতে থাকবে মেরুন রঙের বড় বড় ডালিম। ডালিমের ভারে গাছটি নত হয়ে পড়বে। সে-ই দিন জীবনে আর কখনো আসেনি। এক সকালে উঠে দেখি চারাটি মরে শুকিয়ে গেছে। কেন এমন হয়েছিল কে জানে। সে-ই চারাটির দুঃখে ছাদের সিঁড়িতে বসে আমি খুব কেঁদেছিলাম। ছেলেবেলা ছাড়া ও রকম পবিত্র কান্না বোধ হয় আর কখনো কাঁদা যায় না।
লেখক : কথাসাহিত্যিক