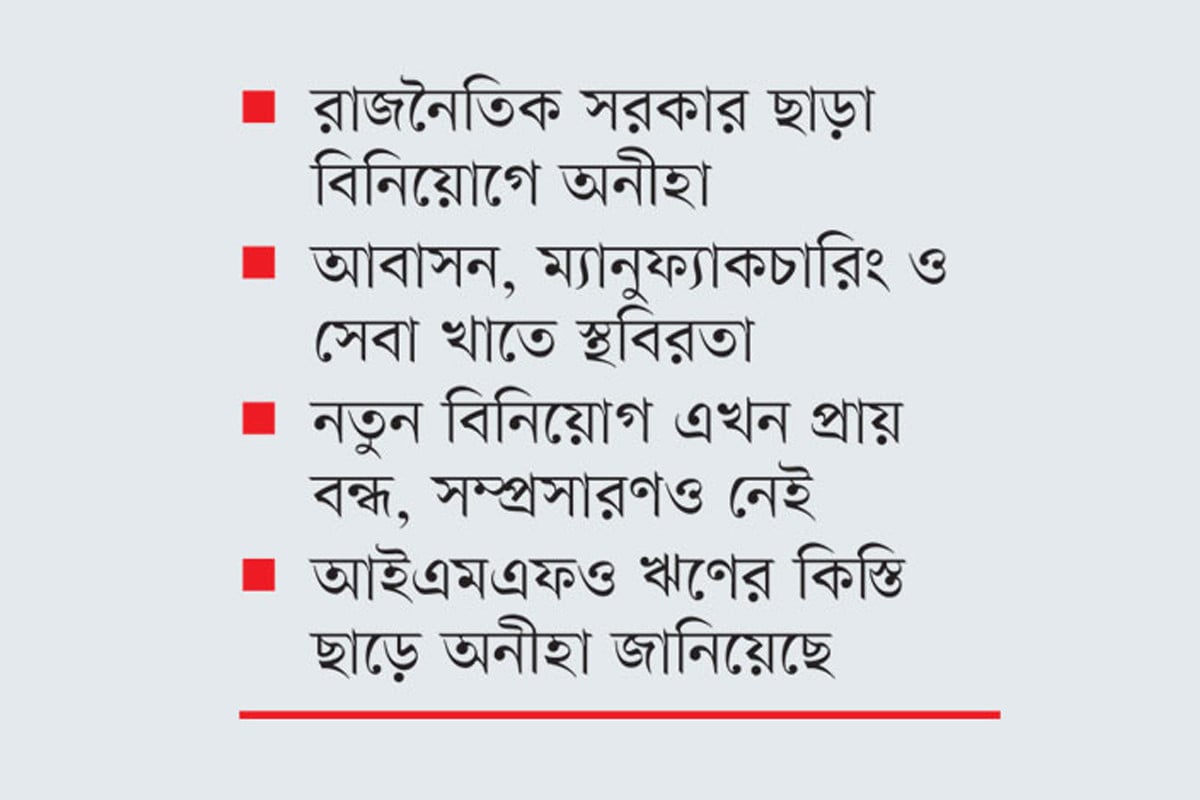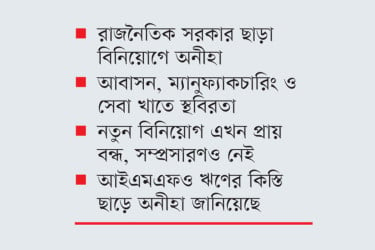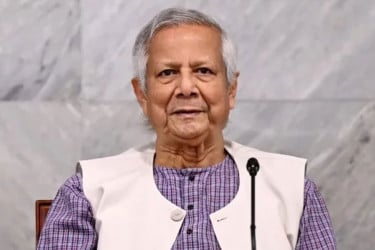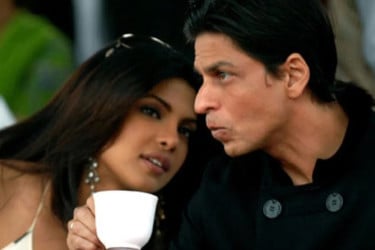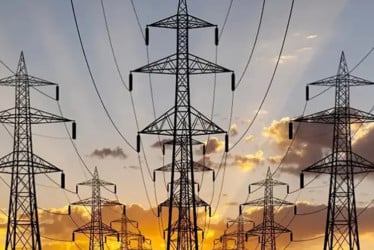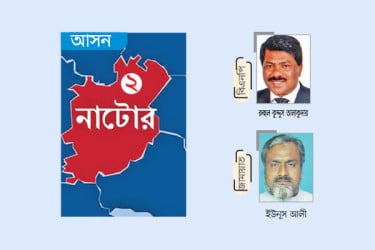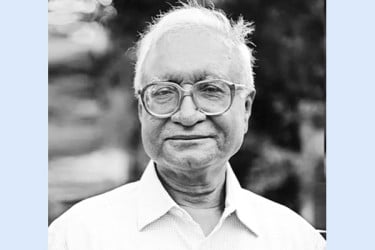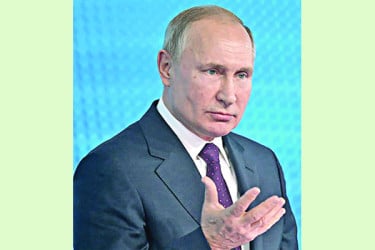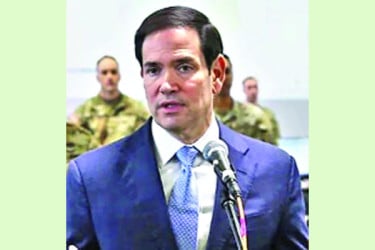দেড় দশকের বেশি সময় ধরে দেশে গৃহস্থালিতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে। ফলে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দিকে ঝুঁকছে মানুষ। গ্রামে-গঞ্জেও এখন রান্নাবান্নায় মাটির চুলার বদলে জায়গা করে নিয়েছে এলপিজি। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতির কারণে শিল্প-কারখানায় ও সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাসসংকট চলছে।
এ অবস্থায় শিল্প উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে অনেক শিল্পোদ্যোক্তা এলপিজি ব্যবহারে যাচ্ছেন। জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য ও প্রাকৃতিক গ্যাসসংকটের কারণে গাড়িতেও এলপিজি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। খরচ কমাতে অনেক গাড়ির মালিক তাদের পেট্রল বা অকটেনচালিত গাড়ির জ্বালানি ব্যবস্থা এলপিজিতে রূপান্তর করছেন। গ্যাসের সংকট থাকায় অনেকে সিএনজিচালিত গাড়িতেও দ্বৈতচালিত জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের সুবিধা রাখছেন। এটি গাড়িতে ব্যবহারের জন্য বর্তমানে অটোগ্যাস হিসেবেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে বর্তমানে এলপিজির ব্যবহার ১.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন বা ১৫ লাখ টনের ওপর। স্থানীয় গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস ও বাসাবাড়িতে পাইপলাইনে নতুন করে গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় এলপিজির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ না থাকায় শিল্প-কারখানায়ও বাড়ছে এ গ্যাসের ব্যবহার।
এলপিজির ব্যবহার বাড়ায় আগামী ২০৩০ সালে পণ্যটির ব্যবহার বেড়ে ২.৫ মিলিয়ন টন বা ২৫ লাখ টনে পৌঁছাবে। সেই হিসাবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে এলপিজির চাহিদা আরো ১০ লাখ টন বা ৬০ শতাংশ বাড়বে। পর্যায়ক্রমে ২০৪১ সালে এলপিজির চাহিদা পাঁচ মিলিয়ন টন বা ৫০ লাখ টনে উন্নীত হবে। ২০৫০ সালে এলপিজির চাহিদা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১০ মিলিয়ন টনে বা এক কোটি টনে। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে দেশের শিল্প খাতকে সরিয়ে আনতে হলে এটি সহজ বিকল্পও হতে পারে।
তবে এলপিজি খাতের প্রসার ও জনসাধারণের কাছে এটিকে সহজলভ্য করতে পলিসি প্রয়োজন বলে জানান বিশেষজ্ঞরা।
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম. তামিম বলেন, ‘দেশে প্রাইমারি এনার্জির ৬৫ শতাংশই আমদানি হচ্ছে। তেল ও কয়লার পুরোটাই আমদানিনির্ভর। গ্যাসের বৃহৎ অংশও আমদানি করতে হচ্ছে। বিপরীতে স্থানীয় গ্যাসের উত্তোলন ক্রমে কমে যাচ্ছে। প্রতিবছর অন্তত ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কমে যাচ্ছে। স্থানীয় গ্যাস উৎপাদনের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও সেখানে ভালো সংবাদ নেই। ক্রমে সাশ্রয়ী দামে সরবরাহ বাড়ানো গেলে গ্যাসের বড় বিকল্প হতে পারে এলপিজি। দেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এলপিজির ব্যবহার ছিল সাত লাখ টন। পরের অর্থবছরে সাড়ে আট লাখ টন, ২০২০-২১ অর্থবছরে সাড়ে ১০ লাখ টনে উন্নীত হয়। পর্যায়ক্রমে চাহিদা বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হয় প্রায় ১৫ লাখ টনের কাছাকাছি।’
ম. তামিম বলেন, ‘দেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ এলপিজির চাহিদা তৈরি হচ্ছে, তার ৯৮ শতাংশ আসছে বেসরকারিভাবে। মাত্র ২ শতাংশ এলপিজি সরকারিভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। এ খাতে ৫৮টি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স নিলেও মাত্র ২৭টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এলপিজি অপারেটর হিসেবে নিয়োজিত।’
বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন এবং কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ সিরাজুল মাওলা বলেন, ‘বাংলাদেশে যেসব গাড়ি মূলত পেট্রল বা অকটেনে চলে, সেগুলোকে সিএনজিতে (কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) রূপান্তরিত করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে সিএনজির ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। গ্যাসসংকটের কারণে সিএনজি স্টেশনগুলোতে দিনের বড় একটা সময় গ্যাসের সরবরাহ ঠিকমতো থাকে না। গ্যাসের প্রেশার বা চাপ কম থাকার কারণে সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস নিতে গেলে গ্রাহকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত লাইন ধরা লাগতে পারে। এ কারণে সিএনজিতে রূপান্তরিত গাড়ির একটি বড় অংশ এখন সিএনজি ব্যবস্থা খুলে দিয়ে এলপিজিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। মূলত সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাসের সরবরাহের অভাবের কারণেই সিএনজি থেকে এলপিজিতে এই রূপান্তর ঘটছে।’
সিরাজুল মাওলা আরও বলেন, ‘এলপিজির চাহিদা বাড়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে নতুন যত গাড়ি আমদানি হচ্ছে, সেগুলোর সবই আর সিএনজিতে কনভার্ট হচ্ছে না; বরং সবই এলপিজিতে কনভার্ট হচ্ছে। সুতরাং পরিবহন সেক্টরে বিদ্যমান সিএনজি রূপান্তরিত গাড়িগুলোর এলপিজিতে রূপান্তর এবং নতুন আমদানি হওয়া গাড়িগুলোর সরাসরি এলপিজিতে রূপান্তরের কারণে দুদিক থেকেই এলপিজির চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।’
জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ম. তামিম আরও বলেন, ‘এলপিজি একমাত্র জ্বালানি, যা কোনো ধরনের ভর্তুকি ছাড়াই গড়ে উঠেছে এবং টিকেও আছে। এটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বাড়ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে শিল্পকে সরিয়ে আনতে হলে এলপিজি সহজ বিকল্প অপশন হতে পারে। এ খাতের প্রসার ও জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করতে শক্ত নীতিমালা প্রয়োজন। শুধু বেসরকারি খাত এগিয়ে এলে হবে না, এ খাতে সরকারি খাতের অংশগ্রহণও বড় আকারে প্রয়োজন।’
খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে এলপিজির ব্যবহার বাড়লেও এখন পর্যন্ত শিল্পে বড় আকারে ব্যবহার দেখা যাচ্ছে না। তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং সরকারি সহযোগিতা ও অবকাঠামো বাড়ানো গেলে বাসাবাড়ির পাশাপাশি শিল্পেও এর বড় ধরনের প্রসার হতে পারে। দেশের মোট এলপিজির ৮০ শতাংশ বাসাবাড়িতে, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ১২ শতাংশ এবং অটোগ্যাস খাতে ব্যবহার হচ্ছে মাত্র ৮ শতাংশ।
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ সম্প্রতি এক আলোচনা সভায় বলেন, ‘বর্তমানে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ১২ লাখ টন এলপিজি আমদানি করে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ পরিমাণ প্রায় ২৫ লাখ টনে পৌঁছতে পারে। ক্রমবর্ধমান আমদানি চাহিদা জ্বালানি নিরাপত্তা ও বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাই এলপিজি খাতে নতুন বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সাশ্রয়ী পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। চাহিদা অনুযায়ী এলপিজি খাতকে বিকশিত করা গেলে তা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।’
ইস্ট কোস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরী বলেন, ‘বাসাবাড়ি, শিল্প-কারখানায় সর্বত্র আমরা এলপিজি সরবরাহ করছি। অবকাঠামো তৈরি হলে এলপিজির চাহিদা আরো বাড়বে। যেমন—শহরের ছোট ছোট এলাকায় পাইপের মাধ্যমে বাসায় গ্যাস সরবরাহ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এতে সিলিন্ডার নিয়ে ঝামেলা কমবে। এটা উন্নত দেশে আছে, আমাদের দেশেও সম্ভব। এখানে নিরাপত্তার বিষয় আছে। তাই রাজউকসহ অন্য যেসব সংস্থা আছে, সবার সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।’
সৌজন্যে : কালের কণ্ঠ