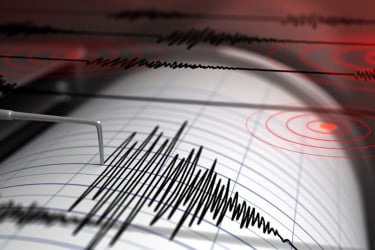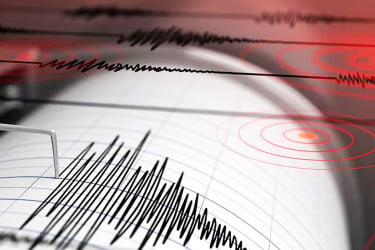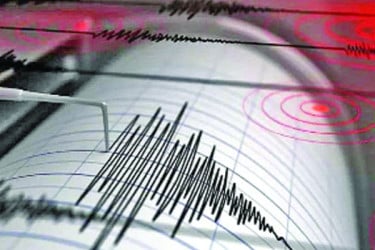১৯৯৩-এ আমি ঢাকা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র। রোজ ক্লাস করতে হতো উত্তরা থেকে। সেটা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। উত্তরা থেকে নিউমার্কেট পর্যন্ত যেতে বাস পাল্টাতে হতো দুই-তিন দফা। সেজন্য সামনে পরীক্ষা থাকলে আমি প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে থেকে যেতাম কলেজের ছাত্রাবাসে। একসঙ্গে নোট ও পড়াশোনা দুটোই ভালো হতো। ঢাকা কলেজে তখন দুটি ছাত্রাবাস ছিল। বিজ্ঞান শাখার ছেলেদের জন্য সাউথ হল। আর মানবিক শাখার জন্য নর্থ হল। মানবিক শাখার ছাত্র ছিলাম বলে আমার থাকা হতো নর্থ হলে। ওখানে থাকার কারণেই হয়তো মজার একটি বিষয় চোখে পড়ল একদিন। আমাদের এক সহপাঠী, ছাত্র হিসেবেও সে তুখোড় ও অসামান্য। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করেছিল। তাকে দেখলাম একদিন রাতে সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। আমরা যখন রাতে ক্যান্টিনে পাতলা ডাল, শিম, ফুলকপির ঠান্ডা সবজি ও ভাত দিয়ে উদরপূর্তি করছি!! ঠিক সে সময়ে ও এসে হাজির হলো। আমাদের সঙ্গে খাবে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে মাথা নেড়ে না-সূচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করল। কাচ্চি বিরিয়ানির ঢেকুর তুলে বলল, জনৈক আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত থাকায় রাতের আহার পর্বটি সেখান থেকেই চুকিয়ে এসেছে। এক-দুই দিন নয়, এরকম প্রায়ই তাকে দেখা যেতে লাগল সেজেগুজে পায়ে পাম্প সু গলিয়ে কাঁধে জাপানি একটি ইয়াসিকা ক্যামেরা ঝুলিয়ে সন্ধ্যার মুখে প্রায়ই সে হাওয়া হয়ে যায় হোস্টেল থেকে। ফেরে রাত ১০-১১টা নাগাদ। বেশ কিছুদিন এভাবে চলছিল ভালোই। হঠাৎ একদিন ও ফিরেছে যথারীতি রাত ১০টার দিকে। কিন্তু চোখেমুখে কোনো উৎফুল্লতা নেই। বরং দেখাচ্ছিল বিষণ্ন, ম্লান ও বিধ্বস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিরে কী হয়েছে তোর? কোনো উত্তর নেই। শক্ত করে ধরলাম ওকে। বললাম, আজ খুলে বলতেই হবে কী হয়েছে তোর। আর তুই মাঝে মাঝে ফিটফাট হয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে যাস কোথায়? এবার সে বলতে শুরু করল। হোস্টেলের বাজে খাবার খেয়ে খেয়ে ওর নাকি মুখে অরুচি ধরে গেছে। এজন্য প্রায়ই ভালো জামাকাপড় পরে রাতের দিকে ঢুকে পড়ে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে। আমাদের সময় সোহাগ কমিউনিটি সেন্টার নামে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ভালো ভেন্যু ছিল। আমার সতীর্থ বন্ধুটি প্রায়ই ওগুলোর কোনো একটিতে ঢুকে পড়ত। আমি ভ্রু কপালে তুলে বললাম, তোর কি ভয়ডর নেই নাকি। যদি ধরা পড়ে যাস! ও বলল, আরে ধরা যাতে না পড়ি সেজন্যই তো কাঁধের এ ক্যামেরাটি। আমি বললাম, ক্যামেরা? ও বলল, হ্যাঁ। বাড়ি থেকে এ ক্যামেরাটি আমি নিয়ে এসেছি। বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েই আমি ফটফট ছবি তোলা শুরু করি। এতে সবাই ভাবে আমি বিয়েবাড়িরই কোনো আমন্ত্রিত অতিথি। কেউ প্রশ্ন তোলে না। আজ হয়েছে কি শোন। টাকার অভাবে ফিল্ম কিনতে পারি না। শুধু ব্যাটারি ভরে নেই ক্যামেরায়, যেন ফ্লাশটা জ্বালানো যায়। তা না হলে তো আর ছবি তোলা মনে হয় না। ক্যামেরার ওপরের দিকটায় একটি নব আছে, সেটা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘোরাতে হয় ফিল্মটা টানার জন্য। একেকটি ফিল্মে ৩৬টি করে ছবি তোলা যায়। নবটা প্রতিবার টানার পর ক্যামেরার ওপরের দিকের ডিসপ্লেতে এক দুই তিন এভাবে লেখা উঠতে থাকে ৩৬ নম্বর না আসা পর্যন্ত। তো হয়েছে কি, বিয়েবাড়ির একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আরে ভাই আপনিই শুধু ক্রমাগত একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছেন। আসুন আসুন বর-কনের সঙ্গে আপনারও একটা ছবি তুলে দেই। ছবি তুলতে গিয়ে উনি লক্ষ্য করলেন, ফিল্ম আর সামনে এগোচ্ছে না। হয়তো ভাবলেন ফিল্মটা আটকে গেছে কোথাও। লোকটি আমাকে কিছু না বলেই ক্যামেরার পেছনের ঢাকনাটি খুলে ফেললেন। দেখা গেল ওখানে কোনো ফিল্ম নেই। আর যায় কোথায়। যা হওয়ার তাই হলো- বিয়েবাড়িতে বজ্রপাত। কী যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হলো তা আর বলতে চাই না। ভাগ্যিস কলেজের পরিচয়পত্রটি সঙ্গে ছিল, তাই রক্ষে। দিন কত বদলেছে। এখন যে কোনো বিয়েবাড়িতে মানুষজন কম হলে আয়োজকদের মন খারাপ হয়ে যায়। যত বেশি অতিথি ও অভ্যাগতের ভিড়, কর্তার মনে তত আনন্দ। বিয়ের অনুষ্ঠানটি বুঝি তাহলে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সার্থক হলো। অথচ এ কথা এখন কে বিশ্বাস করবে যে দেড়-দুই যুগ আগেও বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হতো আঙুলের কড় গুনে। দাওয়াতপত্রের খামে লেখা থাকত- ‘মিস্টার অমুক’ কিংবা ‘মিস্টার ও মিসেস তমুক’। পুরো পরিবারকে দাওয়াত করা হলে সেক্ষেত্রে খামের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকত ‘পরিবারবর্গ’। আমরা সাধারণত দেখি যে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রগুলো করে থাকেন বর কিংবা কনের পিতা-মাতা। পিতা-মাতা জীবিত না থাকলে সেক্ষেত্রে বর-কনের ভাই কিংবা অন্য কোনো গুরুজন।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিয়েতে হয়েছিল ভিন্নরকম কাণ্ড। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সবই আধুনিক। পুরোনোকে ভেঙেচুরে নতুন কিছু গড়ে তোলার সাহস দেখিয়েছেন তারা বারবার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা করে দেখালেন তা নজিরবিহীন। নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের লেখক তিনি নিজেই। যা যুগপৎভাবে কৌতূহলোদ্দীপক ও চমকপ্রদ। বন্ধুবর্গের কাছে ঠাকুরবাড়ি থেকে যে নিমন্ত্রণপত্রটি গেল, তাতে লেখা ছিল- ‘প্রিয়বাবু- আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি- অনুগত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।’
আমাদের বাবা-দাদাদের সময় অবশ্য নিমন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ছিল ভিন্ন সংস্কৃতি। সে সময় দাওয়াত হতো তিন রকমের- এক কেয়ারি, মেজবানি ও হাঁড়িবারণ। এক কেয়ারি জেয়াফতের দাওয়াত হলে বুঝতে হবে বাড়ির একজনের দাওয়াত। সেটা অবশ্যই বাড়ির প্রধান কর্তার। এর পরের ধাপ মেজবানি। এ দাওয়াতে বাড়ির সব লোকের খাওয়ার সুযোগ থাকবে। মেজবানি-মেহবানি দাওয়াত হলে বুঝতে হবে বাড়ির সব সদস্য তো বটেই বাড়িতে যদি আচমকা কোনো কুটুমও এসে পড়েন তিনিও অংশগ্রহণ করতে পারবেন বিয়েবাড়ির খানাপিনায়। তবে সবচেয়ে বড় জেয়াফত হচ্ছে হাঁড়িবারণ। এর অর্থ হচ্ছে- নিমন্ত্রিত অতিথিদের বাড়িতে অন্তত একদিনের জন্য হলেও হাঁড়ি চড়বে না উনুনে। খুব কাছের আত্মীয়স্বজন ছাড়া সাধারণত অন্য কেউ হাঁড়িবারণ দাওয়াত পেত না। কিন্তু সেসব সংস্কৃতি এখন শুধুই ইতিহাস।
ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি এ তিন মাস প্রধানত বিয়ের মৌসুম। বছরজুড়ে যত বিয়ে হয় তার বোধকরি অর্ধেকেরও বেশি বিয়ে হয় এ তিন মাসে। ধনাঢ্য ও সম্পন্ন পরিবারের জন্য অবশ্য শীতকালটা সব কালেই বিয়ের আদর্শ মৌসুম। রবীন্দ্রনাথও বিয়ে করেছিলেন শীতকালে। তার বিয়ের দিনটি ছিল ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরের ৯ তারিখ। তবে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থ কৃষক পরিবারগুলোতে একসময় বিয়েশাদির অনুষ্ঠান হতো বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান কাটার পর। বর্ষার ঠিক আগে। তবে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তারাও এখন বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নিচ্ছেন শীত ঋতু। শীতের আমেজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে চোখে পড়ে জাঁক করা সব বিয়ের অনুষ্ঠান। ঢাকার প্রতিটি বিয়ের উৎসবই যেন হয়ে ওঠে বলিউড তারকাদের পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠান। বর-কনের সাফল্যমণ্ডিত ভবিষ্যৎ কিংবা সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে তাদের ঝোঁক কম। এখন বিয়ে মানেই শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ওড়ানো। খুব কম বিয়েতেই চোখে পড়ে বুদ্ধিদীপ্ত ছোঁয়া। অথচ আবহমানকাল ধরে আমাদের বিয়েশাদির অনুষ্ঠানগুলো হতো এর সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি মানুষের হƒদয়নিংড়ানো ভালোবাসা ও যত্নআত্তির মধ্য দিয়ে। পুরোনো দিনের বিয়েগুলোতে অবশ্য কিছু অপসংস্কৃতিও চোখে পড়ত। বিশেষ করে বিয়ে উপলক্ষে বর-কনের আত্মীয়স্বজন যখন পাত্র-পাত্রী সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে অন্য গ্রামে যেত তখন গ্রামের মানুষজন মিছেমিছি পাত্র-পাত্রী সম্পর্কে নিন্দা মন্দ করে সে বিয়ে ভেঙে দিত। এ প্রবণতা যে শুধু গ্রামের মানুষের মধ্যে ছিল, তা নয়। আমরা উঁচু শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে রাজরাজড়াদের মধ্যেও এমন নিকৃষ্ট আচরণ দেখি। হিন্দু ধর্মে একসময় বিধবাদের পুনর্বিবাহের নিয়ম ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাতদিন হাঁড়ভাঙা খাটুনি খেটে হিন্দু ধর্মের সব আইনকানুন ও শাস্ত্র ঘেঁটে প্রাচীনপন্থিদের দেখাতে সক্ষম হলেন যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ফলে ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি বিধবা বিয়ে আইনটি পাস করেন। এ আইনটি হয়তো পাস হতে পারত আরও ১০০ বছর আগে। সেটা সম্ভব হয়নি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকৃষ্ট এক আচরণে। ঢাকার মহারাজা রাজবল্লভের মেয়ে অভয়া বিধবা হন অল্প বয়সে। রাজবল্লভ ভারতবর্ষের পণ্ডিতদের একত্র করে বিধান চান কীভাবে তার মেয়ের পুনরায় বিবাহ দেওয়া যায়। সে সময় ভারতের সব পণ্ডিত শাস্ত্র ঘেঁটে এ রায় দেন যে, বিধবা বিয়ে শাস্ত্রসম্মত। নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও সে বিধান অকাট্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র হিংসার বশবর্তী হয়ে টাকা-পয়সা খরচ করে পণ্ডিত সমাজকে প্ররোচিত করে সেটা ভণ্ডুল করে দেন। কে বলবে এ কৃষ্ণচন্দ্রই ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র ও গোপালভাঁড়ের মতো লেখক-সাহিত্যিকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।
প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের আরেকটি সংস্কৃতি হচ্ছে, পাত্রী দেখতে গিয়ে পছন্দ হলে কাজি ডেকে তৎক্ষণাৎ বিয়ের পিঁড়িতে বসে যাওয়া। নিঃসন্দেহে এটা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংস্কৃতি। কারণ সেক্ষেত্রে কন্যা পক্ষ হয়তো পাত্রের ও পাত্রের পরিবার সম্পর্কে ভালোভাবে জানার সুযোগ করে উঠতে পারে না। বিয়ের পর হয়তো দেখা যায় পাত্র দোজবরে কিংবা পাত্রীর এমন পরিবারে বিয়ে হয়েছে যেখানে হয়তো নিজেকে মানিয়ে চলতেই তাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের ঘটনাটি স্মরণযোগ্য। এ বিষয়ে লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই ভারতবর্ষের প্রথম আইএস অফিসার সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তিনি লিখেছেন- সারদা দেবীর (রবীন্দ্রনাথের মা) এক কাকা নাকি শুনেছিলেন যে দেবেন্দ্রনাথের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। তিনি দেশে এসে সারদা দেবীকে কোলে তুলে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। সারদা দেবীকে নিয়ে আসার সময় তার মা (রবীন্দ্রনাথের নানি) বাড়িতে ছিলেন না। গিয়েছিলেন গঙ্গাস্নানে। বাড়ি ফিরে এসে যখন শুনলেন মেয়েকে তার দেবর না বলেকয়ে নিয়ে গেছেন কলকাতায়। তখন তিনি উঠানের পাশে গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকেন। কেঁদে কেঁদে নাকি তিনি অন্ধই হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় সারদা দেবীর বয়স মাত্র ছয় বছর। এ কাহিনি থেকে সে যুগের সামাজিক ব্যবস্থায় মেয়েদের স্থান যে কোথায় ছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ২০০ বছর পর বর্তমানে আমাদের সমাজেও মেয়েদের অবস্থা প্রায় একই বলা চলে।
বিনা দাওয়াতে বিয়ে খাওয়া নিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম। শেষে প্রথিতযশা আইনবিদ ড. কামাল হোসেনকে দিয়ে শেষ করি। আমাদের এক বন্ধু ব্যারিস্টার মঈন ঘানি, ড. কামাল হোসেনেরই জুনিয়র। ড. হোসেন গেছেন তাঁর বিয়েতে। বিয়ে হচ্ছিল চীন মৈত্রী কনভেনশন সেন্টারে। সেখানে পাশাপাশি অনেক ভেন্যু থাকে। ভুলবশত ড. হোসেন মঈন ঘানির বিয়ের আসরে না ঢুকে, ঢুকে পড়েছেন অন্য আরেকটি অনুষ্ঠানে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর টের পেলেন যে, তিনি আসলে চলে এসেছেন ভুল জায়গায়। কিন্তু কী আর করা ইতোমধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ।
লেখক : গল্পকার ও আইনজীবী
ইমেইল : [email protected]