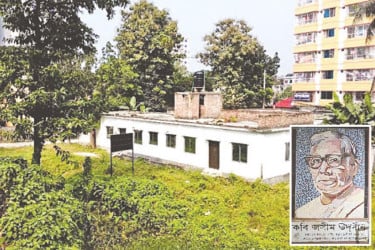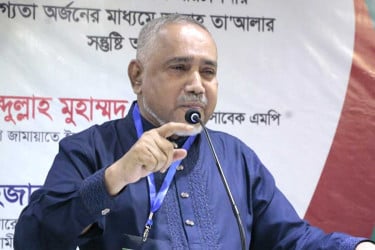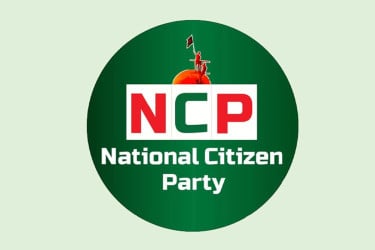আধুনিক টেলিকম অবকাঠামো গড়তে তিন বছর আগে বিটিসিএল ফাইভ-জি রেডিনেস প্রকল্প হাতে নিলেও তা আলোর মুখ দেখছে না। অপতথ্য, প্রশাসনিক দুর্বলতা, দেশীয় কোম্পানির প্রভাব, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ, মালামাল বন্দরে পড়ে থাকা ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর চিঠি নিয়ে ধোঁয়াশাসহ নানা জটিলতায় পড়েছে প্রকল্পটি। ফাইভ-জি প্রকল্পটি আলোর মুখ না দেখলে অন্ধকারেই থেকে যাবে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটির সক্ষমতা বৃদ্ধি ৩০০ কোটি টাকার আরেক প্রকল্প। ফলে সরকারের ৬০০ কোটি টাকার বেশি গচ্চা যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
এই প্রকল্প বাতিল হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিটিসিএল ও সরকার। কারণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিসিএল সারা দেশে উচ্চমানসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করতে পারবে। আর এই অপটিক্যাল ফাইবার চালু হলে টেলিকম অপারেটর ও আইএসপি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভাড়া নেবে। যার ফলে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিটিসিএলের। একই সঙ্গে দেশীয় বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুনতে হবে লোকসান। তাদের আক্ষেপের বিষয়টি সম্প্রতি ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের বক্তব্যেও উঠে এসেছে।
স্বার্থক্ষুণ্ন হতে পারে এক্স-ফার নামে একটি আইসিটি প্রতিষ্ঠানেরও। এক্স-ফার লিমিটেড আন্তর্জাতিক টেলিকম কোম্পানি যেমন তুরস্কের নেটাস-এর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে এবং বিটিসিএল-এর বিভিন্ন দরপত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে। এক্স ফার-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মালিক মুশফিক আনাম। যে কোনো দরপত্রে সাধারণত অংশগ্রহণকারী সব প্রতিষ্ঠানেরই অপরপক্ষের প্রস্তাবিত মূল্যের বিষয়ে নিজস্ব একটা পূর্বানুমান থাকে। বিটিসিএল-এর চলমান ফাইভ-জি রেডিনেস প্রকল্পে চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান জেডটিইরও তা ছিল। শেষ পর্যন্ত এই দরপত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে- সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে হুয়াওয়ে যে মূল্য প্রস্তাব করে তার থেকে জেডটিই-এর প্রস্তাবিত মূল্য ৯০ কোটি টাকা বেশি। অন্যদিকে, এই প্রকল্পে যে সমস্ত পণ্য চাওয়া হয়েছে সেগুলো সরবরাহের সক্ষমতা এক্স-ফার-এর থাকলেও কোনো এক বিশেষ কারণে দরপত্র জমা দিতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। কাজেই যদি এই প্রকল্পের চলমান দরপত্র বাতিল হয়ে আবারও খোলা হয় তাহলে আগে বেশি মূল্য প্রস্তাব করা প্রতিষ্ঠান এবং বাদ পড়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান, সবার জন্যই একটি নতুন সুযোগ তৈরি হবে। দুদকে চলমান তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ জুন ডাক টেলিযোগাযোগ সচিব বরাবর দুদকের তৎকালীন সচিব খোরশেদা ইয়াসমিন একটি চিঠি দেন। সেখানে প্রথমেই বলা হয়- এই দরপত্র প্রক্রিয়ায় পিপিএ ও পিপিআর এর প্রাথমিকভাবে ব্যত্যয় পেয়েছে দুদক। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ উল্লেখ না করে এর বাকি কার্যক্রম স্থগিত রাখতে বলা হয়। প্রকল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে আগেই এলসি হয়ে যাওয়া পণ্যের খালাস প্রক্রিয়া চালিয়ে নিতে সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে দুদককে একটি আধা-সরকারি চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। সেই চিঠিতে দুদকের পর্যবেক্ষণকে প্রভাবিত করার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা ছিল না। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হলে বিশেষ সহকারী সংবাদ সম্মেলনে এসে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেন। দুদকের উপপরিচালক আখতারুল ইসলাম বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁর মন্তব্যে নিশ্চিত করেন যে এই আধা-সরকারি চিঠি দুদকের তদন্তে কোনো রকম প্রভাব ফেলবে না। ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বরারর প্রকল্প দরপত্রের সরঞ্জামের কারিগরি সক্ষমতার বিষয়ে একটি অভিযোগপত্র জমা দেয় জেডটিই। যার উদ্দেশ্য ছিল এই দরপত্রটি বাতিল করে পুনরায় আহ্বান করানো। অথচ এর আগে ৩০ অক্টোবর সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিবের সভাপতিত্বে সব পরিচালক পর্ষদ, বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এবং দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিতে বিটিসিএল অফিসে একটি সভা আয়োজন করা হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখের আগে আয়োজিত সেই সভায় সবাইকে আহ্বান করা হয়। তারা যেন দরপত্র বিষয়ে যে কোনো মতামত, অভিযোগ কিংবা পরামর্শ সেই সভায় বিনা দ্বিধায় উল্লেখ করে বা ২০২২ সালের অক্টোবর মাসের ২ তারিখের মধ্যে বিটিসিএল বরাবর লিখিত আকারে জমা দেয়। কিন্তু সেই সভায় কিংবা পরবর্তীতেও কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো আপত্তি পেশ করেনি। বরং সবকিছু মেনে-বুঝে দরপত্র জমা দিয়েছে। আর দরপত্র জমা এবং কারিগরি মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর হঠাৎ জেডটিই এই চিঠি দেয় তৎকালীন মন্ত্রী বরাবর যা নিয়মের বাইরে ছিল। চিঠি দিতে চাইলেও নিয়মানুযায়ী তা প্রকল্প পরিচালককে দেওয়ার কথা ছিল। এরপর শুরু হয় এই প্রকল্পে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি নেওয়া হচ্ছে এমন দাবি। বুয়েটের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে উপেক্ষা করে পুরাতন এক প্রতিবেদনের দোহাই দিয়ে ২৬ আর ১২৬ টেরাবাইটের বিষয়টি বাজারে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়। এ নিয়ে অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদির জন্য যে ব্যান্ডউইথ এর প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশি ব্যান্ডউইথ এর প্রয়োজন হয় লোকাল ক্যাশ সার্ভারের জন্য। অন্যদিকে ভবিষ্যতে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রযুক্তি এলে আরও বেশি ব্যান্ডউইথ লাগবে। এ ছাড়াও ফাইভ-জি চালু হওয়ার পর হাই-কোয়ালিটি ভিডিও এবং হাই স্পিড ইন্টারনেটের জন্য আরও বেশি ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হবে। ফলে টেন্ডারে যে ১২৬ টেরাবাইট ক্যাপাসিটির সংস্থান রাখা হয়েছে তা বর্তমান বাস্তবতায় সঠিক আছে। ১২৬ টেরাবাইট থেকে আরও অধিক ক্যাপাসিটির সংস্থান টেন্ডারে রাখা হলেও তা আরও বেশি যুগোপযোগী হতো। ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ইন্টারনেট ফুটপ্রিন্টটা হলো ক্যাশ এবং টোটাল ইন্টারনেট মিলে আনুমানিক ৩৫-৩৬ টেরাবাইট। বৈশ্বিক ইন্টারনেটের যে কম্পাউন্ড এনুয়াল গ্রোথ রেইট তা হলো ২৮ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সেখানে এই রেইট অনেক বেশি। আফ্রিকান দেশগুলোতে ৩৪ ভাগ আর বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে ৪৫ ভাগ। এখন আমরা যদি বাংলাদেশের এই ৩৫ টেরাবাইট ইন্টারনেটের ওপর বছর বছর ৩৪ ভাগ থেকে ৪৫ ভাগ একটা হিসাব যোগ করি তাহলে এই প্রবৃদ্ধি আজ থেকে ১২ বছর পরে দাঁড়াবে প্রায় ১৭৫ টেরাবাইট। তিনি বলেন, বুয়েট ২০১৬-২০১৭ সালের দিকে একটা স্টাডি করেছে সেখানে দেখানো হয়েছিল এবং তখন থেকে ১০-১২ বছর পরে এটা লাগবে ১০০ টেরাবাইটের বেশি।