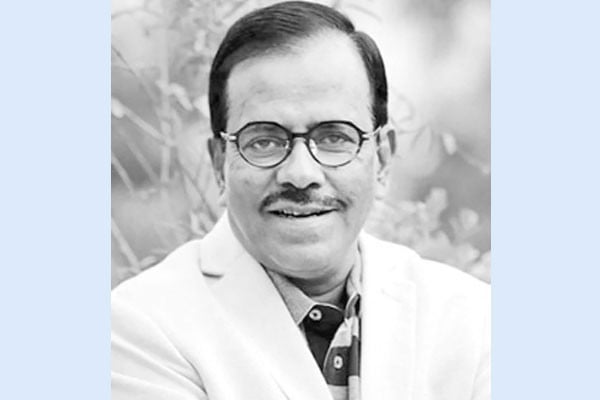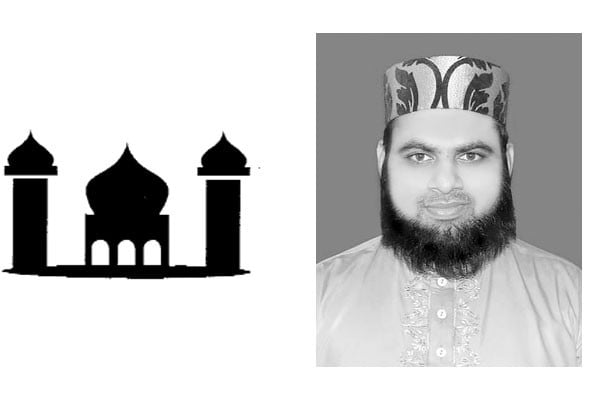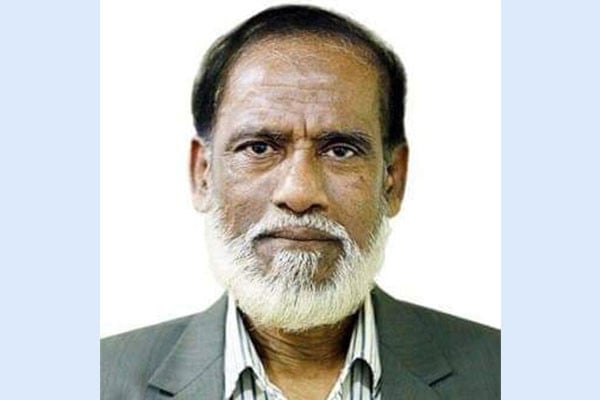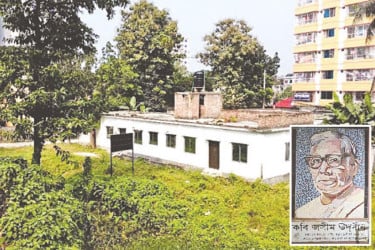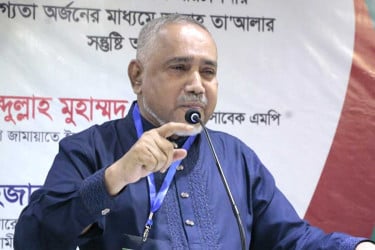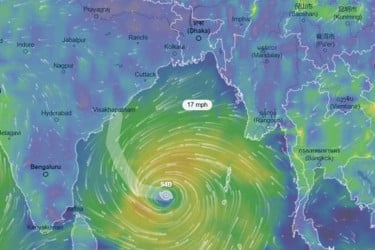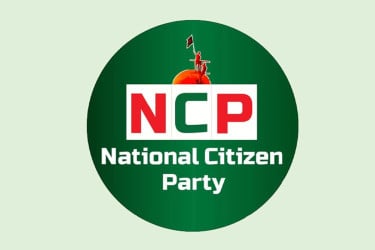গত শতকের আশির দশকের প্রথম দিকে গ্রামগঞ্জে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি কৃষকরা তাদের বাড়িতে এক-দুইটা গরু-গাভি পালতেন। দেশি গাভি বলে দিনে সর্বোচ্চ দেড়-দুই লিটার দুধ পেতেন। সেখান থেকে যে দুধ পাওয়া যেত, কৃষক তা নিজের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি গ্রামের বাজারে বিক্রি করতেন। ধানের খড় আর মাঠের ঘাস খাইয়ে দুই-একটা গরু লালনপালন করতে খুব একটা খরচ হতো না তাদের। কিন্তু আমরা উৎসাহিত করলাম বিদেশি জাতের সঙ্গে সংকরায়িত উন্নত গাভি লালনপালনে। বেশি দুধ পাওয়া যাবে ভেবে কৃষক সেই গাভি পালন শুরু করলেন। কিন্তু উন্নত জাতের গাভির খাবার খরচ বেশি। নিজের পরিবারের খাবার জোগাতে হিমশিম খাওয়া কৃষকের পক্ষে গাভির খাবার জোগানো কষ্টকর হয়ে যায়। নিজে খেয়ে না খেয়ে গাভিকে খাইয়ে যখন ১৫-২০ লিটার দুধ নিয়ে বাজারে গিয়ে দুধের উপযুক্ত দাম পাননি, কৃষক অভিমানে দুধ ফেলে দিয়েছেন। ফলে আমাদের দুগ্ধ খাত প্রত্যাশিতভাবে বিকশিত হয়নি।
যে কোনো কিছু উৎপাদনের আগে দুটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। প্রথমটি বাজারব্যবস্থাপনা। উৎপাদিত পণ্যটির বাজার তৈরি আছে কিনা, এবং কী পরিমাণ বিক্রি করতে পারব, সে বিষয়টি মাথায় রেখেই উৎপাদনে যাওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যটি সংরক্ষণ করতে পারব কিনা। বাজারে দর না পেলে কিংবা বিক্রি করতে না পারলেও অন্য বাজারে বিক্রির জন্য সেটা কত দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে সে বিষয়টিও ভাবনায় রাখতে হয়। দুধ পচনশীল পণ্য। খামারি যখন তার উৎপাদিত দুধ কাক্সিক্ষত দরে বিক্রি করতে পারেন না, তখন তাকে বাধ্য হয়েই লোকসান হলেও কম দামে বিক্রি করে দিতে হয়। আমরা দুধের উৎপাদন বাড়ানোর কাজটি শুরু করলেও একই সঙ্গে দুধ প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণের কাজটি করিনি বা করতে পারিনি।
বাংলাদেশের প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয় গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য আমদানি করতে। স্বাধীনতার পরপরই এ খাতকে উন্নত করার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও আমরা চাহিদার ২০ শতাংশও উৎপাদন করতে পারছি না। দেশে দুগ্ধ খাত বিকশিত না হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যার মধ্যে আমদানি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিকেই বোধ হয় বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। না হলে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করার বিষয়টিকে কেন আমলে নেওয়া হচ্ছে না। প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে উৎপাদনব্যবস্থা উন্নতকরণ সম্ভব নয়।
১০০ গরুর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট গরুকে চেহারা দেখে আলাদা করা যাবে কি? সাধারণভাবে নিশ্চয়ই না। আমাদের কাছে সব গরুই আদতে দেখতে একই রকম। চোখে দেখে শুধু রং ও আকারের পার্থক্য আমরা করতে পারব। কিন্তু আধুনিক যন্ত্র ঠিকই গরুর মুখে ক্যামেরা ধরে বলে দিতে পারে গরুর শারীরিক অবস্থা কেমন, কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করেছে। প্রযুক্তি, বিশেষ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) এবং আইওটি (ইন্টারনেট অব থিংস) উৎপাদনব্যবস্থাকে নিয়ে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য রকম এক প্রান্তে; যা কিছুদিন আগেও ছিল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, আজ তা চরম বাস্তব। এখন একা একজনের পক্ষেও একটি বিশাল খামার পরিচালনা করা কঠিন কাজ নয়।
২০১৫ সালে নেদারল্যান্ডসের ডো মার্কে গরুর খামারে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম। আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল গরুর খামার নয়, যেন কোনো এক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চলে এসেছি। ইন্টারনেট অব থিংস বা আইওটি কৃষিতে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর আনতে যাচ্ছে, এটা ছিল তারই স্মারক। যাকে বলা হচ্ছে স্মার্ট প্রযুক্তি। বর্তমান সময়ে স্মার্ট মানেই ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকা। মুহূর্তেই সব তথ্য পাওয়া যায় যেখান থেকে। এই শতাব্দীতে আমরা প্রবেশ করেছি স্মার্ট যুগে। নেদারল্যান্ডসের খামারটিও ছিল স্মার্ট একটি গরুর খামার। গরুর খাদ্য দেওয়া থেকে শুরু করে দুধ সংগ্রহ পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় যান্ত্রিক উপায়ে, স্মার্টলি। ডো মার্কের দুধ দোয়ানোর আধুনিক পদ্ধতিটাও বেশ চমকপ্রদ। সেখানে গাভি উন্মুক্ত বিচরণ করতে করতে নিজেই যখন উপলব্ধি করে তার দুধ দেওয়ার সময় হয়েছে, তখন লাইন ধরে দুধ দোয়ানো কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। শুধু গাভির উপলব্ধি দিয়ে যন্ত্র সন্তুষ্ট হয় না, যন্ত্র যখন তার হিসাব দিয়ে উপলব্ধি করবে যে দুধ দোয়ানোর জন্য গাভি প্রস্তুত, তখনই সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুধ দোয়ানো শুরু করবে, অন্যথায় নয়। ২০১৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার চুংনাম প্রোভিন্সের থম্বক গ্রামের কিম নামের এক খামারির খামারে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কিম দুই শতাধিক গরুর একটি খামার একাই পরিচালনা করছিলেন। অফিসকক্ষে বসে কম্পিউটারে সব নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। গরুর খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে দুধ দোহানো, দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সবই হচ্ছিল অটোমেটিক যন্ত্রের সাহায্যে। এ বছর এপ্রিলে নেদারল্যান্ডসের ফ্রেইডোপিল এলাকায় আর একটি ডেইরি ফার্ম দেখার সুযোগ হয়েছিল। ১১০০ হেক্টর জমির ওপর বিশাল এক খামার। খামারে ২৬০০টি গাভি। একেকটি গাভি বছরে দুধ দেয় ১১ হাজার লিটার। অথচ সম্পূর্ণ খামারটিতে মাত্র দুজন লোক। গাভির গোসল, খাবার দেওয়া, দুধ দোহানো সবই করছে যন্ত্র। উৎপাদিত দুধ চিলিং হয়ে অটোমেটিক প্যাকেটজাত হয়ে যাচ্ছে। দেখে বিস্মিত হতে হয়!
আমাদের দেশেও স্মার্ট গরুর খামার গড়ে উঠতে শুরু করেছে। নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চনে ব্যবসায়ী এম এ সবুর তার গরুর খামারটি নিয়ে এসেছিলেন গ্রামীণফোনের স্মার্ট গরুর খামার ব্যবস্থাপনায়। স্মার্ট ফার্ম ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি গরুর জন্য একটি করে চিপ থাকে। চিপটি সাধারণত গলার কলারে বা কানে ট্যাগে যুক্ত থাকে, যা গরুর শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক সব ধরনের তথ্যই সংগ্রহ করতে সক্ষম। যেমন গরুর দেহের তাপমাত্রা, রক্ত সঞ্চালন, জাবরকাটা থেকে শুরু করে প্রজনন সময়ের নির্ভুল হিসাব দেয়। মাতৃগরুর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য দিয়ে অসময়ের গর্ভপাত রোধ করতে সাহায্য করে। গরুর কী ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন, কী পরিমাণ আলো-বাতাস লাগবে, এমনকি গাভির দুধ দেওয়ার সময় সম্পর্কেও নানা তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত বেজ স্টেশন থেকে সরাসরি খামারির মোবাইল ফোনে চলে আসে। জানি না কী কারণে গ্রামীণফোনের ডিজি কাউ আর অগ্রসর হতে পারেনি। তবে আদর্শ প্রাণিসেবা লিমিটেডের ফিদা হক তার বোলাস কার্যক্রম এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রামে নাহার অ্যাগ্রো, গাজীপুরের আমেরিকান ডেইরি কিংবা মুন্সিগঞ্জের ডাচ ডেইরি তাদের খামারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছেন বেশ আগে থেকেই। কৃষি খামারে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব অর্থাৎ ইন্টারনেট অব থিংস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার যে আমূল পরিবর্তন এনেছে, তা উন্নত বিশ্বের এসব খামার না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হতো। এতে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে উৎপাদন ব্যয়, বেড়েছে খাদ্যের গুণগতমান।
টেকসই কৃষি অর্থনীতির প্রশ্নে সময় এখন বাণিজ্যিক কৃষি সম্প্রসারণের। উৎপাদনে বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে চাইলে প্রযুক্তির দিকেই ধাবিত হতে হবে। না হলে পিছিয়ে যেতে হবে প্রতিনিয়ত। বাণিজ্যিক কৃষি মানেই প্রযুক্তির কৃষি। আর প্রযুক্তির কৃষি মানেই বড় বিনিয়োগের কৃষি। একজন ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে বাণিজ্যিক কৃষিতে বিনিয়োগ সম্ভব নয়। ফলে শিল্প উদ্যোক্তাদেরই বাণিজ্যিক কৃষিতে অগ্রসর হতে হবে। আগেই বলেছি দেশে দুগ্ধ খাতে বাজার আছে। বাজারব্যবস্থাপনা ঠিক করে সুপরিকল্পিত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে এখনই আগামীর পথে হাঁটতে হবে।
লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব