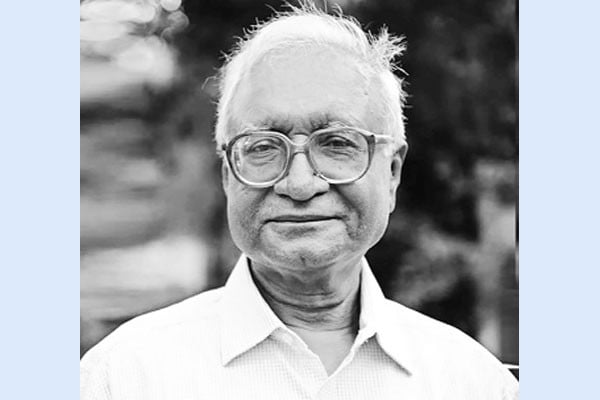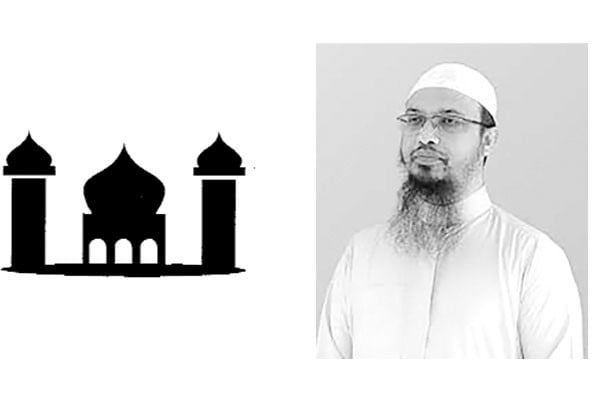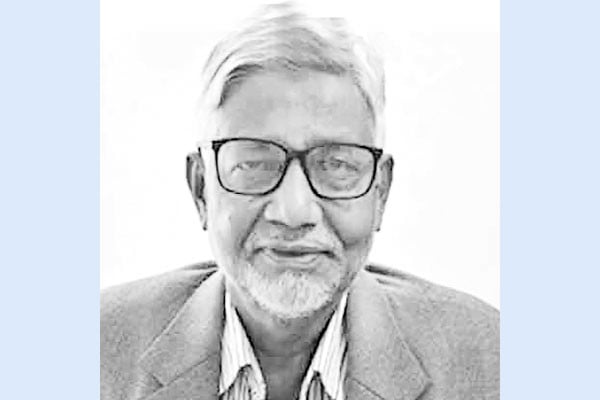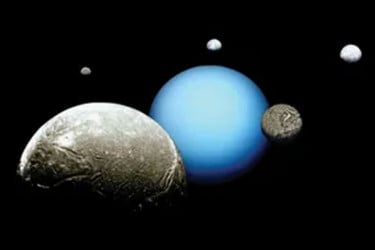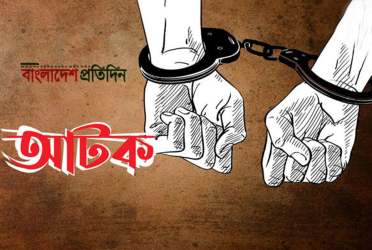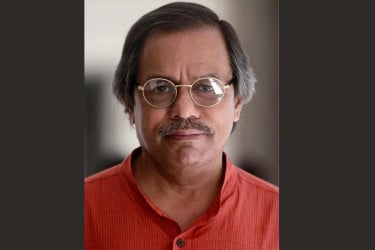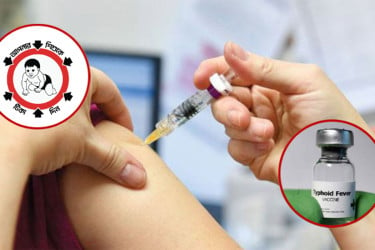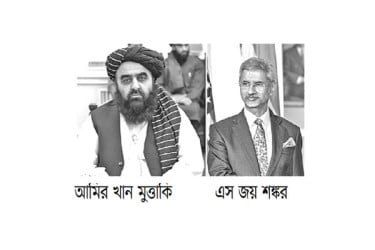ভাষার দূরত্বটা সামান্য নয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয় প্রধানত ভাষার কারণেই। ভারতের হিন্দুরা সবাই এক জাতি, মুসলমানরাও তেমনি এক জাতি। এই যে বিভাজন, এর ভিত্তিটা হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, সব হিন্দু এক নয়, তারা ভাষার দ্বারা বিভক্ত। ভাষাগত বিভক্তিই হচ্ছে চূড়ান্ত উপাদান, যার কারণে ভারতে এখন আঞ্চলিক বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। বিরোধের পেছনে অর্থনৈতিক বৈষম্যও অবশ্যই কার্যকর রয়েছে। যেমন বৈষম্য ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের কালে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর। যে বৈষম্যের দরুন অনিবার্য ছিল ওই রাষ্ট্রের ভেঙে যাওয়াটা। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যে নিজেদের আলাদা করে চিনেছিল, সেটা ভাষার ভিত্তিতেই। ভারতের আসামে একসময় উগ্র বাঙালিবিদ্বেষ বিরাজমান ছিল। কারণ ছিল এই যে অসমিয়ারা মনে করত বাঙালিরা নানা ক্ষেত্রে জবরদখল চালাচ্ছে। এবং ওই বাঙালিদের আলাদা করে চেনা যেত ভাষা দিয়েই। এখনো অসমিয়ারা বাঙালিদের পাশাপাশি বিহারিদের অপছন্দ করা শুরু করেছে বলে শোনা যায়। কারণ এই যে তারা দেখছে বাংলা ভাষা নয়, হিন্দি ভাষাই এখন দৌরাত্ম্য করছে, এবং হিন্দিভাষীদের আধিপত্যও প্রকাশ পাচ্ছে। ধর্ম কী সেটা জানার আগে ভাষা কী সেটাই জানার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিভক্ত ভারতে যখন প্রবল হিন্দু, মুসলিম বিরোধ চলছিল, তখন ভাষাগত পরিচয়ের প্রশ্নটি ওপরে উঠতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের নিচে তা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারত-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আর চাপা পড়ে থাকতে রাজি হয়নি। গণপরিষদের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে জিন্নাহ যা বলেছিলেন, সেটা অনেকেরই জানা। জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন যে পাকিস্তানে আর দ্বিজাতিতত্ত্ব থাকবে না, সবাই হবে পাকিস্তানি। তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের নাগরিকদের উদ্দেশে তার উক্তিতে ইসলামি রাষ্ট্রের কথা ছিল না, মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এমন বক্তব্যও ছিল না। বলা হয়েছিল, নতুন রাষ্ট্রে সব নাগরিক সমান অধিকার ও সুযোগ পাবে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। আসলে তিনি একটি নতুন জাতীয়তাবাদের কথাই বলেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের। এই রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ ও বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো বৈষম্য থাকবে না। জিন্নাহ বললেন; কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এটা যে ভাষার কথাটা তিনি মোটেই আনেননি। তার অর্থ এই নয় যে ভাষাকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অর্থ সম্ভবত এটাই যে তিনি ধরেই নিয়েছেন যে নতুন রাষ্ট্র এবং তার জাতীয়তাবাদ উভয়েরই ভাষা হবে উর্দু। যদিও এটা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই না-জানার কথা ছিল না যে ওই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে তখন শতকরা ৫৬ জন ছিল বাঙালি।
ভাষার প্রশ্নকে তিনি যে খুবই গুরুত্ব দেন, সেটা বোঝা গিয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই। জিন্নাহ বলতেন ‘We are a nation with our distinctive culture and civilization, language and literature’ ইত্যাদি। বিশেষভাবে বোঝা গেল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত মাস পরে যখন তিনি ঢাকায় প্রথম ও শেষবারের মতো এলেন এবং জনসভায় ঘোষণা দিলেন, ‘উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা’। এর কয়েক মাস আগে গণপরিষদের বক্তৃতায় ভারত বিভাগের যৌক্তিকতার প্রশ্নে স্বল্পমাত্রার হলেও যে সংশয়ের আভাস পাওয়া গিয়েছিল, এ বক্তৃতায় সেটা অন্তর্হিত। এবং ভাষার প্রশ্নে তিনি অনমনীয়। কেবল সভায় উপস্থিত ঢাকাবাসীকে নয়, তাদের মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গের সব মানুষকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কোনো রকমের দ্বিমত সহ্য করা হবে না, উর্দুর বিরুদ্ধে যারা বলবে, তাদের নির্ভেজাল রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হবে। ধর্মের ভিত্তিতে এক করা গেল না, তাই ভাষার ভিত্তিতেই পাকিস্তানিদের ঐক্যবদ্ধ করবেন বলে আশা করেছিলেন। তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি, বরঞ্চ ঘটনার চরম বক্রাঘাত এখানেই যে উর্দু ভাষাভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি বাংলা ভাষাভিত্তিক পাল্টা বাঙালি জাতীয়তাবাদ গঠনে পূর্ব বঙ্গবাসীকে উৎসাহিত করেছেন। ভাষার প্রশ্নে রাষ্ট্রদ্রোহের ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহকেই তিনি অনুপ্রাণিত করলেন। এবং পরে সামরিক অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানকে দমন করা যায়নি, বরঞ্চ তাকে আরও আপসহীন করে তোলা হয়েছে।
 বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(১) ধারায় বলা হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পুরুষ-নারী অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হবে না। সংগতভাবেই বলা যায় যে ভাষা যে বৈষম্য সৃষ্টির একটা উপাদান হতে পারে সংবিধান রচনার সময় সেই ব্যাপারটা খেয়াল করা হয়নি। পাকিস্তানি রাষ্ট্রের কর্তারা যেমন ধরে নিয়েছিলেন যে ওই রাষ্ট্রে উর্দুই হবে প্রধান ভাষা, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষও তেমনি, সেই একইভাবে, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার কথা ভাবেনইনি। পরে অবশ্য দেখা যাচ্ছে নানা ক্ষেত্রে বাংলার কোণঠাসা হওয়ার দশা হয়েছে, ইংরেজির ধাক্কায়। সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলাভাষী ভিন্ন অন্য কোনো নাগরিক থাকবে না, এটা তো সত্য হতে পারে না। অবাঙালিরা এখানে তখনো ছিল, এখনো আছে। এবং থাকবেও। উর্দুভাষীরা আছে, তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সদস্যরা। পাকিস্তানিরা যেমন ধারণা করেছিল তাদের রাষ্ট্র হবে এক জাতির, সেই পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে এসে বাঙালিরাও ধরে নিল যে তাদের রাষ্ট্রও হবে এক জাতিরই। কেবল বাঙালিদেরই। বোঝা গেল অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। জিন্নাহ যদি আশা করে থাকেন যে ভেদাভেদ ভুলে সবাই হবে পাকিস্তানি, তাহলে আমাদের শাসকরা ধরে নিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের সব নাগরিকই হয়ে যাবে বাঙালি।
বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(১) ধারায় বলা হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পুরুষ-নারী অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হবে না। সংগতভাবেই বলা যায় যে ভাষা যে বৈষম্য সৃষ্টির একটা উপাদান হতে পারে সংবিধান রচনার সময় সেই ব্যাপারটা খেয়াল করা হয়নি। পাকিস্তানি রাষ্ট্রের কর্তারা যেমন ধরে নিয়েছিলেন যে ওই রাষ্ট্রে উর্দুই হবে প্রধান ভাষা, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষও তেমনি, সেই একইভাবে, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার কথা ভাবেনইনি। পরে অবশ্য দেখা যাচ্ছে নানা ক্ষেত্রে বাংলার কোণঠাসা হওয়ার দশা হয়েছে, ইংরেজির ধাক্কায়। সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলাভাষী ভিন্ন অন্য কোনো নাগরিক থাকবে না, এটা তো সত্য হতে পারে না। অবাঙালিরা এখানে তখনো ছিল, এখনো আছে। এবং থাকবেও। উর্দুভাষীরা আছে, তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সদস্যরা। পাকিস্তানিরা যেমন ধারণা করেছিল তাদের রাষ্ট্র হবে এক জাতির, সেই পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে এসে বাঙালিরাও ধরে নিল যে তাদের রাষ্ট্রও হবে এক জাতিরই। কেবল বাঙালিদেরই। বোঝা গেল অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। জিন্নাহ যদি আশা করে থাকেন যে ভেদাভেদ ভুলে সবাই হবে পাকিস্তানি, তাহলে আমাদের শাসকরা ধরে নিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের সব নাগরিকই হয়ে যাবে বাঙালি।
অথচ ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগ মোহাজের সমস্যার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিল। প্রতিশ্রুতিটা ছিল এরকমের যে মোহাজেরদের স্থায়ী ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে তারা যাতে অন্য নাগরিকদের মতো সুযোগসুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানে সংখ্যালঘু সমস্যার স্বীকৃতি এলো না। সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে অস্বীকৃতি হলো আরও প্রবল।
স্মরণীয় যে কেবল সত্তরে নয়, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি তুলে নেওয়ার পর ১৯৫৬-তে অনুষ্ঠিত (মে ১৯-২০) কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে মোহাজের সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, ‘পাকিস্তানের মোহাজের সমস্যা এক বৃহৎ সমস্যা। মোহাজের সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত কোন কর্মসূচি সরকারের নাই। দুস্থ মোহাজেরদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে হইলে সরকার ও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। মোহাজের তথা, শরণার্থীদের আশ্রয়দাতাগণই আনসার। এই আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়দাতা তথা মোহাজের, আনসারদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। এই ঐক্য সহযোগিতা বর্ধনের জন্য এই সভা কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইতেছে।’
অবাঙালিরা যে পূর্ব পাকিস্তানে অসুবিধায় আছে এ কথা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার জনসভায় উল্লেখ করেছিলেন। ওই বিশাল সমাবেশে বাঙালিরা তো ছিলই, অবাঙালিরাও ছিল। ‘উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে’ এই ঘোষণায় বাঙালিরা ভড়কে গেছে, কেউ কেউ ‘না না’ বলেছে; কিন্তু উর্দুভাষীরা সেদিন নিশ্চয়ই অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিল। হওয়ারই কথা। তাদের পক্ষে এটাই ভাববার কথা যে মাতৃভূমি ত্যাগ করে তারা পাকিস্তানে এসেছে বটে, তবে পাকিস্তানি রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বরঞ্চ তারাই হবে এর প্রকৃত নাগরিক। তাদের তুলনায় বাঙালিরা থাকবে নিচের স্তরে। কেননা বাঙালিরা উর্দুভাষা জানে না। উর্দু শেখার চেষ্টা করবে হয়তো, কিন্তু যতই চেষ্টা করুক উর্দু যাদের মাতৃভাষা তাদের স্তরে উঠতে পারবে না। উর্দুভাষীরা এমনিতেই বাঙালিদের চেয়ে নিজেদের উঁচু জ্ঞান করত, যে মনোভাবের পেছনে তারা একাধিক যুক্তিও দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। প্রথমত তারা মনে করতো উর্দু হচ্ছে মুসলমানদের ভাষা, আর বাংলা ভাষা হলো অমুসলমানদের ভাষা, সেদিক থেকে তারা তাই উচ্চতর মুসলমান। স্মরণীয় যে ভাষার ব্যাপারে বাঙালিদের মধ্যেও কারও কারও মনে হীনম্মন্যতা বোধ ছিল। যেজন্য কেউ কেউ ঘরে উর্দু ব্যবহার করতে চাইত, নিজেদের মুসলমানত্ব ও আভিজাত্যের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে। এটাও ভুললে চলবে না যে অবিভক্ত বাংলার দুজন মুখ্যমন্ত্রী, খাজা নাজিমুদ্দিন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উর্দুভাষী ছিলেন। এবং এমনকি এ কে ফজলুল হকও বিয়ে করেছিলেন উর্দুভাষী গৃহে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে এ ঘোষণা নাজিমুদ্দিন জোর গলাতেই দিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী অতটা জোরে না বললেও এমনকি বায়ান্ন সালেও একুশে ফেব্রুয়ারির পরে করাচি থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সরকারের ‘আহাম্মকি’র সমালোচনা করেছিলেন এ কথা বলে যে সরকার শিক্ষার মধ্য দিয়ে উর্দুকে গ্রহণযোগ্য করে না তুলে জোর করে তাকে চাপাতে গিয়ে সংকটের সৃষ্টি করেছে। উর্দুভাষীদের উচ্চম্মন্যতার দ্বিতীয় কারণ ছিল তাদের এই বোধ যে তারা স্থানীয় জনগণের চেয়ে যোগ্যতা, দক্ষতা ও শিক্ষায় অধিক অগ্রসর। কৃষিকার্য করত যে বিহারি, সে তো আর পূর্ব পাকিস্তানে আসেনি, যারা এসেছিল তারা নানা পেশা ও ব্যবসায় জড়িত ছিল। তাদের অনেকের মধ্যে খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহ ছিল, যেজন্য ১৯৪৮-৬৯-এর মধ্যে ঢাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে উর্দু ভাষায় ছয় ছয়টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, ঢাকা ও অন্যান্য শহর থেকে সাপ্তাহিক ও সান্ধ্য দৈনিক মিলিয়ে প্রকাশনার সংখ্যা ছিল বিশটি। শেষ দিকে পাকিস্তান অবজারভার গোষ্ঠী থেকে উর্দুভাষায় দৈনিক ওয়াতান ও চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক চিত্রালীর উর্দু সংস্করণও প্রকাশ করা শুরু হয়েছিল।
উচ্চম্মন্যতার এই বোধ উর্দুভাষীদের পক্ষে বাঙালির সঙ্গে একই রাজনৈতিক ধারায় মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে। এই সমস্যাটা পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী মোহাজেরদের ক্ষেত্রে ততটা দেখা দেয়নি। রাজনৈতিকভাবে তারা মিশে যেতে চেষ্টা করেছে এবং মুসলিম লীগের জন্য কোনো ভোটব্যাংক তৈরি করতে সম্মত হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানে যেটা তারা করেছিল। কেবল তাই নয়, একাত্তরে তারা চিহ্নিত হয়েছিল চরম বাঙালিবিদ্বেষী বলে। পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী হয়ে তারা বাঙালিনিধনে অংশ নেয় এবং যুদ্ধ শেষে নিক্ষিপ্ত হয় বিপদের ভীষণ গহ্বরে। মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে তারা নিজেদের মনে করেছে আটকে পড়া পাকিস্তানি। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিরা ছিল, যাদের বাংলাদেশ সরকার ফেরত নিয়ে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি। যার ফলে তাদের অধিকাংশকেই মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। অর্থাৎ পাকিস্তান তাদের দুই দুইবার শরণার্থী করল, একবার সৃষ্টির সময়ে আরেকবার পতনের মুহূর্তে।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়