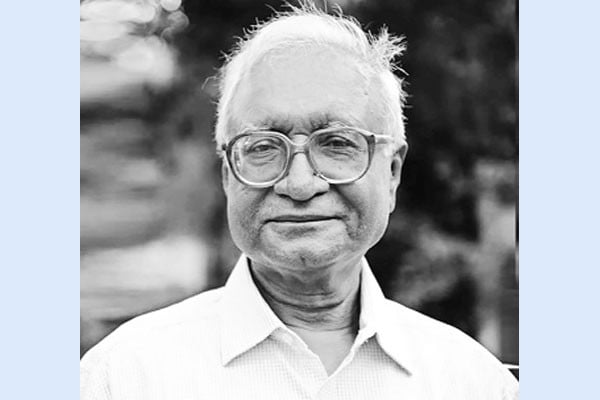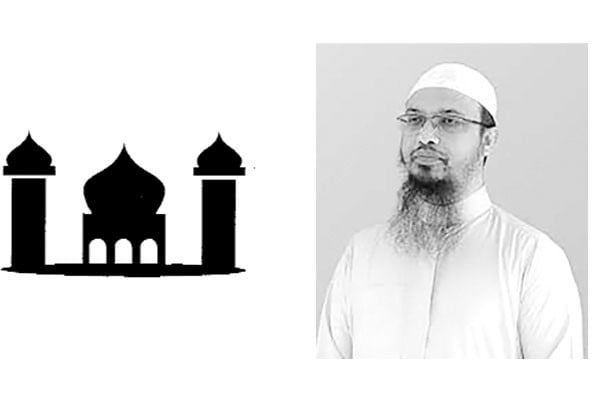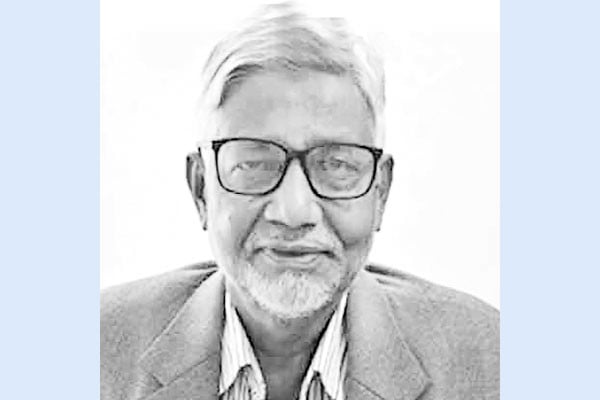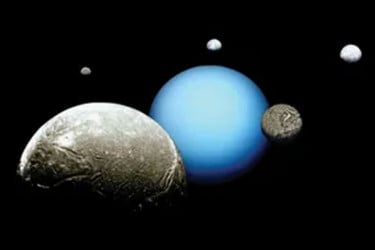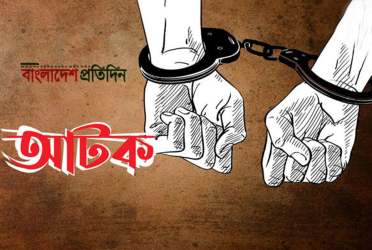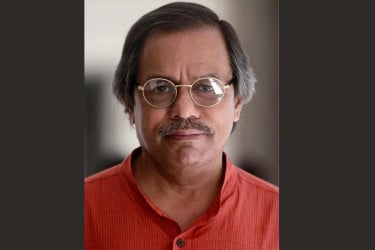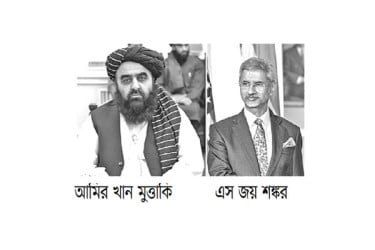গত মাসে মানিকগঞ্জে একটি কৃষিবিষয়ক তথ্যচিত্র নির্মাণের সময় দেখা হয় তরুণ এক উদ্যোক্তার সঙ্গে। নাম শহিদুল ইসলাম। কথা বলে বুঝতে পারি শহিদুল একজন দারুণ উদ্ভাবনী কৃষক। তিনি নিজেই তৈরি করেছেন মালচিং পেপার কাটার একটি সহজ, দ্রুত ও নিখুঁত পদ্ধতি। প্রয়োজন আর সৃজনশীলতা থেকেই জন্ম নিয়েছে এই উদ্ভাবন। দেশজুড়ে এমন অসংখ্য কৃষক রয়েছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনেই নতুন কিছু আবিষ্কার করে চলেছেন। মনে পড়ে গেল নেত্রকোনার কেনু মিস্ত্রির কথা, যিনি একসময় দেশীয় উপায়ে তৈরি করেছিলেন অসংখ্য কৃষিযন্ত্র।
এই গল্পগুলো শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বজুড়েই। কৃষকরা যুগে যুগে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করেছেন নানা ধরনের যন্ত্র। তবে আজকের কৃষি এক নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে যান্ত্রিকীকরণ মানে শুধু মাঠে উদ্ভাবন নয়, বরং প্রযুক্তি, তথ্য এবং নির্ভুলতার মাধ্যমে কৃষির রূপান্তর। বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের যাত্রা হতে হবে বৈশ্বিক পরিবর্তনেরই অংশ, যেখানে স্থানীয় উদ্ভাবন আর আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটবে। প্রতি বছর চীনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কৃষি যন্ত্রপাতির মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। প্রতি বছরই দেখি যন্ত্রপাতিগুলো আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে। প্রশ্ন যখন একই সঙ্গে অধিক উৎপাদন এবং মানে নিরাপদের, তখন যান্ত্রিক কৃষির বিকল্প আর কী হতে পারে?
বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি এখনো কৃষি। প্রায় ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান এবং জিডিপির প্রায় ১২ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। এ কথা সত্য, বৈশ্বিক তুলনায় পরিবর্তনের গতি কম হলেও গত কয়েক দশকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে এক নীরব বিপ্লব ঘটেছে, যা বদলে দিয়েছে ফসল উৎপাদন, শ্রমের চাহিদা এবং গ্রামীণ জীবনের চিত্র। এশিয়ার মধ্যে চীন সবচেয়ে এগিয়ে। তাদের ধান, গম ও ভুট্টা উৎপাদনের প্রায় পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিকীকরণ হয়েছে। বাংলাদেশও ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, প্রতিবেশী দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের বাস্তবতায় তা প্রয়োগ করছে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৯০ শতাংশ জমি প্রস্তুত করা হয় পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টরের মাধ্যমে। যেখানে ১৯৯০-এর দশকে এই হার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। সেচব্যবস্থাও এখন প্রায় ৮০ শতাংশ যান্ত্রিক, যা সম্ভব হয়েছে লো-লিফট পাম্প ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে। তবে ফসল কাটার ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে। ধান কাটার ক্ষেত্রে মাত্র ১০-১৫ শতাংশ যান্ত্রিকীকরণ হয়েছে, যেখানে চীনে এই হার ৮০ শতাংশেরও বেশি। বোরো ও আমন মৌসুমে শ্রমিকসংকটে ভোগেন কৃষকরা। যার ফলে প্রতি বছর ৬-১০ শতাংশ ফসল উৎপাদন পরবর্তী ক্ষতির মুখে পড়ে (DAE-এর তথ্য অনুযায়ী)। সরকার ও বেসরকারি উদ্যোক্তারা কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার ও রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছেন। তবে বরাবরের মতো সরকারের বক্তব্য আর মাঠের চিত্র এক হয় না। ভর্তুকি দেওয়া কৃষিযন্ত্রের বিষয়ে আমরা যে মাঠ প্রতিবেদন পেয়েছি, তা হতাশাজনক। প্রথমত অনেক প্রকৃত কৃষক বঞ্চিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত কৃষকের নামে ব্যবসায়ীরা ভর্তুকির যন্ত্র তুলে নিয়েছেন। তৃতীয়ত অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মনে পড়ছে, বরগুনায় একদল কৃষক একসময় অভিযোগ করেন, তারা চেয়েও কৃষিযন্ত্র পাননি। আর যিনি পেয়েছেন, তিনি আসলে কৃষক নন।
যাই হোক, সব সময় বিশ্বাস করি, যারা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে, অভিজ্ঞ, সে বিষয়ে তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া, শিক্ষা নেওয়া কর্তব্য। চীনের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। তাদের প্রায় ৩০ কোটি হেক্টর জমিতে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার হয়। জিপিএসনির্ভর ট্রাক্টর, স্প্রে করার জন্য ড্রোন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক পোকা শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। BeiDou স্যাটেলাইট সিস্টেমের মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন যন্ত্র যুক্ত হয়েছে নির্ভুল কৃষিকাজে। চীনের সরকারের সঙ্গে আমাদের সরকারের সম্মিলিত একটা প্রয়াস হতে পারত এ সংকট নিরসনের দারুণ পদক্ষেপ।
কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারত ও নেপালের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে ধীর। ভারতে জমি প্রস্তুত ও সেচে প্রায় ৬০ শতাংশ যান্ত্রিকীকরণ হয়েছে, তবে ফসল কাটার প্রযুক্তি রাজ্যভেদে ভিন্ন। পাঞ্জাব অনেক এগিয়ে, কিন্তু পূর্বাঞ্চল পিছিয়ে। নেপাল, যেখানে জমির মালিকানা খণ্ডিত, সেখানে যান্ত্রিকীকরণ ৪০ শতাংশের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। তবে চীনের সঙ্গে ব্যবধান এখনো অনেক।
বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২৫ মেয়াদে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যেখানে কৃষিযন্ত্রের মূল্যের ৫০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০ হাজারের বেশি আধুনিক যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে কৃষক, সমবায় ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা ভিন্ন। বাংলাদেশে জমির পরিমাণ কম, অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র বা মাঝারি। তাই ভর্তুকি দেওয়া উচিত ছোট আকারের যন্ত্রে। কিন্তু এ পরামর্শগুলো গুরুত্ব পায়নি। যান্ত্রিকীকরণে বৈশ্বিক র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে। তবু আশার কথা হচ্ছে, দেশীয় উদ্ভাবন বাড়ছে। বেসরকারি পর্যায়ে অনেক প্রতিষ্ঠান ছোট আকারের, হালকা যন্ত্র যেমন মিনি-কম্বাইন হারভেস্টার ও লাইট রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এখন আমদানি বা স্থানীয়ভাবে তৈরি করছে, যা খণ্ডিত জমির জন্য উপযোগী।
যান্ত্রিকীকরণ যেমন সম্ভাবনা নিয়ে আসে, তেমনি উদ্বেগও। একদিকে এটি শ্রম কমায়, উৎপাদন বাড়ায়, ফলন স্থিতিশীল করে। অন্যদিকে এটি জীবাশ্ম জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় এবং বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকলে গ্রামীণ শ্রমিকদের বিপদে ফেলতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন ‘ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ দরকার, যেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, দক্ষ সেচ পাম্প এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক পরামর্শব্যবস্থার সমন্বয় থাকবে।
বাংলাদেশ এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। গ্রামীণ শ্রম কমছে, খাদ্য নিরাপত্তার চাহিদা বাড়ছে। এই অবস্থায় যান্ত্রিকীকরণ বিলাসিতা নয়, বরং অপরিহার্য। চীনের অভিজ্ঞতা দেখায়, কীভাবে AI, রোবটিক্স ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি কৃষিকে বদলে দিতে পারে। বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো এই অভিজ্ঞতাগুলোকে নিজেদের ক্ষুদ্র কৃষকভিত্তিক ব্যবস্থায় মানিয়ে নেওয়া, যাতে সব স্তরের কৃষক, বড় কিংবা প্রান্তিক, সবাই উপকৃত হতে পারেন।
এখন সময় বদলেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক নতুন যুগের দোরগোড়ায়, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে। এখন কৃষি উদ্ভাবন শুধু মাঠের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, প্রযুক্তি, তথ্য আর নির্ভুলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে। বাংলাদেশের কৃষি যাত্রা এই বৈশ্বিক পরিবর্তনেরই প্রতিচ্ছবি, যেখানে ঐতিহ্যগত জ্ঞান আর আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধরাধরি করে এগোচ্ছে। পুরো এশিয়া এখন স্মার্ট কৃষির যুগে প্রবেশ করছে, বাংলাদেশও ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ভবিষ্যতের কৃষিতে, ফসলের ভাগ্য নির্ধারণে প্রযুক্তি হবে বৃষ্টির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি এখনই উপলব্ধিতে আনতে হবে।
লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব