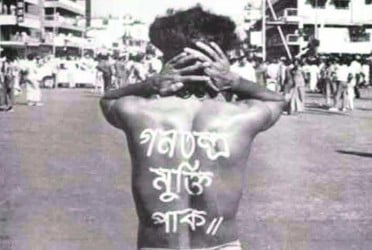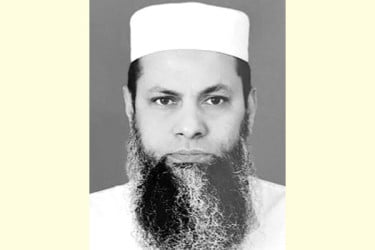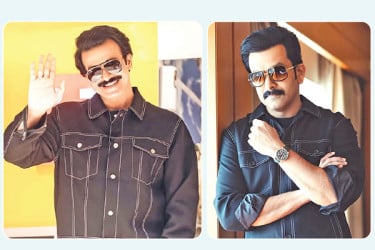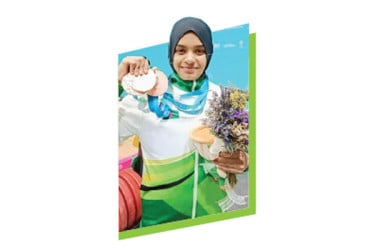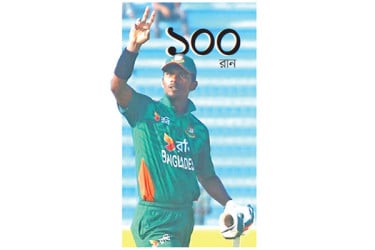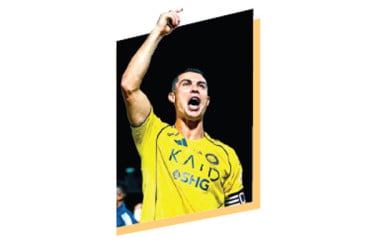যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যেরকম তাড়াহুড়ো করেছিল, সেই সিদ্ধান্ত বিচারের ক্ষেত্রেও এখন বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্লেষকদের মধ্যে একই ধরণের তাড়াহুড়ো দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি এরা সবাই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এই বলে তিরস্কার করছেন যে, এই সিদ্ধান্তটি ছিল অপ্রয়োজনীয়। এটি আফগানিস্তানে যারা লড়াই করতে গেছে, তাদের এবং আফগান জনগণ- এই উভয়ের সঙ্গেই একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা।
কাবুল বিমানবন্দরের যেসব মর্মান্তিক ছবি প্রকাশ পেয়েছে, তা যেন আরও জোরেশোরে এই একই বার্তা দিচ্ছে। এবং এ নিয়ে অনেক ধরণের আবেগের প্রকাশ ন্যায়সঙ্গতভাবেই দেখা যাচ্ছে। আফগানিস্তানে পশ্চিমা দেশগুলো অনেক রক্ত, সময় এবং অর্থ বিনিয়োগ করেছে। আফগান জনগণের বিনিয়োগ ছিল তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি।
বাইডেন প্রশাসনের তড়িৎ গতিতে আফগানিস্তান ত্যাগের যে সমালোচনা চলছে, তার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দেয়া কঠিন। আফগানিস্তানকে হয়তো আসলেই আর উদ্ধার করা যাবে না। দেশটির শাসন কাঠামো একেবারেই অপ্রতিনিধিত্বশীল এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু এই কথার মাধ্যমে কিন্তু আবার এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, আফগানিস্তান যে রসাতলে গেছে, সেটা গত দু বছরে ঘটেনি, এটা চলছিল আসলে গত ২০ বছর ধরেই।
তবে তারপরও একটা কথা বলতেই হচ্ছে- আফগানিস্তান থেকে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে সটকে পড়লো, তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এক বিরাট আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে একটি মিত্রদেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্ব পরিসরে তাদের নৈতিক অবস্থান কিন্তু এখন বিরাট প্রশ্নের মুখে। অথচ প্রেসিডেন্ট বাইডেন যখন দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তখন কিন্তু একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন- আমেরিকা আবার বিশ্বে তার আগের ভূমিকায় ফিরে এসেছে।
ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা
আফগানিস্তানে যা ঘটেছে তার তুলনা করা হচ্ছে ভিয়েতনামের সঙ্গে। শত্রুপক্ষের হাতে পতন ঘটছে এমন এক শহর থেকে মার্কিন নাগরিকদের হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হচ্ছে- সংবাদপত্রগুলোর পক্ষে এরকম ছবি প্রথম পাতায় ছাপানোর লোভ সামলানো বেশ কঠিন। তবে বাস্তবে- এই দুটি ঘটনায় উপরে উপরে যত মিলই থাক- কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও কিন্তু আছে।
দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতন ঘটেছিল মার্কিন সৈন্যরা চলে যাওয়ার দুই বছর পর। মনে হচ্ছে আফগানিস্তানের বেলায় যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল, তারা চলে আসার পরও তাদের আফগান মিত্ররা মার্কিনীদের ছাড়াই আরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় ধরে টিকে থাকতে পারবে।
ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা যুক্তরাষ্ট্রকে একেবারে হতমান করে দিয়েছিল। ভিয়েতনাম নিয়ে মার্কিন জনমত ছিল পুরোপুরি বিভক্ত, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর মনোবল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু ভিয়েতনাম ছিল স্নায়ুযুদ্ধের এক বিয়োগান্তক সাইড শো। যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এই স্নায়ুযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। ভিয়েতনামের কারণে নেটো দুর্বল হয়নি। বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা এরপরও কিন্তু মার্কিন সাহায্য প্রত্যাশা করতে কোন দ্বিধা করেনি। বিশ্বের প্রধান এক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থানে অটুট ছিল।
কিন্তু আফগানিস্তানের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। আফগানিস্তান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রে যে ধরণের আভ্যন্তরীণ বিভেদ ছিল, তার সঙ্গে ভিয়েতনামের কোন তুলনাই চলে না। আফগানিস্তান মিশন নিশ্চয়ই অজনপ্রিয় ছিল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে কোন গণবিক্ষোভ দেখা যায়নি, যেটি ঘটেছিল ভিয়েতনামের বেলায়।
মনে রাখা দরকার, ১৯৭০ এর দশকের আন্তর্জাতিক পটভূমির সঙ্গে আজকের পটভূমির বিরাট ফারাক আছে। যুক্তরাষ্ট্র- বা আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে পশ্চিমা বিশ্ব অনেকগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, যার কোন কোনটিতে তারা সুস্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছে।
'ওয়ার অন টেররের' বিপর্যয়
আফগানিস্তান যেভাবে ধসে পড়লো সেটা তথাকথিত 'ওয়ার অন টেরর' বা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের জন্য এক বড় বিপর্যয়। কিন্তু গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারের যে বৃহত্তর সংঘাত- সেই পটভূমিতে ওয়াশিংটনের এই ব্যর্থতাকে কেবল একটি গুরুতর পিছিয়ে-পড়া বলে গণ্য করা যেতে পারে।
মস্কো এবং বেইজিং এর মুখে হয়তো এখন হাসি ফুটবে, অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও। গণতন্ত্র আর আইনের শাসন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার কথা বলে পশ্চিমা দেশগুলো যে ধরণের উদারনৈতিক হস্তক্ষেপের নীতি এতদিন অনুসরণ করেছে- আফগানিস্তানের পরীক্ষায় তা পুরোপুরি যেন ধসে পড়লো। ভবিষ্যতে এরকম কাজে আর কারও উৎসাহ থাকবে বলে মনে হয় না।
ওয়াশিংটনের যে মিত্রদেশগুলো আফগানিস্তান প্রজেক্টে যুক্ত হয়েছিল, তারা এখন ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে মরছে। তারা মনে করছে ওয়াশিংটন আসলে তাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। যে ব্রিটিশ মন্ত্রীরা ওয়াশিংটনের সঙ্গে ব্রিটেনের 'বিশেষ সম্পর্ক' নিয়ে বড়াই করেন, তারাও কিন্তু এখন প্রকাশ্যে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সমালোচনা করছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের যারা ইউরোপীয় মিত্র, তাদের জন্য এবারের ঘটনায় কিন্তু একটা বিষয় পরিস্কার হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তারা যতই নির্ভর করুক, ওয়াশিংটন যখন কোন নির্দিষ্ট দিকে যাবে বলে ঠিক করে ফেলেছে, সেখানে তাদের মতামতের কোন তোয়াক্কাই আসলে হোয়াইট হাউজ করে না।
কাজেই আফগানিস্তানের এই বিপর্যয় পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য দুঃসংবাদ। কিন্তু বেইজিং, মস্কো এবং ইসলামাবাদের মুখে যে হাসি এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা কতদিন স্থায়ী হবে? তালেবানকে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিয়ে লালন করেছে পাকিস্তান, তালেবানকে একটা ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য ঠিক করে দিতে ভূমিকা রেখেছে তারা। কিন্তু আফগানিস্তানে তালেবানের নতুন শাসনের মানে যদি হয় সেই আগের দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া, যদি দেশটি আবারও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নিরাপদ চারণভূমি হয়ে উঠে- তাহলে কিন্তু পাকিস্তান নিজেও আবার বিপদে পড়বে। ঐ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার নেতিবাচক পরিণাম তাদেরও ভোগ করতে হবে।
চীনের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা চীনকে বেশ খুশি করবে। সত্যি কথা বলতে কী, বাইডেন যদি চীনকে ঠেকানোর দিকে বেশি মনোযোগ দেয়ার লক্ষ্যেই আফগানিস্তান থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাতে বরং উল্টো ফল হতে পারে। এটি বরং চীনকে আফগানিস্তানে এবং তারও বাইরে অন্যান্য দেশে তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ খুলে দিয়েছে।
তবে চীনেরও কিছু উদ্বেগ কিন্তু আছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে তাদের ছোট্ট এক অভিন্ন সীমান্ত আছে। চীন তার দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের কঠোরভাবে দমন করছে। বেইজিং বিরোধী ইসলামী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো এখন আফগানিস্তানকে একটা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে- সেরকম একটা দুশ্চিন্তা তাদের আছে। কাজেই সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে চীনা কূটনীতি তালেবানের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে যেরকম উদগ্রীব ছিল, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
আফগানিস্তানে অস্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবাদ ফিরে আসলে সেটা রাশিয়ার জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ। আফগানিস্তানের উপজাতীয় যোদ্ধাদের হাতে ১৯৮০র দশকের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে পরিণতি হয়েছিল, এখন যুক্তরাষ্ট্রও যে সেই একইভাবে নাকানি-চুবানি খেয়েছে, তা দেখে মস্কো হয়তো কিছুটা ভালো বোধ করছে। কিন্তু মস্কোর মূল স্বার্থ হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়ার বিরাট অঞ্চলের নিরাপত্তা, যেখানকার বহু দেশ মস্কোর মিত্র।
এবারের গ্রীস্মে সামরিক মহড়ার জন্য তাজিকস্তান-আফগান সীমান্তে মস্কো তাদের ট্যাংক মোতায়েন করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল এটা পরিস্কার করে দেয়া যে, আফগানিস্তানে সব ধসে পড়লে সেখানকার ঢেউ যেন সীমান্তের এদিকে এসে না লাগে, তা ঠেকাতে তারা প্রস্তুত।
কাজেই স্বল্প মেয়াদে আফগানিস্তানের এই বিপর্যয় থেকে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিপক্ষ নিশ্চিতভাবেই লাভবান হবে। তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন এমনিতেই হবে না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি, তা হলো, ওয়াশিংটনের মিত্রদের ওপর এর কী প্রভাব পড়তে যাচ্ছে।
আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে তারা কী শিক্ষা নেবে? এখনকার যে সংকট, সেটা কেটে গেলেও, ভবিষ্যতে নেটোর সদস্যদেশগুলো, কিংবা ইসরায়েল, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া বা জাপানের মতো দেশ কি যুক্তরাষ্ট্রকে আগের চেয়ে একটি কম নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে দেখবে?
যদি তারা সেরকমটাই ভাবে, তাহলে বাইডেনের আফগানিস্তান ছাড়ার সিদ্ধান্তের পরিণাম হবে সুদূরপ্রসারী।
বিডি প্রতিদিন/জুনাইদ আহমেদ