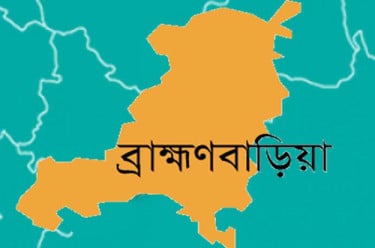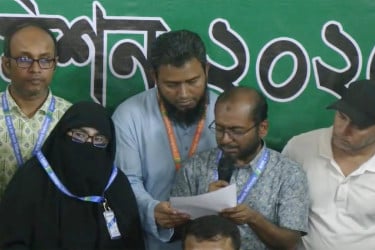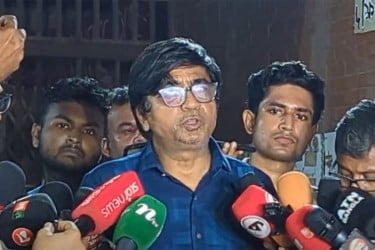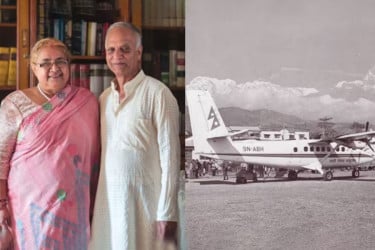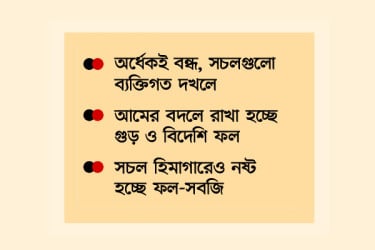বাংলাদেশ সশস্ত্র যুদ্ধের ইতিহাসে জাতীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য নৌ-কমান্ডো অপারেশন এক উজ্জ্বলতম অনন্য অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে পৃথিবীব্যাপী পরিচিত করেছিল নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা ১৫ আগস্ট 'অপারেশন জ্যাকপটের' অধীনে বাংলাদেশে চারটি বন্দরে ২৬টি জাহাজ ডোবানোর মাধ্যমে। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এমন কৃতিত্ব এবং দুঃসাহসিকতার নজির নেই। প্রবল পরাক্রমশালী এবং অপরাজেয় বলে খ্যাত পাকিস্তানি সেনা ও নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধজাহাজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল না বলেই ৫০০ বাঙালি যুবক জীবনকে উৎসর্গ করে শত্রুবাহিনীকে মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন। ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের বন্দরে ২৬টি জাহাজডুবির পর বিদেশি পত্রপত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমগুলো নৌ-কমান্ডো অভিযানকে অত্যন্ত সাফল্যজনক বলে মন্তব্য করে। নৌ-কমান্ডোদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে সারা বিশ্ব অবিভূত হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাকিস্তান নৌ-বাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল মুজাফফর হাসান পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং প্রায় মৃত নৌ-যানগুলো মেরামতের জন্য যন্ত্রাংশ, কারিগরি সাহায্য এবং নতুন নৌ-যান সংগ্রহের জন্য চীন, সৌদি আরব, তুরস্ক এবং মিসর সফর করেন। সামরিক বাহিনীতে বিশেষ গুরুত্ববহ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সমাধা করার জন্য একটি ছোট দল নির্বাচিত করে তাদের উচ্চতর বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াও পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষার জন্যও এমন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীকে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে।
যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি, শত্রুকে বিভ্রান্ত করা এবং মানসিক শক্তি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ দল গঠন করা হয় এবং তাদের ঠিক এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। যেমন- ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুর কবল থেকে নিজ পক্ষের সৈন্যদের ছিনিয়ে আনা, শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করা। একটি দেশের সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে এই বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলের কৃতকার্য (Special operation forces) সে দেশের গর্ব। সবসময় সেনাসদস্যদের এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দেওয়া হয় না। বিশেষ মুহূর্তে দেশকে রক্ষা অথবা অনুরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের নিয়োজিত করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নৌ-কমান্ডো অপারেশন এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। তারা সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ বাহিনীর (Special operation forces) গুরুত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।
নৌ-বাহিনীর অনেক সদস্য বিদেশে দায়িত্বরত ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেক বাঙালি কর্মকর্তা ও নাবিক অবস্থান করছিলেন। ফ্রান্সের তুল পোতাশ্রয়ে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর খরিদকৃত সাবমেরিন ম্যানগ্রোতেও বেশ কয়েকজন নাবিক কর্মরত ছিলেন। সাবমেরিনটি ১৯৭০ সালের ৫ আগস্ট ফ্রান্সে কমিশনে ছিল। তারা সাবমেরিনে প্রশিক্ষণকালীনই দেশে বিরাজমান গণআন্দোলনের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ রাখছিলেন। ২৫ মার্চ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্র্যাকডাউন হলে বিদেশি প্রচার মাধ্যমে এই সংবাদ প্রচারিত হয়। ২৭ মার্চ '৭১ তারা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া হয়েছি এ কথাও জানতে পারেন। এরপর অনেক প্রতিকূলতা মাড়িয়ে ৮ এপ্রিল ৮ জন বাঙালি নাবিক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারতে এসে পেঁৗছেন। মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডো দলের প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ। বিপজ্জনক স্পর্শকাতর মাইন ও বিস্ফোরকের সঠিক ব্যবহার রপ্ত করতে নিয়মিত নৌ-বাহিনীর একজন ক্যাডেট/নাবিকের সময় প্রয়োজন হয় কমপক্ষে তিন বছর। এ ছাড়া তাদের দেওয়া হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, পানির নিচ দিয়ে চলার জন্য আন্ডার ওয়াটার স্ক্রুতার রেডিও, ঘড়ি, বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য আধুনিক রিমোটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি। এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে আত্দঘাতী দল 'সুইসাইডাল স্কোয়াড'। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তারা কুণ্ঠিত ছিল না। অল্প সময়ে এই কঠিন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে তাদের দৈনিক ১৮ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছে। লিমপেট মাইন যেটি নৌ-কমান্ডোরা ব্যবহার করেছে, এর নির্মাণশৈলী অত্যন্ত কঠিন এবং সংযোজন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যে কারণে এই মাইনে ডেটনেটরাইজড করার জন্য পৃথক (বিশেষজ্ঞ) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একজন নৌ-কমান্ডোকে প্রতিকূল পরিবেশে পানির নিচ দিয়ে ১০/২০ মাইল সাঁতার কাটায় পারদর্শী করে তোলা হয়। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে ক্ষুদে সাঁতারু যুবকদের (frogmen) দ্বারা এতবড় যুদ্ধ সম্ভব কিনা তা নিয়ে পরিকল্পনাকারীরা সন্দিহান ছিলেন। তরুণ নৌ-যোদ্ধাদের দ্বারা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি একটি পরীক্ষামূলক অভিযান ছিল। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধে এতবড় সাফল্য বয়ে এনেছে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে তার হদিস পাওয়া যায় না।
'৭১-এর ১১ জুলাই মুজিবনগর উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ও যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন এবং কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্য স্থাপন করেন। এই বৈঠকে কর্নেল আবদুর রব সেনাপ্রধান এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার উপ-সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের পুরো যুদ্ধাঞ্চলকে একেকটি সেক্টরে বিভক্ত করে একেকজন অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।
স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল (অব.) এমএজি ওসমানীর একান্ত আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে স্থলবাহিনীর পাশাপাশি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য প্রথম একটি ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দরে জাহাজ ডোবানোর মতো বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ, বিদেশি জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে আসতে নিরাপদ না ভাবে এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে শত্রুবাহিনীর পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও শত্রুবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসনের মূলে আঘাত হানাই ছিল নৌ-কমান্ডো অভিযানের লক্ষ্য।
প্রবল পরাক্রমশালী ও শক্তিধর পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে টিকে থাকার মতো পর্যাপ্ত সরঞ্জাম, যুদ্ধজাহাজ এবং সেনাবল ছিল না বলেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যুদ্ধবিশারদরা নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এমন পরিকল্পনা এবং দৃষ্টান্ত বিরল। ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত শতাধিক অভিযান চালিয়ে নৌ-কমান্ডোরা ছোট-বড় মিলিয়ে শত্রুবাহিনীর ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ১৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে নৌ-কমান্ডো বাহিনীর দুনিয়া কাঁপানো সাফল্যজনক নৌ-বিধ্বংসী তৎপরতায়। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, নৌ-কমান্ডোদের সার্থক অপারেশন, চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য বাঙালি জাতির যুদ্ধজয়ের পথে নতুন গতিপথের সন্ধান দিয়েছিল।
স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানী দৈনিক বাংলা পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '১৯৭১-এর ১৫ আগস্ট আমাদের নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ শুরু হয়। তারা যে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই।'
১৯৭১-এর ১৩ মে প্রথম নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প 'সি-২ পি' সাংকেতিক নাম দিয়ে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী দিনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমান্ডার এমএন সামন্ত, লে. কমান্ডার জি মার্টিস এবং সাবমেরিনার আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী। সবারই বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়- এই স্বল্পতম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠিত হচ্ছে তা মূলত একটি 'সুইসাইডাল স্কোয়াড'। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বুঝিয়ে দেওয়ার পর কমান্ডোদের প্রত্যেককেই একটি করে সম্মতিসূচক ফরমে স্বাক্ষর করে ছবিসহ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়। ফরমে এই বলে উল্লেখ ছিল যে- 'আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে সম্মত হয়েই এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি। যুদ্ধে আমার মৃত্যু ঘটলে কেউ দায়ী থাকবে না।'
সাঁতারু বাঙালি নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের মূল অংশটি গঠিত হয়েছিল বাঙালি নাবিকদের ঘিরে, যারা পাকিস্তানি সাবমেরিন 'ম্যানগ্রো' থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে পরে যুক্ত হন আরও আটজন বাঙালি নাবিক, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দরে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে তারা কর্মস্থল ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। এই দুই দলের ১৬ জন সি-ম্যান মিলে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অতীব দক্ষ প্রশিক্ষণার্থীদের সাহায্যে গড়ে তোলেন মুক্তিবাহিনী ফ্রগম্যান বা সাঁতারু মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশটি। অসম সাহসী ও অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এসব যুবককে বাংলাদেশের নদীগুলো থেকে যথাসম্ভব সুবিধা নেওয়ার মতো সাঁতার কৌশল এবং দুঃসাহসী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সাহস তাদের ছিল। সম্পূর্ণ অন্ধকারে তাদের বিশ-পঁচিশ মাইল সাঁতরাতে হয়েছে বিশেষ পদ্ধতিতে চিৎ সাঁতারের মাধ্যমে। এরকম বিপজ্জনক ও দুঃসাহসী কাজ সাধারণত দেওয়া হয় উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'স্পেশাল মেরিন কমান্ডো গ্রুপকে'। উন্নত নৌ-বাহিনীতে এদের বলা হয় 'সিলস'। 'সাঁতারু মুক্তিবাহিনী শারীরিক-মানসিক দু'দিক থেকেই ছিল দুর্ধর্ষ। একটা গেরিলা অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন তার সবই বাঙালি সাঁতারু বাহিনীর ছিল। যেমন : অসম সাহসিকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং প্রচণ্ডতা। সব কিছুর ওপরে মুক্ত স্বদেশের স্বপ্ন এবং পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর তীব্র প্রতিশোধ গ্রহণের সাধ তাদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত করেছিল। তা ছাড়া তাদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, করত না কোনো লাভ-লোকসানেরও হিসাব। তারা তাদের লক্ষ্যের প্রতি ছিলেন উৎসর্গচিত্ত।'
১৫ আগস্ট, ১৯৭১ মধ্যরাতের পর বাংলাদেশের সমুদ্র ও নদীবন্দর কেঁপে ওঠে কমান্ডোদের পাতা মাইনের বিরতিহীন বিস্ফোরণে। দখলদার বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। বাণিজ্যিক জাহাজগুলো প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত বুঝতে পেরে S.O.S বার্তা পাঠাতে শুরু করে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-কমান্ডো বাহিনীর মাইন হামলায় দখলদার বাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ একের পর এক তলিয়ে যায় চট্টগ্রাম, মংলা, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরে গভীর পানির নিচে। এদিন বাংলাদেশের চারটি বন্দরে একই পরিকল্পনার অধীন আক্রমণ পরিচালিত হয়। নৌ-অভিযান একই দিনে পরিচালনার জন্য দুটি গানকে সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নৌ-কমান্ডোদের জানিয়ে দেওয়া হয়- ১৪/১৫ আগস্ট সকাল ৭টা ৩০ মিনিট আকাশবাণীতে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান'টি বাজলে অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে হবে। এর পরদিন অথবা যখন একই কেন্দ্র থেকে একই সময়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বাজবে, 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি'-এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেভাবেই হোক অপারেশন চালাতে হবে। কেবল প্রথম অপারেশনে এই সাংকেতিক গান ব্যবহৃত হয়। এরপর নৌ-কমান্ডোরা নিজেদের পরিকল্পনায় যুদ্ধ পরিচালনা করে। মধ্য আগস্ট থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত নৌ-কমান্ডোরা বাংলাদেশের জলসীমায় শতাধিক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে শত্রুবাহিনীর প্রায় এক লাখ টন যুদ্ধাস্ত্র ও সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত এবং প্রায় এক লাখ টন আংশিক বা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোরা স্বাধীনতার জন্য গৌরবময় ভূমিকা রাখে।
লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর কর্মকর্তা।