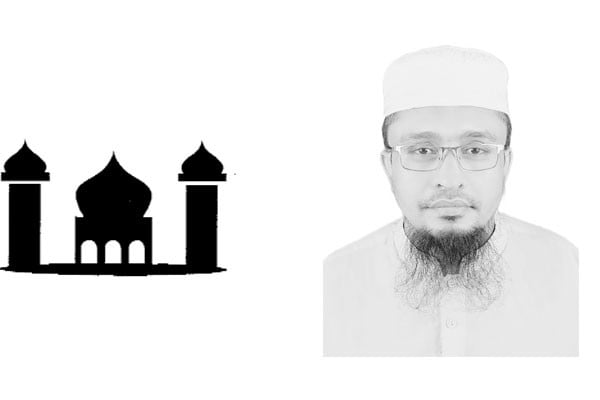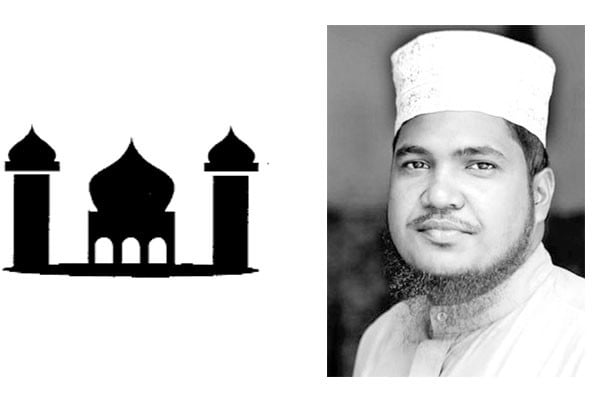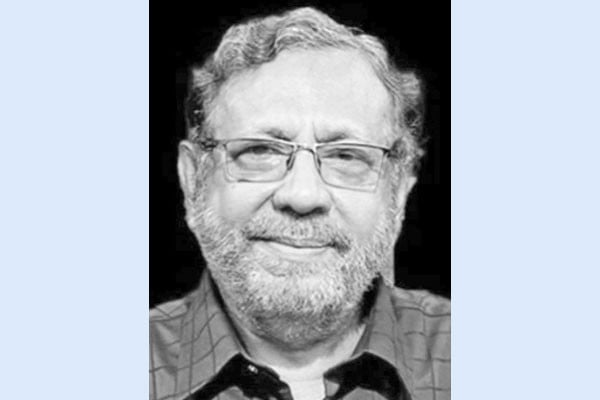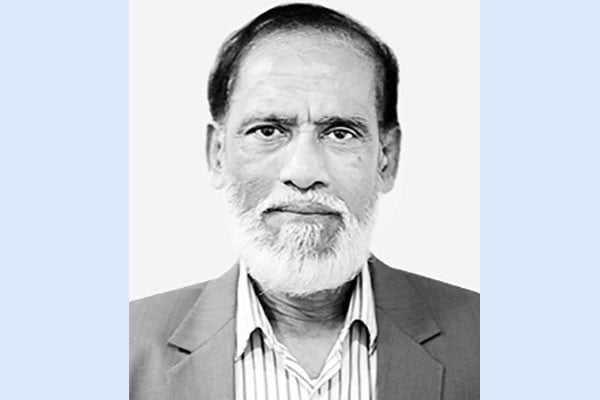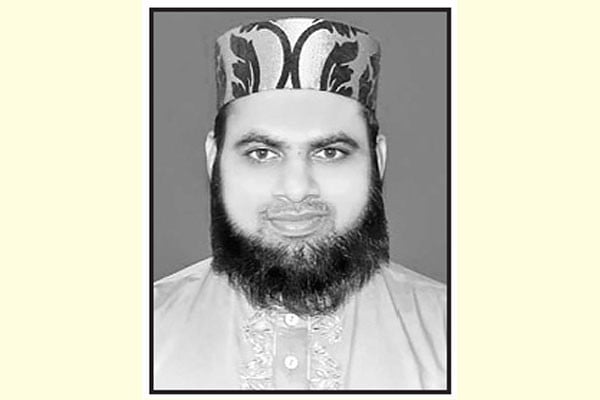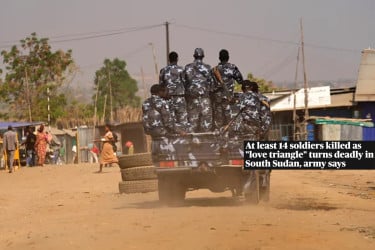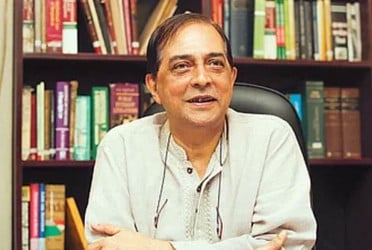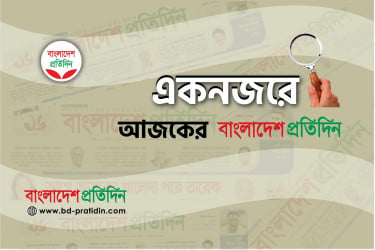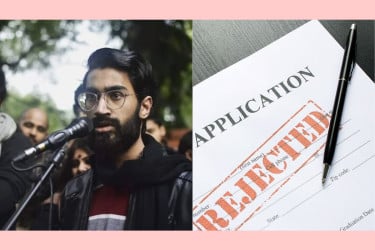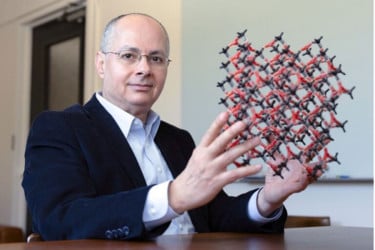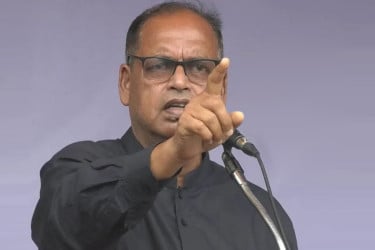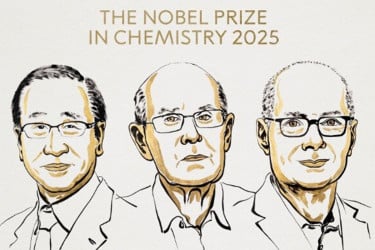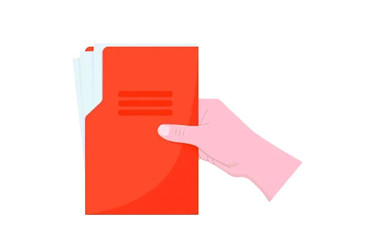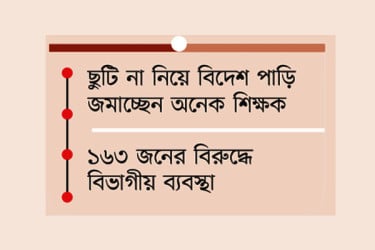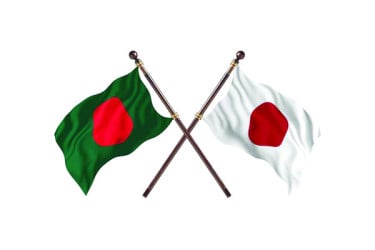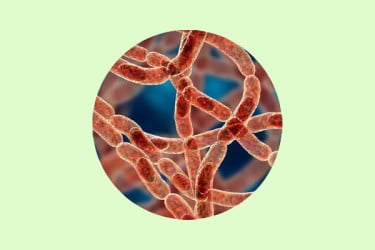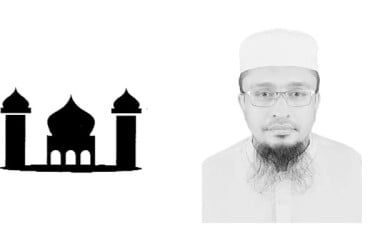স্বাস্থ্য খাতে পরনির্ভরশীলতা আমাদের একটি গুরুতর সমস্যা, যা দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা এবং জনগণের স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসায় পরনির্ভরতা প্রকট। এর মূল কারণ স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা, আর্থসামাজিক বৈষম্য, স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধার ঘাটতি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে অসন্তুষ্টিই বেশি। এই অসন্তুষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের না হলেও নেহাত কমও নয়। স্বাস্থ্য খাতে আস্থার সংকট প্রকট এবং তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সম্প্রতি স্বাস্থ্য খাতের ১০টি সংকটকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে সংবাদ সম্মেলন করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো মেধা, জ্ঞান ও যোগ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থা। যেখানে নিয়োগে মেধাশক্তির গুরুত্ব দেওয়া হয় না; দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া উপেক্ষিত এবং পেশাগত উদ্দেশ্য অর্জনের কোনো সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
যদিও স্বাধীনতা-উত্তরকালে চিকিৎসাসেবা যেখানে ছিল সেখান থেকে অনেক দূর এগিয়েছে। তারপরও স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ ১৮ কোটি লোকের চিকিৎসা প্রদানে এখনো সক্ষমতার ঘাটতি আছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বেসরকারি বিনিয়োগে দ্রুত পাল্টে যায় আমাদের স্বাস্থ্য খাত। বিশেষায়িত চিকিৎসায় দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন শাখা-উপশাখার বিকাশ হতে থাকে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাহিদা মেটাতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রচুর মেডিকেল কলেজ গড়ে ওঠে। বর্তমানে ভারতসহ পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ থেকে এসে বিপুল ছাত্রছাত্রী এ দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছেন। দুরারোগ্য ক্যানসার চিকিৎসা, কার্ডিয়াক সার্জারি, কিডনি প্রতিস্থাপনসহ নানা রকম জটিল চিকিৎসা এখন দেশেই সম্ভব হচ্ছে। এসব চিকিৎসা ২৫-৩০ বছর আগে বাংলাদেশে তেমন একটা হতো না। চিকিৎসা খাতে এগুলো আমাদের ঈর্ষণীয় অর্জন। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।
তারপরও রোগীরা বিদেশে চিকিৎসা নিতে যায় তার কারণ কেবল অপ্রতুল চিকিৎসা, তা নয়। দেশে চিকিৎসাব্যয়ও তুলনামূলক বেশি। বিশেষ করে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা এবং দক্ষ জনবল অপ্রতুল। চিকিৎসাব্যয় সাশ্রয়ী না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগ বা বাজেটস্বল্পতা। একই সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর অতি মুনাফালোভী দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকাংশে দায়ী। দেশে স্বাস্থ্য খাতে অসন্তুষ্টির কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞদের মতে, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মেডিকেল ট্যুরিজমের প্রভাবকেও কিছুটা দায়ী করা যায়।
অবকাঠামো বা প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকার পরও কেন মানুষ বিদেশমুখী হয়? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ নানা কারণে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইকোনমিক্সের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় জটিল রোগের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, ভুল রোগনির্ণয়, উচ্চ খরচ এবং চিকিৎসক ও রোগীর বোঝাপড়ার মতো বিষয়গুলো নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকার ও রাষ্ট্রের ‘অপরিহার্য’ ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই নিয়মিত চিকিৎসা নিতে বা শারীরিক পরীক্ষার জন্য বিদেশ যান। চিকিৎসার জন্য তাদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের মতো দেশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বিদেশে চিকিৎসা নিতে গেলে জনগণের মধ্যে তো অনাস্থা তৈরি হবেই। জনগণ ভাববে এখানে নিশ্চয় ভালো চিকিৎসা হয় না। এ সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। সেটাই মূল জায়গা। রাষ্ট্রের এই জায়গাটাতে দুর্বলতা আছে। মানসম্মত চিকিৎসাসেবা দেওয়া রাষ্ট্র বা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সিএমএইচে নিচ্ছে। খুব অল্প মানুষ সেখানে চিকিৎসার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রীয় খরচে বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার পরিবর্তে দেশেই কি আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়? উচ্চবিত্তরা কেন চিকিৎসার জন্য বিদেশ যান? দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা কতটা যুগোপযোগী? চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতার কারণ কী? সরকার বা অন্য কোনো বেসরকারি সংস্থা থেকে সাধারণ নাগরিকদের এই বিদেশমুখিতার কারণ নিয়ে কোনো জরিপ হয়েছে কি না, জানা নেই। তবে এ কথা সত্যি যে রোগী বা তার স্বজনদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আস্থাহীনতা বিদেশমুখিতায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে হলে, দেশীয়ভাবে চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধপত্র এবং কাঁচামাল উৎপাদন, সেই সঙ্গে জনবলব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশীয় উৎপাদন, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সরকারি-বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। পাশাপাশি জনসচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ওপর জোর দিয়ে স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থাকে আরও স্বনির্ভর করা যায়। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
লেখক : গবেষক