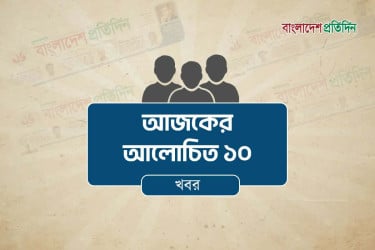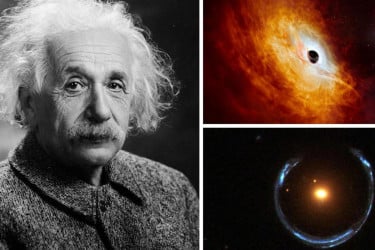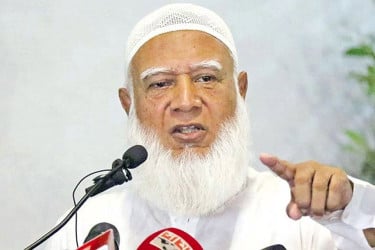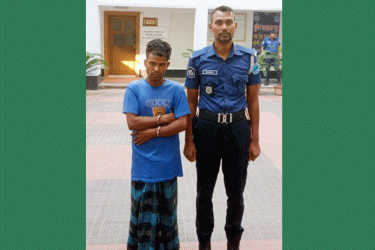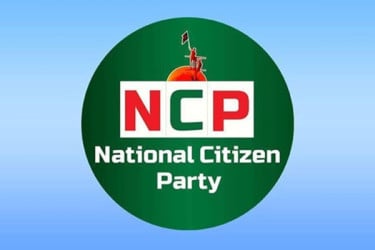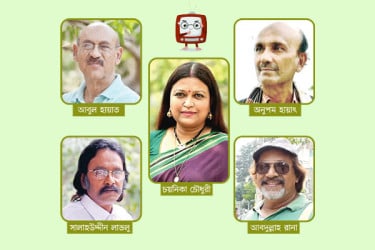সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন ডিপফেকের ছড়াছড়ি। ডিপফেক বলতে ভুয়া বা এআই-জেনারেটেড অডিও, ভিডিও এবং ছবি বোঝায়—যেগুলো বাস্তবের মতোই দেখতে বা শুনতে লাগে। অধিকাংশ সময় এসব ব্যবহার করা হয় মিথ্যা প্রচারণা, গুজব ছড়ানো বা জালিয়াতির উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে সাধারণ মানুষ—অনেকে ইতিমধ্যেই এই ডিপফেকের শিকার হয়েছেন।
ডিপফেক যাচাইয়ের কিছু কার্যকর পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো—
উৎস পরীক্ষা করা
সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ছবি বা ভিডিও ভাইরাল হলে প্রথমে এর উৎস যাচাই করুন। যে অ্যাকাউন্ট বা আইডি থেকে পোস্টটি এসেছে, সেটি সত্যি না ভুয়া তা দেখুন। অ্যাকাউন্টের পুরোনো পোস্ট, ফলোয়ার সংখ্যা, প্রোফাইল ছবি ইত্যাদি দেখে আসল বা নকল বোঝা যায়।
মুখের দিকে তাকানো
ছবি বা ভিডিওতে মুখ ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। ভিডিও থামিয়ে চোখ, ঠোঁট ও চুলের রেখা খেয়াল করুন। ডিপফেকে মুখের রেখা অস্বাভাবিক লাগে, চোখের পলক ফেলা বা দাঁত–কানের গঠন অদ্ভুত হয়। হাত, পা, আঙুল, চোখ বা চুলের প্রান্তেও অসামঞ্জস্য চোখে পড়তে পারে।
আলো ও ছায়া খেয়াল করা
ছবি বা ভিডিওতে আলো, ছায়া ও প্রতিফলন স্বাভাবিক কিনা দেখুন। এআই-তৈরি কনটেন্টে আলোর প্রতিফলন প্রায়ই অস্বাভাবিক হয়। পরিবেশের আলো ও বস্তু বা মানুষের ওপর আলোর প্রভাবের অসঙ্গতি ডিপফেকের বড় লক্ষণ।
কণ্ঠস্বর শোনা
ডিপফেক অডিও বা ভিডিওর কণ্ঠস্বর মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এআই-তৈরি কণ্ঠে প্রায়ই অস্বাভাবিক বিরতি, নিঃশ্বাসের ভাঙন বা সিনথেটিক টোন থাকে। কণ্ঠস্বর কিছুটা রোবটিক শোনায়। সন্দেহ হলে সেই ব্যক্তির অন্য আসল ভিডিওর কণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করুন।
ভিডিওর ফ্রেম যাচাই
ভিডিও থামিয়ে একাধিক ফ্রেম বিশ্লেষণ করুন। আগের ফ্রেম ও পরের ফ্রেমে মুখ বা বস্তুর আকৃতি হঠাৎ পরিবর্তন হচ্ছে কিনা দেখুন। মুখের চারপাশে ঝাপসা দাগ, খাঁজকাটা প্রান্ত বা নড়াচড়ায় অস্বাভাবিকতা থাকলে সেটি ডিপফেক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
মেটাডেটা মূল্যায়ন করা
মেটাডেটা হলো ছবি, ভিডিও বা ফাইলের ভেতরে থাকা লুকোনো তথ্য। এটি জানায় ফাইলটি কবে, কোথায়, কীভাবে তৈরি হয়েছে। ছবির মেটাডেটায় তারিখ, লোকেশন, ক্যামেরা মডেল, এমনকি সেটিং পর্যন্ত থাকে। ফাইল সেভ করে ইনফো অপশন থেকে এসব তথ্য দেখা যায়।
স্ক্যান ও অনুসন্ধান করা
সন্দেহজনক ছবি দেখলে স্ক্রিনশট নিয়ে গুগল ইমেজ সার্চে দিন। এতে আসল ছবিটি কোথায় এবং কখন প্রকাশিত হয়েছে, তা জানা যায়।
টুল ব্যবহার করা
ডিপফেক যাচাইয়ের জন্য এখন অনলাইনে অনেক টুল পাওয়া যায়। ফোটোফরেনসিক, ডিপওয়্যার এআই, মিডিয়াইনফো ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ছবি ও ভিডিওর ভুয়া উৎস চিহ্নিত করা সম্ভব।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
বিডি প্রতিদিন/আশিক