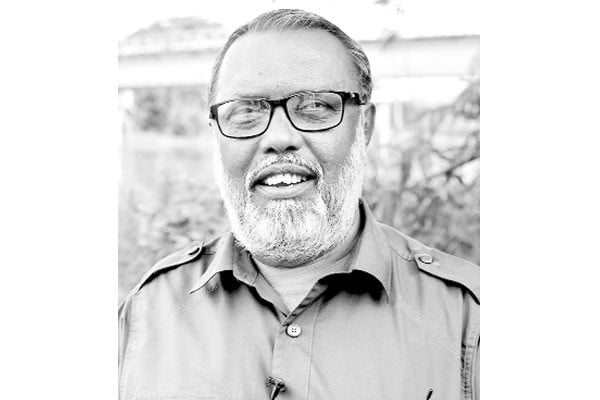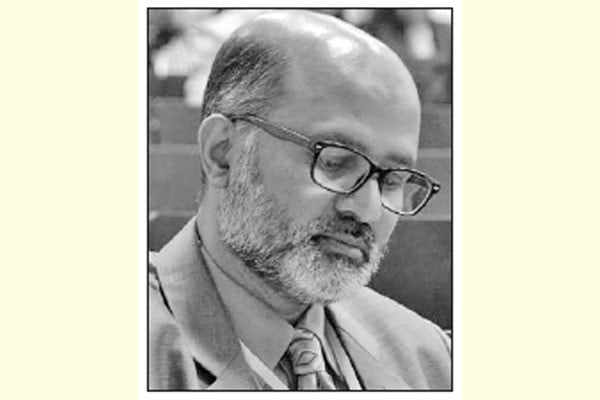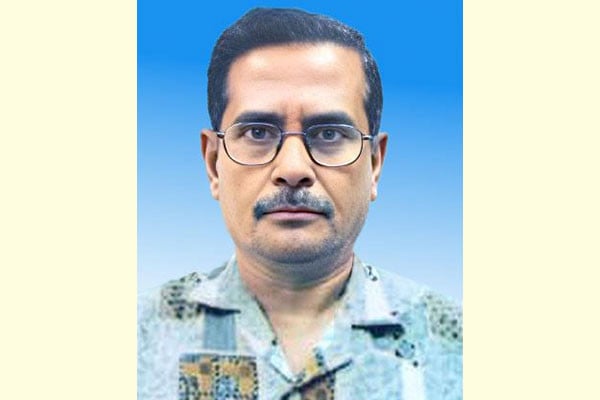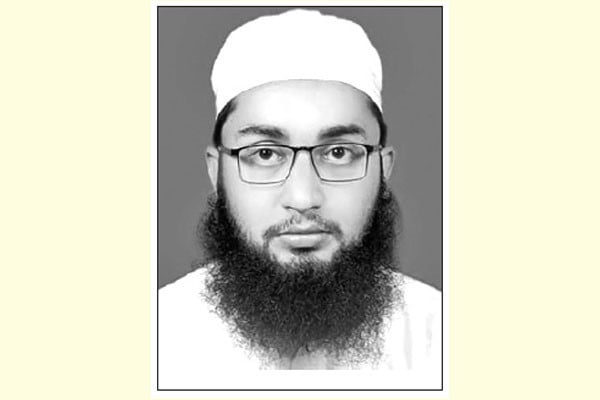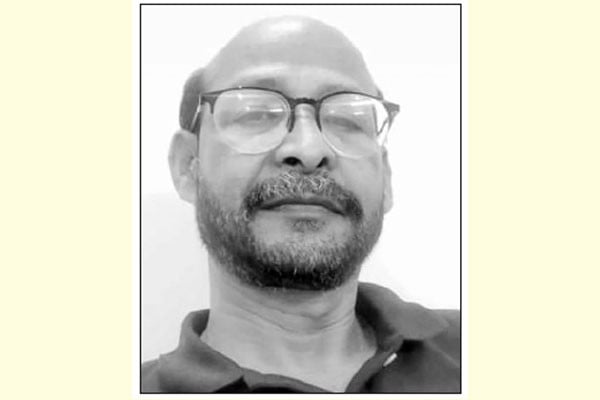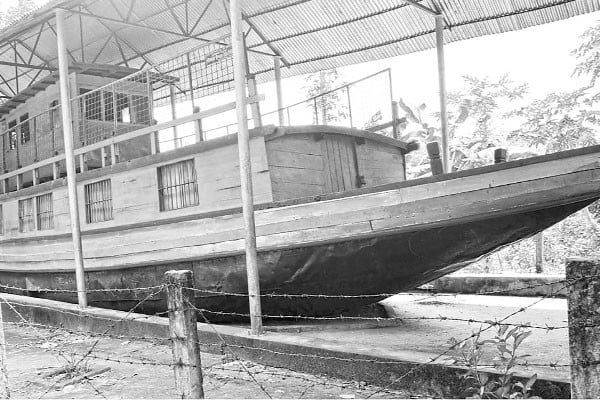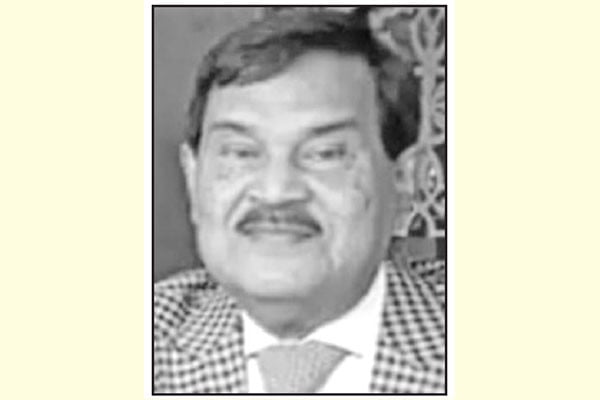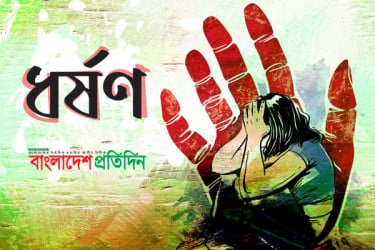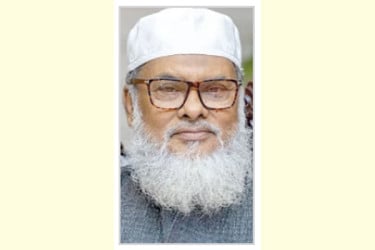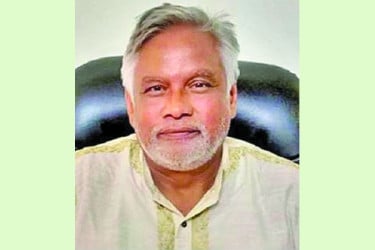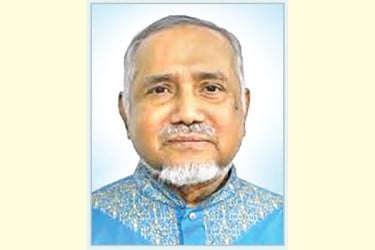অনেক প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকির মধ্যেও দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতি বেশ ভালো। শত সংকটের ভিতরও কৃষক একভাবে উতরে যাচ্ছেন, ফসল ভালো হচ্ছে। গত বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া দুই-তিন বছরে ধানের সব কটি মৌসুমেই ভালো ফলন পেয়েছেন কৃষক। অন্যান্য ফল-ফসলেরও ফলনের হার মন্দ না। এ কথাও সত্য, গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে শুধু কৃষি নয়, সব ক্ষেত্রেই জলবায়ু সম্পর্কে টনক নড়েছে। সারা বিশ্বেই জলবায়ু বিষয়টি এখন সবচেয়ে আলোচিত ও এক নম্বর ইস্যু হিসেবে গণ্য। আর এই ইস্যুতে আমরা আছি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়। বিপর্যয় সহনশীলতার প্রশ্নে আমাদের কৃতিত্ব দৃষ্টান্তমূলক। তবে দিনের পর দিন ঝুঁকি বাড়ছে। উদ্বেগও বাড়ছে। বন্যা, লবণাক্ততা, খরা, ভূমিকম্পের ঝুঁকি আমাদের সারাক্ষণই তাড়া করে ফিরছে। বেশি উদ্বেগের কারণ হলো, এসব বড় বড় বিপর্যয় মোকাবিলা করার মতো শক্তিসামর্থ্য বা প্রস্তুতি কোনো কিছুই আমাদের নেই। বড় চিন্তা দেশের জনসংখ্যা ও তাদের মুখের খাবার নিয়ে। এই ছোট্ট দেশের বিপুল জনগণ এখনো খাচ্ছে দাচ্ছে, ঠিকমতো টিকে আছে। দুশ্চিন্তা-হতাশা আছে, তারপরও একেবারে করুণ কোনো দশায় পড়তে হচ্ছে না। কিন্তু সারা পৃথিবীই যেখানে জলবায়ু ঝুঁকিতে সংকটাপন্ন, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান একটু বেশিই দুশ্চিন্তায় ফেলার মতো।
 আমরা ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং ওপরে দুদিকেই বিপদের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আন্তর্জাতিক সমীক্ষার তালিকায় দেশের অবস্থান বন্যার ঝুঁকিতে প্রথম, সুনামিতে তৃতীয় এবং ঘূর্ণিঝড়ে ষষ্ঠ। যা বাংলাদেশের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা আবাদি জমি নষ্ট করছে এবং বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে মৎস্য ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। তারা শহরে পাড়ি জমাচ্ছে এবং সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। যে আশঙ্কার কথা বারবার উচ্চারিত হয় তা হচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। দুই কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে এবং চার কোটিরও বেশি মানুষ জীবনযাত্রা হারিয়ে ফেলবে। বিজ্ঞানীদের মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। এসব চ্যালেঞ্জ এবং আশঙ্কার ভিতর আমরা আছি সবচেয়ে ভীতিকর একটি জায়গায়।
আমরা ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং ওপরে দুদিকেই বিপদের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আন্তর্জাতিক সমীক্ষার তালিকায় দেশের অবস্থান বন্যার ঝুঁকিতে প্রথম, সুনামিতে তৃতীয় এবং ঘূর্ণিঝড়ে ষষ্ঠ। যা বাংলাদেশের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা আবাদি জমি নষ্ট করছে এবং বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে মৎস্য ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। তারা শহরে পাড়ি জমাচ্ছে এবং সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। যে আশঙ্কার কথা বারবার উচ্চারিত হয় তা হচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। দুই কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে এবং চার কোটিরও বেশি মানুষ জীবনযাত্রা হারিয়ে ফেলবে। বিজ্ঞানীদের মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। এসব চ্যালেঞ্জ এবং আশঙ্কার ভিতর আমরা আছি সবচেয়ে ভীতিকর একটি জায়গায়।
দেশের নদ-নদীগুলো নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। কৃষিকাজে অনুকূল সেচসুবিধা নেই। একসময় শুধু বোরো মৌসুম সেচনির্ভর হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এখন আমনসহ সব ফসল মৌসুমেই কৃত্রিম সেচ দিয়ে মেটাতে হচ্ছে ফসলের পানি চাহিদা। নদীর নাব্যতা না থাকার কারণে, নদ-নদীবেষ্টিত এলাকাগুলোতেও কৃষি আবাদ এখন আর অনুকূল নেই। ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে নদী ও খাল খনন করে সেচব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেচের প্রশ্নে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। সেচ নিয়ে প্রতি বছরই শুষ্ক মৌসুমে এসে দেশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের হাহাকার চোখে পড়ে। দিনদিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও পানির স্তর এত বেশি নিচে নেমে গেছে, এখন আর সেচপাম্প মাটির ওপরে স্থাপন করে পানি ওঠে না। কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ ফুট গর্ত করে গভীরে স্থাপন করতে হচ্ছে পাম্প। আগামীর দিনগুলোতে পরিস্থিতি কোথায় যাবে এমন প্রশ্ন আর উদ্বেগ এখন সবখানে।
ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ গবেষণা সাফল্যেরও একটি শেষ আছে। অর্থাৎ বলতে চাইছি, প্রধান খাদ্যশস্যগুলোর ফলন বা উৎপাদন হার উন্নত গবেষণার আলোকে আর কত দিন বাড়ানো সম্ভব হবে? স্থানীয় জাত থেকে উচ্চ ফলনশীল, উচ্চ ফলনশীল থেকে হাইব্রিড, হাইব্রিড থেকে সুপার হাইব্রিড। তারপরে কী? মনে রাখা প্রয়োজন, ফলন বৃদ্ধির প্রয়াসের চূড়ান্ত সীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বিশ্ব। যদিও আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি। মাটির জৈবশক্তিরও সাধ্যসীমা আছে। একইভাবে আছে ফসলের ফলনেরও চূড়ান্ত সীমা। প্রযুক্তি ও জ্ঞানের উৎকর্ষে বিজ্ঞানীরা যেখানে পৌঁছেছেন, তাতে বড় জোর আগামী ১০-২০ বছর ফসলের বেশি ফলনের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। তারপর ফসলের ফলনের হার একটি নির্দিষ্ট হারে এসে পৌঁছবে। সেখান থেকে ফলন শুধু কমবেই, বাড়বে না। কিন্তু জনসংখ্যা তো বাড়তে থাকবে, কমতে থাকবে আবাদি জমি। মোটা দাগে যে কথা বলা হয়, বছরে ১ শতাংশ হারে জমি কমছে। ১০০ বছরের মাথায় এসে আবাদি জমি শূন্যে পৌঁছাবে। আর ধানের উৎপাদন আমরা হেক্টরপ্রতি তিন-চার টন থেকে বাড়িয়ে হাইব্রিডে গিয়ে হয়তো চূড়ান্তভাবে সাত-আট মেট্রিক টনে পৌঁছতে পারব। তাতেও সন্দেহ রয়েছে কারণ, আমাদের মাটির জৈব উপাদান কমতে কমতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে মাটির জৈব উপাদান চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে। এতে ওই সব অঞ্চলে ফসল উৎপাদনই অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর ওপরে রয়েছে বিভিন্নমুখী দূষণের কারণে মাটি ও পানিতে ‘হেভি মেটাল’ ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের পরিমাণ বৃদ্ধি। যা শুধু ফসল উৎপাদনকেই বন্ধ্যাত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না, ফসলের সঙ্গে মিশে মানবদেহের জন্যও মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনছে। সব মিলিয়ে আগামী দিনে ফসলের উৎপাদনই যে যে প্রক্রিয়ায় ব্যাহত হবে, সেই একই প্রক্রিয়াগুলো মানুষের স্বাভাবিক জীবনচক্রে ফেলবে কঠিন ও নেতিবাচক প্রভাব।
বস্তুত এগুলোই কৃষির চ্যালেঞ্জ, খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ। যে কারণে শুরুতে যে কথা বলেছি কয়েক বছর আমাদের ফসল উৎপাদনের হার আশাব্যঞ্জক হলেও এই সাফল্য বর্তমানের, একে আগামীর নিরিখে বিবেচনা করা যাবে না। আর আগামীর খাদ্য উৎপাদনের প্রস্তুতি যদি এখনই না নেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এক কঠিন অবস্থায় পড়তে হবে আমাদের। বলা বাহুল্য, আয়তনে ছোট, সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ কৃষিপ্রধান এই দেশটির জন্য ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই উদ্বিগ্ন সারা বিশ্বের পরিবেশবিজ্ঞানী ও খাদ্যনিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। তারা বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের টিকে থাকার যোগ্যতা ও পারদর্শিতায় প্রশংসা করলেও আগামীর প্রস্তুতির প্রশ্নে আমরা যে খুব ভালো জায়গায় নেই, তা এখনই স্পষ্ট।
দুর্যোগে সহনশীলতা অর্জনের জন্য দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো নানামুখী কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত কৃষক পর্যায়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেগুলো কৃষককে খুব বেশি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের আইলাকবলিত এলাকায় যেখানে লবণাক্ততার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত লবণসহিষ্ণু জাতগুলো আবাদ করতে পারছেন না কৃষক। তার বদলে তারা নিজেদের সংগৃহীত বহু পুরোনো স্থানীয় জাত আবাদ করে তুলনামূলক ভালো ফলন পাচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলো সম্পর্কে ল্যাবরেটরি ও গবেষণা মাঠের তথ্যের আলোকে ফলনের যে হিসাব দেন, কৃষকের মাঠে গিয়ে তার ব্যাপক হেরফের লক্ষ করেন।
বিভিন্ন ফসলের জলবায়ু সহনশীল জাত থেকে শুরু করে কৃষির বিভিন্নমুখী গবেষণা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। দুর্যোগ যে কোনো সময়ই গ্রাস করতে পারে, তার জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন খাদ্যের মজুত রাখা, অন্যদিকে নতুনভাবে উঠে দাঁড়ানোর কৌশল নির্ধারণ। খাদ্য মজুত রাখার প্রশ্নেও আমাদের সীমাবদ্ধতা দূর করা দরকার। বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৫ লাখ টনের ঊর্ধ্বে মজুত বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না, এই মজুতে আমরা অনেক সময় সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও এটি সন্তুষ্টির কোনো কারণ হতে পারে না। খাদ্যশস্যের মজুত আরও বাড়ানো প্রয়োজন।
কৃষক ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে উপকরণের উচ্চমূল্য, আর উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমূল্যে। মনে রাখা দরকার, আজকের দিনে জীবনযাপন যেখানে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং, সেখানে কৃষক যদি বাণিজ্যিক কৃষিতে গিয়ে কোনোভাবে লাভবান না হতে পারে। তাহলে সে কৃষি ছেড়ে অন্য পেশার দিকে ধাবিত হবে। বিষয়টি বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা প্রয়োজন। যে কোনো ফল ফসলের মৌসুমের শুরুতেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা লোকসানের শিকার হচ্ছেন। এটি গোটা কৃষির জন্য নেতিবাচক চিত্র। আগামীর সব ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচানোর জন্য যে কৃষকের সম্মিলিত শক্তি সবচেয়ে আগে প্রয়োজন, তাদের বারংবার হতাশ করে কোনো লক্ষ্যেই পৌঁছানো সম্ভব নয়। এজন্য আগামীর খাদ্যনিরাপত্তার সব পরিকল্পনা নিতে হবে কৃষককে সঙ্গে নিয়ে, কৃষি উপকরণ আনতে হবে কৃষকের ক্রয়সীমার মধ্যে, আর নিশ্চিত করতে হবে পণ্যের মূল্য। তাহলেই যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সার্বিক শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হতে পারবে কৃষক।
♦ লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব