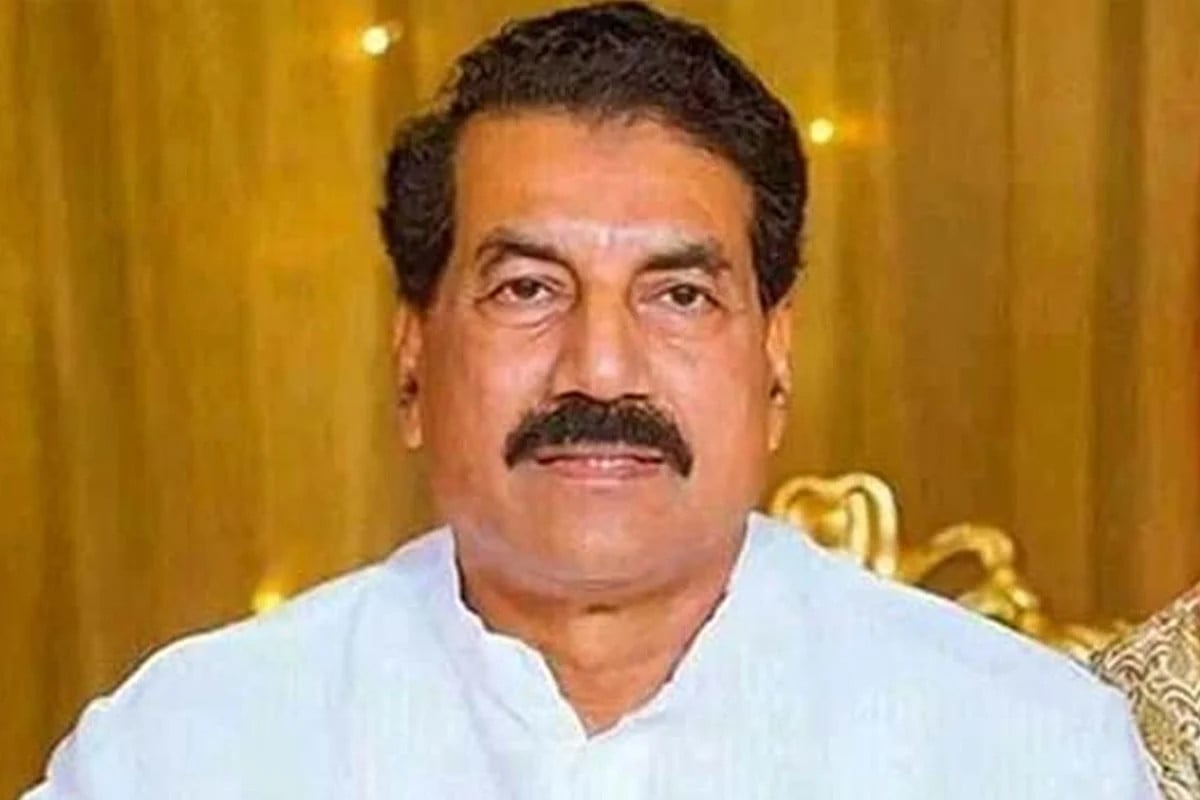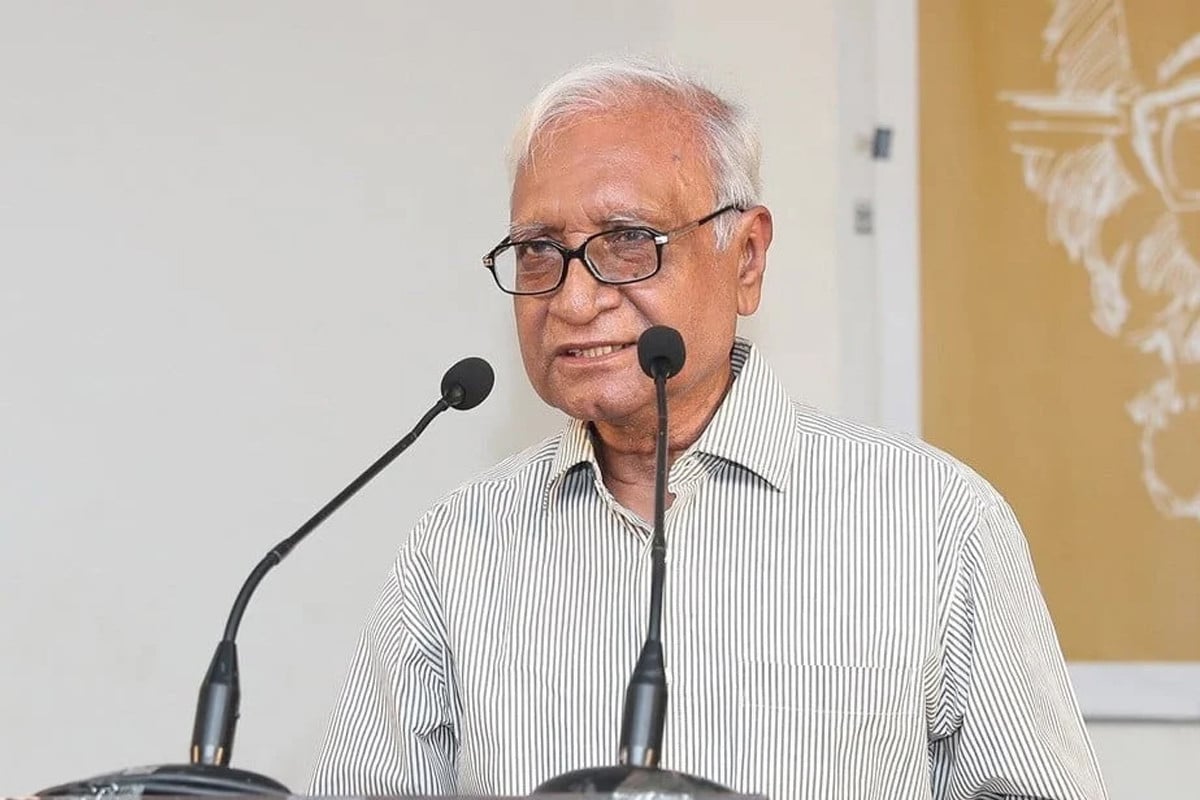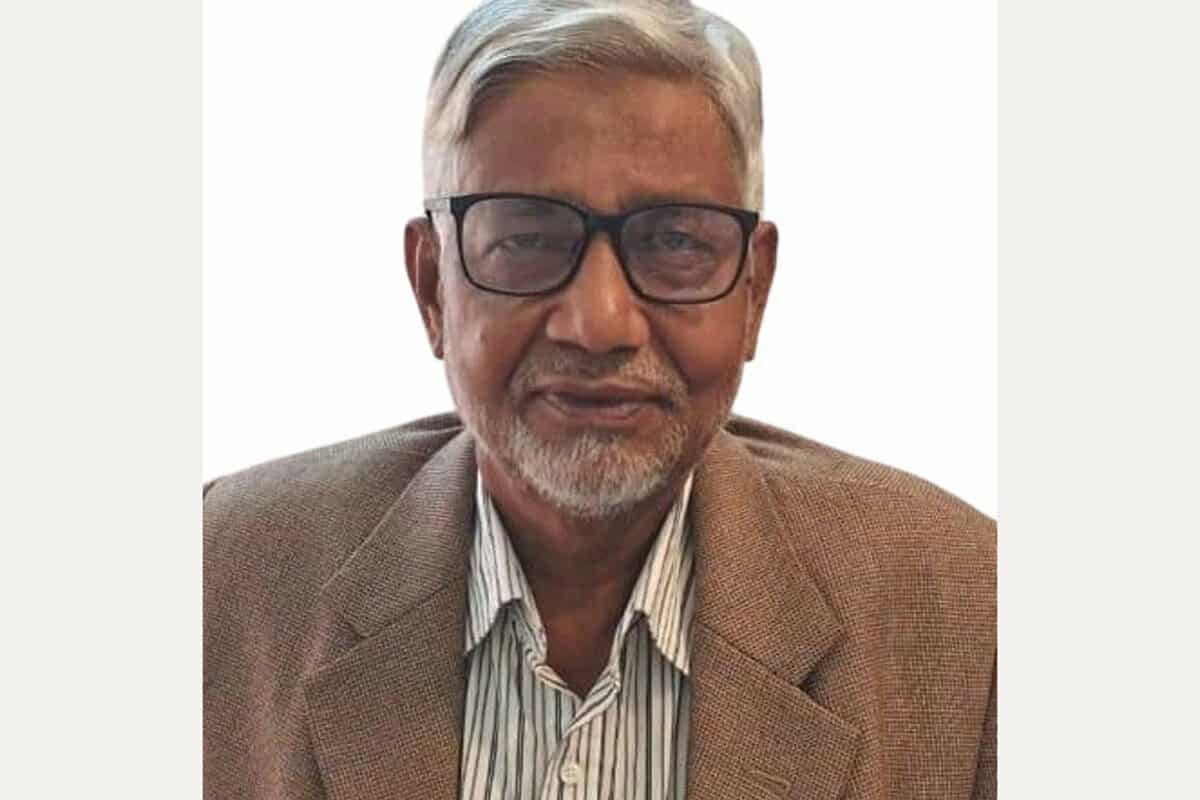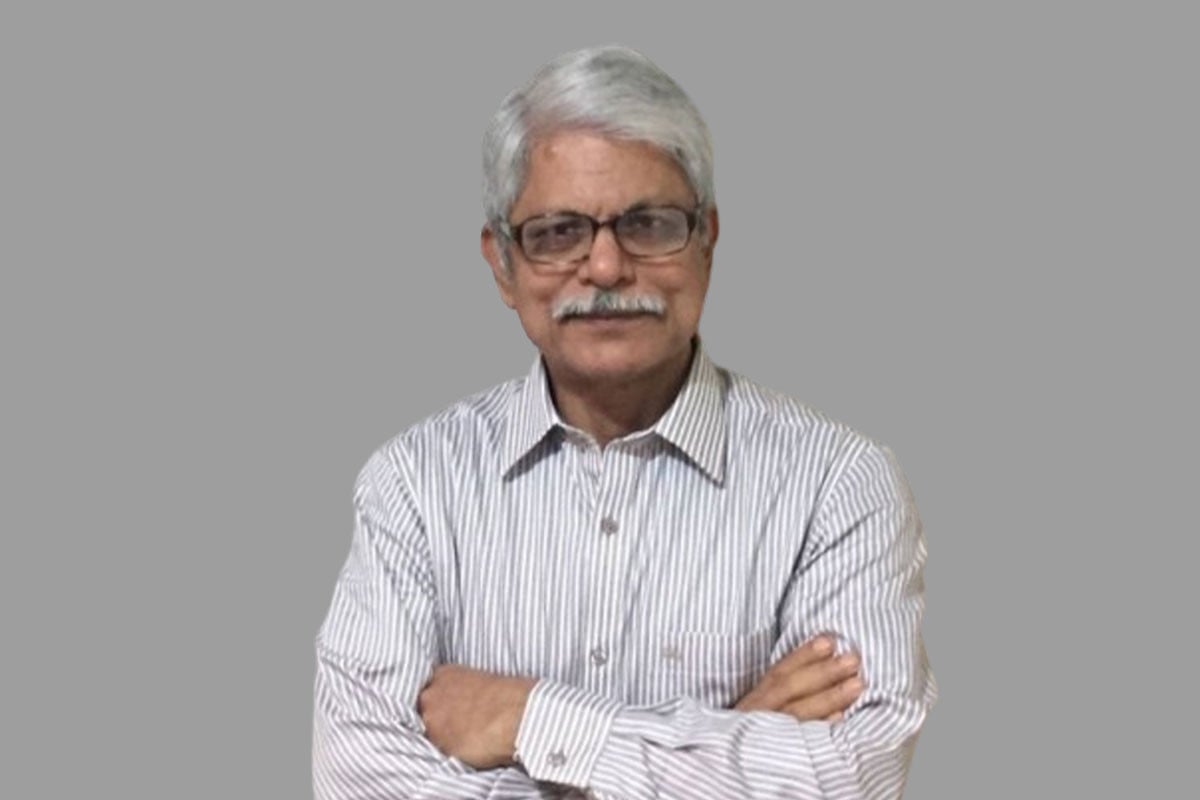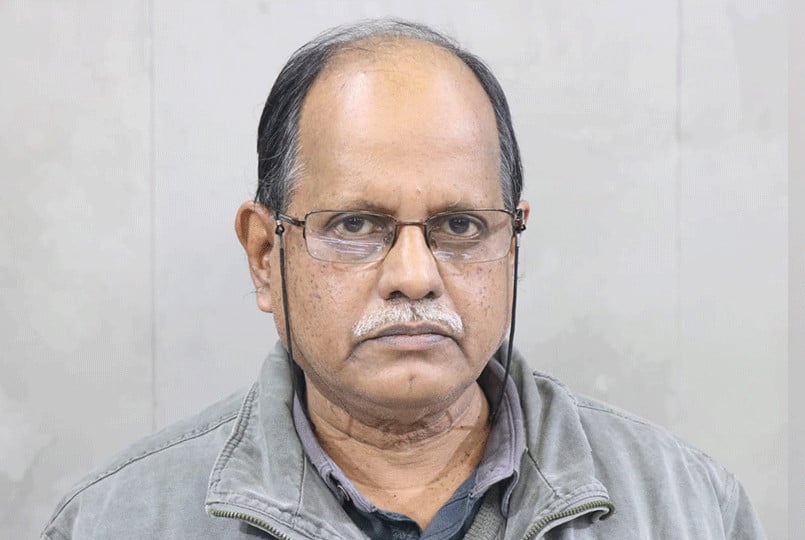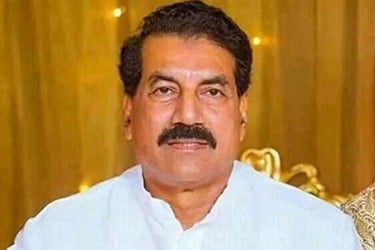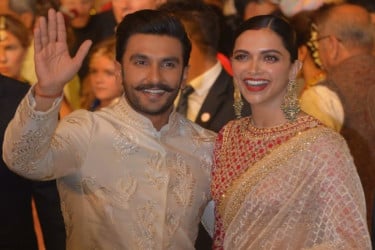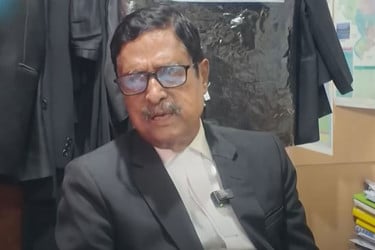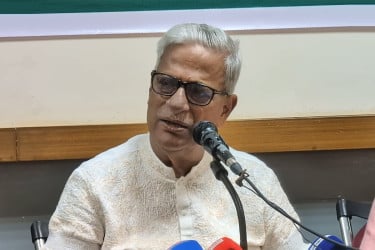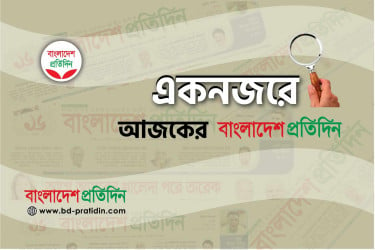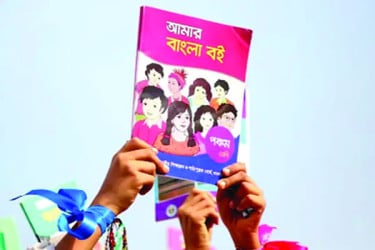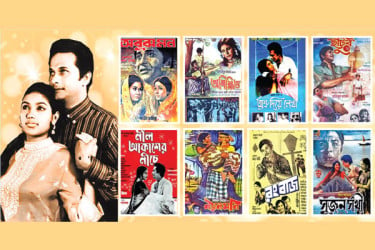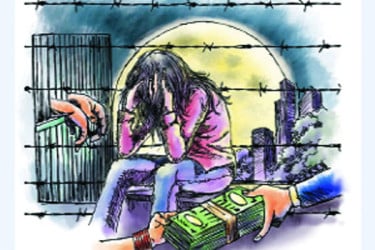সর্বোচ্চ ও চরম শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। আদিকাল থেকে এ মৃত্যুদণ্ডাদেশের প্রচলন। কার্যকারিতা এখন সোজা হলেও প্রাচীনকালে ছিল নিষ্ঠুর এবং নির্মম।
উল্লেখ্য, গত ১৩ মে বাংলাদেশের হাইকোর্ট “মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে আসামিকে কনডেম সেলে রাখা যাবে না” মর্মে রায় প্রদান করেন। কিন্তু রাষ্ট্র পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ওই রায় স্থগিত করে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। এ বিষয়ে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ২৫ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে। ফলে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আপিল বিভাগের রায়ের ওপর।
প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীজুড়েই মৃত্যুদণ্ড কার্যকারিতার ধরন বদলেছে যুগে যুগে। সেসবের কিছু চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে।
যেমন একটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কিভাবে করা হয়েছিল, সেটা বলছি। মাননীয় বিচারক একটি হত্যাজনিত অপরাধ কর্মের জন্য এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন। তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতিও বাতলে দিলেন। ঐতিহাসিক রায়ে বিচারক আদেশ করলেন যে, ‘অপরাধীর ডান হাত তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা এমনভাবে পোড়াতে হবে, যাতে তার হাড় হতে মাংসপেশি চিমটি দিয়ে টেনে তুলা যায়। অপরাধীর প্রতিটি অঙ্গ হতে মাংসপেশি এমনভাবে তুলতে হবে যাতে অপরাধী প্রচণ্ড কষ্ট পায় কিন্তু জীবিত থাকে। অধিকন্তু অপরাধীর শরীরকে এমনভাবে ঝলসাতে হবে, যাতে তার শরীর হতে মাংসপেশি মোমের মতো ঝড়ে পড়ে। অবশেষে তার হ্রদপিণ্ডে যখন আগুনের আঁচড় লাগবে এবং পুরো শরীর অবশ হয়ে যাবে তখন তার মুণ্ডু কর্তন করতে হবে। বিচারকের সেই আদেশ অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তির ওভাবেই দিনের পর দিন চরম নির্যাতনের মুখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুদণ্ড ব্যক্তি হচ্ছে ফ্রান্সের অভিজাত গিরার্ড। আর যে ব্যক্তিটিকে হত্যা করেছিলেন, সেই ব্যক্তি হলেন উইলিয়াম দ্য অরেঞ্জ। যাঁকে নেদারল্যান্ডের Father of the Motherland (মাতৃভূমির জনক) বলা হয়, যাঁর নামে জাতীয় সঙ্গীত ‘Het William.. ১৫৩৩ সালের ২৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণকারী উইলিয়ামকে ১৫৮৪ সালের ১০ জুলাই ডেলফটের বাসভবনে (প্রিন্সেনহপ) ঘাতক গিরার্ড ফ্রান্সের অভিজাত পরিচয়ে সাক্ষাৎ করতে এসে গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে। এটিই বিশ্বের কোন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম হত্যা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে উইলিয়ামের মুখে শেষ শব্দটি ছিল, ‘হে ঈশ্বর এ অভাগা লোকটির প্রতি আপনি সহানুভূতি দেখান, আর আমার আত্মাকে শান্তি দিন’।
মাননীয় বিচারক উইলিয়ামের হত্যাকারীর প্রতি উপরোক্ত অনুকম্পার বিষয়টি আমলে নেননি, বরং নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদান করে ইতিহাস রচনা করেছেন। রাশিয়ান জাতির জনক পিটার ১৬৯৮ সালে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা ১২’শ বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরও ছিল চরম নির্যাতনমূলক। শুধু তাই নয়, সতর্ক বার্তাস্বরূপ বিশ্বাসঘাতকদের লাশ প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল।
স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরও ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে উচ্চ আদালতের রায়ে প্রচলিত পদ্ধতিতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এমনকি জনগণের চরম ঘৃণা ক্রোধ থাকা সত্ত্বেও স্বজনদের হত্যাকারীদের কবরস্থ করার সুযোগ দেয়া হয়। যাহোক, মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজের অপরাধীকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি যতটা নিবারণমূলক অন্যকোন শাস্তি ততটা নয়।
বিশ্ববরেণ্য অপরাধ বিজ্ঞানী Garofalo এর মতে, মৃত্যুদণ্ড অবলোকনে অন্যান্য ব্যক্তিরা আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়। কারণ মৃত্যুদণ্ড তাদের কাছে যেন একসমূহ বিপদ সঙ্কেত। যে সঙ্কেত সহজে উপেক্ষীয় নয়।
বস্তুত, নির্মম হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ড ভোগ করলে বিচার প্রত্যাশী জনগণ খুশী হয়। তাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে।
মৃত্যুদণ্ডও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার অন্যতম দৃষ্টান্ত। যদিও প্রতিশোধমূলক নীতি শাস্তির ক্ষেত্রে ক্রমে পরিত্যক্ত হয়ে আসছে, তারপরও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কেননা, কোন ব্যক্তি হত্যা করে যদি কারাগারে কিছুকাল থাকার পর মুক্তি পেয়ে যায় তাহলেই ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তৃপ্ত হয় না, বরং তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। তাই মৃত্যুদণ্ড প্রতিশোধমূলক হলেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
তাছাড়া মৃত্যুদণ্ড সামাজিক সংহতিকে দৃঢ়তর করে। প্রকৃত অপরাধী মৃত্যুদণ্ড ভোগ করলে সমাজে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ মৃত্যুদণ্ডই কেবল সুগম করতে পারে। মৃত্যুদণ্ড মারাত্মক অপরাধীদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করে। মৃত্যুদণ্ড অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করার সুযোগ দেয় না। সেহেতু সমাজ অপরাধীর কার্যকলাপ থেকে রেহাই পায়।
যদিও ইউরোপের ৩৪টির মতো দেশ মৃত্যুদণ্ডের প্রচলন বাতিল করেছে। তারা বলছে, মৃত্যুদণ্ড সুস্থ মস্তিষ্কে স্বত্বঃস্ফূর্তভাবে আরেকটি হত্যাকাণ্ডের নামান্তর। এটা মানবিক মূল্যবোধ ও অনুভূতিকে আঘাত করে। মৃত্যুদণ্ডের নির্মম সাজা মানবীয় মূল্যবোধকে ঘায়েল করে। কিন্তু ইউরোপের বাস্তবতা আর আমাদের সমাজচিত্র এক নয়। এই দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আজ বাতিল হলে কাল হত্যার মিছিল বেরুবে।
শাস্তির ধরন ও প্রকৃতিও অনেকটা পাল্টে গেছে। যেমন আদিম সমাজে ভয়ঙ্কর শাস্তির মধ্যে ছিল অঙ্গচ্ছেদ। প্রাচীন ভারতেও কেউ চুরি করে ধরা পড়লে তার হাত কেটে দেয়া হতো। মধ্যপ্রাচ্যে আজও এ আইনের প্রচলন থাকলেও পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ইটালিসহ অনেক দেশে লৌহ পুড়িয়ে অপরাধীর গায়ে ছাপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ১৮২৯ সালে নির্মম এ শাস্তি বিলোপ করা হয়। পিলোরী অর্থ কাঠ নির্মিত শাস্তিস্তম্ভ। এর মধ্যে অপরাধী ব্যক্তির মাথা ও হাত ঢুকিয়ে আটকে রাখা হতো। ১৮৩৭ সালে এ প্রচলনও বিলুপ্ত করা হয়। নিঃসঙ্গ কারাবাসঃ কারাবাসের চেয়ে অধিকতর কষ্টদায়ক শাস্তি হল নিঃসঙ্গ কারাবাস। এ ধরনের শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধীর সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে অবদমিত করা হয়। এ প্রথা নিষ্ঠুর হলেও এর প্রচলন রয়েছে। কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার রীতি সর্বজনীন। শাস্তি অন্য আর সবার জন্য এমন একটি দৃষ্টান্ত যাতে আর কেউ অপরাধ কর্মে লিপ্ত হতে সাহস না পায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এমন শিক্ষা দেয়া যাতে সে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হতে না পারে।
বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অপর সদস্যদের ক্ষতিসাধন করলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো না। অর্থাৎ শাস্তি দেওয়া হতো না। পুত্র তার পিতাকে হত্যা করলেও পরিবারের সদস্যরা এটাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করে শাস্তি দিতো না। পরিবার মনে করতো যেহেতু পরিবারের একজন সদস্য হত্যার শিকার হওয়ায় পরিবার নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হত্যাকারীকে শাস্তি দিয়ে পরিবারের আরও ক্ষতি করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আদিম সমাজে অপরাধীদের যেসমস্ত ব্যবস্থা শাস্তি হিসেবে গ্রহণ করা হতো সেগুলোকে কোনপ্রকার শাস্তি বলা যায় না। রাজতন্ত্রের উৎপত্তিতে অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান প্রজাদের বিষয় হিসেবে গণ্য হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে অপরাধীকে শারীরিক শাস্তি দেয়া চালু হয়। আধুনিক যুগ শুরু হবার পর আইন ভঙ্গের প্রতি শাস্তিমূলক প্রতিক্রিয়া গৃহীত হতে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের সময় নব্য সনাতন মতবাদ প্রসার লাভ করে। যেহেতু শিশু বা পাগলরা শাস্তি ও আনন্দের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে অক্ষম, সুতরাং তাদের অপরাধী বলা চলে না। দৃষ্টি বাদী মতবাদে অপরাধীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব অস্বীকার করা হতো। প্রতিক্রিয়া মূলক শাস্তি ছিলো না। অপরাধকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো স্বাভাবিক ঘটনা মনে করা হতো। তাদের মতে যে সব অপরাধী সংস্কারের উপযুক্ত তাদের সংস্কার করা এবং যারা অনুপযোগী তাদের সমষ্টি থেকে আলাদা করে মেরে ফেলা উচিত।
আধুনিক যুগের প্রথমদিকে অপরাধীকে জনসমক্ষে অপমান করে সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই ধরনের শাস্তি ছিল। আধুনিক যুগেও কোন কোন অধিকার থেকে অপরাধীকে বঞ্চিত করা হয়। ভোট দেয়ার অধিকার, ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার, বিদেশ পাড়ি দেয়ার অধিকার, চাকুরী করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। দ্বীপান্তর ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন রোমেও। নির্বাসন দেওয়া হতো। ইংল্যান্ডে ১৫৯৭ সালে দ্বীপান্তর ব্যবস্থা গৃহীত হলেও তা রহিত করে। তবে অনেক দেশে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। মধ্যযুগে দগ্ধ করে, চাকায় পিষ্ট করে, ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। শারীরিক নির্যাতন দেওয়া হতো অঙ্গচ্ছেদ করা, কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ছেঁকা, খাঁচায় আবদ্ধ রাখা, বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি। আদিম সমাজে এবং মধ্য যুগে কারা শাস্তি ছিল না। প্রাচীন গ্রীসেও না। ইংল্যান্ডে এ্যাংলোর আমলে কারা ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে চার্চ কারাদণ্ড দিতেন, ছিপ নৌকায় এই শাস্তি কার্যকর করা হতো।
লেখক: সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন।
বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন