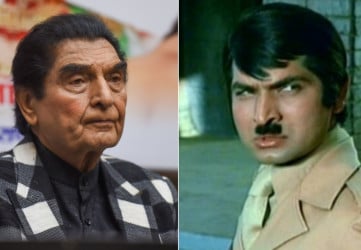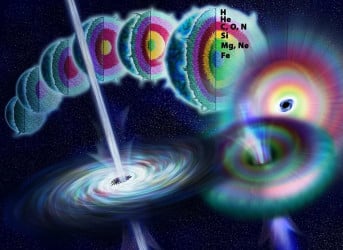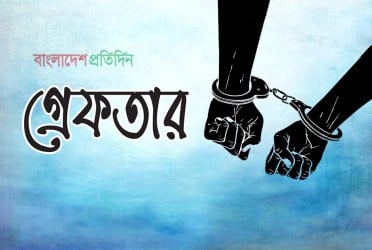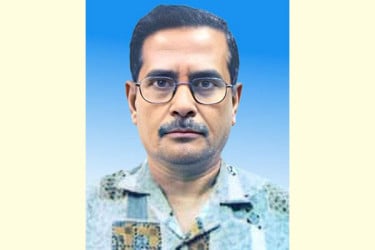লেখক হয়েছি কিনা জানি না। তবে লেখকই হতে চেয়েছি চিরকাল; লেখা ভালোবেসেছি; লেখাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কারণ এটি কোনো শখের বিষয় নয়। কিংবা নয় এমন কিছু যা খণ্ডকালীন মনোযোগের। ধরুন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলাম, স্টার্ট নিলাম, তারপর সাবধানে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে; কাজ সেরে আবার একইভাবে গাড়ি চালিয়ে এসে গ্যারেজে ঢুকিয়ে তৃপ্ত মনে হাতে চাবি নিয়ে লিভিংরুমে ফিরলাম। লেখা এমন নয়। লেখা হচ্ছে চিরজীবনের যাত্রা, তাতে সুনির্দিষ্ট গন্তব্য থাকে না। নেই গন্তব্যের সীমারেখা। নেই পরম স্বস্তিভরে ফিরে আসা। প্রতিটি লেখাই একেকটি যাত্রা ও সংগ্রাম, তাতে থাকে কিছুটা দ্বিধা ও মিশ্রছন্দ। থাকে লেখার মান নিয়ে সংশয়, প্রকাশসফলতা নিয়ে দোদুল্যমানতা। লেখা নিয়ে লেখক চূড়ান্ত তৃপ্ত ও সুখী হলে বুঝতে হবে তার লেখক হওয়ার ঢের বাকি। যা হোক, আমার শৈশবই কি নির্ধারণ করেছিল আমি লেখক-জীবন বেছে নেব? লেখার ভুবন আমাকে কীভাবে টেনেছিল? প্রথমেই মনে পড়ে বইয়ের কথা। বাসায় নিবিষ্ট মনে বই পড়তে দেখেছি আম্মাকে। বলা যায় কিশোরী বয়সই তো ছিল তাঁর, খুলনার এক গহিন পল্লী থেকে আব্বার চাকরিসূত্রে তার বড় শহর করাচিতে আসা। জানি না কী করে তিনি বইকেই আত্মীয় করে নিয়েছিলেন। বইয়ের জন্ম দেয় কারা— এমনটা ভাবতাম ছেলেবেলায়। তারাও কি একেকজন ঈশ্বর, মানে স্রষ্টা! এভাবে ছেলেবেলাতে লেখকই আমার কাছে নায়ক। কিন্তু আমার লেখার শুরু কবে, কীভাবে? এক জায়গায় লিখেছি: ‘সম্ভবত সহপাঠিনীর প্রেমে পড়ার পর নিজের ভিতর কবিতার কলকল টের পাই, কবিকে নয়। সদ্য কলেজপড়ুয়া তখন আমি। একতরফা ছিল সে প্রেম। প্রেমনিবেদনের মাধ্যম হিসেবে কবিতা বেছে নেওয়া। পরে অবশ্য প্রেমিকার বদল হয়। মানবী থেকে কবিতা। সেই প্রেম টুটেনি, যদিও সেটাও একতরফা।’
ওই বক্তব্যে আংশিক সত্যতা রয়েছে। আমার তারুণ্যের শহর যশোরে শিল্পী এস এম সুলতানের কাছে ছবি আঁকা শিখতে যেতাম। আঠারোয় যখন ঢাকা চলে এলাম, অল্প ক’বছরের মধ্যে অভিনয় এবং সংগীতশিক্ষা— দুটোই হয়ে উঠেছিল ধ্যানজ্ঞান। অথচ শিল্পের ওই তিন শাখার কোনোটিতেই আমি সক্রিয় থাকিনি। চিনে নিয়েছি নিজের প্রকৃত প্রেমকে, ফিরে এসেছি শব্দের গ্রহে। সতেরোর তোরণে দাঁড়িয়ে যে-কিশোর লিখতে শুরু করেছে তার কিনা প্রথম গ্রন্থটি বেরুলো বহু বিলম্বে, ত্রিশ বছর বয়সে! নিজের লেখা মলাটবন্দী করায় কি ছিল উদাসীনতা? নাকি সংশয় সংকোচ!
আমার তখন মোটে উনিশ। আমাদের নাটকের দল আরণ্যক মে দিবস উপলক্ষে কবিতা-গান ও পথনাটক প্রদর্শনীর সূচনা করল। সেখানে কবিতা পড়লাম। মোহাম্মদ রফিক পিঠ চাপড়ে দিলেন। বেতার মুক্তিযোদ্ধা মুস্তাফা আনোয়ার তত্ক্ষণাৎ আমন্ত্রণ জানালেন পরদিন কবিতাটি রেডিও সেন্টারে গিয়ে রেকর্ড করার। দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানও পছন্দ করতেন সেই তরুণের কবিতা; একের পর এক প্রকাশ করেছেন তার সম্পাদিত সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা বাংলা একাডেমির ‘উত্তরাধিকার’ সম্পাদনা করতেন আবু হেনা মোস্তাফা কামাল। অখ্যাত অপরিচিত এক তরুণকে তিনিও দারুণ অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার কবিতা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন হুমায়ুন আজাদ। তুখোড় সমালোচক হিসেবে তখনই বিখ্যাত তিনি। আশ্চর্য এক কথা বললেন দেশের কবিদের সম্পর্কে। জানতাম জীবনানন্দ বলেছেন— সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। তিনি বললেন শত শত ব্যক্তির কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে প্রকৃত কবি হলেন মাত্র পনেরজন। উপস্থিত কবিরা তাকে অনুরোধ করলেন এই পনেরজনের নাম প্রকাশ করতে। আর কী অবাক কাণ্ড, তিনি একে একে নামও বলতে শুরু করে দিলেন। গ্রন্থহীন এই আনাড়ি নবীনের কয়টা কবিতাই বা বেরিয়েছে সে সময়। হুমায়ুন আজাদ তার অতিসংক্ষিপ্ত কবিতালিকায় নামটিকে স্থান দিলেন। অথচ আমার ব্যক্তিজীবন তখন টালমাটাল, নিজেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারব কিনা নিজেই জানি না। ‘আত্মহনন’ নামের শয়তান আমার ছায়ার সঙ্গে হাঁটে নিত্যদিন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস হয়তো বুঝেছিলেন। তিনিই জোরাজুরি করলেন কবিতার বই বের করার জন্য। দূরদৃষ্টি ছিল তার। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন বই বেরুনোর পর তাতে বাঁধা পড়ে যান লেখক, তাকে নতুন নতুন সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তার আর অন্য কোথাও যাওয়া হয় না। জনপ্রিয় লেখক ইমদাদুল হক মিলন প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখলেন আমার প্রথম বই প্রকাশে। তিনিই তখন বইয়ের বাজার বাংলাবাজারের রাজকুমার। সদ্যভূমিষ্ঠ কন্যাসন্তানটিকে উৎসর্গ করলাম আমার প্রথম কাব্য ‘স্বপ্নভস্মের চারুকর্ম’। কিন্তু বই বেরুনো মানেই কি লেখক হিসেবে সনদপ্রাপ্তি? না, তা নয়। প্রথম বইটি বেরুনোর পরই শুরু হয় আসল লেখক-জীবনে প্রবেশের সংগ্রাম। ২০১০ সালের কথা। আমার ত্রয়োদশ কাব্য ‘ধুলোয় লুটোনো দিন’ রচিত হয়েছিল যখন দিনগুলো ধুলোয় লুটোচ্ছিল। আর রাতগুলো সাঁতার কাটছিল জোছনার দিঘিতে। ধুলোর ভিতরও থাকে সোনা, আমার তখনো জানা ছিল না। দিনগুলো টাকা কামানোর চাকরগিরিতে লুটোপুটি খেতে খেতে অকস্মাৎ বলে উঠেছিল— তুমি না মানুষ! দাসত্বের সঙ্গে কেন বাঁধবে গাঁটছড়া।
সাহিত্য সম্পাদক এ লেখার জন্য শব্দসংখ্যা বেঁধে দিয়েছেন, আর বলেছেন আমি যেন নবীন-তরুণদের উদ্দেশে কিছু বলি। সত্যি বলতে কি, নিজের লেখার পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। সেখানে অন্য কারু পরামর্শ কোনো কাজে আসে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই তো একজন নবীনের লেখক হওয়ার সংগ্রাম। তাই এ জীবনের দিকে তাকিয়ে কোনো ইশারা হয়তো পাওয়া যাবে। শুরুতে বইয়ের কথা বলেছি। লেখার জন্য বই পড়ার যে কোনো বিকল্প নেই— সেকথা এখন নিশ্চয়ই সবাই মানেন। শুধু কি নিজের ভাষার লেখা পড়লেই চলে? চলে না। ছাত্রজীবনে ইউসিস লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের কার্ড করেছিলাম। একসঙ্গে চারখানা করে বই আনা যেত। কবিতার বই তো নিতামই, বেশি করে নিতাম প্রবন্ধগ্রন্থ আর উপন্যাস। পরে কর্মজীবনে সাহিত্য সম্পাদনার কারণে আমার সুবিধে ছিল দেশের তাবৎ লেখকের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। সুযোগটা আমি শিক্ষার্থীর মতোই কাজে লাগিয়েছি। বলতে চাইছি, সমকালীন কোনো লেখককেই হেলাফেলা করতে নেই। শামসুর রাহমানকেই দেখেছি তিনি নবীনদের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। আর বানান ও ছন্দ সম্পর্কে খুঁতখুঁতে ভাবও তাঁর কাছ থেকেই আমার পাওয়া। আজকাল অনেকেই ভাবেন ছন্দ ছাড়াই বুঝি কবিতা লেখা সম্ভব। আচ্ছা সারগাম ছাড়া কি কণ্ঠে সঠিক সুর তোলা সম্ভব? আর উঁচু দরের কণ্ঠশিল্পী হতে হলে উচ্চাঙ্গসংগীত কি না জানলে চলে! শব্দের মাত্রা ও ওজন যিনি না বুঝবেন, বাংলা কবিতার ছন্দ যাঁকে ভালো না বাসবে তিনি যত নাম করুন না কেন ফেসবুকে—আমার বিবেচনায় তিনি কবি নন। শিল্পের প্রতিটি শাখারই নিজস্ব ‘ভাষা’ রয়েছে, রয়েছে তার রং ও আদল, সুধা ও সৌন্দর্য, শক্তি ও সুষমা। এটা অস্বীকার করে বেশিদূর যাওয়া যায় না। আর কবিতার মতো শুদ্ধতম শিল্পের বেলা এসব যে কত জরুরি তা কাব্যসাগরে একবার ডুবুরির পোশাকে (অর্থাৎ পাঠক হিসেবে) ডুব দিয়েই অনুধাবন সম্ভব। কবিতা লেখার জন্য এখনো যখন চুপটি করে নিজের মুখোমুখি এসে বসি, মনে হয় এর আগে কখনো কোনো কবিতা লিখিনি; জীবনে বুঝি এই প্রথম লিখতে বসেছি। আর লেখা হয়ে যাওয়ার পর এত অতৃপ্তি আর অসহায়ত্ব কাজ করে যে, তরতাজা নতুন কোনো বইয়ের ভিতর আশ্রয় খুঁজতে হয়; তখন পুনরায় নিমজ্জিত হতে চাই জীবনের বহিরঙ্গ ছাপিয়ে গভীর গহিন কল্পনা, ভাবনা এবং অনুভূতি রাজ্যে।