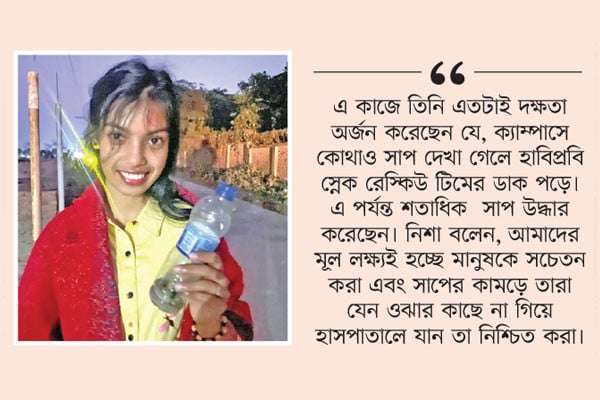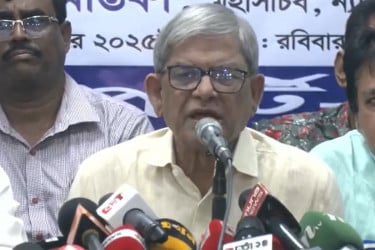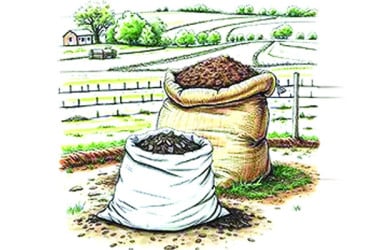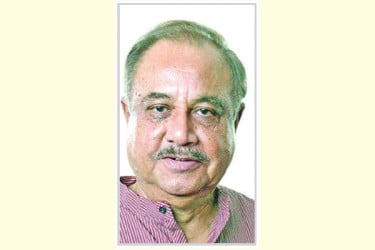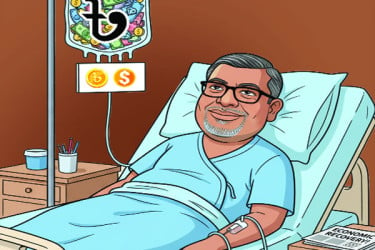ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শুধু একটি ভবন নয়, এটি জ্ঞানের ইতিহাস সংগ্রহ ও প্রজন্মের সাক্ষী। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জন্ম নেওয়া এই গ্রন্থাগারই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ একাডেমিক লাইব্রেরি। শতবর্ষ পেরিয়ে আজও এটি গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবার কাছে নির্ভরতার জায়গা। তবে সময়ের পালাবদলে গ্রন্থাগারটি যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি পাল্টেছে এর পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও পাঠক সংস্কৃতিও। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গঠিত হয় ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ থেকে পাওয়া প্রায় ১৮ হাজার বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে। প্রথমে এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ভবনে ছিল। পরে কার্জন হল প্রাঙ্গণের পুকুরপাড়ে স্থানান্তরিত হয়। সর্বশেষ, ১৯৫০-এর দশকে বর্তমান ভবনে উঠে আসে। টিএসসিসংলগ্ন, চারুকলা অনুষদের দিকেই মুখ করা এই স্থাপনাটি। এর প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন ঢাকা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এফ সি টার্নার। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৮৭৭ শিক্ষার্থী ও ৬০ জন শিক্ষক ছিলেন। সেই সূচনা আজ পরিণত হয়েছে প্রায় ৯ লাখ বই ও জার্নালের বিশাল ভান্ডারে, যেখানে সংরক্ষিত আছে ৩০ হাজারেরও বেশি বিরল পাণ্ডুলিপি। বাংলা, ফারসি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষার অমূল্য দলিল। গ্রন্থাগারের এই সংগ্রহে মোগল আমলের দলিল থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক সময়ের সরকারি নথিপত্রও পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেক বই-ই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থাগারের বিরল সংগ্রহে রয়েছে ১৮ ও ১৯ শতকের পুথি, ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক রিপোর্ট এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত পোস্টার, সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক বিবৃতি এখানে সংরক্ষিত থাকায় এটি গবেষকদের জন্য অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থাগারের রেয়ার কালেকশন সেকশনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দলিলভান্ডারগুলোর একটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও জাতীয় আর্কাইভ সংরক্ষণে এই উপকরণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এটি তিনটি ভবনে বিভক্ত। প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন এবং বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ভবন। আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই তিন তলা ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বিশাল ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে বইয়ের গন্ধে ভরা এক প্রশান্ত পরিবেশ। গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক ভবনে রয়েছে বই অধিগ্রহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হিসাব, সেমিনার, পুরাতন সংবাদপত্র, পাণ্ডুলিপি ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ রিসোর্স সেন্টার। প্রধান ভবনে রয়েছে পাঠকসেবা, বিরল বই ও থিসিস রুম, আর্কাইভস, সংবাদপত্র পাঠাগার, সাইবার সেন্টার ও অনলাইন ক্যাটালগ সেবা (OPAC)। বিজ্ঞান ভবনে চারটি রিডিং রুমে একসঙ্গে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী বসতে পারেন; রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেফারেন্স রুম ও শিক্ষকদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা। শিক্ষক ও গবেষকরা ১৪ দিনের জন্য তিনটি বই, শিক্ষার্থীরা ১০ দিনের জন্য ১০টি বই ধার নিতে পারেন। প্রতি তলায় রাখা হয়েছে অভিযোগ বাক্স, যা সপ্তাহে একবার খোলা হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিশেষভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে রিসোর্স সেন্টার, যেখানে ব্রেইল বই, স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার ও ব্রেইল প্রিন্টারের মাধ্যমে তারা পাঠ গ্রহণ করেন। বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারটি ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্প্রতি ‘ই-লাইব্রেরি’ উদ্যোগ চালু করেছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার জার্নাল, গবেষণাপত্র ও ই-বই পড়তে পারছেন। গত দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল ইউজার কার্ড, অনলাইন সার্চ ক্যাটালগ, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ও ই-জার্নাল সেবা। লাইব্রেরির সাইবার সেন্টার থেকে এখন গবেষকরা JSTOR, ScienceDirect, Taylor & Francis, Wiley Online Library - এর মতো আন্তর্জাতিক জার্নাল প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে পারেন। এ ছাড়া সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭২-৭৫ সালের পুরোনো সংবাদপত্র আর্কাইভ ডিজিটালভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা দেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ ছাড়া লাইব্রেরির ডিজিটাল আর্কাইভে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন দলিল ও গবেষণাপত্রগুলো ধীরে ধীরে অনলাইনে সংরক্ষণের কাজও চলছে। তবে সব উন্নতির মাঝেও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। পুরোনো ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যাপ্ত আসনসংখ্যার অভাব এবং পর্যাপ্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি অনেক সময় পাঠকদের বিরক্তির কারণ হয়। তা ছাড়া, পুরোনো কিছু বই ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি থাকায় ক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়ছে। অনেক শিক্ষার্থী আরও বেশি সময় খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন, যাতে তারা সন্ধ্যা বা রাতেও পড়াশোনা করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একসময় ছিল শিক্ষার্থীদের প্রতীক্ষার প্রতীক। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে সিট পাওয়া লাগত রিডিং রুমে। তবে ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়মে আবাসিক হলগুলোতে বৈধ সিট বণ্টন কঠোর হওয়া, অবৈধভাবে থাকা অছাত্র ও বহিরাগতদের সংখ্যা কমে আসার ফলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আগের মতো ঠেলাঠেলি, ভোরবেলার লাইন, এসব আর নেই। এ ছাড়া প্রযুক্তি, নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ডিজিটাল ক্যাটালগ ও আধুনিক রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক নতুন পর্বে।
২০০৭-০৮ অর্থবছরে গ্রন্থাগারে নতুন বই ও জার্নাল সংগ্রহের জন্য প্রায় ৯.৯ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই বরাদ্দ বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় কমে এসেছে। এর প্রভাব পড়েছে নতুন বই, বিদেশি জার্নাল ও গবেষণা উপকরণ সংগ্রহে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদিত বাজেট বৃদ্ধি না পেলে ভবিষ্যতের গবেষণাভিত্তিক লাইব্রেরি গড়ে তোলা কঠিন হবে এমন আশঙ্কা জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ২ হাজার ৮৪০ কোটি টাকার এক মাস্টারপ্ল্যান ঘোষণা করেছে। সেই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন ধ্বংস করে নতুন ১২ তলা ও ছয় তলাবিশিষ্ট দুটি আধুনিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন ভবনে থাকবে প্রায় ৪ হাজার সিট, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বই-ধার ব্যবস্থা, ই-লাইব্রেরি সেকশন এবং বিশেষ গবেষণা আর্কাইভ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ধারণা, আগামী তিন বছরের মধ্যে নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। সব সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে গ্রন্থাগারটি আজ শুধু শিক্ষার্থীদের পাঠাগার নয়; এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অংশ। এক শতাব্দী ধরে এটি জ্ঞানের বাতিঘর হিসেবে আলোকিত করছে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। বইয়ের মলাটে, পাণ্ডুলিপির পাতায় আর নীরব পাঠকক্ষের ভিতর জড়িয়ে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কেবল একটি ভবন নয় এটি জ্ঞানের অনন্ত যাত্রায় এক নির্ভরযোগ্য দিশারি, যা আগামী প্রজন্মকেও একই আলোয় পথ দেখাবে।