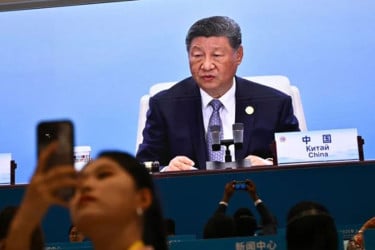আওয়ামী লীগের ক্ষমতার রাজনীতির শুরু ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় নির্বাচনি জোট ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠিত হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি), নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রাব্বানী পার্টি সমন্বয়ে। ৯টি সংরক্ষিত নারী আসনসহ ৩০৯ আসনের প্রাদেশিক আইনসভায় যুক্তফ্রন্ট লাভ করেছিল ২২৮টি আসন। এর মধ্যে ১৪৩ আসনেই জয়ী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা। যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দল কৃষক শ্রমিক পার্টি পেয়েছিল ৪৮টি আসন। আইনসভার বাদবাকি আসন পেয়েছিলেন অন্যান্য শরিক দল এবং অমুসলিম, স্বতন্ত্র ও তফসিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন। এই নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করার মতো রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানে আর দ্বিতীয়টি নেই।
প্রথমবার ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যে কোনো দেশে, যে কোনো দল যেমন বেপরোয়া হয়ে ওঠে, আওয়ামী লীগের লোকজনের স্বভাবচরিত্রে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো এত প্রকট হয়ে উঠেছিল যে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান শুরু করেছিল। যার পরিণতি ছিল প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে দুই মাসের মধ্যে প্রাদেশিক আইনসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভা পুনর্বহাল হলে আইনসভায় আওয়ামী লীগের একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার কারণে আগের মতো একই ধরনের হাঙ্গামা অব্যাহত থাকে। ১৯৫৪ সালের মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটোয়ারীকে হত্যা করার ঘটনা পর্যন্ত দুই বছর প্রাদেশিক আইনসভা ও প্রাদেশিক সরকার না থাকা সময়কে বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাতবার মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করতে হয়। যেহেতু প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল, অতএব রাজনীতি ও ইতিহাসসচেতন পাঠকরা সহজে বুঝতে পারবেন যে ঘটনাগুলো কাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে।
 এ সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায় পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ১৫ জন গভর্নরের এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মেজর এস জি জিলানির আত্মজীবনীমূলক ‘ফিফটিন গভর্নরস আই সার্ভড উইথ : আনটোল্ড স্টোরি অব ইস্ট পাকিস্তান’ গ্রন্থে। জিলানির বর্ণনা অনুসারে, ‘১৯৫৮ সালের ১৮ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ১৩৮-১২৬ ভোটে পরাজিত হয়। ন্যাপের ১৮ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকায় আওয়ামী লীগ সরকারের এই বিপর্যয় ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ দাখিল করতে গভর্নমেন্ট হাউসে আসেন। পরদিন গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার। তিনি দাবি করেন যে হাউসে তার দল কেএসপির প্রতি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন রয়েছে এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠনের মতো সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। গভর্নর পরদিন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেন। কিন্তু এর মধ্যেই গভর্নর খবর পান যে ন্যাপের ১৮ জন সদস্য আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অতএব আবু হোসেন সরকারের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করেন আবু হোসেন সরকার এবং তার মন্ত্রিসভার দুজন সদস্য মি. লাহিড়ি ও আবদুল হামিদ। কারণ আবু হোসেন সরকার তার মন্ত্রিসভার অন্যান্যের ব্যাপারে তখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এ অবস্থায় তার সরকার স্থায়ী ছিল মাত্র তিন দিন। ১৯৫৮ সালের ২৩ জুন হাউসে তার সরকারের বিরুদ্ধে ১৫৬-১৪২ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। কিছুক্ষণ পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা আতাউর রহমান খান আসেন নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি নিয়ে। আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন।’
এ সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায় পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ১৫ জন গভর্নরের এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মেজর এস জি জিলানির আত্মজীবনীমূলক ‘ফিফটিন গভর্নরস আই সার্ভড উইথ : আনটোল্ড স্টোরি অব ইস্ট পাকিস্তান’ গ্রন্থে। জিলানির বর্ণনা অনুসারে, ‘১৯৫৮ সালের ১৮ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ১৩৮-১২৬ ভোটে পরাজিত হয়। ন্যাপের ১৮ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকায় আওয়ামী লীগ সরকারের এই বিপর্যয় ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ দাখিল করতে গভর্নমেন্ট হাউসে আসেন। পরদিন গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার। তিনি দাবি করেন যে হাউসে তার দল কেএসপির প্রতি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন রয়েছে এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠনের মতো সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। গভর্নর পরদিন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেন। কিন্তু এর মধ্যেই গভর্নর খবর পান যে ন্যাপের ১৮ জন সদস্য আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অতএব আবু হোসেন সরকারের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করেন আবু হোসেন সরকার এবং তার মন্ত্রিসভার দুজন সদস্য মি. লাহিড়ি ও আবদুল হামিদ। কারণ আবু হোসেন সরকার তার মন্ত্রিসভার অন্যান্যের ব্যাপারে তখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এ অবস্থায় তার সরকার স্থায়ী ছিল মাত্র তিন দিন। ১৯৫৮ সালের ২৩ জুন হাউসে তার সরকারের বিরুদ্ধে ১৫৬-১৪২ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। কিছুক্ষণ পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা আতাউর রহমান খান আসেন নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি নিয়ে। আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল কেএসপি ও আওয়ামী লীগ। কিন্তু আইনসভার কোন সদস্য কোন দলে তা নিয়ে তখনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। কারণ সদস্য তালিকায় একই সদস্যের নাম আওয়ামী লীগ ও কেএসপি উভয় দলেই ছিল। গভর্নর এ অবস্থা নিরসন করতে উভয় দলের নেতাদের নির্দেশ দেন এ ধরনের দোদুল্যমান সদস্যদের তার সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের দলীয় আনুগত্য প্রমাণ করতে হবে। একদিন সকালে বর্ষীয়ান নেতা ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মি. আলীকে সঙ্গে নিয়ে গভর্নরের কাছে এসে গভর্নরকে জানান যে, মি. আলী কেএসপির সদস্য। রাত সাড়ে ১১টার দিকে গভর্নর তার পাঠকক্ষে ছিলেন, আমি দ্রুতবেগে দুটি গাড়ি আসতে দেখি। গাড়ি দুটি পোর্চের নিচে কড়া ব্রেক করে থামে। প্রথম যিনি গাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। তার পেছনে অন্য যারা ছিলেন তাদের মধ্যে আমি শুধু মি. আলীকে চিনতে পারি, যিনি সকালে গভর্নমেন্ট হাউসে এসেছিলেন। তার মাথার চুল এলোমেলো ও পরনে লুঙ্গি, চেহারা বিধ্বস্ত। শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরও দুই ব্যক্তি তাকে সঙ্গে নিয়ে গভর্নরের পাঠকক্ষে যান। অন্যরা বাইরে অপেক্ষা করেন। জানা যায়, মি. আলী সকালে গভর্নমেন্ট হাউসে এসে কেএসপির পক্ষে তার সমর্থনসূচক স্বাক্ষর দিয়েছেন জানার পর আওয়ামী লীগ নেতারা ঘণ্টাখানেক আগে তার বাড়িতে গিয়ে ঁতাকে পিটিয়েছে এবং হুমকি দিয়েছে। এখন তাকে গভর্নরের কাছে আনা হয়েছে কেএসপির প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করানোর জন্য। আমি গভর্নরের পাঠকক্ষে প্রবেশ করার পর মি. আলীকে বলতে শুনি যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস সকালে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে নিয়ে এসেছিলেন, আসলে তিনি আওয়ামী লীগের লোক। আতাউর রহমান খান আবারও মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ করেন।’
আওয়ামী লীগ এ দেশে তাদের রাজনীতির সূচনাকাল থেকেই অন্য কাউকে সহ্য করার সংস্কৃতি চর্চা করতে শেখেনি। মওলানা আবদুল খান ভাসানীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং তিনি দলটির সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ও আদর্শগত মতপার্থক্যের কারণে তাকে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করতে হয়। ১৯৫৭ সালে রূপমহল সিনেমা হলে আয়োজিত ন্যাপের কনভেশনে হামলা করে আওয়ামী লীগ কর্মীরা এবং কনভেনশন পণ্ড করে দেয়। এরপর ন্যাপ পল্টন ময়দানে জনসভা আয়োজন করলে আওয়ামী লীগ জনসভাও ভন্ডুল করে দেয়। কাউকে সহ্য না করার আওয়ামী ‘গণতন্ত্র’ এত বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের বিলয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে শান্তিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কোনো উপায় ছিল না।
সন্দেহ নেই, অতি সহজে জনগণকে সস্তা মুখরোচক স্লোগানের জালে আটকে ফেলতে আওয়ামী লীগের জুড়ি কখনো ছিল না, এখনো নেই। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মুখরোচক স্লোগান ও নির্বাচনি ইশতেহার মূলত একই ধরনের ছিল। ১৯৫৪ সালের ১২ বছর পর ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা এবং এর চার বছর পর ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক চক্রের বিরুদ্ধে এত সফল প্রচারণা চালিয়েছিল যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে কার্যত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমানকে অখণ্ড পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে বাধাদানকারী পশ্চিম পাকিস্তানের সব রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেও যদি ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে সরকার গঠন করতে আহ্বান জানাতেন, তাহলেও কি আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক সরকার গঠন ও ভাঙনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছে, তার চেয়ে ভালো কোনো পরিস্থিতি ফিরে আসত। কখনোই আসত না।
আওয়ামী লীগ এককভাবে অথবা দুর্বল কোনো দল বা দলসমষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করলেই যদি তাদের শাসিত দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করত, তাহলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ এত দিনে উন্নয়নের মগডালে পৌঁছে যেত, দেশ থেকে বিপুল সম্পদ বিদেশে পাচার হতো না, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টারের শিকার হতো না, গুম বা নিহত হতো না, প্রতিপক্ষের লোকজনকে পালিয়ে বেড়াতে হতো না বা লাখ লাখ লোকের বিরুদ্ধে ভুয়া মামলা দায়ের হতো না, কিংবা বিনা বিচারে কারাগারে আটকে থাকতে হতো না। শেখ মুজিবের ১৯৭২-৭৫ মেয়াদের শাসন, শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের শাসন এবং সর্বশেষ তার ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনকালে বাংলাদেশে যে রামরাজত্ব কায়েম হয়নি, তা শেখ মুজিবের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং প্রাণভয়ে শেখ হাসিনার পলায়নই তার দৃষ্টান্ত।
আওয়ামী লীগই যে বাংলাদেশের মা-বাপ, গণতন্ত্রের শিখণ্ডী এবং সর্বোপরি মাঝখানে দুবার বিরতি ছাড়া তারাই স্বাধীনতার ৫৪ বছরের মধ্যে এককভাবে ২৪টি বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অধীনে ছিল না। শাসক হিসেবে আইউব ও ইয়াহিয়া খান ছিলেন না। হ্যাঁ, দেশে দুবার জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন ছিল। যেহেতু উভয় জেনারেল বাঙালি ছিলেন এবং পাকিস্তানি ছিলেন না, অতএব এই দুই সামরিক শাসকের অধীনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দিয়েছিল।
মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের ডাকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গুটি কতক পাকিস্তানপন্থি ছাড়া সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, অকাতরে জীবন দিয়েছে, মা-বোনেরা সম্ভ্রম হারিয়েছে। তাদের ত্যাগে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমগ্র জনগোষ্ঠীর ত্যাগে অর্জিত দেশের একক দখল নিয়ে প্রচণ্ড দম্ভে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে শুরু করেছিল আওয়ামী লীগের বাইরের যারা দেশ পুনর্গঠন কাজে সবার ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল, তাদের আহ্বানে কোনো পাত্তাই দেননি বাঙালির ‘অবিসংবাদিত’ নেতা ‘গণতন্ত্রের মানসপুত্র’ সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য শাগরেদ শেখ মুজিবুর রহমান। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। শেখ মুজিব স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যে ‘তিনিই বাংলাদেশ, তিনিই নেতা’। তাঁর অনুসারীরা স্লোগান তুলেছে, ‘এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ’। তারা শেখ মুজিবকে দেবত্বের আসনে বসিয়েছিল। তাদের কাছে বর্তমানই ছিল সবকিছু। তারা নগদ প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতে, যা ৯০০ বছর আগে ওমর খৈয়ামের বাণীর পূজারি ছিল : ‘নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক/দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।’ শুরুতেই উল্লেখ করেছি, জন্মাবধি আওয়ামী লীগ কাউকে দিয়ে থুয়ে খাওয়ার রাজনীতিতে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, খাওয়ায় ভাগ বসাতে পারে এমন কাউকে কখনো সহ্য পর্যন্ত করেনি।
শেখ হাসিনা হয়তো ব্যতিক্রম ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে পারেননি, তা কি মাটি বা জলবায়ুজনিত দোষে। এই মাটি ও আবহাওয়া তো সোনা ফলায়। সুবাস জড়ানো ফসল ফলায় যে মাটি, সে মাটির সংস্পর্শ তো যে কোনো মানুষকে খাঁটি করে তোলার কথা। তবু বারবার এ মাটির দখল শাসককে নিষ্ঠুর, ক্রূর করে তোলে কেন? বারবার তারা কেন প্রমাণ করেন ‘অঙ্গার : শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে,’ (কয়লা শতবার ধুলে ময়লা যায় না।) মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর মানুষের মাঝে যখন অনুশোচনা আসার কথা, অনুতাপে দগ্ধ হওয়ার কথা, এর পরিবর্তে প্রতিশোধ চরিচার্থ করার আস্ফালন ও উসকানি দান কোনোভাবে সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। এসব থেকে সহজ উপসংহার টানা যায়, ‘রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই’ বলে যে প্রবচন আছে, তা হতে পারত জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে বিপ্লব বা অভ্যুত্থানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দম্ভ ও প্রতিশোধপরায়ণতার মনোবৃত্তি না থাকত। তাদের চালু করা ঘৃণা-বিদ্বেষের রাজনীতি বুমেরাং হয়ে তাদের ওপরই বর্ষিত হয়েছে, তা থেকেও যদি তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করে, তাহলে প্রতিপক্ষও পুনরায় একই আচরণ করবে এবং যুগ যুগ ধরে এ ধারার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। ঘৃণা-বিদ্বেষের রাজনীতিই দেশে একটি শ্রেণিকে দুর্বৃত্তায়নের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে।
প্রত্যাখ্যাত শাসকের ও লালিত রাজনৈতিক এতিমদের কথাবার্তায় মনে হয়, বাংলাদেশ এখনো কোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। এটি এখনো কোনো দুর্বল ও রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক কলহবিবাদে বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ এক ভূখণ্ড, যাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলাফল হিসেবে কোনো ঔপনিবেশিক ও আধিপত্যবাদী শক্তি ওত পেতে বসে আছে ভূখণ্ডটিকে সহজে তাদের কবজায় নিতে। কারণ এমন পরিস্থিতিতে দেশে মীরজাফর পাওয়া কঠিন কাজ নয়। মীরজাফরের সময় রাজনীতি বলে কিছু ছিল না, সবই হতো ঊর্ধ্বতনদের ‘প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে’। এখন রাজনীতি আছে, ঘৃণার রাজনীতি অগণন মীরজাফর সৃষ্টি করেছে। তারা দেশকে বাইরের শক্তির হাতে তুলে দিয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতেও প্রস্তুত। কারণ তারা মুখে যা বলেন, অন্তরে পোষণ করেন ভিন্ন কিছু। তারা জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণের কথা বলে মুখে ফেনা তোলেন, কিন্তু ক্ষমতা পেলেই জনগণকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজ নিজ মর্জি অনুযায়ী কাজ করে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন ও ঘৃণা ছড়ান। স্বাধীনতার চেতনা, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ আওয়াজ তোলা আওয়ামী লীগের মোক্ষম এক অস্ত্র হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের রাজনীতিতে। সযত্নে লালন করছে তারা এসব চেতনা। বিভাজনের রাজনীতির খেসারত দিয়েও হুঁশ হয়নি তাদের। রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়েছে বারবার এবং প্রতিটি পরিবর্তনে আশা করা হয়েছিল রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরে আসবে। কিন্তু তা আসেনি। স্বাধীনতার পর জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়নি। এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। কখনো কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরে আসবে?
লেখক : যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক ও অনুবাদক