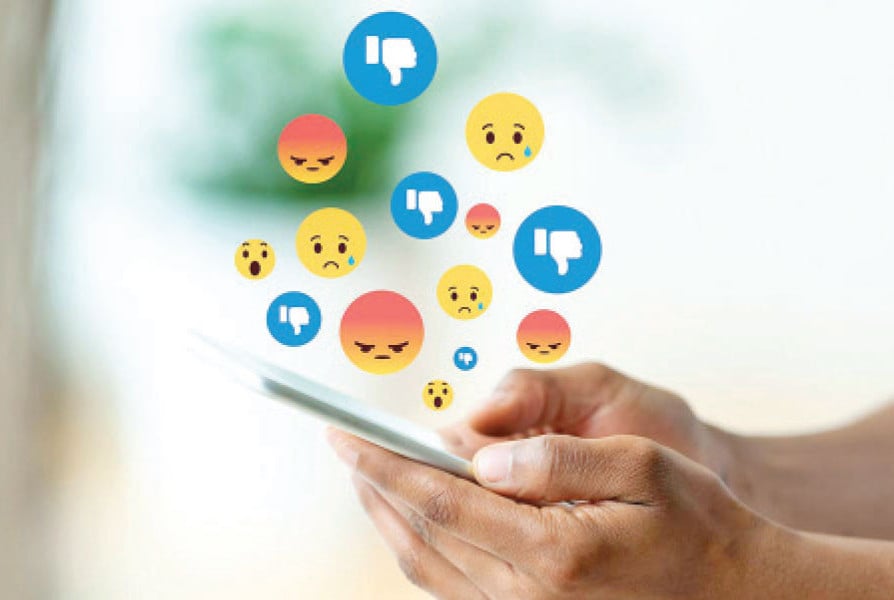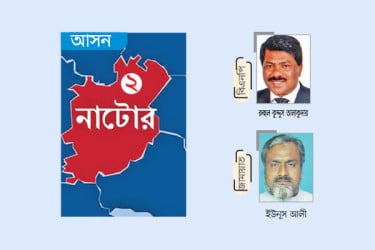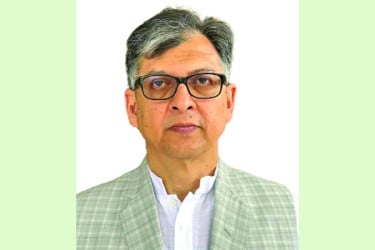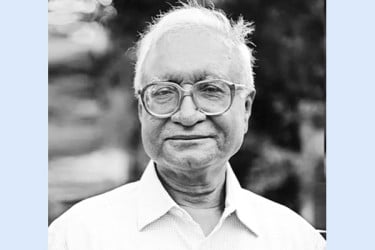বর্তমানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে অপরাধ দমনের একটি কার্যকরী মাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সমাজের অসংগতিগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরে জনগণের দৃষ্টিতে আনার মাধ্যমে জনমত তৈরি করলে অনেক সময় খুব দ্রুত প্রতিকার পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা তখন সেই অসংগতি ঠিক করার জন্য খুব তৎপর হয়ে ওঠে। এদিক থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এসব কার্যক্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।
কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর উল্টো হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে, ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা ভিউ বাড়ানোর আশায় অনেক নিরপরাধ মানুষকে জাতির সামনে অপমান করা হয়। মন্দ উপাধি দিয়ে তার ও তার পরিবারের লোকদের ভার্চুয়ালি হেনস্তা করা হয়। মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়া তো হয়ই, যেকোনো সময় শারীরিক হেনস্তায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ফেলে দেওয়া হয়, যা সুস্পষ্ট জুলুম।
ইসলামের দৃষ্টিতে এভাবে সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যমে মব তৈরি করা জঘন্য অপরাধ। নিম্নে কোরআন-হাদিসের আলোকে ইন্টারনেটকেন্দ্রিক এসব জুলুমের কিছু পদ্ধতি ও অপকারিতা তুলে ধরা হলো—
অনলাইন শেমিং : কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অযথা কারো ভুল প্রকাশ করে অপমান করা, ছোট বিষয়কে বড় করে প্রচার করা। তিলকে তাল বানিয়ে অনলাইন বট বাহিনীর মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে কাউকে রাতারাতি জাতীয় বেঈমান বানিয়ে দেওয়া। অথচ দেখা গেছে, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকটিকে আক্রমণ করা হলো, তার সঙ্গে সেই লোকের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত নয়।
পবিত্র কোরআনে এ ধরনের প্রপাগান্ডাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ‘হে ঈমানদাররা, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা কোরো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম।’
(সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১১)
ডক্সিং : ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করার মতো কোনো তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া।
ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব জেন্ডার, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনের মতে, ডক্সিং বলতে কারো অনুমতি ছাড়া তার ফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা, শনাক্তকরণ নম্বর, ছবির মতো স্পর্শকাতর বা ব্যক্তিগত গোপনীয় নথি ও তথ্য প্রকাশ করা বোঝায়। সাধারণত কোনো ব্যক্তির জীবনকে হুমকিতে ফেলতে ডক্সিং করা হয়। পবিত্র কোরআনে এ রকম অসৎ উদ্দেশ্যে কারো গোপন তথ্য অনুসন্ধানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান কোরো না এবং একে অপরের গিবত কোরো না। (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১২)
কারো বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ভুল তথ্য ছড়িয়ে জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তাকে আরো বেশি চাপে ফেলার জন্য অনলাইনে তার ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। এমনকি মজা করেও কাউকে এভাবে ভয় দেখানো উচিত নয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলাহ (রহ.) বলেন, আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে একদা তাঁরা নবী (সা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তাঁদের এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে তাঁদের মধ্যকার কেউ গিয়ে (মজার ছলে) তার সঙ্গের রশি নিয়ে এলো। তাতে সে ভয় পেয়ে গেল। নবী (সা.) বলেন, কোনো মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।
(আবু দাউদ, হাদিস : ৫০০৪)
ক্যানসেল কালচার : ক্যানসেল কালচার হলো সামাজিক মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা ধারণাকে বয়কট করা, নিন্দা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো, যা প্রায়শই জনসম্মুখে অপমানের মাধ্যমে করা হয়। এটি বিতর্কিত বা অনৈতিক কাজের জন্য সমালোচনা ও জবাবদিহি চাওয়ার একটি উপায়, তবে এটি কখনো কখনো অতিরিক্ত, অন্যায্য এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে যেতে পারে, যা লক্ষ্যবস্তুর ক্যারিয়ার, খ্যাতি ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অথচ হাদিস শরিফে মুসলমানের এমন দোষ গোপন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা ব্যাপকভাবে সমাজের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাতে তাদের দোষ গোপন রাখবেন।
(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৫)
এখন তো অনলাইনে দেখা যায়, কোনো একজন ব্যক্তিতে পরিকল্পিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করতে গিয়ে তার পরিবার কিংবা তার জেলা নিয়ে পর্যন্ত অপপ্রচার চালানো হয়। অথচ ওই ব্যক্তি বাস্তবে অপরাধী হলেও তার পরিবার কিংবা তার জেলার সবাই তো ওই অপরাধে লিপ্ত ছিল না, তাহলে ওই পরিবার বা জেলার বাকি সবাইকে গণহারে দোষী সাব্যস্ত করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের ট্যাগ করে হেনস্তা করা জুলুম বৈ কিছু নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম।’ (প্রাগুক্ত)
ট্রোল আর্মি : সংগঠিতভাবে মিথ্যা অ্যাকাউন্ট বা বট ব্যবহার করে আক্রমণ চালানো। সাধারণত এসব কার্যক্রমের মূল উপাদানগুলো হয় বানোয়াট। মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে হেনস্তা করাই হয় এদের উদ্দেশ্য। অথচ পবিত্র কোরআনে মিথ্যা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ...আর মিথ্যা কথা পরিহার করো।
(সুরা : হজ, আয়াত : ৩০)
মহানবী (সা.) বলেছেন, আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যাকে পরিহার করবে, কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৭১)
মিম বানিয়ে অপমান করা : কাউকে বিদ্রুপ করার জন্য তাকে নিয়ে মিম বানানোও মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। কারণ পবিত্র কোরআনে বিদ্রুপ করার প্রতি অনুৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আবার মিম বানাতে গিয়ে তার বা অন্য কারো ছবি তৈরি বা এডিট করার প্রয়োজন হয়, যার ব্যাপারে ইসলামে গুরুতর আপত্তি আছে।
অতএব ইন্টারনেটের এই যুগে আমাদের উচিত, আরো সতর্ক হওয়া। ক্ষোভ কিংবা মজার ছলে এমন কাজে রত হওয়া উচিত নয়, যা আমাদের ইহকাল ও পরকালের বিপদের কারণ হতে পারে।
বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন