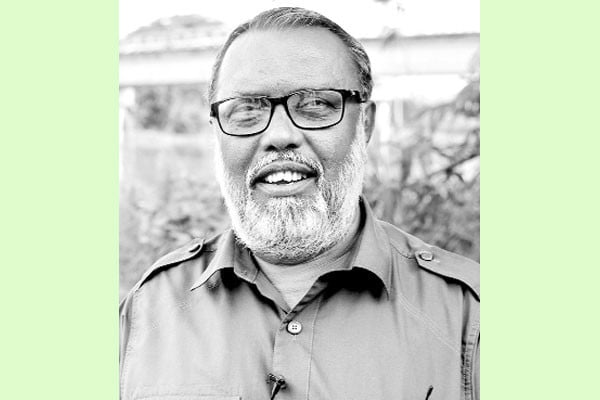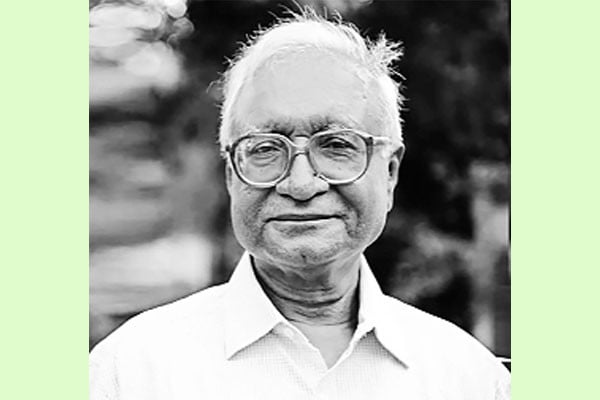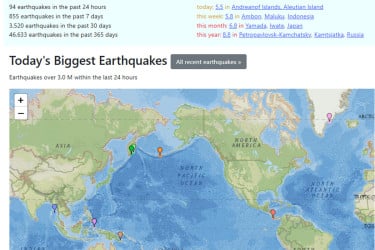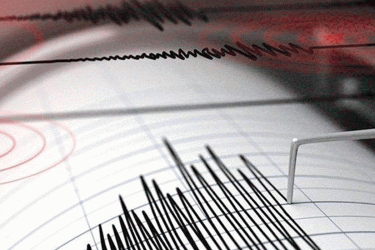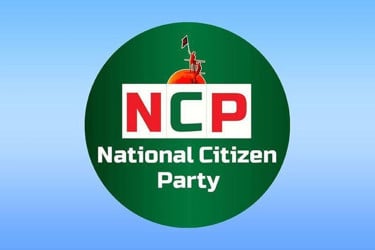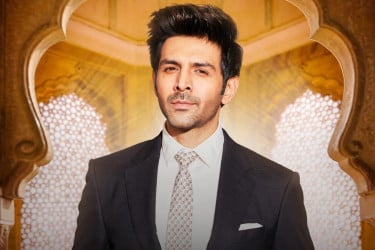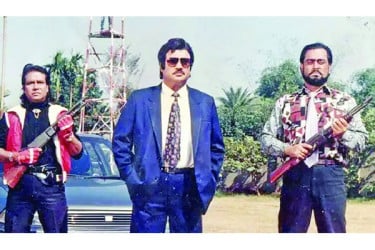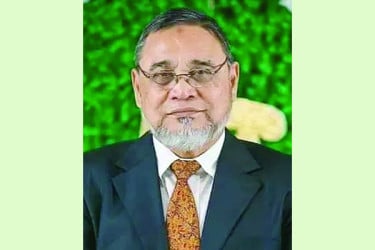এক. 'May I Come in Sir'- মুণ্ডটা কচ্ছপের মতো করে দরজা গলে কক্ষের ভেতরে ঢুকিয়ে কিঞ্চিৎ ভয় মিশেল গলায় উপরোক্ত কথাগুলো বললাম আমি। প্রতিউত্তরে ভদ্রলোকটি বললেন- Yes, please come in. তাকে দেখেই একেবারে চমকে উঠলাম আমি। মানুষটি দেখতে অনেকটাই ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের মতো। সেই শুভ্র সফেদ ধবধবে সাদা কেস বিন্যাস। দুজনেরই প্রায় একই রকম মুখাবয়ব। পার্থক্য শুধু এতটুকুই- জন মেজর খানিকটা শীর্ণকায় ও লম্বাটে, অন্যদিকে এই মানুষটি ঈষৎ খর্বকায় ও হৃষ্টপুষ্ট। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল যে, আমার কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও ডিন, প্রফেসর ফিলিপ থমাসকে। আর সে জন্যই আমি এসেছি তার সঙ্গে মোলাকাত করতে। আমি তাকে সাড়ম্বরে 'স্যার' সম্বোধন করে আমাদের মধ্যকার কথোপকথনের সূত্রপাত করলাম। আর এতেই ঘটল বিপত্তি। উনি খানিকটা অপ্রসন্ন ও উষ্মা কণ্ঠে বললেন- Who is your Sir! I’m not your Sir. My name is Phillip Thomas. You can call me ‘Phill’. প্রফেসর থমাসের কথাগুলো শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একি বলছেন তিনি! যিনি বয়সে আমার বাবার চেয়েও বড়; তিনি কি না আমাকে বলছেন তার নাম ধরে ডাকতে! তাও আবার তার প্রথম নাম 'ফিল' বলে! আমাদের সংস্কৃতিতে শুধু মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবসহ একান্তই কাছের কিছু মানুষ সাধারণত আমাদের উপনামগুলো ডাকার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু তিনি কেন আমাকে সে অধিকার প্রদান করছেন? পরে অবশ্য জেনেছি, পাশ্চাত্যে কালক্রমে আধুনিক যুগে এটাই এখন তাদের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে।
প্রফেসর ফিল থমাস আমাকে বললেন, 'ঔপনিবেশিকতার যুগ অতিক্রম করে আমরা এখন বহুদূর চলে এসেছি। এখন আর স্যার-ট্যার ডাকার সুযোগ নেই। তোমরা এশিয়ানরা এখানে এসে কেন যে আমাদের স্যার ডাকা শুরু করে দাও, বুঝি না।' ফিলিপ থমাস ঠিকই বলেছেন, স্যার, মাইলর্ড, হুজুর, ধর্মাবতার- এই সম্মানসূচক অনুষঙ্গগুলো প্রশাসনিক কাজের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল সেই ঔপনিবেশিক সময়ে অর্থাৎ ইংরেজরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে। তবে এসব শব্দের উদ্ভব হয় ইউরোপে সেই সামন্ত যুগে। 'স্যার' শব্দের উৎপত্তি ফরাসি দেশে, সেখানে জমিদার বা সামন্ত প্রভুদের প্রজারা সম্বোধন করত 'স্যায়ার' বলে, সেই 'স্যায়ার' শব্দটি কালক্রমে বারোশ শতকের দিকে ঢুকে পড়ে ইংরেজি ভাষায়। পৃথিবীতে সামন্ত ও ঔপনিবেশিকতার যুগ শেষ হলেও সেসব যুগের ভূতগুলো এখনো চেপে আছে আমাদের ঘাড়ে।
পাশ্চাত্যে আধুনিক যুগে ছাত্র-শিক্ষক, আমলা-প্রজাসহ অন্য সব সম্পর্ক সহজ সাবলীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে আসছে; কিন্তু আমরা সেই পুরনো সংস্কৃতিতেই আটকে আছি। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে স্যার শব্দটিকে এখন অনেকটাই খেলো কিংবা হালকা করে ফেলা হয়েছে। আর সে জন্যই আমরা দেখি আমেরিকাতে রাগবি খেলার কোচকে যেখানে স্যার বলা অনেকটাই বাধ্যতামূলক, সেখানে সর্বোচ্চ পদের মানুষটি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে মাননীয় কিংবা মহামান্য তো অনেক দূরের কথা, তাকে শুধু সম্বোধন করা হয় মি. প্রেসিডেন্ট। উত্তরজীবনে প্রফেসর ফিল থমাসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এক অন্যরকম অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছিল। আইন পড়ার শেষ পর্যায়ে এসে ব্যারিস্টারিতে ভর্তি হওয়ার সময় তিনি আমার শিক্ষাজীবনের ওপর এমন একটি প্রত্যয়নপত্র দিয়েছিলেন যে, আমি যে পাঁচটি ইনস্টিটিউটে আবেদন করেছিলাম সম্ভবত হাতেগোনা গুটিকয়েক ছাত্রের মতো আমিও পাঁচটি (একজন ছাত্র সর্বোচ্চ পাঁচটি ইনস্টিটিউশনে আবেদন করতে পারে) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তির আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলাম। এটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। বেশ কয়েক বছর আগে প্রফেসর ফিল থমাস ঢাকায় এসেছিলেন। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট থেকে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই সময় অসুস্থ বাবাকে নিয়ে ব্যাংককে ছিলাম বলে তার সঙ্গে দেখা হয়নি। বন্ধু ব্যারিস্টার জুনায়েদ ও অনুজপ্রতিম ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ ফারুকের কাছে আমার অনেক খোঁজখবর নিয়েছিলেন বলে শুনেছিলাম। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে দুঃখও করেছিলেন।
দুই. ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য কার্ডিফ থেকে চলে এলাম লন্ডনে। যা হোক, লন্ডনে এসে আমি দ্রুতই শহরটিকে ভালোবেসে ফেললাম। চারদিকে আভিজাত্যময় উঁচু উঁচু হর্ম্য। নদী, প্রাসাদ, পার্লামেন্ট, শপিংমল... কী নেই শহরটিতে। আধুনিক চাকচিক্যে ইউরোপের বোধকরি আর কোনো শহর এর সামনে দাঁড়াতে পারে না। তবে এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্যারিস। লন্ডন যদি ব্যারিস্টারদের সেকেন্ড হোম বলে বিবেচিত হয়, তবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য ফার্স্ট হোম হচ্ছে প্যারিস। সাহিত্য, কবিতা, নন্দনতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্পকলায় কার চেয়ে কে এগিয়ে এই প্রতিযোগিতা চলছে যুগ যুগ ধরে এ দুটি শহরের মধ্যে। এহেন অসাড় প্রতিযোগিতায় দুই শহরকেই খুশি করে উপন্যাস লিখেছিলেন চার্লস ডিকেন্স 'এ টেল অফ টু সিটিস'। বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক বালজক দুই শহরকে একসঙ্গে খুশি করতে স্টাইল ও ফ্যাশন সম্পর্কে একটি অসাধারণ কথা বলেছিলেন সেই কবে; যা আজও সমান সত্য বলে বিবেচিত হয় “What is French Fashion in London is English Fashion in Paris” অর্থাৎ লন্ডনে যা ফরাসি ফ্যাশন হিসেবে চলে, সেটাই আবার প্যারিসে চলে ইংরেজি ফ্যাশন বলে।
বড় বড় ইমারত, প্রাসাদ, পার্লামেন্ট, শপিংমল ঘুরে বেড়িয়ে আমি যখন আত্দপ্রসাদের স্বগতোক্তি করছি যে, আমি লন্ডনের সব কিছু দেখে ফেলেছি, সেই সময় আমার এক অগ্রজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মোহাম্মদ আল ফায়াদের বিখ্যাত শপিংমল 'হ্যারোডস্' দেখেছি কি-না? আমি বললাম, না। তিনি পরামর্শ দিলেন সেই শপিংমলটি ঘুরে দেখতে। যা হোক, এক দিন হাতে সময় নিয়ে সকাল সকাল চলে গেছি বিখ্যাত সেই শপিংমল হ্যারোডস্ দেখতে। শপিংমলের মূল ফটকটি দিয়ে প্রবেশ করতেই চিরাচরিত সুসজ্জিত বেশ-ভূষার একজন দারোয়ান মাথাটি ঈষৎ নিচে নামিয়ে হাত দুটি সম্প্রসারিত করে বলতে লাগলেন- 'আসুন স্যার আসুন, ভিতরে আসুন'। প্রথম দর্শনেই লোকটিকে আমার বেশ পরিচিত মনে হলো। ভেতরে প্রবেশ করে আমি এক দোকান পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করলাম- আচ্ছা, শপিংমলের মূল প্রবেশমুখে যে দারোয়ানটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে। উনি কি মোহাম্মদ আল ফায়াদের সহোদর? দোকানি স্মিত হেসে আমাকে বললেন- আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার; তবে উনি আসলে মোহাম্মদ আল ফায়াদের সহোদর নন। উনি স্বয়ং হ্যারোডসের মালিক মোহাম্মদ আল ফায়াদ। মোহাম্মদ আল ফায়াদকে আমি বেশ ভালো করেই চিনতাম। কারণ সেই সময়টায় মোহাম্মদ আল ফায়াদ ও বিখ্যাত জাঁদরেল এক ব্রিটিশ এমপি নীল হ্যামিল্টনের মধ্যে ঘুষ আদান-প্রদানের একটি মোকদ্দমা চলছিল। ফলে সেই সময়ে প্রায়ই ফায়াদ ও নীল হ্যামিল্টনের ছবি ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বেশ বড় বড় সাইজে ছাপা হতো। দোকান পরিচারিকার কাছ থেকে আমি যখন জানলাম যে, দারোয়ানটি আসলে স্বয়ং মোহাম্মদ আল ফায়াদ, তখন খানিকটা বোকামো ও নির্বুদ্ধিতা ভর করল আমার মাথায়। আমি দু-তিনবার করে হ্যারোডস্ শপিংমলে প্রবেশ করলাম ও বের হলাম। শুধু মোহাম্মদ আল ফায়াদের মুখ থেকে 'স্যার প্লিজ ভিতরে আসুন...' কথাগুলো বার বার শোনার জন্য। ঘোরাঘুরি শেষ করে অপরাহ্নে পাতাল রেলে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম ট্রেনে বসে- নিজের বোকামির কথা চিন্তা করে নিজেই নিজের কাছে অপ্রস্তুত ও হেয়প্রতিপন্ন হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, উত্তপ্ত রোদেলা দুপুরে মোহাম্মদ আল ফায়াদ নিজে দারোয়ান সেজে যতই 'স্যার' 'স্যার' বলুক; বেলা শেষে কিন্তু তিনি হাজার কোটি টাকার মালিক। আর আমি সেই কপর্দকশূন্য এক আইনের ছাত্র।
তিন. সম্ভবত ঘটনাটি ১৯১৫ সালের জানুয়ারির একেবারে প্রথম দিকের। ইন্ডিয়ান কংগ্রেস পার্টির সভা হচ্ছে কলকাতায়। কংগ্রেসের মধ্যমণি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে একটি টেবিল পেতে চেয়ারে বসে দলীয় নানা কাজের ফর্দ তৈরিতে ব্যস্ত। এমন সময় জনৈক ব্যারিস্টার সন্তর্পণে একটি ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিলেন গোখলের হাতে এবং বললেন- স্যার, আমি এসেছি গুজরাটের রাজকট থেকে। মাথাটি না তুলেই ভিজিটিং কার্ডটিতে চোখ বুলালেন গোখলে। কার্ডটিতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে- 'মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, ব্যারিস্টার-এট-ল, ইনার টেম্পল'। গোখলে কার্ডটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এক গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন গান্ধীকে। গান্ধী ও গোখলে দুজন দুজনার পরম বন্ধু। ১৯১২ সালে গোখলে সাউথ আফ্রিকা ঘুরে এসেছেন গান্ধীর আমন্ত্রণে। তার অহিংস আন্দোলনের দারুণ ভক্ত তিনি। অন্যদিকে গান্ধী তার শুভানুধ্যায়ী, পরামর্শক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করেন গোখলেকে। গান্ধী গুজরাটের রাজকট থেকে ছুটে এসেছেন কলকাতায়; নিজেকে কংগ্রেসের কোনো কাজে লাগে কি-না সেই বিবেচনায়। প্রথমেই গান্ধী লক্ষ্য করলেন যে, সভাটিতে এত মানুষের সমাগম অথচ পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটারি সুবিধার বেহাল অবস্থা। অন্যদিকে কলকাতায় তখন মেথর সম্প্রদায়ের ধর্মঘটের কারণে শৌচাগারগুলো উপচে পড়ছিল মানুষের মল ও বিষ্ঠায়। গান্ধী লক্ষ্য করলেন- যে ভবনটিতে পার্টির ক্যাম্প করা হয়েছে সেই ভবনটির বারান্দায় পর্যন্ত কেউ কেউ পুরীষ ত্যাগ করে রেখেছে তার দুর্গন্ধে যেখানে টেকাই দায়। কংগ্রেসের দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বললেন- 'ভাইসব ভারত মুক্তির আগে আসুন আমরা এই দুর্গন্ধময় নোংরা বর্জ্য থেকে মুক্ত হই।' রেকর্ডপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, এই কাজে সেদিন তাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি, তাকে একাই করতে হয়েছিল সব কাজ। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রথম আলো উপন্যাসে লিখেছিলেন ত্রিপুরা মহারাজের অবৈধ পুত্র ভরতসিং নোংরা পরিষ্কারের এই কাজে গান্ধীকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনা থেকে হয়তো মনে হতে পারে, জীবনে এই প্রথম হয়তো তিনি সবাইকে অবাক করে দেওয়ার জন্য এই কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। আসলে কিন্তু তা নয়, তিনি যখন মাত্র ১২ বছরের কিশোর, তার রাজকোটের বাড়িতে যে মহিলাটি তাদের শৌচাগার পরিষ্কার করত তার নাম ছিল উকা, গান্ধীর মা গান্ধীকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলতেন- গান্ধী যদি উকাকে স্পর্শ করে তবে তাকে সমস্ত রাত ঘরের বাইরে কাটাতে হবে এবং তাকে স্নান সেরে তবেই ঘরে প্রবেশ করতে হবে। উত্তরে কিশোর গান্ধী তার মা-কে বলেছিল- রামায়ণে, গুহাকা নামে এক চণ্ডালকে রাম যখন আলিঙ্গন করেছিল, তাতে রামের জাত গিয়েছিল কি না? কিশোর গান্ধীর মুখে এসব কথা শুনে গান্ধীর মা পুতলীবাই আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়ও তার নিজ ঘরের নোংরা পুরীষ তিনি নিজেই পরিষ্কার করতেন এবং ভার্যা কস্তুরবাকে তিনি উৎসাহ জোগাতেন এই কাজ করতে। কিন্তু তার স্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করলে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ধাঙড়গিরি কিংবা ঝাড়ুদার হিসেবে গান্ধীর বেশ নাম ডাক ছিল, সেখানে তার বন্ধু-বান্ধবরা প্রায়ই তাকে দুষ্টামি করে মেথর গান্ধী বলে ডাকতেন। সে দেশে প্রথমবার যখন তাকে গারদে পোরা হলো, তিনি স্বেচ্ছায় সেখানকার শৌচাগারের বর্জ্য পরিষ্কার করতে চাইলেন। এর পর থেকে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে দিয়েই সব সময় জেলের মলমূত্র পরিষ্কার করাতেন। ভারতেও তিনি কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য সভা-সমিতিতে স্থাপিত অস্থায়ী শৌচাগারগুলোর নোংরা বর্জ্য নিজে উদ্যোগী হয়ে পরিষ্কার করতেন।
চার. কয়েক দিন আগে জাতীয় সংসদে আমাদের এক মাননীয় মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান নেতা বিএনপির এক জ্যেষ্ঠ নেতাকে যথেচ্ছা গালমন্দ করলেন। আমি মনে করি, নিন্দে-মন্দ করার অধিকার তার যথেষ্ট রয়েছে। পৃথিবীতে কেউই আলোচনা ও সমালোচনার ঊধের্্ব নয়, কিন্তু তার কিছু সীমা কিংবা ভাষা-পরিভাষা থাকে। প্রায় পঞ্চাশ বর্ষীয় একজন মানুষকে এভাবে তুইতোকারি করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখা দরকার। ওই মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, বিএনপির ওই সিনিয়র নেতার বাবা তাকে স্যার স্যার বলে মুখে ফেনা তুলতেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাসে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যই নির্ধারিত হয় তার কর্ম ও দর্শন দ্বারা। জীবনে চলার পথে গান্ধী, আব্রাহাম লিংকন, ম্যান্ডেলার মতো নেতারা হরহামেশাই হয়তো অনেককে স্যার বলে সম্বোধন করেছেন। কেউ কেউ মানুষের মলমূত্রও পরিষ্কার করেছেন। এতে করে তারা কেউ কারও কাছে ছোট হয়ে যাননি। বরং তাদের এই আত্দত্যাগ ও কর্ম তাদেরকে ইতিহাসে অনেক উঁচুতে স্থান করে দিয়েছে। আমাদের জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য যে মানুষগুলো একটি দেশকে স্বাধীন করার সঙ্গে যুক্ত। যারা তাদের কর্ম, দর্শন ও চিন্তাশক্তি দ্বারা অনায়াসে ইতিহাসে একটি বড় জায়গা করে নেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন তারা প্রায়ই নিজেদের মর্যাদার প্রতি সুবিচার করতে পারেন না। শত কিংবা অর্ধশত বছর পর অসংলগ্ন রাজনীতির উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে যখন আর্কাইভ থেকে সেসব ভাষণ-উক্তি বার বার বাজিয়ে শোনানো হবে তখন তাদের নাতি-পুতিরা কেউ হয়তো দুঃখ কিংবা আক্ষেপ করে বলবেন- 'হায়রে আমাদের পিতামহ কিংবা প্রপিতামহরা যদি কিছু ভালো কথা ও কাজ করে যেতেন তাহলে আজ আমরা সেগুলোর ফল ভোগ করতে পারতাম।' শুধু প্রবীণদের কথাই বা কেন বলি? বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কিংবা কোর্ট প্রাঙ্গণে অপেক্ষাকৃত কিছু তরুণ নেতার আচরণ দেখে মনে হয়, যেন তারা ইতিমধ্যে মন্ত্রী-মিনিস্টার কিংবা দলের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের কিছু একটা হয়ে গেছেন। তাদের এই বাগাড়ম্বর ও আস্ফালন দেখে অদৃষ্টের দেবতা অন্তঃরীক্ষে বসে নিশ্চয়ই অট্টহাসি হেসে বলেন, "ওরে মূর্খ, ইতিহাস খুলে দেখে নে, ইতিহাস কীভাবে রচিত হয়। একদল যখন আত্দঅহমিকা ও নিজের অসাড় শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর কাজে ব্যস্ত আরেক দল তখন নিভৃতে ও সবার অলক্ষ্যে ইতিহাস তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। জীবনানন্দ দাশ, কমলকুমার মজুমদার, শহীদুল জহির প্রমুখ এদের মধ্য থেকে কিছু প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে আরেক দল আছেন, যারা ভিন্নরকম ও অতি সাধারণ জীবনযাপন করে এবং জনমানুষের জন্য ব্যতিক্রমী কিছু কর্ম ও দর্শন প্রদান করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রচিত করে যান এক সুমহান ইতিহাস। আব্রাহাম লিংকন, মহাত্দা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ। তাদের মধ্যে কিছু প্রজ্বল্যমান উদাহরণ।
লেখক : গল্পকার ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী।
ই-মেইল : [email protected]