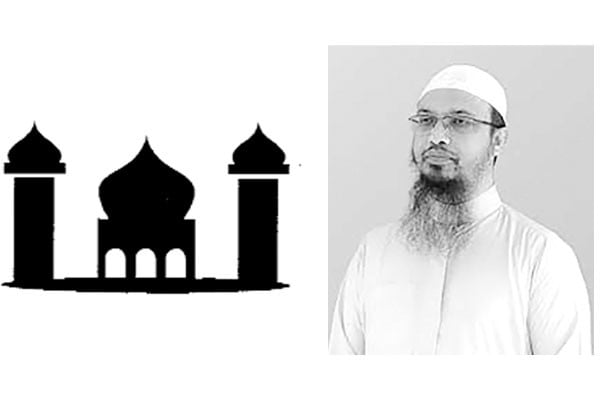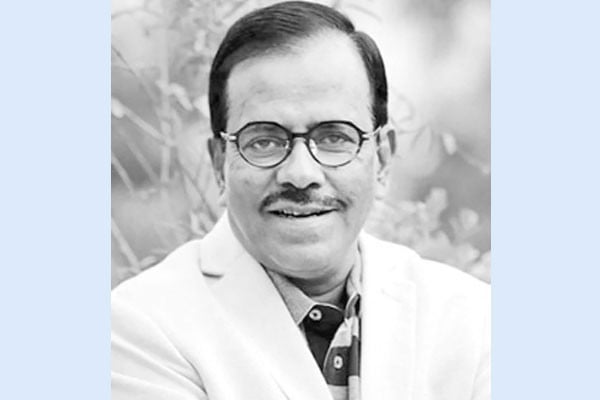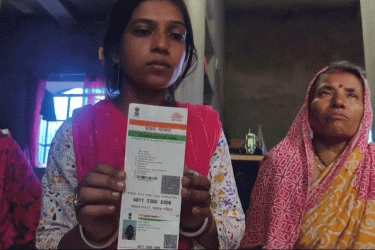১৪ মে বিকালে আমার বাবা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান চিরদিনের জন্য চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না তাঁর অনেক দিন ধরেই। কিন্তু সেদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না একেবারেই। এক বাড়িতেই ছিলাম বলে কিছুদিন থেকেই খেয়াল করছিলাম তাঁর শরীর ভেঙে আসছে ধীরে ধীরে। কষ্ট হচ্ছিল চলাফেরায়ও। তাঁর মৃত্যুর দুই মাস আগে যখন তাঁকে দেখছি বেশ কষ্ট পাচ্ছেন, তখন একবার জিজ্ঞেসও করলাম, চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি কী ভাবছেন। খুবই স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিলেন- তেমন কিছুই ভাবছি না। এই না ভাবাটাই হয়তো কাল হলো শেষ পর্যন্ত। এ বছরে দুবার ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে- ফেব্রুয়ারি আর এপ্রিলের শুরুতে। এপ্রিলের শেষে, শেষবারের মতো বাসা থেকে গেলেন হাসপাতালে। দুই হাসপাতালে ১৭ দিন চিকিৎসা শেষে হার মানলেন ওইদিন বিকাল ৪টা ৫৫ মিনিটে। তাঁর সৌভাগ্য কিনা জানি না, তবে মৃত্যুর ক্ষণটিতে আমার মা আর আমরা তিন ভাইবোন উপস্থিত ছিলাম সবাই।
আমার মা এখনো আফসোস করে চলেছেন- তিনি যদি একটু বিশ্রাম নিতেন, শরীরের প্রতি যত্নশীল হতেন তাহলে হয়তো আরও দীর্ঘায়ু লাভ করতেন। কিন্তু আমি এই বলে সান্ত¡না খুঁজছি যে আব্বা যেভাবে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন- কর্মের মধ্যে, ব্যস্ততার মাঝে -সেভাবেই প্রায় তাঁর পূর্ণ জীবন পার করে যেতে পেরেছেন। কারও প্রতি নির্ভরতা তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না, শেষ পর্যন্ত তারও বেশি প্রয়োজন হয়নি।
হাসপাতালে থাকাকালে শেষ দিকে মাঝেমধ্যে তাঁর স্মৃতিভ্রম হচ্ছিল। নতুন হাসপাতালে, অজানা-অচেনা পরিবেশে একদিন জানতে চাইলেন তিনি এই হাসপাতালে কেন? প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে জানার পর একটু নিশ্চুপ হলেন। সক্রিয় অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাক্সক্ষী, মন্ত্রী-সচিব সবাই যখন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের কথা বলতেন তিনি সব সময়ই মানা করতেন। মারা যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগে শরীর যখন বেশি খারাপ, নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ; তখন জীবনে প্রথমবারের মতো আমি দায়িত্ব নিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছিলাম এবং প্রায় সবার বকা খেয়ে, আব্বা পছন্দ করবেন না জানা সত্ত্বেও কিছুটা অসহায় হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের সিদ্ধান্ত নিই। এর আগে কখনই তিনি আমাদের কাউকেই তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে বা অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেননি, এমনকি তাঁকে নিয়ে কেউ বিচলিত হোক- তাও চাননি।
অথচ বিচলিত ছিলাম আমরা সবাই। কর্মমুখর অবস্থায় যেমন শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, অসুস্থতায় তেমনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সবাই, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও। তাই তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। তাঁর কণ্ঠে আমি অভিভাবক হারানোর বেদনা খুঁজে পাই- তিনি সেটা উল্লেখও করলেন। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলি যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আব্বাকে যেভাবে সম্মান জানিয়েছেন- সবার সামনে চাদর ঠিক করে দিয়েছেন, আব্বাকে বসিয়ে রেখে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলেছেন- তার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। উত্তরে তিনি বললেন, ‘করব না? উনি তো আমার স্যার!’ আমার কণ্ঠ পুরোপুরি রুদ্ধ হলো।
এই অভিভাবক হারানো আর বাবা হারানোর কষ্ট এতজন আমাদের জানিয়েছেন যে আমরা অবাক হয়েছি। অন্য আরেক জায়গায় যখন আব্বাকে নিয়ে লিখেছি, তখন আমি আমাদের তিন ভাইবোনের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছি যে আব্বাকে আমরা বাবা হিসেবে খুব কমই পেয়েছি। অথচ এই মানুষটাই এত মানুষের বাবা আর অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। কিছু মানুষ এতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে কখনো কখনো তাদের সান্ত¡না দেওয়া আমার জন্যও কঠিন হয়ে উঠেছিল। এখানেই বোধহয় তাঁর জীবনের সার্থকতা।
আব্বা মাত্র ২৫ বছর বয়সে পিএইচডি করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ বা সর্বকনিষ্ঠদের একজন হিসেবে। সেটাও জেনেছি তাঁর মৃত্যুর পরে। পন্ডিত মানুষ ছিলেন, কিন্তু কখনো পা-িত্য দেখাতেন না। গুণী মানুষদের নিয়ে যখন লিখতেন সেখানেও ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো, সম্পর্কগুলো বেশি সামনে আসত না। আমি বলতাম, আমার তো মনে হয় মানুষ বেশি জানতে চায় তুমি উনাকে কত গভীরভাবে, নিবিড়ভাবে চিনতে, জানতে। আব্বা চাইতেন সে মানুষ কর্মে কত বড় তা বোঝাতে। অবশেষে হয়তো কিছুটা আমার কথা মাথায় রেখেই গত বছর শেখ হাসিনার জন্মদিনের একটা লেখায় ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতি লিখলেন, তাও সামান্য। যেখানে তাঁকে উল্লেখ করলেন ‘আমাদের ছাত্রী শেখ হাসিনা’ বলে। তাও ‘আমার সরাসরি ছাত্রী’ বা ‘শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী’ হলো না!
আব্বার মতো এত সুন্দর করে শাল গায়ে দিতে আমি খুব কম মানুষকেই দেখেছি। এ বছরের বাংলা একাডেমির বইমেলায় যাওয়ার পথে খেয়াল করলাম গায়ে শালের বদলে সোয়েটার। আব্বাকে বললাম, গতবার তো শাল নিয়েছিলে। মনে আছে তোমার শালটা প্রধানমন্ত্রী ঠিক করে দিলেন, ফেসবুকে অনেক আলোচনা হলো। আব্বা বললেন, সেই ভেবেই এবার আর পরলাম না। আসলে প্রচার চাইতেন না একদমই।
আব্বার সাক্ষাৎকার নেবে নিউজ টোয়েন্টিফোর। আগের দিন অসহায় হয়ে আমাকে ফোন করলেন সামিয়া (রহমান) আপা। বললেন স্যারের তো কাল সাক্ষাৎকার নেব, কিন্তু তাঁর জীবনী পড়ে তো আপনাদের ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানতে পারছি না! আমি বললাম, এই তো মজা! আমাদের কোথাও খুঁজে পাবেন না! তিনি বললেন, দাঁড়ান, কাল আমি স্যারের ব্যক্তিগত-পারিবারিক জীবনটা বের করার চেষ্টা করব! তাঁর পণ পুরোটা না হলেও বেশ কিছুটা সফলও হয়েছিল।
শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আব্বার একটা লেখা বেশ সাড়া ফেলল। আমি নানা কারণে, বিশেষ করে কিছু জায়গায় ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে এ আশঙ্কা করছিলাম। হলোও তাই। সরকারি দলের এক নেতার সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে দেখা হলে তিনি বেশ কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন আমার কাছে। বাসায় ফিরে আব্বাকে জানালাম। আব্বা বললেন, ওর ভালো না লাগলে কী করা যাবে! যেটা ঠিক মনে হয়েছে লিখেছি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল অপি করিম এক অনুষ্ঠানে আব্বাকে প্রশ্ন করেছিলেন- আমাদের এত রাজনৈতিক বিভক্তির মাঝেও সব আমলেই আপনাকে সম্মানিত করা হয়েছে, এটা কীভাবে সম্ভব হলো? আব্বা বললেন, সেটা আমার সৌভাগ্য। কেননা এরশাদ সরকার যখন আমাকে একুশে পদক দেয়, আমি তখন সক্রিয়ভাবে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে দলীয় বিভাজন থাকলেও তারা যে এক হয়ে আমাকে প্রফেসর ইমেরিটাস বানালেন সেটাও আমার জন্য একটা বড় পাওয়া। আব্বা মারা যাওয়ার পর ভিন্ন মত-পথের মানুষের শোকবার্তা ছিল ব্যতিক্রমী ও উল্লেখযোগ্য।
আমাদের ভাইবোনদের বেড়ে ওঠাও বেশ ব্যতিক্রমভাবেই। পড়াশোনা করতে বা প্রবাসী হতে আমরা বিদেশ যেতে চেয়েছি, আপত্তি করেননি। ফিরে আসতে চেয়েছি, নিষেধ করেননি। নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করতে চেয়েছি, মেনে নিয়েছেন। পড়াশোনা করতে চেয়েছি বা চাইনি-সব আমাদের ইচ্ছাতেই! ভিন্ন পরামর্শ যে কখনো দেননি, তা নয়। তবে বেশির ভাগই দিয়েছেন পড়াশোনা-ভর্তি এসব নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে। কখনো তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছি, কখনো করিনি। কিন্তু বাধা দেননি কখনই। সব মিলিয়ে এত স্বাধীনভাবে মানুষ হয়েছি। সততা-সত্যবাদিতা-ভালো মানুষ হওয়ার পাশাপাশি শিখিয়েছিলেন উদার হতেও। চিন্তায়, শব্দের ব্যবহারেও তা প্রকাশ পেত। বলতেন বন্ধু বলতে, বান্ধবী নয়। এ নিয়ে নানা বিড়ম্বনা হতো। গল্পের মাঝে যখন কেউ বুঝত এটা মেয়েবন্ধু তখন ভাবত আমি হয়তো কৌশলে বিষয়টা গোপন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। বন্ধুদের মুখে বিজয়ের হাসি আমার মাঝে বেশ একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত!
ব্যতিক্রম আরও ছিল। আমি বোধহয় তখন মাত্র গাড়ি চালানো শিখছি। একদিন আব্বাসহ আমরা সবাই রাত করে বাড়ি ফিরছি। আমার কী কথায় আব্বা হঠাৎ বললেন, তুমি চালাও। আমি বললাম, না, পারব না। আব্বা বললেন, না, পারবে! কি অদ্ভুত কথোপকথন! ছেলে বলছে গাড়ি চালাবে না, আর বাবা বলছে চালাতে!
এ রকম অদ্ভুত ঘটনা আরও একবার হলো। আমি আম্মাকে নিয়ে বাইরে গেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগল গন্ডগোল। রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আমি আব্বাকে বললাম, গাড়ি নিয়ে বাসায় ফেরা বিপজ্জনক হবে। আব্বা বললেন, কিছু হবে না। এ যাত্রায় আমি আর তাঁর এই ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাবে রাজি হলাম না। অবশেষে আব্বা কষ্ট করে কোনোমতে শাহবাগ এলেন। সেখানে হাতবদল করে তিনি গাড়ি চালিয়ে বাসার উদ্দেশে রওনা দিলেন। যা ভেবেছিলাম তাই। পথে একদল ছাত্র উত্তেজিত অবস্থায় রোকেয়া হলের সামনে গাড়ি থামাল। আব্বাকে দেখে সালাম দিয়ে পথ ছেড়ে দিল। এ যাত্রায় রক্ষা হলো। আমি নিজের বুদ্ধির তারিফ করার একটা সুযোগ পেলাম!
মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন আব্বা। আমার এক খালু গল্প বলেন, অনেক আগে তাঁর বিয়ের পর গিয়েছিলেন আমাদের চট্টগ্রামের বাড়িতে। রান্নাঘরে কোনো জিনিস ভাঙার আওয়াজ পেয়ে সবাই যখন কী ভাঙল এ নিয়ে চিন্তিত, তখন আব্বা নাকি রান্নাঘরে থাকা মানুষটিকে প্রশ্ন করেছিলেন ‘তুই ঠিক আছিস?’
ব্যতিক্রম ছিলেন আরও অনেক ব্যাপারেই। আশির দশকে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যের মান নিয়ে যখন অনেকের প্রশ্ন, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের মাঝে; তাঁর উপন্যাসকে ‘অপন্যাস’ বলে সমালোচনা করা হতো; তখন সাংবাদিকদের হতাশ করে দিয়ে আব্বা বলতেন- মান নিয়ে আলোচনা যে কোনো লেখকের লেখা নিয়েই হতে পারে। কিন্তু আমি দেখেছি ইংরেজি মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা শুধু তাঁর বই পড়ার জন্য বাংলা শিখেছে, বাংলা বই হাতে নিয়েছে। একজন লেখক যদি সমাজের একটা বড় অংশকে, একটা প্রজন্মকে এভাবে একটা ভাষার প্রতি আগ্রহী করতে পারে, বই পড়াতে পারে, তবে তাঁকে কৃতিত্ব ও স্বীকৃতি দিতে হবে।
আব্বার সৌজন্যবোধও ছিল প্রবল। আমার অনুপস্থিতিতে, বাসার ফোনে বন্ধুরা ফোন করলে আর আব্বা ধরলে পরে নিশ্চিত হতে চাইতেন যে আমি তাদের সঙ্গে আবার কথা বলেছি কিনা! আমি ফিরতি ফোন না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই! বলতেন তুমি না করলে ভাববে আমি তোমাকে ফোনের কথা বলিনি। সভা-সমিতিতে কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলে, ফিরে এসে আমাদের বলতেন এবং আব্বা চাইতেন আমরা যেন তাদের ফোন করে কৃতজ্ঞতা জানাই।
খাদ্যাভ্যাসেও ছিল ব্যতিক্রম। পরিমাণে খেতেন খুবই কম। তবে মানের ব্যাপারে সেটা বলার সুযোগ নেই। মুখরোচক খাবারের প্রতি ছিল দুর্বলতা। স্বাস্থ্যকর খাবার খেতেন খুবই সামান্য। মাছ তেমন পছন্দ করতেন না। বিদেশে গেলে খুবই সমস্যা হতো। প্রবাসী বাঙালিরা খাতির করে, খুব আগ্রহ নিয়ে নানা রকম মাছ রেঁধে আব্বার জন্য অপেক্ষা করতেন। কত দিন মাছ-ভাত ছাড়া আব্বা আছেন তা ভেবে তাঁরা বেশ আকুল থাকতেন। অথচ আব্বা মাছ না খেতে পারলেই বাঁচেন, বরং স্টেক পেলে মহানন্দে খাওয়াটা উপভোগ করতেন!
একবার আমার একদল বন্ধু-সহকর্মী দেশ-সমাজের আলোচনার এক পর্যায়ে বলল, আচ্ছা স্যার চলে গেলে তাঁর জায়গায় আমরা কাকে দেখব, কেউ তো নেই! অন্যরাও সমর্থন দিল। আমি সাহস করে দুই-একটা নাম বললাম। শুরুতেই বিপত্তি। বলল তুমি প্রথমে যার নাম বললে, তাঁর পোশাক দেখ? আমি বললাম, এ রকম ছিদ্রান্বেষী হলে তো কাউকেই পাওয়া যাবে না। সে বলল, আমি তো সেটাই বললাম! চলনে-বলনে-কথনে, পোশাকে-আচারে-আচরণে সেই মানুষ তো নেই! আমি আলোচনায় ইতি টানি!
আব্বার সঙ্গে খুব বেশি অনুষ্ঠানে না গেলেও দেশে-বিদেশে পুরস্কার নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছি। ২০১৭ সালে আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। এত গুণী-জ্ঞানী মানুষের মাঝে আব্বাকে দেখে, আব্বার প্রতি তাদের উষ্ণ ভালোবাসা দেখে খুব ভালো লেগেছিল। দেশের বাইরের সবচেয়ে বড় পুরস্কার ছিল ভারত সরকারের দেওয়া পদ্মভূষণ। ২০১৪ সালে মাত্র তিনজন বিদেশি প্রাপকের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন! সে বছরের ২৫ জানুয়ারি, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। আব্বা তখন ছিলেন মুহিত চাচার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে, তাঁর বাসায়। ভারত থেকে তাঁর কোনো এক স্বজন তাঁকে খবরটা দেন প্রথমে। আব্বা অবাক হয়ে আমাকে ফোন করে বললেন খবরের সত্যতা যাচাই করতে। নেহাতই গুজব মনে করা সত্ত্বেও আমি ইন্টারনেট ঘাঁটতে লাগলাম। কিছু না পেয়ে আমরা দুজনই একসময় নিশ্চিত হলাম খবরটা সঠিক নয়। কিন্তু ভারত থেকে তাঁর বন্ধুরা একের পর এক ফোন করতে থাকলে আমরা আবারও সন্দেহ প্রকাশ করি। বাসায় ফিরলে, বেশ রাতে আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবরের সত্যতা জানতে পারি।
প্রায় দুই মাস পর মার্চের শেষে আব্বা পদ্মভূষণ গ্রহণ করতে দিল্লি যান। নানা কারণে আসা-যাওয়া একসঙ্গে করতে না পারলেও অনুষ্ঠানে ঠিকই উপস্থিত ছিলাম। এত বড় পুরস্কার, এত বড় অনুষ্ঠান, এত বড় আয়োজন- কিন্তু আব্বার মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই! পুরস্কার গ্রহণের সকালে হোটেলের রুম থেকে বের হতেই যখন দেখা, তাঁর সাদামাটা পাঞ্জাবি দেখে আমার খুব রাগ হলো। আম্মাকে বললাম এর চেয়ে খারাপ পাঞ্জাবি কি আর পাওয়া গেল না! আম্মা হাসলেন। লিফট থেকে নেমে রিসিপশনে বসে যখন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি, পায়জামার দিকে তাকিয়ে দেখি লন্ড্রির ট্যাগ ঝুলছে! রিসিপশন থেকে কাঁচি খুঁজে সেটা কাটার ব্যবস্থা করলাম।
রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে আব্বা আর আম্মা- আমি আলাদা হয়ে গেলাম। শুরু হলো সেই জমকালো অনুষ্ঠান। আব্বা প্রণব মুখার্জির হাত থেকে পুরস্কার নিলেন, সেই নিরাবেগভাবে। অনুষ্ঠানে ড্রেসকোড থাকায় আমাকে পরতে হয়েছিল স্যুট। অনুষ্ঠান শেষে যখন রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ছবি তুললাম তা দেখে বিভ্রান্ত হতে হয়- কে পুরস্কার পেল আর কে সঙ্গী! পরে অনুষ্ঠানের আরও কিছু ছবি দেখলাম। নির্লিপ্ত আব্বার সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিসহ সর্বোচ্চ সারির নেতারা। শিক্ষা ও সাহিত্যের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হলেও আব্বার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছিল ‘গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে তাঁর অবদান ও সংগ্রাম একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।’
আব্বার আনিসুজ্জামান হয়ে ওঠার শুরু খুব অল্প বয়সে। বায়ান্ন সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে লিখেছিলেন, ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন- কী ও কেন?’। এটা ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে লেখা প্রথম পুস্তিকা। তবে তা দেখে দিয়েছিলেন অলি আহাদ। কিন্তু এ দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনে শামিল হওয়া আব্বার সবচেয়ে বড় অবদান বাহাত্তরে, এ দেশের সংবিধান রচনায়। আর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। আব্বার মৃত্যুর পর আমার লেখা আরেকটা স্ট্যাটাস দিয়ে শেষ করছি। পরে মনে হয়েছে তাঁর পুরো জীবনটা হয়তো তুলে ধরা গেছে এই মন্তব্যে-
‘পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও দুঃখ প্রকাশ :
এত মানুষের ভালোবাসা-সাহায্য-সহযোগিতা-সহমর্মিতা পেয়ে আমরা অভিভূত।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনাদের পোস্ট, কমেন্ট, গদ্য-কবিতা-আঁকা দেখে আমরা মুগ্ধ। জাতীয় দৈনিকে আব্বাকে নিয়ে লেখাগুলো পড়ে আমরা আপ্লুত। কিছু শিরোনাম আমাদের কাঁদিয়েছে, কিছু সম্পাদকীয় আমাদের সামনে আব্বাকে নতুন করে চিনিয়েছে। আমরা কৃতার্থ।
সাধারণ মিডিয়ার সাংবাদিকদের কথা আগেই বলেছি। কবরস্থানে ক্যামেরা মাটিতে নামিয়ে, হাতে মাটি নিয়ে যখন তারা কবরে দিয়েছেন তখন তাদের আর সাংবাদিক বলে মনে হয়নি; মনে হয়েছে অতি আপনজন।
টিভি চ্যানেলের টকশো, ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম প্রচার করায় আমরা কৃতজ্ঞ।
ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আমাদের ফোন করেছেন কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে, কারও সঙ্গে হয়নি। যাদের ফোন ধরতে পারিনি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক পরিচিত ও অপরিচিত মানুষ আব্বার চিকিৎসার সাহায্যে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাতে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। সব ধর্মের মানুষ একযোগে যেভাবে দোয়া-প্রার্থনা করেছেন তা আমাদের জন্য অনেক পাওয়া। আব্বার মৃত্যুর পরে করোনার কারণে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে, সুষ্ঠুভাবে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করায় আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাছে ঋণী। একটা পর্যায়ে গার্ড অব অনার প্রদান করা নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে আমরা আশাহত হই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অবশেষে গার্ড অব অনার প্রদান করা সম্ভব হয়। তাঁর প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।
যে মানুষটা এ দেশের ভাষার সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন, দেশটা স্বাধীন করায় ভূমিকা রেখেছিলেন- সেই মানুষটা পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে বিদায় না পেলে একটা কষ্ট থেকে যেত। যে হাত দিয়ে দেশের সংবিধানের অক্ষরগুলো লেখা হয়েছিল সেই হাত জাতীয় পতাকার স্পর্শ না পেলে সারা জীবন একটা দুঃখ থেকে যেত আমাদের।
আমরা ভাগ্যবান সেই দুর্ভাগ্য আমাদের স্পর্শ করেনি।
অনেকেই আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন- আড়ম্বরপূর্ণ বিদায় দিতে না পেরে। সত্যি কথা বলতে, আব্বা আমাদের নানাভাবে গত চার বছরে বুঝিয়েছিলেন তিনি এত আড়ম্বরপূর্ণ প্রস্থান চান না। এমনকি অস্থায়ী কবরে তাঁকে দাফনের অনুরোধ করেছিলেন। আবেগের কারণে আমরা সে অনুরোধ রাখতে পারিনি, তবে প্রকৃতির খেয়ালে তাঁর বিদায় হলো খুবই অনাড়ম্বরভাবে।
আব্বাকে শেষ বিদায় দিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে যখন ফিরে আসছি তখন মনে হলো তাঁকে সঙ্গে নিয়েই যেন বাড়ি যাচ্ছি।’
লেখক : জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ছেলে।