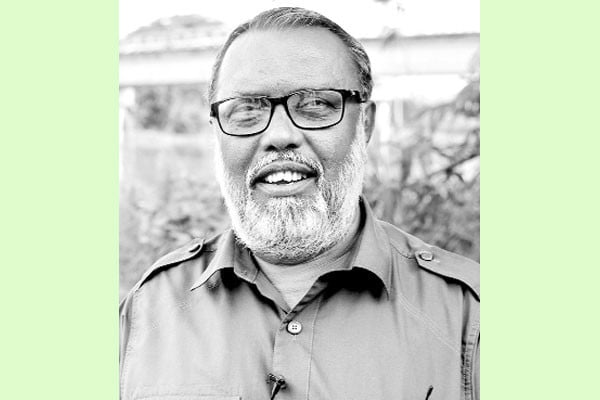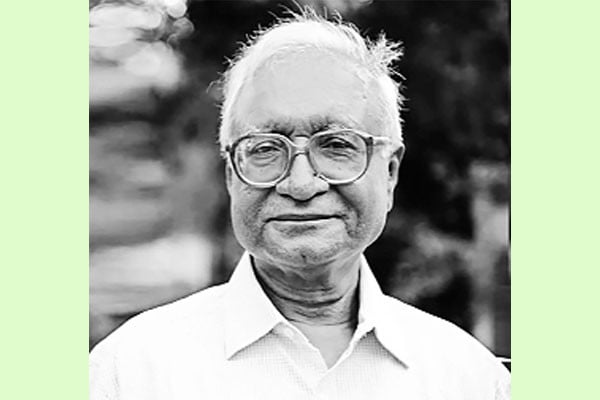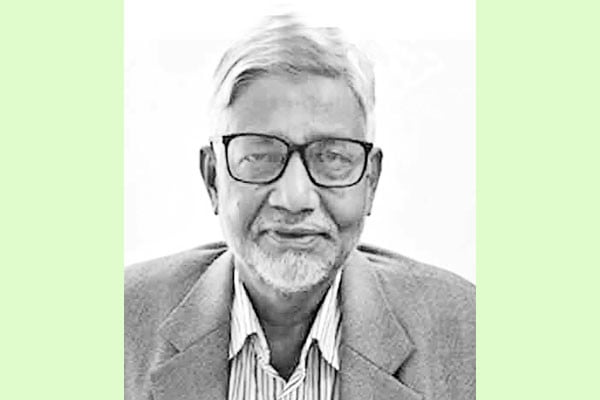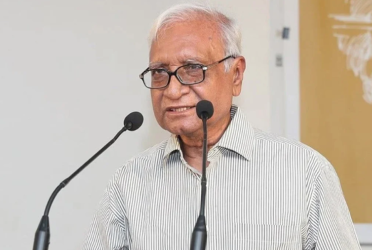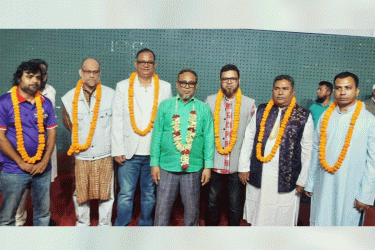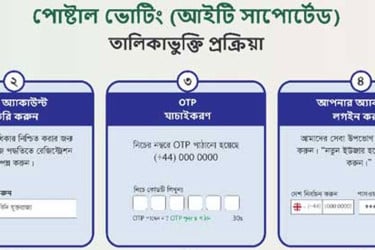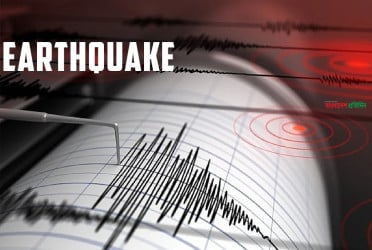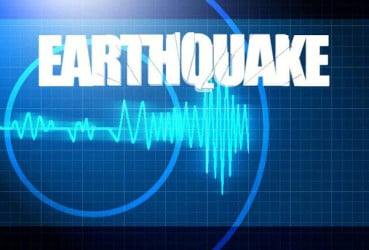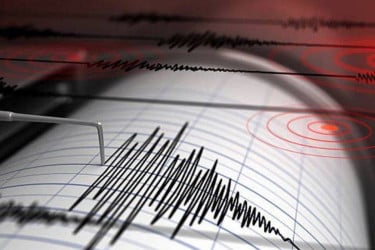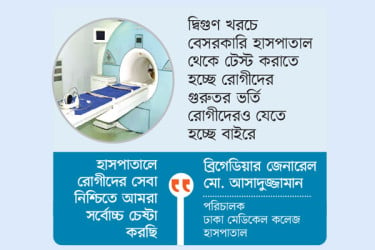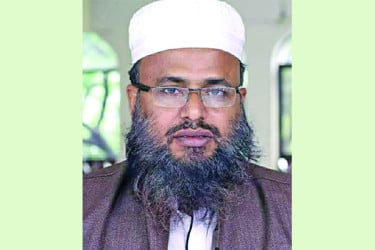দ্রুত শহরমুখী হচ্ছে বিশ্ব। গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যেখানে জনসংখ্যার বেশির ভাগই বাস করত গ্রামাঞ্চলে, সেখানে ২০২৪ সালের হিসাব বলছে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এখন নগরে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা পূর্বাভাস জানায়, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্তত ৬৮ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করবে। দক্ষিণ এশিয়াসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই নগরায়ণের গতি আরও দ্রুত। ফলে শহরের মাটিতে চাপ বাড়ছে, বাড়ছে আবাসন ও অবকাঠামোর চাহিদা, আর কমছে খোলা জায়গা ও সবুজ পরিবেশ।
এই জনবহুল নগরজীবনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা। কারণ গ্রামের কৃষিজমি কমে যাচ্ছে, জমিতে চাপ বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনের, আর শহরের মানুষের খাবারের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে দূরদূরান্তের গ্রামীণ অঞ্চল বা বিদেশি উৎসের ওপর। শহরে তাপমাত্রা বাড়ছে; বাড়ছে দূষণ, ট্রাফিক ও খাদ্য পরিবহন খরচ।
এই প্রেক্ষাপটে কৃষিবিশ্বের দৃষ্টি এখন শহরের দিকে। প্রশ্ন হচ্ছে, শহর কি নিজেই খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পৃথিবীর নানা দেশে শুরু হয়েছে নতুন এক বিপ্লব Urban Agriculture বা নগরকৃষি।
নগরকৃষির ধারণাটি খুব সহজ। শহরের ছাদ, বারান্দা, স্কুলের মাঠ, কমিউনিটি স্পেস, পরিত্যক্ত প্লট বা অফিস ভবনের শীর্ষতলায় ছোটবড় স্কেলে সবজি, ফল, ফুল বা ঔষধি উদ্ভিদের চাষ। শুধু খাদ্য উৎপাদনই নয়, এটি পরিবেশ শীতল করে, বাতাসের মান উন্নত করে, পানি সংরক্ষণে সাহায্য করে এবং শিশু থেকে তরুণদের কৃষিশিক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। বিশ্বে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, নগরকৃষি হয়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক খাত। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, শহরে উৎপাদিত প্রতি কেজি সবজির কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৫০ শতাংশ কম। কারণ পরিবহন লাগে না। বড় শহরে ছাদকৃষি তাপদ্বীপ প্রভাব ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমাতে পারে। নিয়মিত ছাদকৃষি একটি পরিবারের মাসিক খাদ্য ব্যয়ের ২০-৩০ শতাংশ সাশ্রয় করতে পারে। বিশ্বের উন্নত কৃষিব্যবস্থায় তাই ‘City as a Farm’ ধারণাটি শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।
 বিশ্বের সবচেয়ে স্মার্ট কৃষিপ্রযুক্তির দেশ নেদারল্যান্ডসে নগরকৃষি এখন জাতীয় কৌশলের অংশ। রটারড্যামে রয়েছে ভাসমান দুগ্ধ খামার, যেখানে শহরের ভিতরেই গরুর দুধ উৎপাদন হয়। আবার বিভিন্ন শহরে কমিউনিটি গার্ডেন ও ছাদখামার ব্যাপক জনপ্রিয়। খাদ্যের মাত্র ১০ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম দেশ সিঙ্গাপুর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ২০৩০ সালের মধ্যে তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৩০ শতাংশ শহরেই উৎপাদন করবে। এজন্য চলছে ছাদকৃষি, ভার্টিক্যাল ফার্ম, অ্যাকোয়াপনিক্স ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদনের নানা উদ্যোগ। সিঙ্গাপুরের বহু বহুতল ভবনের ছাদ এখন বাণিজ্যিক ফার্ম। টোকিওর বহু কারখানা ভবনে স্থাপিত হয়েছে অটোমেটেড indoor greens production system, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লিফি গ্রিনস উৎপাদিত হচ্ছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। নিউইয়র্ক, লন্ডন, বার্লিন, প্যারিসসহ বহু নগরেই অফিস ভবনের ছাদে বাণিজ্যিক সবজি উৎপাদনের চর্চা আছে। অনেকে ছাদে মৌমাছিও পালন করছেন। এসব উদ্যোগ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, নগরকে আর আলাদা করে দেখা হচ্ছে না; বরং শহরকে দেখা হচ্ছে উৎপাদনের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে।
বিশ্বের সবচেয়ে স্মার্ট কৃষিপ্রযুক্তির দেশ নেদারল্যান্ডসে নগরকৃষি এখন জাতীয় কৌশলের অংশ। রটারড্যামে রয়েছে ভাসমান দুগ্ধ খামার, যেখানে শহরের ভিতরেই গরুর দুধ উৎপাদন হয়। আবার বিভিন্ন শহরে কমিউনিটি গার্ডেন ও ছাদখামার ব্যাপক জনপ্রিয়। খাদ্যের মাত্র ১০ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম দেশ সিঙ্গাপুর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ২০৩০ সালের মধ্যে তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৩০ শতাংশ শহরেই উৎপাদন করবে। এজন্য চলছে ছাদকৃষি, ভার্টিক্যাল ফার্ম, অ্যাকোয়াপনিক্স ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদনের নানা উদ্যোগ। সিঙ্গাপুরের বহু বহুতল ভবনের ছাদ এখন বাণিজ্যিক ফার্ম। টোকিওর বহু কারখানা ভবনে স্থাপিত হয়েছে অটোমেটেড indoor greens production system, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লিফি গ্রিনস উৎপাদিত হচ্ছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। নিউইয়র্ক, লন্ডন, বার্লিন, প্যারিসসহ বহু নগরেই অফিস ভবনের ছাদে বাণিজ্যিক সবজি উৎপাদনের চর্চা আছে। অনেকে ছাদে মৌমাছিও পালন করছেন। এসব উদ্যোগ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, নগরকে আর আলাদা করে দেখা হচ্ছে না; বরং শহরকে দেখা হচ্ছে উৎপাদনের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে।
বাংলাদেশেও গত এক দশকে ছাদকৃষি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের তথ্য বলছে, দেশে প্রায় ৪ কোটি মানুষ শহরে বাস করে। রাজধানী ঢাকার ৪ লাখ ৫০ হাজার ছাদ এখনো অব্যবহৃত, যা মোট ৪ হাজার ৫০০ হেক্টর জমির সমান। কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য মতে, এই ছাদগুলো ব্যবহার করলে ঢাকার খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে।
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ড্রোন জরিপে দেখা গেছে, শহরের মাত্র ২ শতাংশ ছাদে ছাদকৃষি আছে। অর্থাৎ ৯৮ শতাংশ ছাদ এখনো অনাবিষ্কৃত সম্পদ। শুধু ঢাকাই নয়; চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল সব জায়গায় ছাদকৃষি চর্চা ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি অনেক গ্রামে দোতলা বা তিনতলা বাড়ির ছাদেও মানুষ চাষ করছেন। এটি এখন যেন এক নতুন শহুরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাংলাদেশে ছাদকৃষির প্রচারণায় গণমাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৮০ সাল থেকে ছাদে কাজী পেয়ারার চাষের ক্যাম্পেইন করে আসছি। চ্যানেল আইয়ে ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক’ অনুষ্ঠানে পাঁচ শতাধিক পর্বে ‘ছাদকৃষি’ তুলে ধরেছি। আরও শ তিনেক পর্ব প্রচার করেছি ‘প্রবাসী বাঙালির আঙিনাকৃষি’। এসব অনুষ্ঠান ছাদকৃষি তথা নগরকৃষিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। জনপ্রিয়তা বাড়ায় দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাদকৃষির উপযোগী মাটিবিহীন চাষ, হাইড্রোপনিক্স ও জৈবসার ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় নগর পরিবেশে পুষ্টিকর সবজি উৎপাদন প্রযুক্তিতে গবেষণা করছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ছাদকৃষি শুধু পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তাই নয়, নগর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। ছাদের বাগান ভবনের তাপমাত্রা কমায়, বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে এবং শহরের সামগ্রিক বায়ুদূষণ কিছুটা হলেও কমাতে সাহায্য করে।
নগরকৃষিকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে নতুন একটি অর্থনৈতিক চেইন। ছাদকৃষির সরঞ্জাম : গামলা, গ্রোব্যাগ, জিও ব্যাগ, অর্গানিক সার, কম্পোস্ট, কীটনাশকবিহীন পেস্ট কন্ট্রোল, এসবের বাজার দ্রুত বাড়ছে। তরুণরা স্টার্টআপ করছে হোম গার্ডেনিং কনসালট্যান্সি, ছাদ ডিজাইন, চাষের মনিটরিং অ্যাপ, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু ঢাকায় ছাদকৃষি সঠিকভাবে সম্প্রসারণ করা গেলে অন্তত ১০-১৫ হাজার নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে।
ছাদকৃষির একটি উজ্জ্বল ইতিবাচক দিক হলো, তরুণদের অংশগ্রহণ। স্কুলে মিনি গার্ডেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকো-ক্লাব, স্টার্টআপ উদ্যোগ, সব মিলিয়ে শহরের তরুণরা এখন কৃষিকে দেখছে নতুন এক লাইফস্টাইল, নতুন ক্যারিয়ার পথ হিসেবে। অনেক আর্কিটেক্ট শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের বিল্ডিং প্ল্যানেই ‘রুফ গার্ডেন’ বাধ্যতামূলক করার ডিজাইন প্রস্তাব দিচ্ছেন। তারা বলছেন, শহর আর গ্রাম, কৃষি আর শিল্প; এই বিভাজন ভবিষ্যতে টিকবে না। খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য শহরকে তার নিজের উৎপাদনব্যবস্থা দাঁড় করাতেই হবে।
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, FAO, বাংলাদেশে নগরকৃষি প্রকল্প পরিচালনা করছে। তারা প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, বীজ, চারা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। উদ্দেশ্য শহরের পরিবার, স্কুল, নারীকেন্দ্রিক গ্রুপ ও তরুণদের ছাদকৃষির সঙ্গে যুক্ত করা। এ ছাড়া উন্নয়ন সংস্থা ‘প্রশিকা’, বিভিন্ন এনজিও, সিটি করপোরেশন, সবাই ছাদকৃষি নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কমিউনিটি উদ্যোগ পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছাদকৃষিতে ১০ শতাংশ হোল্ডিং ট্যাক্স রিবেট ঘোষণা করে, যা নগরকৃষির ইতিহাসে বড় মাইলফলক। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছাদকৃষি সহায়তা দিচ্ছে।
এগুলো দেখাচ্ছে নগরকৃষি আর একক কোনো ব্যক্তিগত চর্চা নয়; এটি এখন সরকার-সমর্থিত এক জাতীয় উদ্যোগ।
জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষিকে অনিশ্চিত করে তুলছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, খরা, অতিবৃষ্টি, এসব কারণে গ্রামীণ কৃষি বহু চাপে আছে। গ্রামে উৎপাদন কমে গেলে শহরের খাদ্যব্যবস্থাই বিপদে পড়বে। এই বাস্তবতায় নগরকৃষি হতে পারে স্থানীয় খাদ্যনিরাপত্তার সাপোর্ট সিস্টেম, শিশু-তরুণদের কৃষিশিক্ষার কেন্দ্র, শহরের সবুজায়ন ও কার্বন কমানোর উপায়, নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্র এবং পরিবেশবান্ধব লাইফস্টাইলের একটি বাস্তব পদক্ষেপ।
শহর বড় হচ্ছে, কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের জমি কমছে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজতেই নগরকৃষির উত্থান।
নগরকৃষি একটি আন্দোলন, একটি নতুন ভাবনা, যা শহরকে শুধু কংক্রিটের জঙ্গল নয়, উৎপাদনশীল একটি পরিবেশ হিসেবে দেখতে শেখায়। সঠিক নীতি, জনসচেতনতা, গবেষণা, প্রযুক্তি, শহরবাসীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে নগরকৃষি বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশ ও অর্থনীতির নতুন শক্তি হয়ে উঠতে পারে। এখন প্রয়োজন কেবল ধারাবাহিকতা, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের পথ ধরে এগিয়ে চলা। ভবিষ্যতের শহর হবে বসবাসের জায়গার পাশাপাশি একেকটি বিশাল সবুজ খামার, যেখান থেকে উৎপাদিত হবে নিরাপদ খাদ্য, পরিশুদ্ধ বাতাস এবং টেকসই আগামী।
লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব