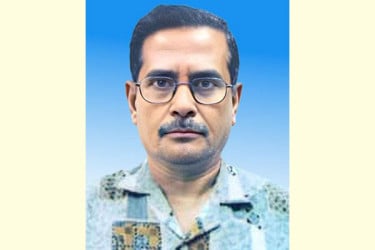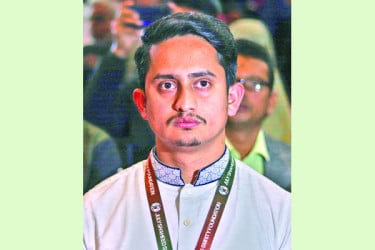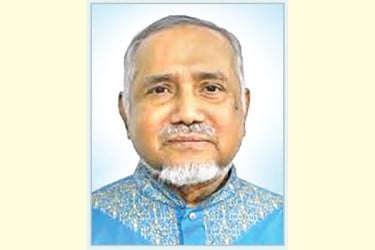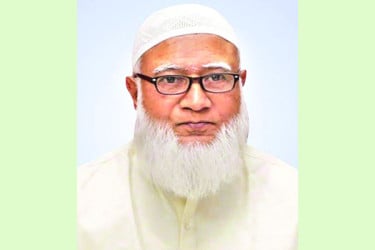ব্যবসায়ীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তারা হতাশ, বিক্ষুব্ধ। লাগামহীন ডলারের দর সহনীয় হয়নি। উচ্চ সুদের হার কমেনি। পতনে পতনে জেরবার পুঁজিবাজার। রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে মূল্যস্ফীতি। ব্যবসা-উদ্যোগের জন্য চাইলেই পাওয়া যাচ্ছে না ঋণ। স্থবির বিনিয়োগ-কর্মসংস্থান। আসছে না শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি। বেচাবিক্রিতে মন্দা। একে একে বন্ধ হচ্ছে ব্যবসা-শিল্প-কারখানা। খুন-খারাবি-মব থামেনি। ফেরেনি নিরাপত্তা। চাকরি হারাচ্ছেন শ্রমিকরা। বাড়ছে বেকারত্ব। বকেয়া পড়ছে বেতন-ভাতা। রপ্তানিও কমছে।
ধাক্কা লাগছে রাজস্বে। এক রেমিট্যান্স ছাড়া প্রায় সব সূচকই ভঙ্গুর অবস্থায়। বলা যায়, অনেকটা পিচ্ছিল পথেই চলছে দেশের অর্থনীতি। ব্যবসায়ীদের ভেতরে রক্তক্ষরণ। দেশের শীর্ষ গ্রুপ ও স্বনামধন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে জীবনেও যাঁদের কখনোই খেলাপির রেকর্ড নেই, তাঁদের কপালেও আজ ঋণখেলাপির তিলক। ছোট-বড় সব স্তরের শিল্প গ্রুপগুলো টিকে থাকার লড়াই করছে। চাকা যেন আর চলছে না! এমনই চিত্র এখন দেশের অর্থনীতিতে। অর্থ মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, এনবিআরসহ বিভিন্ন সূত্রের তথ্য পর্যালোচনা করে এমন চিত্র পাওয়া যায়।
অন্তর্বর্তী সরকার প্রায় ১৪ মাস পার করল। ব্যবসায়ীরা এই সরকারের কাছ থেকে এখনো এমন কোনো আশা-জাগানিয়া বার্তা পাননি। সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোনো পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে তাঁরা মনে করতে পারেন যে তাঁরা সন্তুষ্ট, খুশি, তৃপ্ত। বরং কখনো কখনো তাদের টুঁটি চেপে ধরার মতো অবস্থাও তৈরি হয়েছে। আগের সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব, ঘুষ-দুর্নীতি, ভুল নীতির কারণে যেমন একটি পরিবর্তনের প্রত্যাশা জেগেছিল; গণ-অভ্যুত্থানে অনেক ত্যাগের পর যে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিল, তাদের সময়ও পরিস্থিতি অনেকটা এমনই।
ব্যবসায়ীরা প্রায়ই বলে আসছেন, তারা রীতিমতো সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার। গত ১৪ মাসে এমন কোনো ফোরাম বা সম্মেলনের কথা শোনা যায়নি, যার মাধ্যমে দেশের ব্যবসায়ীসমাজকে ডেকে সরকার তাদের সমস্যা, সংকট ও চ্যালেঞ্জের কথা শুনবে। প্রধান উপদেষ্টা দূরের কথা; অর্থ, বাণিজ্য, পরিকল্পনা, কৃষি, খাদ্য কিংবা শিল্প খাতের সঙ্গে জড়িত কোনো উপদেষ্টাও বড় পরিসরে দেশের ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের কষ্টের কথাগুলো শুনতে চাননি। দীর্ঘদিনের সমস্যা নিয়ে সবাই রাজপথে নামলেও দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য যাঁদের হাতে, তাঁরা অনেকটা বিপন্ন হয়েও নিজেদের দাবি আদায়ে রাজপথে নামেননি। সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কারো পথ আগলে ধরেননি। বলেননি- আমাদের দাবি না মানলে লাগাতার ধর্মঘট-আন্দোলন।
ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরকারের শীর্ষ মহলের একটি আহবানই তাঁদের মনোবল চাঙ্গা করতে পারত। একটু আশ্বাসের বার্তাও কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারত। পাশে ডেকে বলার মতো সরকারের পক্ষ থেকে এমন কারো আহবান আসেনি। ফলে তারা হতাশায় শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক সরকারের অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁরা যে কী অবর্ণনীয় সংকট ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে পণ্য ও সেবার উৎপাদন অব্যাহত রেখে চলেছেন, দেশের সাপ্লাই চেইনে অবিরাম পণ্য ও সেবার সরবরাহ নিশ্চিত করে রেখেছেন, তার পেছনে কষ্টের গল্প কেউ জানে না- না সরকার, না লাইন মিনিস্ট্রি।
সময়ের সবচেয়ে সংকটময় পরিস্থিতি পার করছে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি। বিশ্বব্যাংকও বলছে, ব্যবসায় এখন মন্দার ছায়া। উদ্যোগে ভাটা। একের পর এক কারখানা বন্ধের নোটিশে প্রতিদিনই চাকরি হারাচ্ছেন হাজারো কর্মী। এক রেমিট্যান্স ছাড়া তেমন কোনো সূচকই সরকারের অনুকূলে নেই। রপ্তানি খাতও ভালো ছিল। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের বাড়তি শুল্কের কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বলা হচ্ছে, বাড়তি শুল্ক হলেও তা তৈরি করবে অপার সম্ভাবনা। চীন-ভারতের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। না, সেই আলামত এখনো দেখা যায়নি। বড় কোনো প্রতিষ্ঠান এখনো চীন-ভারত থেকে তাদের বিনিয়োগ উঠিয়ে নিয়ে বাংলাদেশে বসানো শুরু করেছে, এমন তথ্য নেই।
উল্টো গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে আগের বছরের চেয়ে কম রপ্তানি আয়ের ঘটনা ঘটেছে। আগস্টে ৩ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বরে ৪.৬১ শতাংশ রপ্তানি আয় এসেছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে কম। এটা মাত্র দুই মাসের তথ্য হলেও বড় কোনো অঘটন নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি তাহলে সামনে আরো প্রকট হতে পারে? কেন রপ্তানি কমে যাবে? এককথায় বললে উত্তর হচ্ছে, চ্যালেঞ্জ আছে। চ্যালেঞ্জটা কী? আসলে আগের শুল্কর সঙ্গে নতুন করে আরো ২০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে পণ্য যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। এতে ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ভোক্তারাও তাদের ভোগ ব্যয় কমিয়ে দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা বেশি দাম দিয়ে প্রয়োজনের বাইরে বেশি পণ্য কিনবে না। তাদের কেনাকাটা সংকুচিত হলে বাজারে পণ্যের চাহিদায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের পরের মাসগুলোতে যদি নেতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে চিন্তার বিষয়। তখন ধরে নিতে হবে যে ভোগ ব্যয় কমাচ্ছে মার্কিন খুচরা ক্রেতারা। এখনো সবাই আশা করে, এমন কোনো চিত্র সামনে দেখতে হবে না!
অর্থনীতির অন্য প্রধান প্রধান সূচকও অনেকটাই নেতিবাচক। পুঁজিবাজার বলতে গেলে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। আগের সরকারের সময়ের ‘দরবেশের’ থাবা এখন নেই, কিন্তু বাজারে ঠিকই কারসাজি চক্র বহাল তবিয়তে রয়েছে। ওই চক্রের সিন্ডিকেটে বাজার পতনে পতনে জেরবার এবং বাজার থেকে প্রায় লাখ কোটি টাকা হাওয়া হয়ে গেলেও এই বাজার টেনে তুলে ধরার উদ্যোগ নেই। সরকার এদিকে বলতে গেলে কোনো নজরই দেয়নি। একটি বাজার যদি ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ের মতো শুধুই নিচের দিকেই যেতে থাকে, তাহলে জনমনে অন্তর্বর্তী সরকারকে নিজের মনে করার কোনো কারণ থাকে না। তখন আগের সরকারের সঙ্গে তুলনা অবধারিতভাবেই চলে আসে। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেষ ভরসাস্থল পুঁজিবাজার এখন শুধুই হতাশার আরেক নাম।
ব্যাংক খাত আগের সরকার প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছে বলে অভিযোগের অন্ত নেই। কয়েকটি ব্যাংক প্রায় লুটে নেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার এসে এদিকে বিশেষ নজর দেয়। দখল ও লুটপাট কিছুটা ঠেকানো সম্ভব হলেও এখনো পুরো আস্থা ফেরেনি। অনেক ব্যাংকে মানুষ টাকা রেখে এখনো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। নিজের জমানো টাকাও চাওয়ামাত্র তুলতে পারছে না। এখন পাঁচটি ব্যাংক মার্জার করে একটি ব্যাংকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। ওই সব দুর্বল ব্যাংকের মালিক ও শেয়ারহোল্ডাররা হা-হুতাশ করছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্জারের ব্যাপারে শক্ত অবস্থানে। এতেই পাঁচ ব্যাংক মিলে এক ব্যাংকে রূপান্তর হতে যাওয়া ব্যাংকটি সবল ব্যাংকে পরিণত হবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
ব্যাংক খাতে সংস্কারের উদ্যোগে কতটা সুফল এসেছে, তা নিয়ে হয়তো বিতর্ক করবেন কেউ কেউ। কিন্তু আইএমএফের শর্তে ছয় মাসের ঋণখেলাপির নীতিতে পরিবর্তন আনার কারণে একলাফে খেলাপি ঋণের চিত্র আকাশে উঠে গেছে! সর্বশেষ তথ্যে খেলাপি ঋণের অঙ্ক ছাড়িয়েছে ছয় লাখ ৬৭ হাজার কোটি টাকা বা মোট ঋণের ৩৩ শতাংশ। বছরের পর বছর রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী ব্যাংক থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা ঋণ তুললেও সেগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলাপি দেখানো হয়নি। এটিই এখন বের হচ্ছে। ২০২৫ সালের জুন শেষে মোট ব্যাংকঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৪ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা। মাত্র তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে দুই লাখ ৪৬ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে এই ঋণের পরিমাণ বেড়েছে চার লাখ ৫৫ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের জুনে খেলাপি ঋণের অঙ্ক ছিল দুই লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। মাত্র এক বছরের মধ্যে খেলাপির পরিমাণ তিন গুণ বেড়েছে। এতে সৎ উদ্যোক্তারা পড়েছেন বিপাকে। যাঁদের দীর্ঘ ব্যাবসায়িক জীবনে কখনো খেলাপি হওয়ার রেকর্ড নেই, সময়ের ফেরে তাঁরাও হয়েছেন ঋণখেলাপি। এর ফলে তারা চলমান শিল্প চালিয়ে নিতেও সংকটের মধ্যে পড়েছেন। অথচ তাঁরা একেবারে অচল হয়ে পড়লে পুরো অর্থনীতিতে এর ধাক্কা লাগবে। বন্ধ হবে উৎপাদন। চাকরি হারাবেন বহু শ্রমিক। বাড়বে অসন্তোষ। সরকার হারাবে রাজস্ব।
মূল্যস্ফীতি ঠেকানোর কৌশল হিসেবে উচ্চ সুদের হার ধরে রাখছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যবসায়ীদের অব্যাহত দাবির মধ্যে তা না কমানোর ফলে বিনিয়োগে স্থবিরতা চলছে। প্রায় ১৬ শতাংশ সুদ দিয়ে কেউ ব্যবসা খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। উল্টো বন্ধ হচ্ছে কারখানা। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি নাজুক অবস্থায় পৌঁছেছে। গত আগস্ট মাসে দেশের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে। ওই মাসে এই প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৩৫ শতাংশে, যা গত জুলাইয়ে ছিল ৬.৫২ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৩ সালের পর এটাই সবচেয়ে কম ঋণ প্রবৃদ্ধি।
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা সব ভয়ভীতি, আশঙ্কা ও সংশয় দূর করে নির্বাচন হবে- সরকারের এই আশ্বাসেই অবিচল। তারা আশা করতে চান যে একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। এতে জনগণের ভোটে একটি রাজনৈতিক দলের সরকার হবে। অন্তর্বর্তী সরকারও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের কৃতিত্ব নিয়ে জনগণের সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এর ফলে দেশে আইন-শৃঙ্খলায় আস্থা ফিরবে। ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীরাও তাদের ব্যবসা-উদ্যোগে পূর্ণোদ্যমে ফিরবেন। এখন সেদিকেই চেয়ে আছেন তারা।
সৌজন্যে - কালের কণ্ঠ।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ