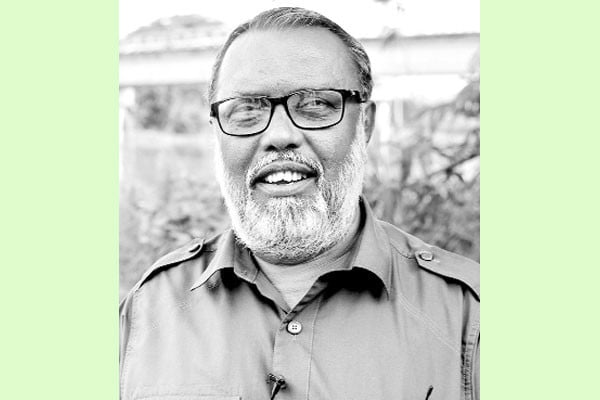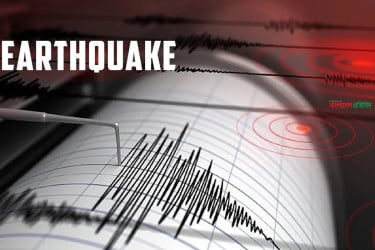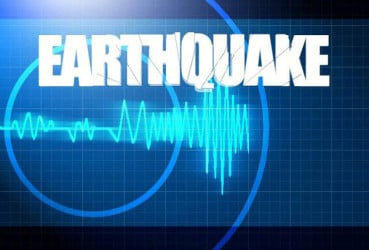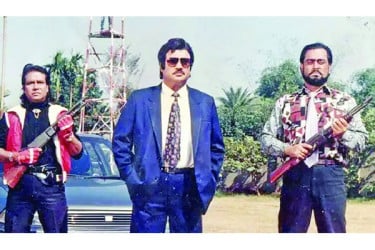৬ ডিসেম্বর আমাদের ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিন। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সেদিনই আমরা প্রথমবারের মতো দুটি দেশ যথা ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতি পাই, যা আমাদের মুক্তির পথকে আরও সুগম করেছিল। এ দিনটি এলেই বহু স্মৃতি মনে পড়ে, মনে পড়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণ এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনন্যসাধারণ অবদানের কথা। ভারত মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পাশে না দাঁড়ালে কী হতো, তা দেশে-বিদেশে বহুজনেরই প্রশ্ন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগে নাইজেরিয়া থেকে আলাদা হয়ে বায়াফ্রা নামে একটি স্বাধীন দেশ গঠনের জন্য যুদ্ধ করেও বিফল হয়েছিল বায়াফ্রার জনগণ। তাদের বিফলতার পেছনে একাধিক কারণ ছিল। আমাদের যুদ্ধ এবং তাদের যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল, আমাদের দেশে জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করায় এটিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি। আর বায়াফ্রায় এমন কিছু না হওয়ায় সারা বিশ্ব তাদের যুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, গৃহযুদ্ধের ঘটনা হিসেবেই দেখেছে বলে তাকে সমর্থন না দিয়ে বরং এর বিরোধিতাই করেছে, যদিও বায়াফ্রার জনগণ প্রায় সবাই স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং অস্ত্র ধরেছিল বায়াফ্রার বহু যুবক এবং প্রথম দিকে তারাই জয়ী ছিল।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সারা বিশ্বে বসবাসরত বাঙালি জনতা অবস্থানরত দেশসমূহে প্রবল প্রচারণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল, যে ভাগ্য বায়াফ্রাবাসীর ঘটেনি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছিল এমন এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যে শুধু বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবেই পরিচিত নয়, বরং বিশ্বসভায় যে দেশের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। বিশেষ করে একাত্তর সালের বিশ্ব রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধের সময় ভারত ছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে এক বিশেষ অবস্থানে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্কও একটি বড় নিয়ামক ছিল। বায়াফ্রার এ ধরনের বা কোনো ধরনেরই সাহায্য-সমর্থনের প্রতিবেশী ছিল না। প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় সহায়তা না পেলে আমাদের স্বাধীনতার কী হতো?
 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে যখন দেশের প্রায় গোটা জনগণই স্বাধীনতার দাবিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে অবস্থায় আমাদের স্বাধীনতা কেউ রুখতে পারত না। স্বাধীন আমরা হতামই, তবে মুক্তিযুদ্ধ আরও অনেক দীর্ঘায়িত হতো, আরও অনেক রক্ত ঝরত। মানুষকে আরও অনেক বিড়ম্বনা সইতে হতো। সেই অর্থে ভারতের কাছে, ভারতীয় জনগণের কাছে এবং তাদের সেই সময়ের নেত্রী ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধীর কাছে আমাদের ঋণ অপূরণযোগ্য। ভারত শুধু ১ কোটির অধিক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়নি, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে, আবাসন দিয়েছে এবং সবশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন ভারতীয় সেনারা, যে যুদ্ধে বেশ কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য শহীদ হয়েছেন।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে যখন দেশের প্রায় গোটা জনগণই স্বাধীনতার দাবিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে অবস্থায় আমাদের স্বাধীনতা কেউ রুখতে পারত না। স্বাধীন আমরা হতামই, তবে মুক্তিযুদ্ধ আরও অনেক দীর্ঘায়িত হতো, আরও অনেক রক্ত ঝরত। মানুষকে আরও অনেক বিড়ম্বনা সইতে হতো। সেই অর্থে ভারতের কাছে, ভারতীয় জনগণের কাছে এবং তাদের সেই সময়ের নেত্রী ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধীর কাছে আমাদের ঋণ অপূরণযোগ্য। ভারত শুধু ১ কোটির অধিক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়নি, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে, আবাসন দিয়েছে এবং সবশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন ভারতীয় সেনারা, যে যুদ্ধে বেশ কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য শহীদ হয়েছেন।
সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে ইন্দিরা গান্ধীর থাকাটাও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দিরা না হয়ে অন্য কেউ ভারতের সরকারপ্রধান হলে কী হতো তাও একটি প্রশ্ন বটে, কেননা ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন একজন বিশ্বকাঁপানো নেতা। তাঁকে বলা হতো অগ্নিমানবী। সেই স্নায়ুযুদ্ধের যুগে ‘জোট নিরপেক্ষ’ দেশসমূহের যে সংস্থাটি ছিল তা ছিল প্রবল পরাক্রমশালী আর ওই সংস্থায় ফিদেল কাস্ত্রো, মার্শাল টিটো, আনোয়ার সাদাত, কেনেথ কাউন্ডা, মুগাবে, নায়ারে, নত্রুমা (১৯৬৬ পর্যন্ত), সুকর্ণ (১৯৬৭ পর্যন্ত), জামাল আবদুল নাসের (১৯৭০ পর্যন্ত), ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ কালজয়ী দাপুটে তৃতীয় বিশ্বের নেতাদের সমান্তরালেই অবস্থান ছিল ইন্দিরা গান্ধীর। আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান নিক্সন একদিকে তাঁকে ঘৃণাভরে ‘দ্যাট ওমেন’ বললেও অন্যদিকে তাঁকে ভয়ও পেতেন। তাঁর কূটনৈতিক চাল, বিচক্ষণতা এবং দূরদৃষ্টি ছিল অভাবনীয়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সবার কাছেই তিনি ছিলেন সমাদৃত। তা ছাড়া সে সময় তদানীন্তন সোভিয়েতের ভূমিকাও ছিল আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আর সেখানেও ছিল ইন্দিরার বিচক্ষণ পদক্ষেপ। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্রিয় না থাকলে নিরাপত্তা পরিষদে আমাদের বিপক্ষে পাকিস্তানি প্রস্তাব গৃহীত হলে, যা সোভিয়েত ভেটোর ফলে ভুল হয়ে যায়, আমাদের স্বাধীনতা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ত। তা ছাড়া মার্কিন রণতরীর অগ্রযাত্রা বন্ধ করা, চীনের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধের পাঁয়তারা বন্ধের জন্যও সোভিয়েত ভূমিকা ছিল একান্ত আবশ্যক। আর এই সোভিয়েত ভূমিকা আদায়ে ইন্দিরার বিচক্ষণতা ছিল অগ্নিপরীক্ষিত। মার্কিন ও চৈনিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কার কথা টের পেয়েই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ২৫ বছরের বন্ধুত্বের চুক্তি করেছিলেন, প্রকারান্তরে যে চুক্তির ফায়দা পেয়েছিলাম আমরা। কেননা ওই চুক্তির ভয়েই চীনের সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ এবং মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পথযাত্রা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের জন্য ওই চুক্তি ছিল পরম নিয়ামক। ওই চুক্তির কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন সীমান্তে ৪০ ডিভিশন সৈন্যের বিশাল সমাবেশ ঘটিয়েছিল যা চীনকে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য করেছিল।
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল আমার লন্ডনে, ১৯৭১-এর ৩১ অক্টোবর। ইন্ডিয়া লীগ সেদিন পিকাডিলি সার্কাসের সন্নিকটে পেলেসিয়াম হলে এক বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করে। আমি বিলেতপ্রবাসীদের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম বলে ভারতীয় হাইকমিশন ছাড়াও ইন্ডিয়া লীগের সভাপতি তারাপদ বসু আমাদের শুধু নেমন্তন্নই করেননি, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলেন।
সেদিনের ভাষণে ইন্দিরা বলেছিলেন, ‘আমার মনে হয় আমি এক আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমি জানি না এটি বিস্ফোরিত হবে কিনা।’ ১ নভেম্বরের সব পত্রিকার শিরোনামে তাঁর ভাষণ ছাপানো হয়। তিনি আরও বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশে যে হত্যাকান্ড চলছে তা সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। শত উসকানির মধ্যেও ভারত শান্ত রয়েছে। তবে ভারত এভাবে আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারে না; বরং ভারত বাংলাদেশের সমস্যার ত্বরিত সমাধান চায়।’ তাঁর সেদিনের ভাষণ আমাদের মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। আমরা অনুধাবন করতে পারলাম যে, ভারত শিগগিরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নেমে পড়বে এবং আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে।
বাংলাদেশকে সাহায্যের ব্যাপারে ইন্দিরার যাত্রাপথ মোটেও সুগম ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো পরাক্রমশালী বিদেশি শক্তিগুলোই নয়, নিজ দেশি প্রতিবন্ধকতাও তাঁকে কম ভোগায়নি। তাঁকে এই মর্মে বোঝানো হতো যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যত্র থেকেও স্বাধীনতার দাবি আসবে। এমনকি ভারতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়ার বিপক্ষের লোকেরও অভাব ছিল না। তদুপরি ১ কোটি উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়া শুধু ভারতের অর্থনীতির জন্যই অশনিসংকেত ডেকে আনেনি, দেশের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতিও হুমকিস্বরূপ ছিল। ’৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাতে গণহত্যা শুরু এবং বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষের ভারত অভিমুখে কাফেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার ওপর একদিকে যেমন চাপ শুরু হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমরে যাওয়ার, অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের কারণে ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনীতি নিয়ে ভাবিয়ে তোলে নেতৃবৃন্দকে।
সবকিছু পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, ইন্দিরা প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কোপ দেওয়ার মতো ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়মতো অগ্রসর হওয়ার পক্ষে না থাকলে ফল হতো উল্টো। তার দ্বারগোড়ায় ছিল চীন, যার কাছে ১৯৬২ সালে ভারত গ্লানিকরভাবে পরাজিত হয়েছিল। ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তানের এক নম্বর বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র। দূরবর্তী দেশ হলেও সমরশক্তিতে, এ দেশ কারও থেকেই দূরে নয়। এ দুটি দেশ প্রথম থেকেই ছিল পাকিস্তানের পক্ষে আর পাকিস্তান তো ছিল সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য।
মধ্যপ্রাচ্যেও পাকিস্তানের বন্ধুর অভাব ছিল না। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে দূরদর্শী ও ধীশক্তির অধিকারী ইন্দিরার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করা। ১ কোটি উদ্বাস্তুর উপস্থিতি ও প্রবাসে থাকা বাঙালিদের ভূমিকা এ ব্যাপারে ছিল শক্তিশালী সহায়ক। তদুপরি তাঁর নিজের কূটনৈতিক চাল ছিল অব্যর্থ ধনুকেরই মতো।
ইন্দিরা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ইন্দর মালহোত্রা লিখেছেন, ‘১৯৭১ ছিল ইন্দিরার জীবনের সবচেয়ে সফল সময়। ২৫ মার্চের কালরাতের পর ৩১ মার্চ ভারতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি ব্যক্ত করেন যে, বাঙালিদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি আরও বলেন, পূর্ববঙ্গের মানুষের সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগে সব সময় ভারতের ঐকান্তিক সমর্থন ও সহানুভূতি থাকবে।’
৭ মে ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপে বসলে প্রায় সবাই বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, ‘যদিও গোটা পৃথিবীর জনতা বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল, তবু স্বীকৃতির ব্যাপারে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন রয়েছে।’ সে মাসেই তিনি বলেছিলেন, ‘এখনই স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের বিপদ ঘটবে।’
তিনি ১৫ মে আগরতলায় বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম বৃথা যাবে না, তারা দিনের শেষে স্বাধীনতা পাবেই।’
এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জেনারেল অরোরা বলেছেন, ‘মে মাসেই ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস ব্যক্ত করেন এবং জুনেই সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার নীলনকশা করা হয়। ইন্দিরা নিজেই বলেন, সুুস্থিরভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে, যাতে ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।’
তাঁর এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, সরাসরি হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু তিনি সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন।
বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা বন্ধ করার জন্য সবচেয়ে বড় চাপ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ইন্দিরার কঠোর অবস্থানের কারণে নিক্সন ছিলেন খুবই ক্ষিপ্ত। তিনি জুলাইয়েই তার প্রভাবশালী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে দিল্লি পাঠান ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষান্ত করতে। কিসিঞ্জারকে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, ‘শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে, তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য চাপ দিতে হবে এবং উদ্বাস্তুদের ফেরার পথ তৈরি করতে হবে।’ ইন্দিরা কিসিঞ্জারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর কাছে কোনো বিকল্প থাকবে না। কিসিঞ্জার এই মর্মে ইন্দিরাকে ভয় দেখান যে, ‘যুদ্ধ বেধে গেলে চীন পাকিস্তানের পক্ষে আসার আশঙ্কা থাকবে।’ তিনি ১৯৬২ সালে চীনের কাছে ভারতের পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। পরে পিকিং থেকে ফিরে গিয়ে হেনরি কিসিঞ্জার জানান, ‘ভারতে চীনা আক্রমণের মুখে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে।’
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে হুমকিমূলক ভেবে ইন্দিরা গান্ধী কালক্ষেপণ না করে আগস্টেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। যেখানে শর্ত থাকে, ‘চুক্তিভুক্ত কোনো দেশের ওপর আক্রমণ হলে অন্যপক্ষ সহায়তা করবে।’ ওই চুক্তি ইন্দিরার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রখর দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। আপাতদৃষ্টিতে এটি ভারত-সোভিয়েত চুক্তি হলেও এর মূল ফায়দা কিন্তু পেয়েছিল বাংলাদেশ। এ চুক্তি না হলে যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে যেমন চীনের আসার জোরালো আশঙ্কা থাকত, তেমন আশঙ্কা ছিল বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের অবস্থান নেওয়া। সপ্তম নৌবহরকে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ইয়াহিয়া নিশ্চিত ছিলেন, চীন আসবে এবং সে কথাই তিনি জেনারেল নিয়াজিকে বারবার বলে সাহস জোগাতেন, যে কথা ইয়াহিয়ার তৎকালীন এডিসি প্রকাশ করেছেন।
ইন্দিরা গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন, বিশ্বনেতাদের সমর্থন ছাড়া এগোনো যাবে না। তাই তিনি চূড়ান্ত যুদ্ধে যাওয়ার আগে বিশ্ব সফরে বেরিয়ে পড়েন অক্টোবরের শেষে। ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কদের ব্যাপারে তেমন বেগ পেতে না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-কিসিঞ্জারকে বোঝানো ছিল কঠিন, বাদাম ভাঙার মতোই। উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠকে আগের অবস্থানে অনড় থেকে নিক্সন ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ করতে হবে।’ তিনি বারবার চীনা জুজুর ভয় দেখান। বিশ্ব সফরে বেরোনোর আগে ইন্দিরা সেপ্টেম্বরে মস্কো যান সোভিয়েতের কাছ থেকে নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা আদায়ের জন্য। তিনি আশানুরূপ সাড়া পান সোভিয়েত নেতাদের কাছ থেকে, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে একটি বৈরী পশ্চিমা মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা বলে মনে করা হয়।
বিশ্ব ভ্রমণ শেষে ১৪ নভেম্বর নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে তিনি বলেছিলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ব এখন উপমহাদেশের সংকটের বিপদ সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল।’
বিশ্ব সফরের পর ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ‘বিভিন্ন দেশে যেসব ভুল বোঝাবুঝি ছিল আলোচনার মাধ্যমে সে ভুল পরিষ্কার করায় তাদের মনোজগতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।’
তিনি চীনের আক্রমণের কথা ভাবতেন না তা নয়, এবং এ কারণেই তিনি ঠিক করেছিলেন ভারত এমন সময় মাঠে নামবে যখন চীনা সীমান্তে বরফ জমবে এবং জেনারেলরাও ওই পরামর্শই দিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন তত দিনে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদের কোণঠাসা করে দিতে পারবে। তিনি তাঁর পশ্চিমা বিশ্ব সফরকালে পশ্চিমা নেতাদের বোঝাতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশের নির্বাচিত নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান ছাড়া কোনো সমাধান হতে পারে না এবং এজন্য বঙ্গবন্ধুর মুক্তি একটি পূর্বশর্ত। তিনি তাদের এও বোঝাতে পেরেছিলেন যে, বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নয় এবং ভারত-পাকিস্তান বিষয়ও নয়। তিনি সংসদ ও সংসদের বাইরে এটা পরিষ্কার করে দেন যে, বাংলাদেশকে নিজস্ব শক্তিতেই মুক্তি আদায় করতে হবে, তবে এ বিষয়ে ভারত পূর্ণশক্তিসহ বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পাশে থাকবে। নভেম্বরে নিউজ উইক সাময়িকীতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষতার প্রশংসা করে তিনি বলেছিলেন, ‘পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিঃশেষিত করতে হলে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষকেই হত্যা করতে হবে।’
এদিকে পাকিস্তান বসে ছিল মার্কিন ও চৈনিক হস্তক্ষেপের আশায়। পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত ছিলেন, চীন ভারতে আক্রমণ করবে আর যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে ভারতকে মোকাবিলা করবে। ভুট্টো এবং অন্যরা পরোক্ষভাবে চীনের জড়িয়ে যাওয়ার কথা প্রায়ই বলতেন। ৪ নভেম্বর ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, ‘ভারত আক্রমণ চালালে গঙ্গার পানির রং পাল্টে যাবে।’ পাকিস্তানের সামরিক হাইকমান্ড তখনকার পাকিস্তানি পুতুল গভর্নর ডা. মালেককে টেলেক্স মারফত এই ধারণা দিয়েছিলেন, চীনাদের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে জেনারেল নিয়াজিকে টেলিফোনে বলা হয়েছিল যে, উত্তর দিক থেকে হলদেরা (চীন) এবং দক্ষিণ থেকে (বঙ্গোপসাগর হয়ে) সাদারা (আমেরিকা) আসছে।
বহুলাংশে চীন-আমেরিকার ভরসা করেই যুদ্ধোন্মাদ পাকিস্তানি জেনারেলরা অতর্কিতে ভারতের কয়েকটি বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে বসলেন ৩ ডিসেম্বর, যা ছিল পাকিস্তানের জন্য আত্মঘাতীকর। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ত্বরিত দিল্লির পথে রওনা দিলেন ইন্দিরা এবং তার পরই যুদ্ধের ঘোষণা।
চীন আসছে না দেখে ভুট্টো-ইয়াহিয়া নিক্সনের সাহায্যের জন্য মরিয়া হয়ে গেলেন। নিক্সন যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইন্দিরার ওপর প্রতিনিয়ত চাপ দিয়েও সুবিধা করতে পারেননি। একদিকে ভারতীয় বাহিনী এবং পাশাপাশি মুক্তিসেনাদের দুর্বার আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী যখন পর্যুদস্ত তখন ৪ ডিসেম্বর আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বন্ধ এবং বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের প্রস্তাব ওঠালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে তা নাকচ করে দেয়।
ভুট্টোর আশা ছিল যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করাতে পারবে। ৮ ডিসেম্বর তিনি নিজেই নিউইয়র্ক চলে যান। যুক্তরাষ্ট্রও চেষ্টার ত্রুটি করেনি। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে ওঠালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবারই তাতে ভেটো দিলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর মাঝে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পোল্যান্ড একটি রাজনৈতিক সমঝোতার প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করলে ভুট্টো তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। ১৪ ডিসেম্বর শেষবারের মতো সোভিয়েত ভেটো যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে নস্যাৎ করার পর নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত ভুট্টো টাল সামলাতে না পেরে উন্মাদের মতো হাতের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে বলেন, তারা হাজার বছর যুদ্ধ করবেন। ইত্যবসরে ইন্দিরা তাঁর কূটনৈতিক কৌশলে চূড়ান্ত প্রদর্শনী দেখালেন ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে। সেই সময় ভুটানও স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বে বাংলাদেশ একটি স্বীকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করল। যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানিরা একের পর এক পরাজয়বরণ করার সময়ও তাদের চীনের আক্রমণ ও মার্কিন সপ্তম নৌবহরের প্রত্যাশা জীবন্ত ছিল। মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসেছিল, কিন্তু সেই নৌবহরকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছিল সোভিয়েত নৌবহর। সে কারণেই মার্কিন নৌবহর বেশি দূর এগোয়নি। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের অবাধ অগ্রযাত্রার মুখে শেষ পর্যন্ত পুতুল গভর্নর ডা. মালেক ও নিয়াজি বুঝতে পারেন চীন বা যুক্তরাষ্ট্র কেউই আসবে না তাদের বাঁচাতে। ডা. মালেক পদত্যাগ করলেন গভর্নরের বাসভবনে ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণের পর, চলে গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। নিয়াজি শুরু করলেন উচ্চৈঃস্বরে কান্না, যা তার সৈন্যদের মনোবল আরও ভেঙে দিল। তখন তারা পাকিস্তান রক্ষার কথা বিসর্জন দিয়ে খুঁজতে থাকলেন নিজেদের জীবন বাঁচানোর পন্থা। তারা বুঝতে পারেন বেপরোয়া গণহত্যা, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যে পরিমাণ মানবতাবিরোধী অপরাধ তারা করেছেন, তার কারণে মুক্তিসেনারা তাদের ছাড়বে না। তাই নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টাই তাদের একমাত্র পাথেয় হয়ে দাঁড়াল। ওই উদ্দেশ্যে তারা আত্মসমর্পণের আগে দাবি তোলেন যে, তাদের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী নিরাপত্তা দিতে হবে এবং সে কথা আত্মসমর্পণ ঘোষণাপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।
দেশ মুক্ত হওয়ার আগেই ইন্দিরা উদ্যোগী হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায়, এমনি এক সময়ে যখন শোনা যাচ্ছিল পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেবে। বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার বন্ধ এবং তাঁর মুক্তির ক্ষেত্রেও পাকিস্তানকে চাপ দেওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বনেতাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।
বঙ্গবন্ধু ইন্দিরার অবদানের কথা ভোলেননি। পাকিস্তান থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লন্ডন থেকে ঢাকায় আসার পথে তিনি ভারতে যাত্রাবিরতি করেছিলেন ইন্দিরার কাছে এবং ভারতের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে।
বঙ্গবন্ধুর প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর ছিল অসাধারণ শ্রদ্ধাবোধ। ১৯৭১-এর ৬ নভেম্বর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তার (ইন্দিরার) চেয়েও অনেক বেশি জনপ্রিয়।
বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাও ভুলে যাননি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর অবদানের কথা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর অসাধারণ অবদানের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করেন, যে সম্মাননা ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সোনিয়া গান্ধী গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে প্রদান করেন ৪ কেজি ওজনের স্বর্ণে নির্মিত ক্রেস্ট। জননেত্রী শেখ হাসিনা এই সিদ্ধান্তও নেন যে, এ ধরনের সর্বোচ্চ সম্মাননা আর কোনো দিন কাউকে দেওয়া হবে না।
লেখক : সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।