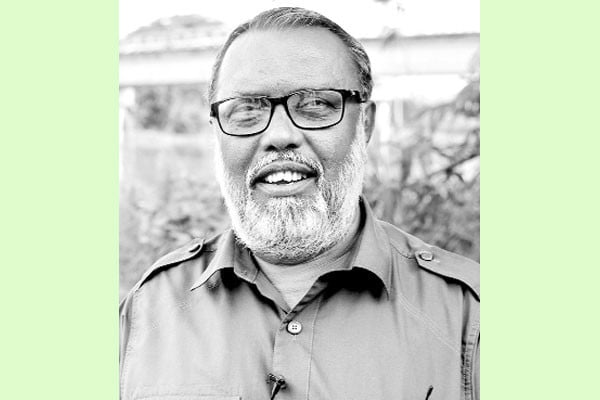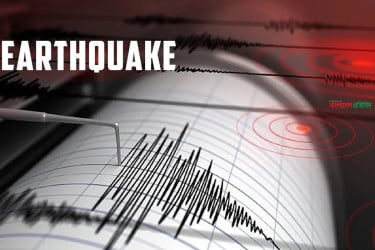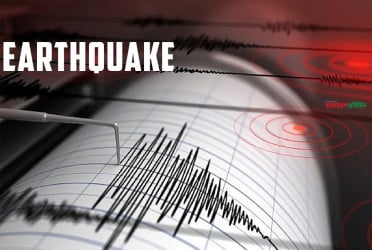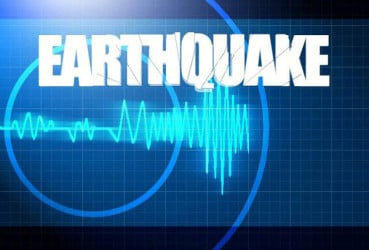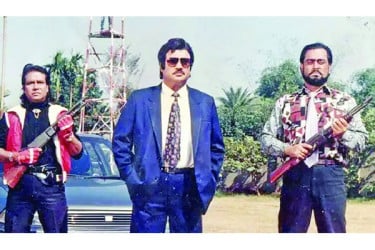পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যখন আশার চেয়ে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়। কোনো জাদুবিদ্যা বা রূপকথার কাহিনি এটা নয় বরং কখনো কখনো এটাই বাস্তবতা হয়। এমন ধরনের অদ্ভুত ঘটনা গবেষণার মাধ্যমেই ঘটতে পারে। গবেষণার ধর্মই হলো এমন নতুন কিছু বের করে আনা যেটা হয়তো যারা গবেষণা করছেন তারাও ঠিক তেমন করে আগে থেকে ভাবতে পারেননি। তবে কিছু একটা ঘটতে পারে তেমন একটা স্বপ্ন গোপনে মনে মনে ধারণ করেছেন। সেখানে গাছের শিকড় মাটির অনেকটা গভীরে গিয়ে নিজের পরিচয় খুঁজতে খুঁজতে একসময় বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। সেখান থেকে চিন্তা নতুন ধারণাকে জাপটে ধরে শাখা-প্রশাখার মতো চিন্তার বিস্তার ঘটায়। মানুষের কাছে সেটা হয়তো উদ্ভট চিন্তা মনে হতে পারে। কিংবা সেটা একটা ঝাপসা শীতের সকালের মতো মনে হতে পারে যেখানে কুয়াশার আবরণ সবকিছু ঢেকে রেখে সৃষ্টিকে আড়াল করার চেষ্টা করে। কিন্তু চিন্তা যখন বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে তখন সৃষ্টি আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। সৃষ্টির মর্মবাণীই এটি, যেটি সবাইকে চমকে দিয়ে বিস্ময়ের জন্ম দেয়। আন্দ্রেয়া সেরেক বলছেন, রোগীরা যখন তাদের ক্যান্সার-মুক্তির খবর জানতে পারলেন, সেটার চেয়ে আনন্দের মুহূর্ত আর ছিল না। অনেকে খুশিতে কেঁদে ফেলেছিলেন। বিজ্ঞানের সৃষ্টি যখন মানুষকে কাঁদায় তখন বোঝা যায় গবেষণার মূল্য কতখানি। গবেষক হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই শুক্রবারের ব্যস্ত সন্ধেটা সাশা রোথ কখনো ভুলতে পারবেন না। তখন তিনি ওয়াশিংটনে। সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়াচ্ছেন ব্যাগ গোছাতে। ক্যান্সার চিকিৎসায় তাঁর পরবর্তী গন্তব্য নিউইয়র্ক। তাঁকে সেখানে গিয়ে রেকটাল ক্যান্সারের রেডিয়েশন থেরাপি নিতে হবে। এমন এক অস্থির সময়ে নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল সেøান ক্যাটারিং ক্যান্সার সেন্টার থেকে একটা ফোন এলো। উত্তেজিত গলায় কথা বলছিলেন মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট ডা. আন্দ্রেয়া সেরসেক, ‘শেষ টেস্টে দেখা যাচ্ছে আপনার শরীরে ক্যান্সারের কোনো অস্তিত্ব নেই।’ শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন সাশা... আনন্দে। এত খুশি কোনো দিন হননি। মানুষ যখন অলৌকিক আনন্দের ভারে নুয়ে পড়ে তখন মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। শব্দগুলো আনন্দের বেড়াজালে আটকে যায়। আনন্দ কেবল শব্দের উচ্চারণে সীমাবদ্ধ থাকে না, নীরবতাও আনন্দের একটা ভাষা। যে ভাষার শক্তি শব্দের চেয়ে অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ, অনেক বেশি শক্তিশালী।
সাশা রোথের মতো মলদ্বারের ক্যান্সারে আক্রান্ত ১৮ জন রোগী মৃত্যুর দিন গুনছিলেন। জীবনের গতিপথটা কেমন করে যেন থমকে গিয়েছিল তাদের। স্বপ্নগুলো পুড়ে পুড়ে মরছিল যন্ত্রণায়। খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। খুব অদ্ভুত হয় সে সময়টা যখন মানুষ বেঁচে থাকা চোখে আর জীবনের কোলাহলকে দেখে না, মৃত্যুর নিস্তব্ধতা দেখতে পায়। মৃত্যুটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে মানুষ ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়ায়। আপনজনদের প্রিয় মুখগুলো তাদের ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে বোবা করে দেয়। সব যেন খেলা, যে খেলায় জয় নেই, পরাজয় আছে, আশা নেই, আনন্দ নেই, ঘরে ফিরে যাওয়ার তাড়া নেই। কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন এবং অস্ত্রোপচারের মতো কষ্টকর চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁরা জানতেন এসব কেবল মনকে সান্ত¡না দেওয়া, জীবনকে আরেকটু টেনে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে কিছুটা হলেও বিলম্বিত করা। কিন্তু এ দুর্বিষহ বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়ে যে অনেক কঠিন। যার হয় সে-ই বোঝে, যে হারায় সে-ই জানে জীবন তার থেকে কতটা হারিয়ে গেছে। আমেরিকার গবেষকরা এমন একটা সময়ে ১৮ জন ক্যান্সার আক্রান্তকে ডোস্টারলিম্যাব নামের ওষুধ সেবন করাতে থাকেন। গবেষকরা জানতেন না এ ওষুধ সেবন করালে কী ঘটতে পারে, তার পরও হয়তো ছোট ছোট স্বপ্ন আনমনে দেখেছেন। কারণ তাদের লজিক, অভিজ্ঞতা ও বিশেষায়িত জ্ঞান কিছু একটা ঘটানোর ইঙ্গিত হয়তো দিয়েছিল, তবে যেটা দিয়েছিল বাস্তবে ঘটেছে তার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো প্রায় বেশির ভাগ মানুষ ভাবে গবেষকরা গবেষণা প্রমাণ করে দেখাবেন তাঁরা যা বলছেন তা সত্য, মিথ্যা নয়। তারপর সেটা ইতিবাচক ফলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলেই বাস্তবে প্রয়োগ করবেন। প্রমাণ ছাড়া এ পৃথিবীর মানুষ কোনো কিছুই মানতে চায় না। গবেষণাটা যে এত সহজ নয় তা হয়তো বোঝানো কঠিন। সাধারণ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম, যারা বিজ্ঞান বোঝেন ও জানেন তাদের মধ্যেও এ ধরনের রক্ষণশীলতা অনেক সময় কাজ করে। কারণ মানুষের মনস্তত্ত্বটাতেই যত গ-গোল। কেউ ভালো কিছু করলে তাতে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেওয়া যেন কারও কারও উদ্দেশ্য হয়ে যাচ্ছে। গবেষণায় সমালোচনা থাকা ভালো। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। তবে সমালোচনা ও ঈর্ষা এক কথা নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে, সমালোচনা করতে যোগ্যতা লাগে না, সমালোচিত হতে যোগ্যতা লাগে। কেউ কেউ এই আধুনিক সময়ে এসেও ভাবছেন, যার যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান আছে তাকে সে বিষয়ের গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অথচ গবেষণার ইতিহাস এমন কথা বলছে না। বর্তমানে গবেষণা কোনো একটি বিষয়নির্ভর নয়, বরং বহু বিষয়ের সমন্বয় সেখানে ঘটছে। বিশেষ করে এই সময়ে যখন বহুমাত্রিক গবেষণার ধারণা সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে উঠছে তখন এ ধরনের কূপমন্ডূকতা গবেষণার বহুমাত্রিক চিন্তাধারায় প্রতিবন্ধক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে। সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো গবেষণায় এ নীতি অবলম্বন করলে আমাদের দেশের কিছু মানুষ সেটাকে বাহবা দিচ্ছেন। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সেটা আরও বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছেন অথচ দেশের গবেষকরা তাঁদের চেয়ে ভালো গবেষণা করলেও সেটাকে কীভাবে নিচু করে দেখানো যায়, প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় এ ধরনের আত্মঘাতী প্রচার করছেন। সেটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহার করে ব্যক্তিক আক্রমণের বিষয়বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এটাই কি দেশপ্রেম? এটাই কি উদারতা? নাকি এসবের পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। একদিন বিদেশিরা আমাদের তাদের গবেষণার গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করেছিল, আর এখন আমাদের দেশের কিছু মানুষ পাশ্চাত্যের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আমাদের গিনিপিগ হিসেবে ভাবছে। গবেষণায় ভুল হতে পারে, ব্যর্থতা থাকতে পারে, দুর্বলতা থাকতে পারে, অপরিপক্বতা থাকতে পারে, তবে এসব আছে বলেই গবেষকরা সেগুলো থেকে ধারণা নিয়ে তাঁদের গবেষণার চিন্তাধারা এগিয়ে নিতে পারেন। আমাদের দেশে এত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যাঁরা গবেষণার সংস্কৃতি এগিয়ে নিচ্ছেন তাঁদের থামিয়ে দেওয়াই কি এর উদ্দেশ্য। যাতে উদ্ভাবন ও গবেষণায় পরনির্ভরশীল দেশ হিসেবে প্রচার করা যায়। সারা পৃথিবী যখন উদার গণতান্ত্রিক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষকে তার মতো করে চিন্তা করার স্বাধীনতা দিচ্ছে। সেখানে কিছু মানুষ মুখে মুখে স্বাধীন চিন্তা বিকাশের কথা বললেও তাদের তথাকথিত স্বাধীনতা আরেকজন গবেষকের স্বাধীন চিন্তাকে কীভাবে রুদ্ধ করা যায় সেই নেতিবাচক ভাবনা দ্বারা তাড়িত হচ্ছে। একজন গবেষক তাঁর বিশেষায়িত জ্ঞানের বাইরে গিয়ে গবেষণা করতে পারবেন না, এমনটা কি গবেষণার ইতিহাস ও প্রবণতা বলছে? পৃথিবীতে এমন অনেক গবেষক জন্ম নিয়েছিলেন যাঁদের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, এমনকি অনেকে স্কুলের গন্ডিও পেরোতে পারেননি। আবার অনেক প্রতিভাধর গবেষক তাঁদের বিশেষায়িত জ্ঞানের বাইরে গিয়েও গবেষণা করেছেন, এখনো অনেকে করছেন। গবেষণা কোনো নিয়ম মানে না, মানুষ গবেষণা নিয়মের মধ্যে আনতে গিয়েই বিপত্তি ঘটায়। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু পদার্থবিদ হলেও উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেছেন। উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন এবং তা প্রমাণ করেও দেখিয়েছেন। মেঘনাদ সাহা গণিত নিয়ে লেখাপড়া করলেও পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়েও গবেষণা করেছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞানের তাপীয় আয়নীকরণ থিওরি প্রদান করেন। তাঁর আবিষ্কৃত সাহা আয়নীভবন সমীকরণ নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মগুলো ব্যাখ্যা করতে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম পন্থা। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল মনোনয়ন প্রাপ্তির তালিকায় বেশ কবার নাম গিয়েছিল তাঁর। নোবেল কমিটি মেঘনাদ সাহার কাজকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হিসেবে বিবেচনা করলেও এটি ‘আবিষ্কার’ নয় বলে তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। মেঘনাদ সাহাকে ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালে আর্থার কম্পটন এবং ১৯৩৯, ১৯৫১ ও ১৯৫৫ সালে শিশির কুমার মিত্র আবারও মনোনীত করলেও নোবেল কমিটি তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। মেঘনাদ সাহাকে সে সময়ের মানুষ মূল্যায়ন করতে পারেনি তবে ইতিহাস ও সময় তাঁর অবদান আজও স্মরণ করে।
আর্নল্ড জোহান্স উইলহেলম সমারফিল্ড একজন বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ। তাঁর ছাত্র ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম তত্ত্বে, ওলফগ্যাং পলি ‘ইপোনিমাস পলি এক্সক্লুসন প্রিন্সিপাল’ তত্ত্বে, হ্যানস বেথাকে ‘স্টেলার নিউক্লীয় সিনথেসিস’ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেও তিনি পাননি। বারবার সুযোগ এসেছে তবে কথিত আছে, তা হাতছাড়া হয়ে গেছে নোবেল বিচারকদের একজনের প্রতিহিংসার কারণে। আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁকে একবার বলেছিলেন, ‘তোমার যে বিষয়টি আমাকে বেশ অভিভূত করে, তা হলো তোমার শিক্ষকতা। যার মাধ্যমে তুমি অনেক নতুন মেধাবী মুখ বের করতে পেরেছ।’
গবেষকের চেয়ে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষক হিসেবে। যিনি তাঁর শিক্ষকতা দিয়ে যুগান্তকারী সব গবেষক গড়তে পারেন তাঁকে কেবল মানুষের পৃথিবীর নোবেল পুরস্কার দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, কারণ কখনো কখনো ত্যাগ পুরস্কারের চেয়েও অনেক বড় হয়। তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি ঠিকই কিন্তু মনে মনে একটা সান্ত্বনা খুঁজেছেন তা হলো পৃথিবীতে নোবেল পুরস্কারের বিষয়টি যখন আলোচিত হবে তখন কোন মানুষটি সবচেয়ে বেশি ৮৪ বার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েও পুরস্কার অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন সে বিষয়টিও আসবে। ব্যর্থতা কখনো কখনো সফল মানুষদের চিনিয়ে দেয়। সারা পৃথিবীর মানুষ সফলতার পূজারি হলেও মানুষকে ব্যর্থ করার দায়ভারও যে সে সময়ের মানুষের তা-ও আমাদের ইতিহাস ও সময় আঙুল তুলে জানিয়ে দেয়।
উদ্ভাবনের একটা প্রধানতম শক্তি হলো কনসেপচুয়ালিটি তৈরি করা। যেমন ব্ল্যাক হোল, থিওরি অব রিলেটিভিটির মতো বিষয়গুলো। গবেষণার সবকিছু একবারে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ক্রমাগত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গবেষণা এগিয়ে যায়, কখনো গন্তব্যের দেখা মেলে, কখনো মেলে না। তার পরও গবেষণার কল্পনার যাত্রা বন্ধ হয়ে যায় না। কোনো কিছু প্রমাণ করার আগে তার থিওরিটিক্যাল অনেক গবেষণা হয়, সেটা অনেকেই জানে না। আবার অনেকে জেনেও না জানার ভান করে। গবেষণায় প্রতিযোগিতা মন্দ নয় যদি তা নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে হয়। তবে সেটা যেন কোনোভাবেই আরেকজন গবেষককে হতাশায় নিমজ্জিত করে নতুন সৃষ্টির ধারণা ধ্বংস করে না দেয়। গ্রাফিন ম্যাটেরিয়ালের অস্তিত্ব একসময় ছিল না। তখন গবেষকরা ভেবেছিলেন এমন একটা মেটেরিয়াল পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারে। গবেষণা এমনই যেটা অদেখা কোনো সৃষ্টিকে আগে থেকেই দেখার শক্তি অর্জন করে। গ্রাফিনের আবিষ্কারের ঘটনাটাও ঘটেছে খুব আকস্মিকভাবে। যাঁরা এটা আবিষ্কার করেছেন তাঁরা কী আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন তা নিজেরাও সে সময়টাতে বুঝে উঠতে পারেননি। অথচ এ আবিষ্কারটা তাঁদের নোবেল বিজয়ী করেছে। গাইম আর নভোসেলভের গ্রুপ প্রতি শুক্রবার বিকালে ফ্রাইডে ইভনিং এক্সপেরিমেন্ট নামে নতুন এক ধরনের বিজ্ঞানের সৃষ্টিকে খোঁজার আনন্দে মেতে উঠতেন। খালি হাতে ল্যাবে যা কিছু আছে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেদের মগ্ন রাখতেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বা কী, যা চোখে পড়ত সেটাতেই নতুন কিছু খোঁজার চেষ্টা করতেন তাঁরা। এমন করে খুঁজতে গিয়েই পেনসিলের কালো সিসার মতো কার্বন বা গ্রাফাইট একটু একটু করে আলাদা করতে করতে একসময় সেখান থেকে এক অণুর আস্তরণ বের করে আনেন আর এভাবেই ঘটে যায় গ্রাফিন আবিষ্কারের মহাকাব্য।
গবেষণার সৃষ্টিটাই এমন যা মানুষ ভাবতে পারে না, সেটাই মানুষের চিন্তাশক্তির জাদুতে সত্যে পরিণত করে। গবেষণায় সেটাই সত্য যেটা সত্য বলে মনে হয় না, যেটা মিথ্যা বলে মনে হয়। গবেষণার গন্তব্যটা ঠিক কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা কেউ জানে না আর সেটা না জানাটাই বেশি যৌক্তিক।
লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।