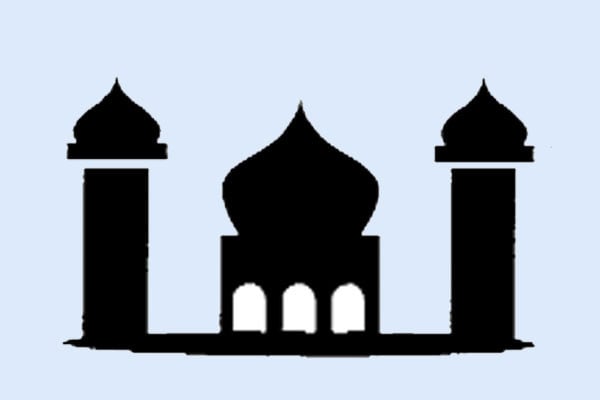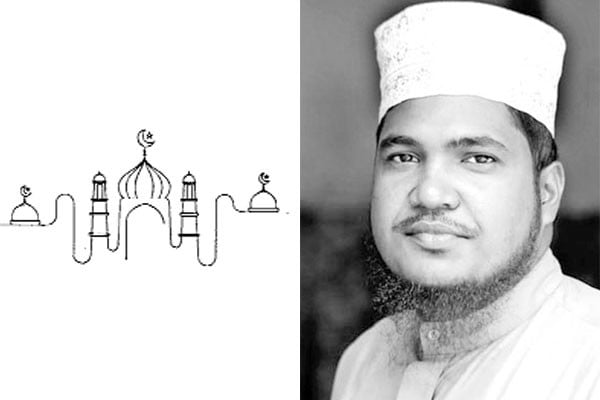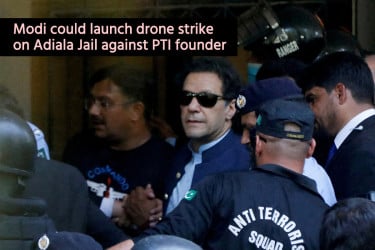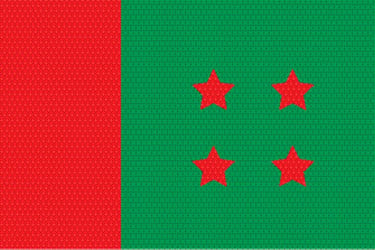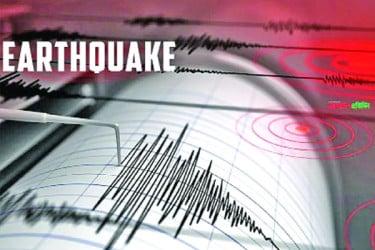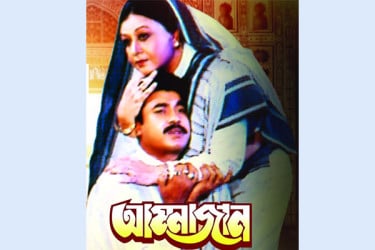‘ব্যবসায়ীরা ঋণ পায়, চাকরিজীবীরা ঋণ পায়, কোম্পানিওয়ালারা ঋণ পায়, আমি কৃষক ব্যাংকে গেলে ঋণ পাই না কেন? আমি কৃষক অন্যের জমি বর্গাচাষ করি। এত কাগজপত্র কই পামু? এনজিও ঋণ দেয় কোনো ঝুট-ঝামেলা নাই; ব্যাংকের ঋণ নিতে গেলে এত ঝামেলা কেন?’ প্রশ্নটি খোদ কৃষিমন্ত্রীর সামনেই উত্থাপন করেন এক কৃষক মধুপুর টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত এবারের কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট অনুষ্ঠানে।
২০০৬ সাল থেকে ‘কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট’ অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই কৃষিঋণ নিয়ে কৃষকের দাবি ওঠে আসছে। কৃষক সহজ শর্তে সহজে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে চায়। কারণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে তাকে সুদ দিতে হবে শতকরা ৪ থেকে ৮ টাকা। আর এনজিও থেকে ঋণ নিলে সেটার সুদের পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষে শতকরা ২০ থেকে ২৫ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। আর মহাজনী ঋণের সুদ তো বিদ্যুতের গতিতে বাড়ে। আমাদের কৃষকদের জন্য ঋণ পাওয়া একটি জটিল বিষয়। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইফপ্রি) ২০১৯ সালের একটি সমীক্ষা রয়েছে। সমীক্ষা বলছে, বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত এনজিও, আত্মীয়স্বজন, বেসরকারি ব্যাংক, দাদন ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন বেসরকারি উৎস থেকে ৮১ শতাংশের বেশি ঋণ নেন। আর এসব ঋণের সুদের হার ১৯ থেকে ৬৩ শতাংশ। অন্যদিকে কৃষি ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেওয়া হয় তার সুদের হার ৯ শতাংশ (এখন আরও কম)। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে কৃষকের মোট ঋণের মাত্র ৬ শতাংশ আসে কৃষি ব্যাংক থেকে। ইফপ্রির সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে মোট ঋণের ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ নেওয়া হয় এনজিও থেকে। যেখানে কৃষককে ঋণের বিপরীতে অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ২০ শতাংশের ওপর সুদ দিতে হয়। ইফপ্রির মতে, আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে ঋণ নেয় ১৯ শতাংশ কৃষক। জমির মালিকের কাছ থেকে ১৫ শতাংশ। মহাজন বা দাদন থেকে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ এবং বিভিন্ন সমিতি থেকে আসে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ঋণ। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকে আসা ৬ শতাংশ ঋণের সবচেয়ে বেশি অংশ পান বড় চাষিরা, প্রায় ১৫ শতাংশ। বড়, মাঝারি ও ছোট চাষি মিলে মোট ঋণের ৩৬ শতাংশ পান। আর প্রান্তিক চাষি পান ৫ শতাংশের মতো। বর্গাচাষি অর্থাৎ অন্যের জমি ইজারা নিয়ে চাষ করেন- এমন কৃষকরা এই ঋণ পান না। ফলে তাদের এনজিওসহ অন্য উৎসের ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়।
অথচ প্রকৃত কৃষক কখনো ঋণখেলাপি হন না তার প্রমাণ আমরা সব সময়ই পেয়ে এসেছি। বিশেষ করে করোনার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পরিসংখ্যান তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর, এ ছয় মাসে ব্যাংকগুলো কৃষকদের ঋণ দিয়েছে ১২ হাজার ৭৭ কোটি টাকা। বিপরীতে একই সময়ে কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করেছে ১৪ হাজার ৯১ কোটি টাকা। সে হিসাবে ছয় মাসে ব্যাংকগুলো বিতরণের তুলনায় ২২ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি কৃষিঋণ আদায় করেছে। অর্থাৎ বলা যায় মহামারিতে আমাদের কৃষকরাই অর্থনীতির হাল ধরে ছিলেন। পাশাপাশি তারা অন্যদের তুলনায় ব্যাংকের অর্থও বেশি পরিশোধ করেছেন। যদিও করোনার মাঝে কৃষকের ঋণের কিস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ শিথিলতা ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে ঋণের কিস্তি আদায়ে কৃষককে বাধ্য করার ব্যাপারটিতে ছিল নিষেধাজ্ঞা, তারপরও বেশির ভাগ কৃষক ব্যাংকের ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেছেন। ২০২০ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৪ হাজার ৬৩৬ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করেছে। মহামারির মধ্যেও সে বছর কৃষি ব্যাংকের ৪ হাজার কোটি টাকার ঋণ আদায় হয়েছে।
দেশের বহু ঋণদান প্রতিষ্ঠান ফুলেফেঁপে বড় হয়েছে। অথচ কৃষকের সে রকম কোনো পরিবর্তন হয় না। কৃষক ঋণের জালে আটকে যায়। কখনো এনজিও, কখনো মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দীর্ঘ ঋণের বোঝা টানতে থাকে। আমার ‘কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট’ অনুষ্ঠানের এক আসরে নাটোরে কৃষক রফিকুল ইসলাম ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘কখনো কোনো রাজনীতিবিদকে তো দেখি নাই রাজনীতি করে নিঃস্ব হয়ে যেতে, সেটা সরকারি দলের হোক আর বেসরকারি দলেরই হোক, কৃষক কেন কৃষি খেতি করে নিঃস্ব হয় তার খোঁজখবর তো কেউ নেয় না। আপনারা তিল থেকে তাল হইছেন, শিল্পপতি হইছেন। আর আমাদের পুঁজি নাই, আমাদের বাজার নিয়ে কেউ ভাবে না, আমাদের কথা কেউ বলে না।’ এ ক্ষোভ শুধু রফিকুল ইসলামের নয়, প্রতিটি কৃষকের। মহাজন কিংবা মহাজনদের মতো যারা কৃষকের দুরবস্থাকে পুঁজি করে নিজেদের ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করেছে তারা কখনোই চায় না মহাজনী দুষ্টচক্র থেকে কৃষক বের হয়ে যাক।
ফসলনির্ভর কৃষকের ঋণের বোঝা বাড়ে সাধারণত দুই কারণে। কৃষক ঋণ নিয়ে ফসল ফলায়। মৌসুমে সে ফসলের দাম পায় না। কিন্তু ওই সময়টাতে তার টাকা বেশি প্রয়োজন। কারণ, সার-ওষুধের দোকানের বাকি মেটাতে হবে, মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করতে হবে এবং পরবর্তী ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হবে। তাই ওই সময়টাতে ফসলের দাম কম থাকা সত্ত্বেও সে ফসল বিক্রি করে দেয়। কম দামে ফসল বিক্রি করে দেনা শোধ করে নতুন ফসল চাষে যেতে যেতে দেখা যায় তার ঋণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে।
সেদিন কথা হচ্ছিল বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, মৌসুমের শুরুতেই এক মাসের মধ্যে উদ্বৃত্ত ধানের ৫২ শতাংশ বিক্রি করে দিতে হয় কৃষককে। এক থেকে দুই মাসের মধ্যে বিক্রি করতে হয় ২৫ শতাংশ ধান, দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে ১৮ শতাংশ এবং চার মাস বা তার বেশি সময়ের মধ্যে বিক্রি করতে হচ্ছে ৫ শতাংশ ধান। অথচ যদি ঋণ পরিশোধের জন্য তিন থেকে চার মাস সময় কৃষকের হাতে থাকত আর ফসল সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা থাকত তাহলে কৃষক অনেক লাভবান থাকতে পারত।
শস্য গুদামজাত রেখে বিনিময়ে ঋণের একটি দারুণ প্রকল্প ছিল kMFc (শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প)। কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে কৃষককে ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য সহযোগিতা করতে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড সরকারের যৌথ উদ্যোগে BASWAP (Bangladesh Switzerland Agricultural Project) প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। প্রজেক্টের মডেল অনুযায়ী কৃষক তার উৎপাদিত ফসল গুদামে মজুদ রেখে, সেই মজুদকৃত ফসলের ওপর ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারত। ঋণের টাকায় পরবর্তী চাষ কার্যক্রম পরিচালনা ও জীবন নির্বাহ করার সুযোগ পেত কৃষক। শস্যের বাজার দাম বেশি হলে গুদাম থেকে শস্য ছাড়িয়ে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করত। সেই আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষে এ কার্যক্রম নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম। এ প্রজেক্টটি বেশ কার্যকর ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সফল এ কার্যক্রমটি হঠাৎ করেই যেন মুখ থুবড়ে পড়ে।
‘kMFc’ শুধু ফসল মজুদের সুবিধাদিই দিত না, এটি ছিল কৃষি বাণিজ্যের একটি চমৎকার মডেল। কৃষককে প্রতি কুইন্টাল ফসল মজুদ রাখার জন্য ১০ টাকা হারে গুদাম ভাড়া দিতে হয়। খাদ্যশস্য ছয় মাস আর বীজ হিসেবে ৯ মাস রাখার সুযোগ রয়েছে। যতদূর জানি গুদামের আয় ব্যাংকে জমা হতো। সঠিকভাবে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে কৃষকই শুধু লাভবান হতো না, সরকারও লাভবান হতো।
ঋণের ব্যাপারে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে- ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিদের ঋণ নিয়ে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৩ কোটি ৫৫ লাখ কৃষির খানার ১৯ শতাংশই বর্গাচাষি। এ হিসাব অনুযায়ী দেশে বর্গাচাষি পরিবারের সংখ্যা ৬৫ লাখেরও বেশি। আবার সারা দেশে প্রায় ২৩ লাখ ২৩ হাজার ২৭০টি ভূমিহীন কৃষক পরিবার আছে। এসব পরিবার সরাসরি কৃষি কাজে নিয়োজিত, অন্যের জমি ভাড়া বা লিজ নিয়ে তাদের চাষ-আবাদ। সরকারের বিদ্যমান কৃষিঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ৫ একর বা ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। সে জন্য তাদের জমির দলিল বন্ধক রাখতে হবে। যাদের জমি নেই তারাও এ ঋণ পাবেন, তবে সে ক্ষেত্রে কৃষক যার জমি ভাড়া বা লিজ নিয়ে চাষ করেন সেই ভাড়ার চুক্তিপত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন রকম। করোনার কারণে সরকার যখন কৃষকদের জন্য প্রণোদনা ঘোষণা করল, শতকরা ৪ টাকা হার সুদে ঋণ প্রদানের কথা বলল বাংলাদেশ ব্যাংক তখন অসংখ্য বর্গাচাষি আমাকে ফোনে জানিয়েছিলেন তাদের ঋণ না পাওয়ার সমস্যা নিয়ে। বলছিলেন, ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে হলে তাদেরকে জমির মালিকের সঙ্গে চুক্তিপত্র দেখাতে হবে। এখানেও একটি সমস্যা আছে। বর্গাচাষি জমি লিজ বা বর্গা নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাদের কোনো চুক্তিপত্র নেই। সাধারণত জমির মালিক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে কোনো চাষিকে জমি বর্গা দিতে চান না। কারণ লিখিত চুক্তির মাধ্যমে জমি বর্গা দিলে জমির মালিককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ফি সরকারকে দিতে হয়। সেটি দিতে চান না বলে বেশির ভাগ জমির মালিক চুক্তিতে জমি বর্গা দেন না। ফলে চুক্তিপত্র না থাকার কারণে অনেক বর্গাচাষি প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।
কৃষি ও কৃষকই হবে টেকসই উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। কৃষক যেন তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঠিকঠাক মতো পায় সেটিই নিশ্চিত করতে হবে। আমি মনে করি কোনোরকম শর্ত ছাড়াই প্রকৃত কৃষক ৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাওয়ার অধিকার রাখে। বিভিন্ন এনজিও বা মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের বেড়াজালে কৃষককে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে। যেখানে শিল্পোদ্যোক্তারা ঋণ পান ৯-১৫% হার সুদে সেখানে ক্ষুদ্র কৃষককে ঋণ নিতে হয় ২০% হারের চেয়েও বেশি সুদে। ব্যাংক খাতে যে পরিমাণে ঋণখেলাপি, রাইট অফ, দুর্নীতি, অনিয়ম হয় সেটা বিবেচনায় নিলে ১৫ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার তাবৎ কৃষিঋণ সরকার চাইলে বিনা সুদে দিতেই পারে।
আমাদের কৃষি সম্প্রসারিত হচ্ছে শিল্পের দিকে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার কারণে বিভিন্ন পেশার মানুষ যুক্ত হচ্ছে কৃষিতে। শিল্পপতিরা কৃষিতে বিনিয়োগ করছেন। এ সময়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের টিকিয়ে রাখতে হবে। না হলে কৃষি থেকে কৃষকই ছিটকে পড়বে। বাড়বে বেকারত্বের সংখ্যা। ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে সফল হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তার জন্য কৃষিঋণ সহজ ও সহজলভ্য করতে হবে।
লেখক : মিডিয়া ব্যক্তিত্ব