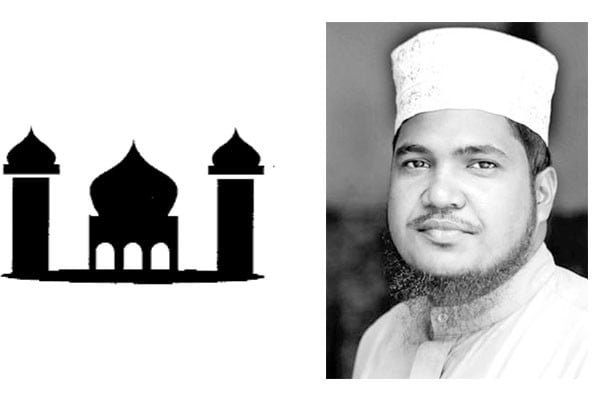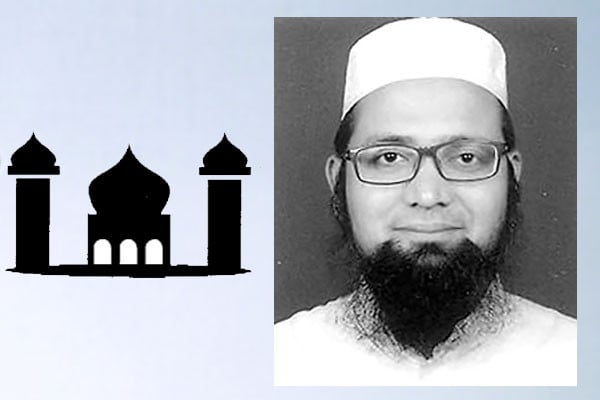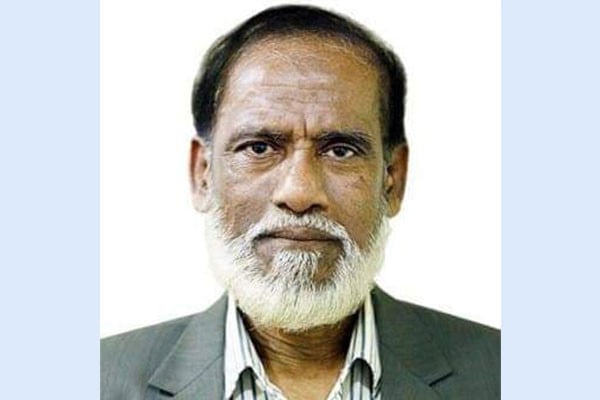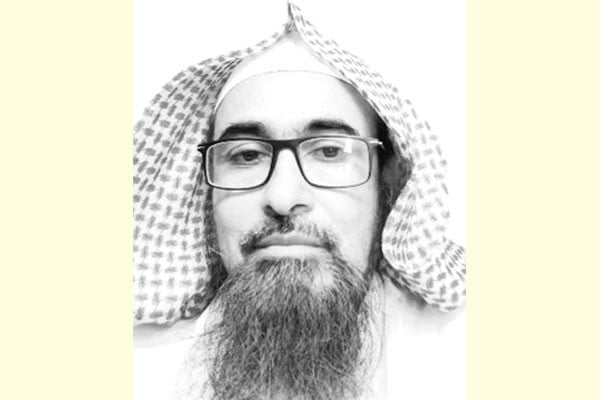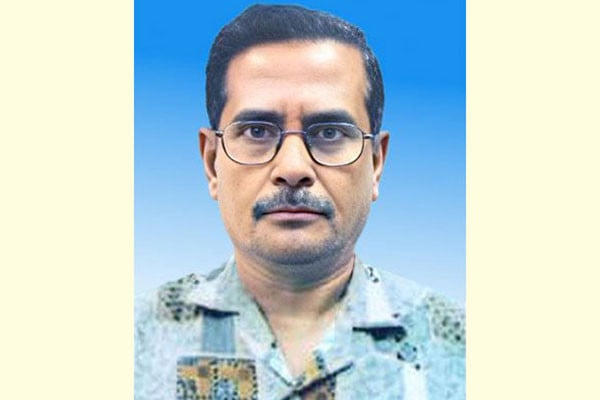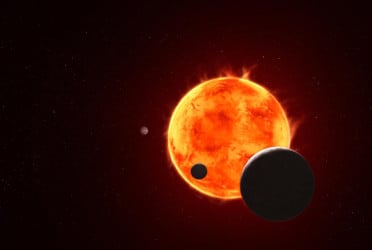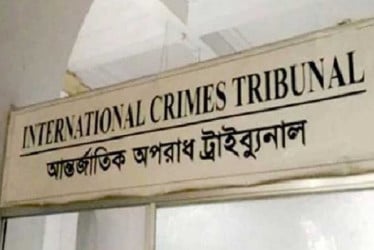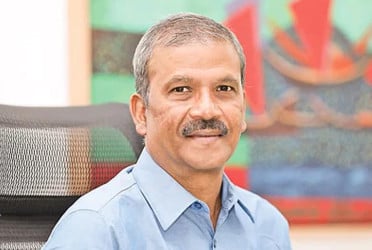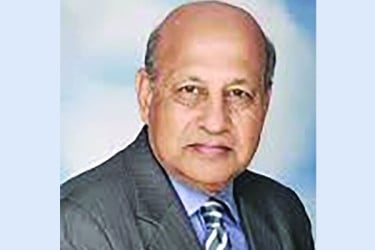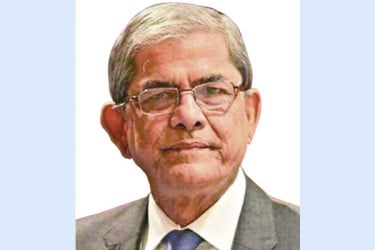ইন্টারনেট, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে যে কোনো তথ্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। যাদের এই সুযোগগুলো আছে, তারা অধিকাংশ সময়ই এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ার অন্য ব্যবহারকারীরা এসব দেখেন, শেয়ার করেন, অনেকে আবার নতুন কিছু সংযোজন করেন। অতঃপর চলতে থাকে পক্ষে-বিপক্ষে কমেন্ট। এভাবে অনেক সত্য ঘটনা অসত্যে পরিণত হয়, আবার অনেক অসত্য ঘটনা সত্য বলে প্রচার করা হয়। আর এ কাজটিতে মারাত্মকভাবে সহযোগিতা করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় কিংবা পুরোনো কোনো ছবি বা ঘটনা কাট-পেস্ট করে বর্তমান সময়োপযোগী করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে ফায়দা লুটছে। বুঝে না বুঝে কিংবা শুধু ভিউ বাড়ানোর জন্য এমনটি করে থাকেন অনেকে। এরপর শুরু হয় নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। একপর্যায়ে উত্তেজিত জনতা সামাজিক যোগাযোগ ও সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্র ধরে নেমে আসে রাস্তায়, শুরু হয় মারামারি, খুনাখুনি ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক ও পারিবারিক অনেক অশান্তি ও কোন্দলের প্রধান কারণ হচ্ছে এসব অপকর্ম, যা ছড়ায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক তথ্য, অপতথ্যে, সংবেদনশীল ও উসকানিমূলক খবরের ছড়াছড়ি দেখা। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসব অপতৎপরতা আরও বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে এসব ঘটনার সঙ্গে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত জড়িত। সংবেদনশীল তথ্য হলো, এমন তথ্য যা প্রকাশের ফলে ব্যক্তি, সংস্থা বা উভয়ের জন্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এ ধরনের তথ্য শেয়ার করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সংবেদনশীল তথ্য সাধারণত গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা প্রবিধানের আওতাভুক্ত থাকে এবং এর ভুল প্রকাশ আর্থিক, আইনি এবং খ্যাতিগত ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তির তথ্য, আর্থিক বিবরণ, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য বা ব্যবসায়িক গোপনীয় তথ্যের মতো সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা এবং তা সুরক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। কতগুলো সংবেদনশীল তথ্যে যেমন : ব্যক্তিগত নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা, জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ক্রেডিট কার্ডের তথ্য ইত্যাদি। আর্থিক তথ্য যেমন বেতন, আর্থিক লেনদেন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি। চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য যেমন রোগীর ইতিহাস, রোগের বিবরণ, চিকিৎসার বিবরণ ইত্যাদি। পেশাগত তথ্য যেমন কর্মীর বেতন, কর্মীর পারফরম্যান্স ইত্যাদি। আইনগত তথ্য যেমন মামলার বিবরণ, আইনি পরামর্শ ইত্যাদি। ব্যবসায়িক তথ্য যেমন বাণিজ্যিক গোপনীয়তা, ব্যবসার কৌশল ইত্যাদি। নিরাপত্তার স্বার্থে সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের তথ্য ফাঁস হওয়া বা অপব্যবহার হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।
কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সংবেদনশীল বা গোপনীয় তথ্য অননুমোদিত ব্যক্তি বা দলের হাতে চলে যাওয়াকে ডেটা লঙ্ঘন (Data breach) বলে। এটি সাধারণত হ্যাকিং, ম্যালওয়্যার বা অন্য কোনো নিরাপত্তাত্রুটির মাধ্যমে ঘটে থাকে। ডেটা লঙ্ঘন হলো, সংবেদনশীল বা গোপনীয় তথ্যের অননুমোদিত প্রকাশ বা ক্ষতি। হ্যাকিং, ম্যালওয়্যার বা অন্যান্য নিরাপত্তাত্রুটির কারণে ঘটতে পারে। ব্যক্তিগত তথ্য, আর্থিক রেকর্ড অথবা কোম্পানির গোপন ব্যবসার তথ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ব্যবহারকারীদের পরিচয় চুরি, আর্থিক ক্ষতি বা সুনামহানি হতে পারে, যা ফিশিং এবং সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শামিল। এই দুটোই সাইবার ক্রাইমের একটি রূপ, যেখানে ব্যবহারকারীদের তাদের ব্যক্তিগত তথ্য যেমন পাসওয়ার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিবরণ ইত্যাদি প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ করা হয়। ফিশিং সাধারণত ইমেইল বা টেক্সট বার্তার মাধ্যমে করা হয়, যেখানে ব্যবহারকারীকে একটি বিশ্বস্ত সংস্থার ছদ্মবেশে একটি লিঙ্কে ক্লিক করতে বা একটি ফাইল ডাউনলোড করতে বলা হয়। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যা ফিশিংসহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের ম্যানিপুলেট করে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়। একইভাবে ইনসাইডার থ্রেট (Insider threat) হলো এমন একটি নিরাপত্তাঝুঁকি যা একটি প্রতিষ্ঠানের ভিতরের কেউ (যেমন কর্মচারী, ঠিকাদার ইত্যাদি) তৈরি করে। এই ঝুঁকি তাদের অনুমোদিত অ্যাকসেস ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করার মাধ্যমে দেখা দেয়। এ ক্ষতি ডেটা চুরি, সিস্টেম হ্যাক করা অথবা সংবেদনশীল তথ্যের অপব্যবহারের মাধ্যমে হতে পারে।
লেখক : অধ্যাপক এবং তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়