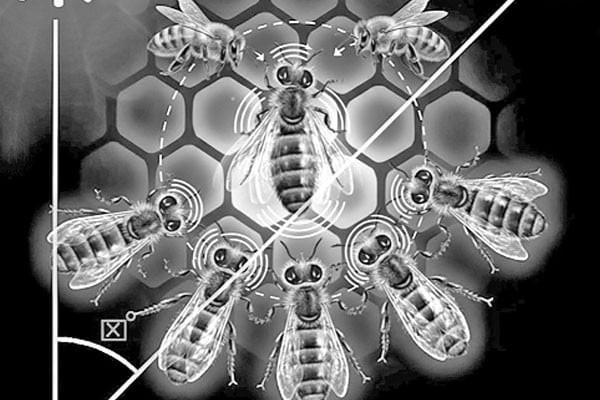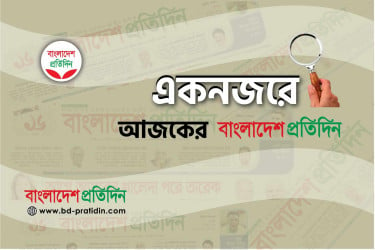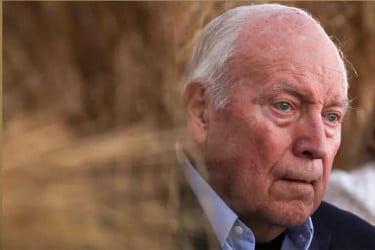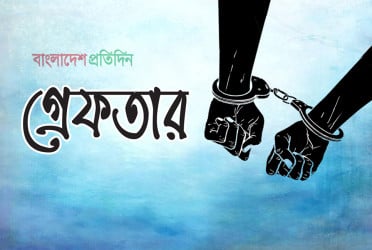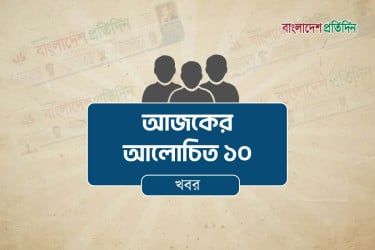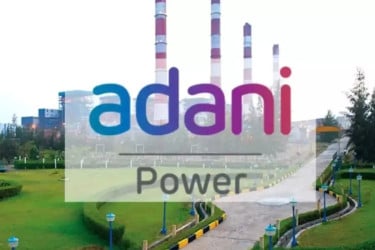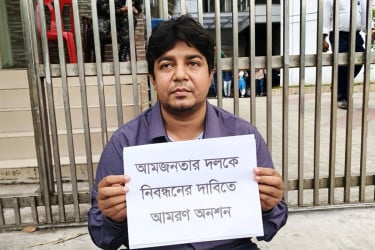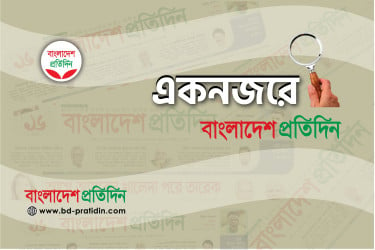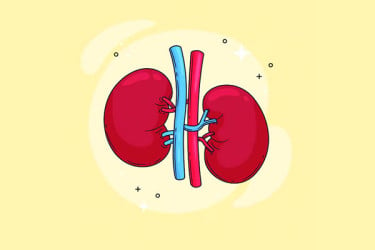পৃথিবীর ভূগর্ভ যেন এক জীবন্ত অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডের মুখের আবরণ বারবার ফেটে বেরিয়ে আসে লাভা, ছাই ও গ্যাস। ভূতাত্ত্বিকরা এই অঞ্চলকে বলেন ‘রিং অব ফায়ার’। এটি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে বিস্তৃত এক অগ্নিপূর্ণবলয়, যেখানে পৃথিবীর প্রায় ৭৫ শতাংশ সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অবস্থান। শুধু তাই নয়, বিশ্বের ৯০ শতাংশ বড় ভূমিকম্পও ঘটে এই অঞ্চলকে ঘিরে। আর একটি বড় অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্প বদলে দিতে পারে বিস্তৃত এলাকার মানচিত্র। বাড়িঘর ধ্বংস, প্রাণহানি, কৃষিজমি নষ্ট, এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণও হতে পারে বড় বিস্ফোরণ। এজন্য রিং অব ফায়ারকে মানবসভ্যতার জন্য এক চিরন্তন হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, রিং অব ফায়ার অঞ্চল মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় কিছু বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে। ১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া বিস্ফোরণ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, এর শব্দ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জায়গা থেকে শোনা গিয়েছিল। সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতে প্রায় ৩৬ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৯১ সালে ফিলিপাইনের পিনাতুবো অগ্ন্যুৎপাত প্রায় ৮০০ মানুষ মারা যায়। গৃহহীন হয় লক্ষাধিক। এই অগ্ন্যুৎপাত থেকে নির্গত ছাই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় দুই বছর ধরে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমিয়ে দেয়। বাংলাদেশ কি ঝুঁকিতে? ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, বাংলাদেশ ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থল থেকে দূরে অবস্থান করছে। এখানে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি নেই, ভবিষ্যতেও সরাসরি কোনো অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা নেই। এখানকার সবচেয়ে নিকটবর্তী সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলো ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার ও আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলে। সেগুলোর প্রভাব বাংলাদেশে সরাসরি পড়বে না। তবে পরোক্ষ ঝুঁকি রয়েছে। বড় ধরনের অগ্ন্যুৎপাত হলে প্রচুর আগ্নেয় ছাই ও সালফার ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সূর্যের আলো কমে গিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা সাময়িকভাবে কমে যেতে পারে। এতে বাংলাদেশের কৃষি, বৃষ্টিপাতের ধরন এবং মৌসুমি জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ১৮১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার তাম্বোরা অগ্ন্যুৎপাতের প্রভাবে বৈশ্বিক জলবায়ু বদলে গিয়েছিল। পরের বছরটিতে পৃথিবীতে গ্রীষ্মকাল আসেনি। তখন বাংলাদেশসহ এশিয়ার কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।
মূলত রিং অব ফায়ার প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এক অগ্নিবলয়। এটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে শুরু হয়ে জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের টেকটনিক প্লেটগুলো প্রতিনিয়ত একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। কখনো ভেঙে যাচ্ছে, কখনো সরে যাচ্ছে। ফলে ভূত্বকের নিচের ৭০০-১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গলিত শিলা ভেন্ট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে।
তথ্য বলছে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১ হাজার ৩৫০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এর অধিকাংশই রিং অব ফায়ার অঞ্চলে। শুধু ইন্দোনেশিয়ায়ই সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সংখ্যা শতাধিক।
জাপানে আছে প্রায় ১২০টি। আবার যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও এই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। রিং অব ফায়ার অঞ্চলে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বাস করে। শুধু ইন্দোনেশিয়ায়ই প্রায় ২৭ কোটি মানুষের জীবনযাপন সরাসরি আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাপানের টোকিও বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ নগরী। আবার চিলি, মেক্সিকো ও পেরুতে আগ্নেয়গিরি কার্যক্রমে প্রায়ই মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়। ঘনবসতি, দুর্বল অবকাঠামো এবং সীমিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনেক দেশের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়। এসব আগ্নেয়গিরি মানবসমাজের জন্য একদিকে যেমন হুমকি, অন্যদিকে ভৌগোলিক পরিবর্তনের শক্তিশালী চালিকাশক্তি। আগ্নেয়গিরির ইতিবাচক প্রভাবও কম নয়। লাভা ঠান্ডা হয়ে উর্বর মাটি তৈরি করে, যা কৃষির জন্য উপকারী। খনিজ সম্পদের বিশাল ভান্ডারও ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। পর্যটন শিল্পে হাওয়াই, আইসল্যান্ড বা জাপানের আগ্নেয়গিরি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ।
আধুনিক বিজ্ঞান আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণে অনেক অগ্রগতি করেছে। সিসমিক কার্যকলাপ, গ্যাস নির্গমন ও ভূমি ফোলাভাব মাপার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস দিতে পারেন। তবে নির্ভুলভাবে তার সময় ও মাত্রা বলা এখনো অসম্ভব। ফলে রিং অব ফায়ার অঞ্চলের মানুষের জন্য এখনো সচেতনতা, দুর্যোগ-পরিকল্পনা ও নিরাপদ অবকাঠামোই প্রধান সুরক্ষা।
রিং অব ফায়ার মানবসভ্যতার কাছে যেমন আতঙ্ক, তেমনই এক প্রাকৃতিক বিস্ময়। এখানকার অগ্ন্যুৎপাত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবী একটি জীবন্ত গ্রহ, যার ভিতরে চলছে অগ্নির অদৃশ্য খেলা। ভূপৃষ্ঠের যখন বরফ পড়ছে, তখন ভূগর্ভে ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার লাভা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। মানুষ প্রযুক্তি দিয়ে এই ঝুঁকি কিছুটা কমাতে পারলেও প্রকৃতিকে পুরোপুরি বশ মানাতে পারেনি। তাই রিং অব ফায়ার আজও মানবসভ্যতার জন্য এক চিরন্তন হুমকি হয়ে রয়ে গেছে।