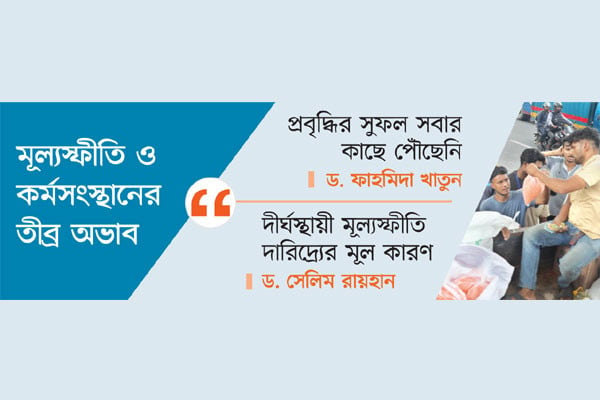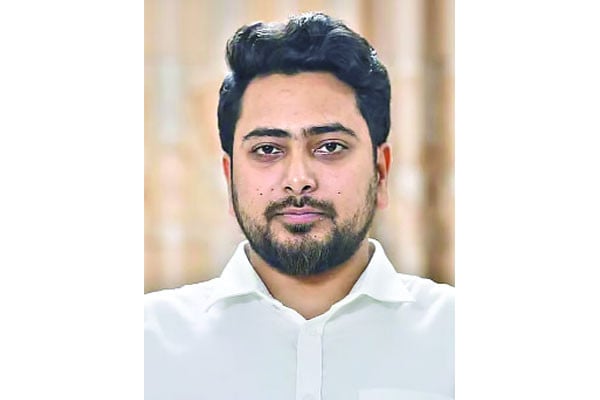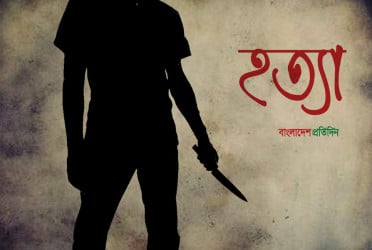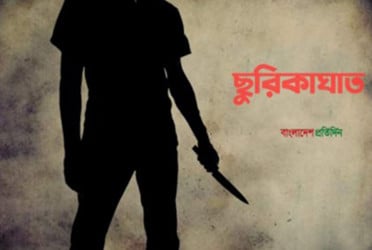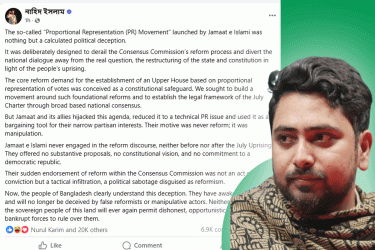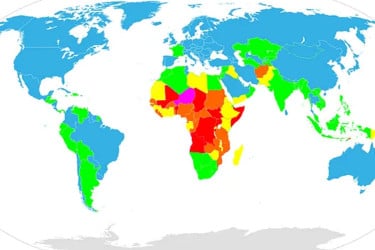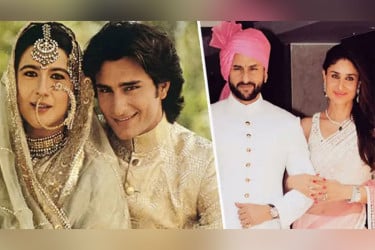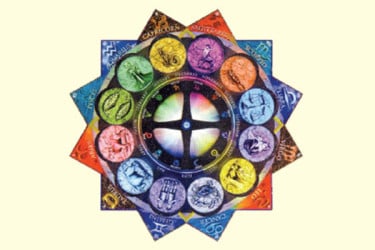বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা তিন দশক ধরে চললেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই ধারা উল্টো দিকে ঘুরেছে। নতুন গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশে বর্তমানে প্রতি চারজনের একজন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, একটি বড় অংশ এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যে, সামান্য আঘাত-অসুস্থতা, চাকরি হারানো কিংবা হঠাৎ সংকট তাদেরও দরিদ্রতার কাতারে ঠেলে দিতে পারে।
করোনা মহামারির আগ পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার ক্রমেই কমছিল। অথচ তিন বছরের ব্যবধানে চিত্র বদলে গেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) করা সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশের দরিদ্রতার হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশে। অথচ ২০২২ সালে সরকারি হিসাবে এ হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। অর্থাৎ অল্প সময়ে প্রায় ১০ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। জরিপে আরও বলা হয়েছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাইরে প্রায় ১৮ শতাংশ পরিবার এখন ঝুঁকির মুখে। আয়ের উৎস সামান্য ব্যাহত হলেই বা খরচ বেড়ে গেলেই তারা সঞ্চয় ধরে রাখতে পারছে না। বিশেষ করে চরম দারিদ্র্যের হার দ্রুত বেড়েছে। ২০২২ সালে যেখানে তা ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে। সংখ্যার হিসাব আরও স্পষ্ট চিত্র দেয়। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৭ কোটি, পরিবারের সংখ্যা ৪ কোটি ১০ লাখ। সেই হিসাবে অন্তত পৌনে ৫ কোটি মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে। জনসংখ্যা বাড়ায় প্রকৃত সংখ্যা আরও বড় হতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে যে সূচক ব্যবহার করে, তাতে একজন মানুষের প্রতিদিন গড়ে অন্তত ২ হাজার ১২২ ক্যালরির খাবার ও ন্যূনতম খাদ্যবহির্ভূত খরচ মেটানো প্রয়োজন। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যের দাম অঞ্চলভেদে ভিন্ন ও ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় অনেকেই এই মানদণ্ড পূরণ করতে পারছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। একটি পরিবারের মাসিক আয়ের প্রায় ৫৫ শতাংশ এখন শুধু খাবার কিনতেই খরচ হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ও বাড়ছে। ফলে আয়ের তুলনায় ব্যয় বাড়তে থাকায় সঞ্চয়ের সুযোগ কমে যাচ্ছে। জরিপে উঠে এসেছে, প্রায় ৪০ শতাংশ পরিবারের ঋণের বোঝা আগের তুলনায় বেড়েছে। এতে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এ পরিস্থিতি শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেই নয়, নিম্ন মধ্যবিত্তকেও নতুন করে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন মনে করেন, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হলেও তার সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছেনি। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘উচ্চ আয়ের মানুষের আয় দ্রুত বেড়েছে, কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষের প্রকৃত আয় তেমন বাড়েনি। মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষ ওপরে উঠতে পারেনি, বরং অনেকে আবার নিচে নেমে গেছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে খাদ্য, জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবার তাদের আয়ের বড় অংশ খাবারে খরচ করায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারছে না। এ ছাড়া শিল্প ও সেবা খাত সম্প্রসারিত হলেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি। বিপুলসংখ্যক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করলেও তাদের জন্য স্থায়ী ও মানসম্মত কাজের সুযোগ সীমিত। ফলে তারা অনানুষ্ঠানিক ও কম আয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যা টেকসই নয়।’ সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান দারিদ্র্য বৃদ্ধিকে দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতির সরাসরি ফল বলে মনে করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে, অথচ মানুষের প্রকৃত আয় বাড়েনি। এর ফলেই এক বড় অংশ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে।’ তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, ‘নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা সবচেয়ে দ্রুত অবনতি হচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রার মান কমে গেছে এবং তারা সঞ্চয় ভেঙে বা ধারদেনা করে খরচ মেটাচ্ছে।’ সেলিম রায়হান বলেন, ‘মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। কারণ সমস্যার সঙ্গে কর্মসংস্থান সংকটও যুক্ত হয়েছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার প্রত্যাশিত নয়, কর্মমুখী খাতে বিনিয়োগও কম। দক্ষতা অর্জন করেও তরুণরা কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাচ্ছে না। তার মতে, ‘শুধু দ্রব্যমূল্য কমালেই হবে না, একই সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আরও শক্তিশালী করতে হবে।’