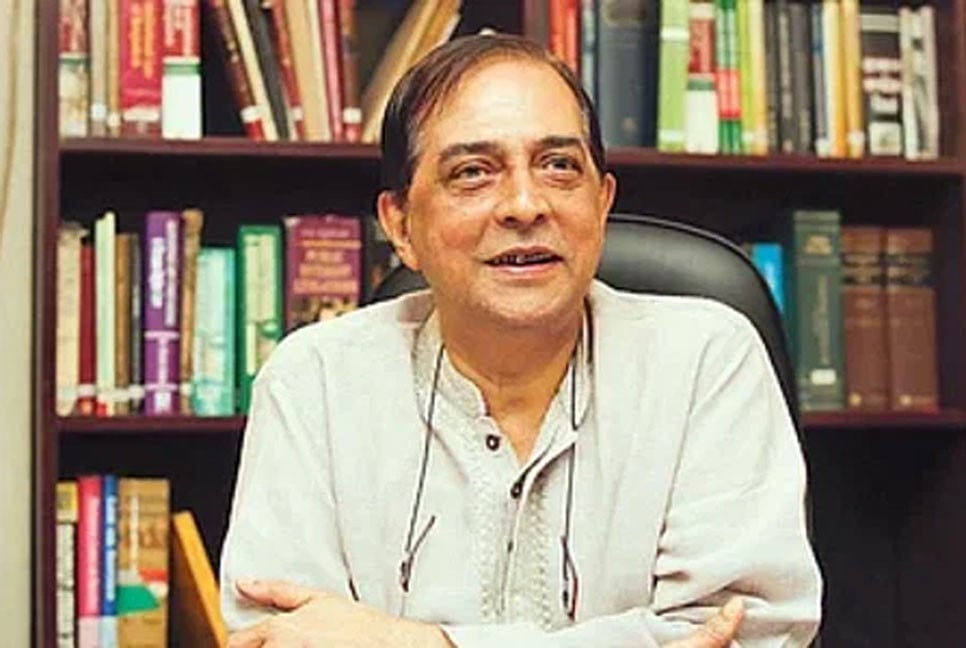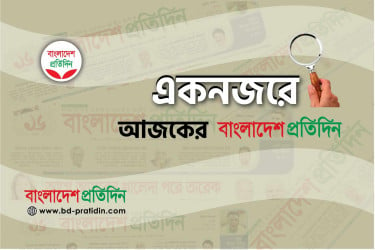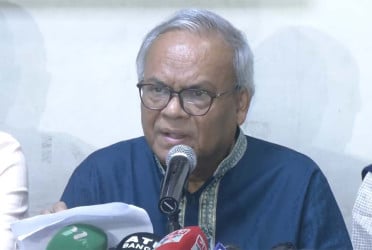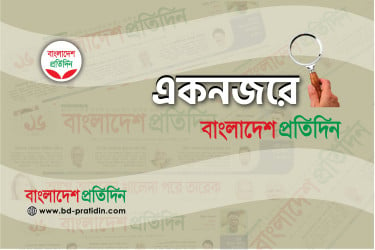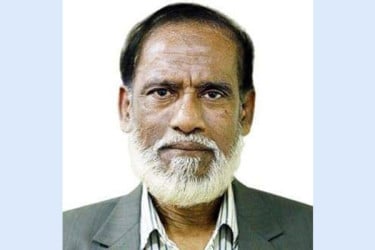নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা নিয়ে হাইকোর্টের একটি পর্যবেক্ষণ এবং রূপরেখা বা রূপকল্প রাজনৈতিক অঙ্গনে আবার কিছুটা 'চঞ্চলতা' সৃষ্টি করেছে। দশম সংসদে অর্ধেকের বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বৈধতার বিষয়ে এক মামলার পর্যবেক্ষণে উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) দুটি রূপরেখার কথা বলেছেন। প্রথমটিতে বলা হয়, 'সংসদের মেয়াদ পুরো হলে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে সংসদ ভেঙে যাওয়ার দিন থেকে ৯০ দিনের জন্য সব দল থেকে ৫০ জন নতুন মন্ত্রী নেওয়া হবে। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগ হবে। তবে বর্তমান সংসদের নির্বাচন বয়কট করার কারণে বিএনপি ও জামায়াত একাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকারে কোনো মন্ত্রী দিতে পারবে না। কিন্তু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদের আওতায় বয়কটকারী দলগুলো পাঁচজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দিতে পারবে।' দ্বিতীয় রূপরেখায় বলা হয়, 'কোনো নির্বাচনে বিজয়ী দল প্রথম চার বছর দেশ শাসন করবে। এরপর প্রধান বিরোধী দল শেষ এক বছর দেশ চালাবে। তবে বিরোধী দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাপ্ত মোট ভোটের অন্তত অর্ধেক সমান ভোট পেতে হবে। তা না পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পাঁচ বছরের শাসন মেনে নিতে হবে বিরোধী দলকে।' হাইকোর্টের এ পর্যবেক্ষণ এমন একটা সময়ে পাওয়া গেল, যখন মধ্যবর্তী বা আগাম নির্বাচন নিয়ে দেশে ও বিদেশে অর্থবহ আলাপ-আলোচনা চলা বা শুরু হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আকস্মিক মোড় নেওয়ার একটা সম্ভাবনার কথা বলছেন দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও। বিএনপি চেয়ারপারসনের একটি মন্তব্যকে তারা এই মোড় পরিবর্তনের লক্ষণ বা ইঙ্গিত বলে মনে করছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম সংসদ নির্বাচন বয়কটের মূল ইস্যুই ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত, যা পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন ও ২০-দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্পষ্টতই সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'আমি বলছি না যে, তত্ত্বাবধায়কই হতে হবে।' এটা তাৎপর্যপূর্ণ একটা নীতিগত ঘোষণাই বটে। নির্বাচন বর্জন এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে তিন মাসের সহিংস আন্দোলনের প্রধান ইস্যুর ব্যাপারে ছাড় দেওয়ায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমঝোতামূলক সমাধানে শুধু উইন্ডোই নয়, সদর দরজাই বেগম জিয়া খুলে দিয়েছেন। লীগ সরকারের মূল আপত্তি তো তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নিয়েই। এরপর একটা ইনক্লুসিভ আগাম নির্বাচন আয়োজনে তাদের আর ভয় থাকার কথা নয়। আর প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরগতভাবে সরকারের নীতিনির্ধারকরাও তো জানেন এবং মানেন যে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে নৈতিক বৈধতার সংকট আছে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক বেসরকারি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান স্ট্র্যাটফোরের এক বিশ্লেষণেও বলা হয়েছে, '২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচনের পর থেকে সহিংসতায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে আসবেন। তবে দলটি নতুন একটি নির্বাচন চায়। অনড় অবস্থান থেকে খালেদা জিয়ার সরে আসার ফলে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সমঝোতার। সামনের সপ্তাহ, মাসগুলোয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে পর্দার আড়ালে নতুন করে সমঝোতা আলোচনা শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।' তাতে আরও বলা হয়, 'বিরোধী দল বিএনপি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মধ্য-ডানপন্থি এবং ইসলামী দলগুলোর একটি জোটের নেতৃত্বে রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলোয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, নিরাপত্তা বাহিনী, ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার এবং অন্যান্য বেসরকারি টার্গেটগুলোয় কট্টরপন্থিদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সহিংস মৌলবাদীদের থেকে নিজেদের দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্রধান বিরোধী দল। দলটির প্রতিবাদ কৌশলের কার্যকারিতা কমে আসায় বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিরোধী দলের একাংশ তাদের কিছু দাবি থেকে সরে আসতে রাজি হতে পারে। যেমন- নির্বাচন আয়োজনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা। এতেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল জটিল সমঝোতা প্রক্রিয়ায় যেতে পারে। দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বেসরকারি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানটির বিশ্লেষণ বেশ মিলে যায়। বেগম খালেদা জিয়ার আরও একটি অবস্থানেও নীতিগত পরিবর্তন হয়েছে। সেটি হচ্ছে তার ভারতনীতি। ২০-দলীয় জোটের দ্বিতীয় প্রধান শরিক জামায়াতে ইসলামীসহ আরও দু-একটি ইসলামী দল এবং জামায়াত ও বিএনপির ডানপন্থিদের প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত বলে কথিত কয়েকটি খুচরা-খাচরা দলের তা পছন্দ হওয়ার কথা নয়। বিএনপি নেত্রী তা আমলে নিচ্ছেন না। এতদিন একটি বিত্তশালী ডানপন্থি গ্রুপের প্রভাবে যেখানে বিএনপিতে এমন একটা ভাব ছিল যে, পারলে তারা দিল্লি দখলই করে ফেলবে, কারণে-অকারণে সর্বদা ছিল ভারত-বিরোধিতার ভ্রান্তিবিলাস, সেখান থেকে সরে এসে বিএনপি এখন দিল্লির 'সখী' হতে চায়, চায় নিবিড় বন্ধুত্ব। এটাও আওয়ামী লীগ-বিএনপির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির একটি নন্দিত উৎস হতে পারে।
দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপাতত ও দৃশ্যত শান্ত। কিন্তু ভিতরগত আবহাওয়াটা গুমোট। লীগ সরকারের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি আশু একটি নির্বাচন আদায়ের চেষ্টা করছে। দৃঢ়ভাবেই বলা যায়, গণতান্ত্রিক দুনিয়ার বাঘা বাঘা রাষ্ট্রগুলো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ এমনকি জাতিসংঘও চায় সংলাপ-সমঝোতার মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্রুত একটি অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক। বিএনপিসহ সরকারবিরোধীদের দাবি এবং আন্তর্জাতিক মহলের এ দাবির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন-সহানুভূতির কারণ কারোরই অজানা থাকার কথা নয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দশম সংসদ নির্বাচনটি ছিল সম্পূর্ণই একপেশে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৪২টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিকল্পধারা, কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন জেএসডি, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, আন্দালিব পার্থের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি, ন্যাপ ও বিভিন্ন ইসলামী দলসহ ৩২টি রাজনৈতিক দলই ওই নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে শাসক লীগ ছাড়া স্বৈরাচার এরশাদের জাতীয় পার্টি (এরশাদ নির্বাচনে যেতে রাজি ছিলেন না। তার স্ত্রী রওশন এরশাদের নেতৃত্বে ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জিয়াউদ্দিন বাবলু, তাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখকে দিয়ে পার্টির একাংশকে নির্বাচনী টোপ গেলানো হয়। এরশাদকে নিয়ে মঞ্চায়ন করা হয় কৌতুক নাটক) ছাড়া প্যাডসর্বস্ব কটি দল- যাদের কয়েকজন বিনা ভোটে অথবা নৌকা মার্কা নিয়ে পাতানো নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হন, কয়েকজন মন্ত্রিত্বের ভাগও পান।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০। এর মধ্যে ১৫৩ আসনে কোনো নির্বাচন-ভোটাভুটি হয়নি। সাংবিধানিক শাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষার অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচনটি করে নেওয়া হয়। স্থাপন করা হয় অদ্ভুত এক 'ভাগাভাগির গণতন্ত্র'। সাংবিধানিক শাসনের ধারাবাহিকতার কথা বলে প্রচ্ছন্নে 'অগণতান্ত্রিক শক্তির' ক্ষমতা দখলের ভয় দেখানো হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছে, এ সরকার কতটা গণতান্ত্রিক? আমাদের দেশে শুধু বর্তমান লীগ সরকার নয়, এ পর্যন্ত এরশাদ স্বৈরাচার ছাড়া বিএনপি-আওয়ামী লীগ যারাই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে, তারা কেউ প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণ করেনি। এরশাদ ছিলেন জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা জবরদখলকারী ঘৃণ্য স্বৈরাচার, খালেদা-হাসিনার সরকারকে বলা হয় নির্বাচিত স্বৈরাচার। যে দল যখন ক্ষমতায় ছিল ও থাকে, অন্য দল তাদের স্বৈরাচার ডাকতে ডাকতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনটি কোনো বিবেচনায়ই একটি আদর্শ নির্বাচন ছিল না। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত জটিলতার সূচনা হয় ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়ার পর। নবম সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লীগ সরকার অনৈতিক কাজটি করেছে। অনৈতিক বললাম এ কারণে যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি সর্বদলীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গৃহীত হয়েছিল। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেতাদের পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস থেকেই নির্বাচনকালীন ব্যতিক্রমধর্মী এ তত্ত্বাবধায়ক কনসেপ্টের উদ্ভব। সাজেদা চৌধুরীকে চেয়ারম্যান এবং সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে কো-চেয়ারম্যান করে যে বিশেষ সংবিধান সংশোধন কমিটি করা হয়েছিল, সেই কমিটির সব সদস্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুই দিন আগেও কমিটির কো-চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ব্যবস্থাটি থাকছে। পরে দেখা গেল একজনের ইচ্ছায় সর্বদলীয় একটি সিদ্ধান্ত অনেকটা একদলীয় সিদ্ধান্তেই বাতিল হয়ে যায়। নির্বাচন নিয়ে সংকট, আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা এবং সংসদ ও সরকারের সর্বজনীনতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কারণটা যে এখানেই, এটা কারও না বোঝার কারণ নেই।
বিএনপি-জামায়াত জোটের, বিশেষ করে বিএনপির এখন মূল এজেন্ডাই হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী বা আগাম নির্বাচন। ২০১০ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে সরকারের 'দলদাস'রা মিডিয়ায় কী বললেন, কী বলছেন সেটা কোনো ধর্তব্য বিষয় নয়। হালুয়া-রুটির আশায় অনেকে অনেক কিছু এমন করতে পারেন। এরই মধ্যে অনেকে অনেক কিছু পেয়েছেন; কেউ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদ, ভালো চাকরি, ভালো পোস্টিং (বেশি ঘুষের জায়গা), রেডিও-টিভির চ্যানেল ইত্যাদি। যারা এখনো পাননি তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু সরকার মনে হয় নমনীয়। শাসক লীগের সাধারণ সম্পাদক যদিও মাঝে মাঝে বলছেন যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা নেই; এটা দলের এমনকি তারও চূড়ান্ত কথা বলে মনে হয় না। কারণ এর আগেই তিনি বলে রেখেছেন যে, দলীয় ফোরামে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি, তবে এ ব্যাপারে সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা দিয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। তিনি চাইলে মেয়াদ ফুরানোর আগেও যে কোনো সময় নির্বাচন হতে পারে। বেগম জিয়ার নতুন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এমন বক্তব্য দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া যায় এবং এও বলা যায় যে, বক্তব্যটি ইতিবাচক। খালেদা জিয়া এটা ঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে, তত্ত্বাবধায়কের দাবি থেকে সরে না এলে শেখ হাসিনা মধ্যবর্তী বা আগাম নির্বাচনের ব্যাপারে রাজি হবেন না। তার বিদেশি মিত্ররাও হয়তো তাকে এমন পরামর্শই দিয়েছেন যে, 'তত্ত্বাবধায়কের দাবি ছেড়ে দাও'।
তত্ত্বাবধায়কেই যত ভয় শেখ হাসিনার। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক হলেই যে বিএনপি-জামায়াত এখন ক্ষমতায় চলে আসবে, তারও কোনো গ্যারান্টি নেই, তা খালেদা জিয়াও বোঝেন। কারণ, তার সংগঠনের বেহাল অবস্থা অনেক দিন থেকেই। জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১৫- এ তিন মাসে হঠকারী আন্দোলনে নেমে বড় একটা আছাড় খেয়েছে বিএনপি। অনেকটা হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার মতো। এ অবস্থায় জনগণের ইতিবাচক-নেতিবাচক সমর্থন মিলিয়ে অবস্থানটা মন্দ না হলেও তা ক্যাশ করার সাংগঠনিক সামর্থ্য বিএনপির নেই। মনোনয়ন প্রশ্নে বিলেতি হস্তক্ষেপ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। তার পরও একটা আগাম নির্বাচন হলে তাতে অংশ নিয়ে সংসদে একটা সম্মানজনক অবস্থান দখল করে জেল-জুলুম, মামলা-মোকদ্দমাসহ নানা নিগ্রহ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের রক্ষা তথা দলরক্ষা এবং তারেক রহমানকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে 'বার্গেইন' করার একটা সাংবিধানিক শক্তি দল অর্জন করতে পারে। আর যদি জনগণের ম্যান্ডেট ক্ষমতায় যাওয়ার অনুকূল হয়ে যায় তো কথাই নেই। অন্যদিকে তেমন একটি ইনক্লুসিভ নির্বাচনে সরকারের জন্যও সুবিধা আছে। বর্তমানে জনসমর্থনের দিকটা বাদ দিয়ে সাংগঠনিক দিক বিবেচনা করলে বলতে হবে, আওয়ামী লীগের সংগঠন তুলনামূলকভাবে বিএনপির সংগঠন থেকে শক্তিশালী এবং আদর্শগতভাবে শ্রেয়তর। তারা নির্বাচন বোঝে। জেতার কৌশল প্রয়োগ করতে জানে। চাকর-বাকর মার্কা লোক দিয়ে পরিচালিত বিএনপিকে বর্তমান অবস্থায় রেখে মধ্যবর্তী বা আগাম নির্বাচন দিলে ফসল তাদের ঘরে ওঠার সম্ভাবনা আছে। যদি তা নাও হয়, নিরাপদ একটা বহির্গমন পথ (সেফ এক্সিট) অন্তত পাওয়া যাবে। বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে তাতে সরকার ও সরকারি দল সুখকর অবস্থানে নেই। রাজনীতি ও গণতন্ত্র চর্চার সব পথ রুদ্ধ করে রাখার পরিণতি কখনো কোথাও শুভ হয়নি। তাই আগাম নির্বাচনের কথা সরকার ভাবছে বা ভাববে, এমন ধারণা করাই যায়। নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা নিয়ে যে জটিলতা, সে ব্যাপারে সম্প্রতি হাইকোর্টের দেওয়া পর্যবেক্ষণটি 'বাতিঘর' হিসেবে কাজ করতে পারে। অনেকেই আলো দেখছেন স্পষ্টভাবে।
২০১০ সালে সুপ্রিমকোর্টে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর উচ্চ আদালতের এ পর্যবেক্ষণ এমন একটা সময় জাতির সামনে এলো, যখন মধ্যবর্তী বা আগাম নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে অর্থবহ আলাপ-আলোচনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনও শোনা যায়, কোনো দলের পক্ষাবলম্বন না করে ভারতের বর্তমান বিজেপি সরকারও বাংলাদেশে দ্রুত একটি অর্থবহ ইনক্লুসিভ ইলেকশন হওয়ার পক্ষে নমনীয় হতে পারে।
২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সব বিষয়ই ভারতের জানা থাকার কথা। কাজেই নির্বাচনমুখী গণতন্ত্রের দেশ ভারত প্রতিবেশী বাংলাদেশে অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত একটি সরকার চাইতেই পারে, সরকার যে দলেরই হোক। বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি ছেড়ে দেওয়ায় এবং উচ্চ আদালত থেকে নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নে একটি পর্যবেক্ষণ পাওয়ার ফলে আশাবাদ জাগছে, জাতীয় রাজনীতির প্রধান দুই পক্ষ জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি, জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় স্থিতি রক্ষার স্বার্থে দ্রুত একটা রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছবে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বিএনপি ও আইনমন্ত্রী প্রায় একই ধরনের নেতিবাচক কথা বলেছেন। এটা স্রেফ রাজনৈতিক খেলা বলে মনে হয়। তা ছাড়া ভিন্নমত থাকতেই পারে। কিন্তু উচ্চ আদালতের এ পর্যবেক্ষণকে তারা আলোচনার সূত্র হিসেবে তো বিবেচনা করতে পারেন। সমঝোতার স্বার্থে গ্রহণযোগ্য একটা জায়গায়ও পৌঁছতে পারেন। উচ্চ আদালত একটা সূত্র ধরিয়ে তো দিলেন আমাদের রাজনীতিবিদদের। বিশেষ করে শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে যে 'অন্ধকার কারাগারে' বন্দী আছেন, সেখান থেকে দুজনের জন্যই একটা সেইফ এক্সিট হতে পারে মহামান্য হাইকোর্টের এ রূপরেখা।
লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট
ই-মেইল : [email protected]