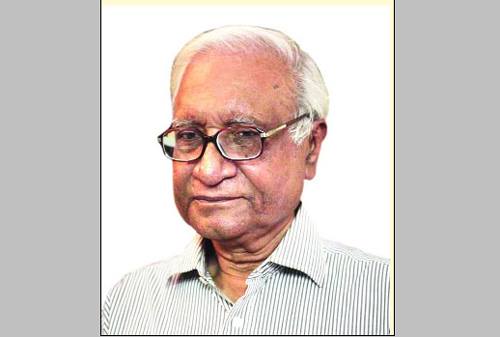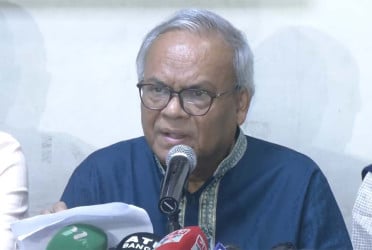অবস্থাটা ভালো নয়। তা ভালো কবেই বা ছিল। ছিল না। কিন্তু সেটা কোনো সান্ত্বনা নয় এখনকার দুর্দশার জন্য। বর্তমানের অবস্থাটা অসহ্য ঠেকছে আরও দুই কারণে। প্রথমত অবস্থাটা বদলাবার জন্য আমরা দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি, দ্বিতীয়ত অতীতে বদলাবে বলে একটা আশা দেখা যেত, এখন যেটা উজ্জ্বল নয়।
তাছাড়া দুর্দশার লক্ষণগুলোও রীতিমতো উদ্বেগজনক। অর্থনীতি টিকে আছে, এবং কিছু কিছু উন্নয়নও দেখা যাচ্ছে; কিন্তু এই উন্নয়ন প্রধানত শ্রমনির্ভর। কৃষক শ্রম দিচ্ছে খেতখামারে, শ্রমিক খাটছে কলকারখানায়, বিশেষ করে গার্মেন্টসে; দেশের লোকেরা বিদেশে গিয়ে পরিশ্রম করছে। বিনিয়োগ উৎসাহব্যঞ্জক নয়, আমদানি বেড়ে যাচ্ছে রপ্তানির তুলনায়, বিদেশি কোম্পানি ঢুকে পড়ছে উত্পাদনের ক্ষেত্রে; বাজার ক্রমশ চলে যাচ্ছে তাদের ব্যবস্থাপনার অধীনে। বিদেশ থেকে যে রেমিট্যান্স আসছে তার একটা বড় অংশ আবার ফেরত চলে যাচ্ছে মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফার আকারে। খরচ হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের খাতে। ধনীরা টাকা ও সম্পদ দুটোই পাচার করছে। তাদের ভবিষ্যৎও বিদেশমুখো। ব্যাংকে সঞ্চিত টাকা অলস থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে; কিন্তু তাই বলে যে নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে তা নয়। একাংশ লোপাট হয়ে যাচ্ছে; দেশি-বিদেশি তস্করেরা অন্য ব্যাংককে তো বটেই এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংককেও টাকা হাতিয়ে নেওয়ার নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে পেয়ে গেছে। সিঁদ কাটাটা পুরনো কায়দা, প্রযুক্তি ব্যবহার ও যোগসাজশে কাজ চলছে। ওদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে বিরাম নেই, কর্মসংস্থান বাড়ছে না, কিন্তু এ নিয়ে রাষ্ট্রের কর্তাদের কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা নেই; গৃহে ও কারখানায় সস্তা শ্রমপ্রাপ্তিতে তাদের লাভ আছে, ক্ষতি নেই। সস্তা শ্রমের চাহিদা বিদেশেও আছে, পাঠাতে পারলে ভালো।
অত্যন্ত উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো এই যে, প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠছে, খরা ও প্লাবন দুটোই দেখা দিয়েছে, সমুদ্রের পানি উঁচু হয়ে ভূমি গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে আছে। নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। নদী কোথাও কোথাও শুকিয়ে গেছে। বনভূমি উজাড়।
সবই তো দেখছি আমরা। কিন্তু এর বিপরীতে আশাভরসার জায়গা তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। বড়, সবচেয়ে বড় বিপদই হয়তো-বা ওইখানেই, ওই হতাশাতে। আশা ছিল বদলাবে, আমরা পারব, শত্রুকে হাঁকিয়ে দিয়ে আমরা মুক্ত হব, সে-আশাটাকে ধরে রাখা এখন ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। আসলে শত্রু যে কে সেটাই তো ঠিক মতো চেনা যাচ্ছে না। এতকাল বিদেশিরা ছিল, কারও গায়ের রং আলাদা, কারও-বা ভাষা স্বতন্ত্র; তাদের চিনতে পারতাম; কিন্তু এখন যারা শত্রুতা করছে তাদেরকে তো নিজেদের লোক বলেই মনে হচ্ছে, কাছেই থাকে, গায়ে-মুখে কাছাকাছি। এদের সঙ্গে লড়ব কী করে? তাছাড়া ক্ষমতা, টাকা-পয়সা, পুলিশ-র্যাব-আর্মি সব তো এদেরই হাতে? তাহলে?
শত্রুর বিরুদ্ধে এতদিন যে আন্দোলন ছিল সেটা এখন বেশ কুণ্ঠিত, যেন সন্ত্রস্ত। প্রধান কারণ শত্রুকে চিনতে না-পারা, এবং শত্রুর শক্তি ও তত্পরতা দেখে হতাশ হয়ে পড়া। শত্রুটা আসলেই কে? কী তার পরিচয়? সেটা কি জানা হয়েছে? না, সঠিকভাবে জানা হয়নি। তবে একটু খেয়াল করলেই কিন্তু দেখা যাবে যে শত্রু কতিপয় ব্যক্তি নয়, শত্রু হচ্ছে ব্যবস্থা। ব্যক্তিকেই সামনে দেখা গেছে। কিন্তু ব্যক্তির শক্তি নিহিত ছিল ব্যবস্থার ভিতরে। ব্যক্তি ছিল ব্যবস্থার প্রতিনিধি, ব্যবস্থার পাহারাদার এবং সুবিধাভোগী। ব্যক্তি বদলেছে, ব্যবস্থা বদলায়নি। ব্যবস্থাটার নাম হচ্ছে পুঁজিবাদ। ব্রিটিশরা পুঁজিবাদী ছিল, পাকিস্তানি শাসকেরাও পুঁজিবাদী ছিল, বাংলাদেশের শাসকেরাও তাই। ব্রিটিশরা একটি পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করেছিল, যাওয়ার সময় সেটিকে অক্ষত অবস্থায় পাকিস্তানি পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে। আমরা ব্রিটিশদের বিদায় করেছি, পাকিস্তানিদেরকে তাড়িয়েছি, কিন্তু রাষ্ট্রের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে পারিনি। রাষ্ট্র আয়তনে ও নামে বদলেছে, কিন্তু তার স্বভাবে কোনো রদবদল ঘটেনি। আর সমাজ? সেও আগের মতোই রয়ে গেছে। তাই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েই সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করছে, আগে যেমনটা করত। অধিকাংশ মানুষই সুবিধাবঞ্চিত। শতকরা বিশজন সুবিধা পাচ্ছে, আশিজন শিকার হচ্ছে বঞ্চনার। এই আশিজন বিক্ষুব্ধ। তবে কার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সেটা তারা জানে না। না-জেনে ঘরের বউকে পেটায়। বিভিন্ন অর্থে।
ওপরের বিশজনের ছেলেমেয়েই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে। খুব ওপরে যে পাঁচজন রয়েছে তারা বিশ্বাসই করে না যে, বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ আছে। নিজেদের ভবিষ্যেক তারা বিদেশে গচ্ছিত রাখছে। বাংলাদেশ তাদের জন্য একটা জমিদারি; এক সময়ে ব্রিটিশদের জন্য যেমন ছিল, ছিল যেমন পাঞ্জাবিদের জন্য, ঠিক তেমনি। তারা সম্পদ লুণ্ঠন করে। সেই সম্পদ কিছুটা ভোগ করে, কিছুটা দেয় পাচার করে। বঞ্চিত আশি ভাগের নিচের অংশ কি আর করবে, তারা মাদ্রাসায় যায়; গিয়ে আরও গরিব হয়। আশিজনের ওপরের অংশের পড়াশোনা বাংলা মাধ্যমে। শিক্ষার মানটা নেমে যাচ্ছে। ইংরেজি মাধ্যমের কথা আলাদা, ওই শিক্ষা কৃত্রিম, তাকে যথার্থ শিক্ষা বলা যায় কিনা সেটাই সন্দেহ। বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানে আগ্রহ হারিয়েছে, ইতিহাস পড়তে পাচ্ছে না; বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্কে খুবই কাঁচা থেকে যাচ্ছে। সৃজনশীল পদ্ধতির আমদানি করা হয়েছে; সেটা না বোঝেন শিক্ষক, না বোঝে ছাত্র।
মারাত্মক ব্যাপার যেটা ঘটে যাচ্ছে সেটা হলো শিক্ষার মধ্য দিয়ে ঐক্য গড়ার পরিবর্তে শ্রেণিবিভাজনকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। বিভাজন আগেও ছিল, কিন্তু সেটা দূর হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সাড়ম্বরে ঠিক উল্টোটা ঘটেছে, শ্রেণিবিভাজন গভীর ও প্রসারিত হচ্ছে। শিক্ষা শ্রেণিগত দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে। যত শিক্ষা তত দূরত্ব— এ এক মর্মান্তিক প্রহসন। মাতৃভাষার মাধ্যমে অভিন্ন শিক্ষারীতি এখন কল্পনাতেও অসম্ভব। সোনার বাংলা জাতীয় সংগীতে আছে, বাস্তবে তার নামনিশানা নেই।
পুঁজিবাদের কিছু কিছু ভালো দিক ছিল, বিশেষ করে উত্পাদনের ক্ষেত্রে তো সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনই এনেছিল। বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীনে বাংলাদেশের উত্পাদন শক্তি কিন্তু সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অপরদিকে পুঁজিবাদের ক্ষতিকর দিকগুলোর সবই এখানে তত্পর। অত্যন্ত ক্ষতিকর যে শ্রেণি-বৈষম্য পুঁজিবাদের দ্বারা তা সযত্নে লালিত-পালিত হচ্ছে। পুঁজিবাদ আস্থা রাখে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপরে। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিটা খুবই পরিষ্কার। সবকিছু চলে যাচ্ছে প্রাইভেটের হাতে। শিক্ষা ইতিমধ্যেই চলে গেছে, স্বাস্থ্যও রওনা দিয়েছে। প্রাইভেট বলতে ব্যক্তিগত ও গোপন দুটোই বোঝায়। ওই ব্যক্তিগত এবং গোপন হওয়াটা অত্যন্ত চলমান। তবে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়াটা ব্যক্তিগত হলেও গোপন নয় এবং ব্যক্তির নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কোচিং সেন্টার থেকে শুরু করে প্রাইভেটে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই বিদ্যার কেনাবেচা চলছে। কী শিখছে সেটা বোঝার উপায় নেই। পাবলিক হাসপাতালে এক সময়ে চলনসই চিকিৎসা পাওয়া যেত, এখন সেটা দুরাশা মাত্র। অসুখ হলে টাকাই একমাত্র ভরসা,
টাকা না থাকলে কী দুর্দশা হয় সেটা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বাঁচা না-বাঁচা ভাগ্যের হাতে নেই, চলে গেছে টাকার হাতে। এখন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে এরকম যে প্রাইভেট অর্থই ভালো, পাবলিক মাত্রেই খারাপ। প্রাইভেট ব্যাংক ভালো সেবা দেয়, পাবলিক ব্যাংক সেটা দেয় না। প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতালে যে মানের ও যত দ্রুত চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব পাবলিক হাসপাতালে তা পাওয়া অসম্ভব। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো উচ্চশিক্ষার জন্য কিছুটা নির্ভরযোগ্য অবস্থানে আছে, কিন্তু সেখানেও প্রাইভেটের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও বাণিজ্যিকভাবেই দ্বিতীয় শিফটে শিক্ষাক্রম চলছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউ কেউ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, এবং তুলনায় অধিকতর মনোযোগ দিচ্ছেন। আগামীতে দুয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে পড়বে এমন ধারণা অমূলক নয়। এটা হাওয়া কোন দিকে বইছে তার উদাহরণ মাত্র। ওদিকে পুঁজিবাদ যে সব কিছুকে প্রাইভেট করে ছাড়ে অথচ ব্যক্তিগত প্রাইভেসিকে টিকতে দেয় না, তেমন ঘটনার আলামত বাংলাদেশে বিলক্ষণ দৃশ্যমান।
সামাজিক সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আগেও ঘটেছে, বাংলাদেশ হওয়ার পরে কিন্তু এর ঘনঘটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া ব্যক্তিগত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তো বটেই, তাদের বিষয়সম্পত্তিও রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করার খোলা পথ দিয়ে সংগোপনে ব্যক্তিমালিকানায় চলে গেছে। কিছু সময় দম ধরে থাকার পর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানাগুলোও ব্যক্তির হাতে চলে যাওয়া শুরু করে দিয়েছিল; একপর্যায়ে বিরাষ্ট্রীয়করণ রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবেই গৃহীত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাংবিধানিক তালিকা থেকে সমাজতন্ত্র মুখ নিচু করে বিদায় নিয়েছে।
পুঁজিবাদ বিচ্ছিন্নতাকে লালনপালন করে। তার প্রমাণও যত্রতত্র পাওয়া যাবে। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। ভাই ভাইকে, ছেলে পিতাকে, পিতা সন্তানকে হত্যা করছে। এমন কি মা’ও নিজের হাতে খুন করছে সন্তানকে। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমানবিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। মানুষের অস্বাভাবিক ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এখন কোনো খবরই হয় না। প্রত্যেকে ব্যস্ত আছে নিজেকে নিয়ে। এই বিবরণ লম্বা করা যাবে; কিন্তু প্রশ্নটা থাকবে আমরা কী করব, আমাদের করণীয়টা কী দাঁড়াবে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াটা তো চলছেই, সে পরামর্শ দিয়ে লাভ নেই। বিশেষ করে এই কারণে যে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদে প্রবহমান নদীর স্রোতের মতোই সমাজের স্রোতও বিষাক্ত হয়ে পড়েছে; সে-স্রোতে স্বাস্থ্যের প্রতিশ্রুতি নেই, রয়েছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। না, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে বাঁচা যাবে না, কেননা স্রোতই তো হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা আবর্জনার ভাসমান স্তূপ মাত্র। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো চাই। স্রোতকে মুক্ত করা চাই আবর্জনার স্তূপ থেকে। এক কথায়, শত্রুমুক্ত করা চাই দেশকে। কিন্তু শত্রু কে সেটাই তো জানা হচ্ছে না। আমরা এটা ওটা বলছি, এই ত্রুটি ওই ত্রুটি দেখাচ্ছি, অসংখ্য বিপদ আপদ, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে, বলাবলি করছি সেসব নিয়ে; কিন্তু এসব তো রোগ নয়, রোগের প্রমাণ ও লক্ষণ বটে। এদের চিকিৎসায় তো রোগ সারবে না। রোগটা রয়ে গেছে ভিতরে। প্রথম কর্তব্য তাই রোগটাকে চিহ্নিত করা। রোগটা হচ্ছে পুঁজিবাদ। রোগের এই পরিচয় বিষয়ে আগে যতটা শোনা যেত এখন কিন্তু ততটা শোনা যায় না। মাঝে মধ্যে এবং চকিতে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ ইত্যাদি। শব্দ তবু উঁকিঝুঁকি দেয়, কিন্তু পুঁজিবাদের কথা ওঠে না। অথচ আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত দুর্গতির মূল কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক দৌরাত্ম্য। পুঁজিবাদ ব্যক্তির মুনাফালিপ্সা ও ভোগের লালসাকে নির্মমভাবে উৎসাহিত করছে। মানুষ কেবল নিজেরটা দেখছে, এবং নিজেরটা দেখতে গিয়ে সকলেরটাকে বিপর্যস্ত করছে। পুঁজিবাদ মানুষকে ব্যস্ত রাখছে নিজের ব্যাপারে, নিষেধ করছে অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাকাতে। ব্যক্তি তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে পরিণত হচ্ছে অসামাজিক প্রাণীতে। পুঁজিবাদকে রোগ হিসেবে চিনতে না পারলে তো প্রতিকারের পথে এক পাও এগোতে পারব না। ব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী, কর্তব্য তাই এই ব্যবস্থাকে বদলে ফেলা। সেটা করতে না পারলে মুক্তি আসবে না। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসটা দীর্ঘ। ধরা যেতে পারে যে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই শুরু। মুক্তির সেই সংগ্রামে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ ব্রিটিশ শাসনের অবসান না ঘটালে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় যে সামাজিক বিপ্লব সেটা ঘটা সম্ভব ছিল না। এক সময়ে ব্রিটিশ গেল, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলো বলে মনে হলো, কিন্তু অচিরেই টের পাওয়া গেল যে স্বাধীনতা আসলে পাওয়া যায়নি, রাষ্ট্রের চেহারাটাই যা বদলেছে, তার স্বভাব-চরিত্র মোটেই বদলায়নি। স্বাধীনতার পুরাতন সংগ্রামটা তাই সবেগে চলল; এবং মুক্তির স্বপ্নও জেগে উঠল। বিশেষ করে একাত্তরের যুদ্ধের ভিতর দিয়ে মুক্তির স্বপ্ন তো বেশ জোরালো হয়েই উঠেছিল। কিন্তু মুক্তি এলো না, কারণ পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা ঠিকই রয়ে গেল। পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের পক্ষে পুঁজিবাদবিরোধী হওয়াটা না ছিল সম্ভব না স্বাভাবিক। নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাটা ছিল বুর্জোয়া হওয়ার। অর্থাৎ পাকিস্তানি বুর্জোয়াদের সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতার গদি ও বিত্তলাভের সুযোগগুলো দখল করা। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থকরণের পথ খুলে দিয়েছে। যে শাসক শ্রেণিটি গড়ে উঠেছে তারা দেশবাসীর শতকরা বিশজনের প্রতিনিধিত্ব করে; আশিজনকে বঞ্চিত রাখতে তারা বাধ্য। শাসক শ্রেণির ভিতর ঝগড়া ফ্যাসাদ চলছে, সেটাই তাদের রাজনীতি, কিন্তু তাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, সেটি পাকাপোক্তই রয়ে গেছে। পুঁজিবাদ অভাব, বেকারত্ব, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ইত্যাদিকে পুষ্ট করে থাকে; বাংলাদেশেও তাই ঘটছে। ব্যবস্থাকে না বদলালে অবস্থা বদলাবে না, পরিত্রাণ লাভের প্রশ্নই ওঠে না। এই কাজটি শাসক শ্রেণি করবে না। করতে হবে বঞ্চিত মানুষদেরকে এবং তাদের পক্ষে যারা দাঁড়াতে চায় ও দাঁড়াতে পারে তাদেরকেই। কাজটা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক; বঞ্চিত জনগণের পক্ষের রাজনীতির। একাত্তরে মনে হয়েছিল জনগণের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটতে যাচ্ছে। যুদ্ধের আসল শক্তি তো ছিল বঞ্চিত মানুষদের অংশ গ্রহণের ভিতরেই, নেতৃত্বটা যদিও ছিল বিত্তবানদের হাতে। ভোটের নয়, সেটি ছিল সংগ্রামের রাজনৈতিক সংহতি। সংহতিটা টেকেনি, যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই দৃশ্যপট বদলে গেছে। স্টিমারটি ঘাটে ভিড়লে যেমনটা ঘটে ঠিক তেমনটি। ওপরতলার যাত্রীরা, যাদের সংখ্যা অল্প, তারাই প্রথমে এবং দ্রুতগতিতে নেমে যায়। নিচের ডেকে অনেক মানুষের ভিড়, তাদেরকে নামতে হয় পরে এবং ধীরে ধীরে। তারা নেমে দেখে যানবাহন বলতে কিছু আর অবিশষ্ট নেই, ওপরতলার মানুষেরা সব দখল করে নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে চলে গেছে। গন্তব্য একটাই। যেখানে যা পাওয়া যায় দখল করা। একাত্তরের ওই রাজনৈতিক শক্তিটি ছিল অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত, এবং তার লক্ষ্যও ছিল সীমিত, হানাদারদের তাড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত। ওই শক্তিটা হারিয়ে যায়নি, জনগণের মধ্যে সুপ্ত আছে, তাকে সংগঠিত করা দরকার, সুস্পষ্ট গন্তব্যের দিকে এগোবার জন্য। বলা বাহুল্য লক্ষ্যটি একুশ দফা কিংবা এগারো দফার নয়, এক দফার। সমাজপরিবর্তনের। সমাজ তো নানা রকমের সম্পর্ক বৈ অন্যকিছু নয়। ওই সম্পর্কগুলোকে বদলানো চাই। সম্পর্কগুলোর ভিতরে একপক্ষে রয়েছে মালিক অপরপক্ষে প্রজা। এতে চলবে না, চলছে না। সব সম্পর্কের মূলনীতি হওয়া চাই বন্ধুত্ব। তার জন্য ব্যবস্থাটাকে বদলাতে হবে। ব্যবস্থা বদলের লড়াইটা অবশ্যই পুঁজিবাদবিরোধী হবে; তাকে সমাজতান্ত্রিকই বলতে হয়, কেননা এর চেয়ে ভালো নাম পাওয়া যাচ্ছে না। এ লড়াই বিশ্বব্যাপী চলছে। তবে প্রত্যেকটি দেশেই এর রণনীতি ও রণকৌশল নির্ভর করবে স্থানীয় অবস্থার ও বৈশিষ্ট্যের ওপর। এটি একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রাম; প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক, কেননা এর ভিত্তিটা স্থানীয়। কারা দেবে নেতৃত্ব? দিতে হবে সচেতন মানুষকেই; অসুখটাকে যারা চিনেছে, মোহমুক্ত হয়েছে, এবং বুঝে নিয়েছে যে আত্মসমর্পণে মুক্তি নেই তাদেরকেই। একাত্তরে আমাদের কী দশা হতো যদি আত্মসমর্পণ করতাম?
জাতীয়তাবাদীরা যা দেওয়ার ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছে, সমাজতন্ত্রীরা কী করে তার ওপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।
লেখক : প্রফেসর এমিরেটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।