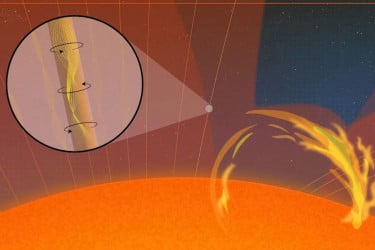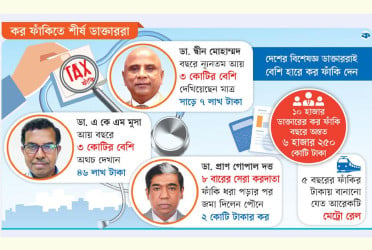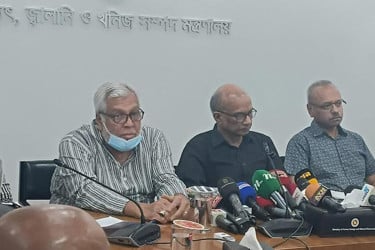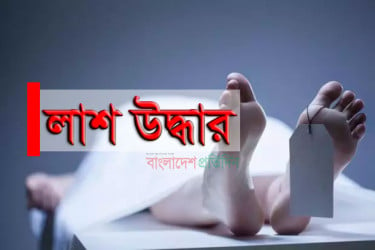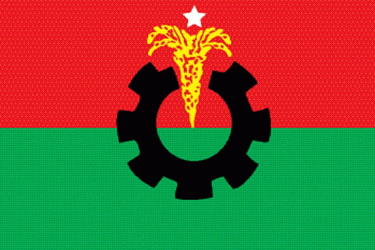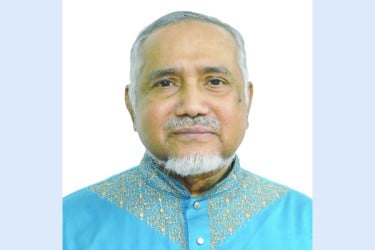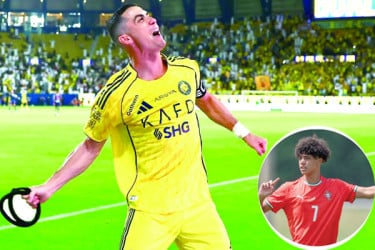একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট হচ্ছে প্রতিদিনের জীবনে—অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া, বন্যা, খরা, কিংবা প্রাণী-প্রজাতির বিলুপ্তি। অন্যদিকে, এর মাঝেই পশ্চিমা বিশ্বের কিছু রাজনীতিতে দৃশ্যমান হচ্ছে এক ধরনের নতুন বিপরীতমুখী ধারা, যেটিকে বলা হচ্ছে ‘অ্যান্টি-এনভায়রনমেন্টালিজম’ বা পরিবেশবিদ্বেষ।
এই প্রবণতা শুধু পরিবেশবাদী কার্যক্রম নয়, পরিবেশ-সুরক্ষামূলক আইন, জলবায়ু নিয়ে গবেষণা এমনকি দূষণ রোধের উদ্যোগগুলোকেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্সের কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতারা এখন সরবভাবে এই অবস্থান নিয়েছেন।
উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে পরিবেশবান্ধব বলে দাবি করলেও তার প্রশাসন জলবায়ু গবেষণার বাজেট কেটে দিয়েছে এবং দূষণ প্রতিরোধের নানা আইন বাতিল করেছে। একই রকমভাবে যুক্তরাজ্যের রিফর্ম পার্টি ও ইউরোপের আরও কিছু কট্টর ডানপন্থী দল পরিবেশ আইনকে ‘অর্থনীতির শত্রু’ বলে প্রচার করছে।
কিন্তু গবেষকেরা বলছেন, পরিবেশবিদ্বেষী এই মনোভাবের ভিত আসলে খুবই দুর্বল। এদের বক্তব্যের মাঝে রয়েছে অসংখ্য স্ববিরোধ। যেমন কেউ বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে না, আবার কেউ বলছেন, হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আমরা কিছু করতে পারি না।
এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ নাগরিক জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রেও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কাজ করা সংস্থাগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দ্বিমুখী মনোভাব আসলে একটি কৌশল—যেখানে জীবনের গতিধারা বা ব্যবসার লাভে হস্তক্ষেপ না করে, পরিবেশের জন্য কিছু না করেই দায়মুক্ত থাকার চেষ্টা চলে। কেউ কেউ এটিকে ‘ঠান্ডা পরিবেশবাদ’ (cold environmentalism) বলছেন—যেখানে প্রকৃতিকে ভালোবাসা শুধু ছবি আর পর্যটনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাস্তব রক্ষায় নয়।
অন্যদিকে, ‘গরম পরিবেশবাদ’ (hot environmentalism) হলো প্রকৃত অংশগ্রহণ—যেখানে মানুষ দায়িত্বশীল আচরণ করে।
বিজ্ঞানীদের মতে, এই পরিবেশবিদ্বেষ মূলত একধরনের ভুল ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে—যেখানে বলা হয়, কর্মসংস্থান বনাম পরিবেশ সুরক্ষা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিভ্রান্তিকর ভাবনা মূলত শ্রমজীবী মানুষকে পরিবেশবাদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
যদিও এসব ভাবনা পশ্চিমা রাজনীতিতে বিস্তার লাভ করছে, বাস্তবে চিত্রটা ভিন্ন। চীনসহ অনেক এশীয় ও আফ্রিকান দেশ এখন পরিবেশ রক্ষায় আরও সক্রিয়। এমনকি সাহেল অঞ্চলের মতো জায়গায় পরিবেশ রক্ষা এখন বেঁচে থাকার লড়াই—যাকে বলা হচ্ছে ‘survivalism’।
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল