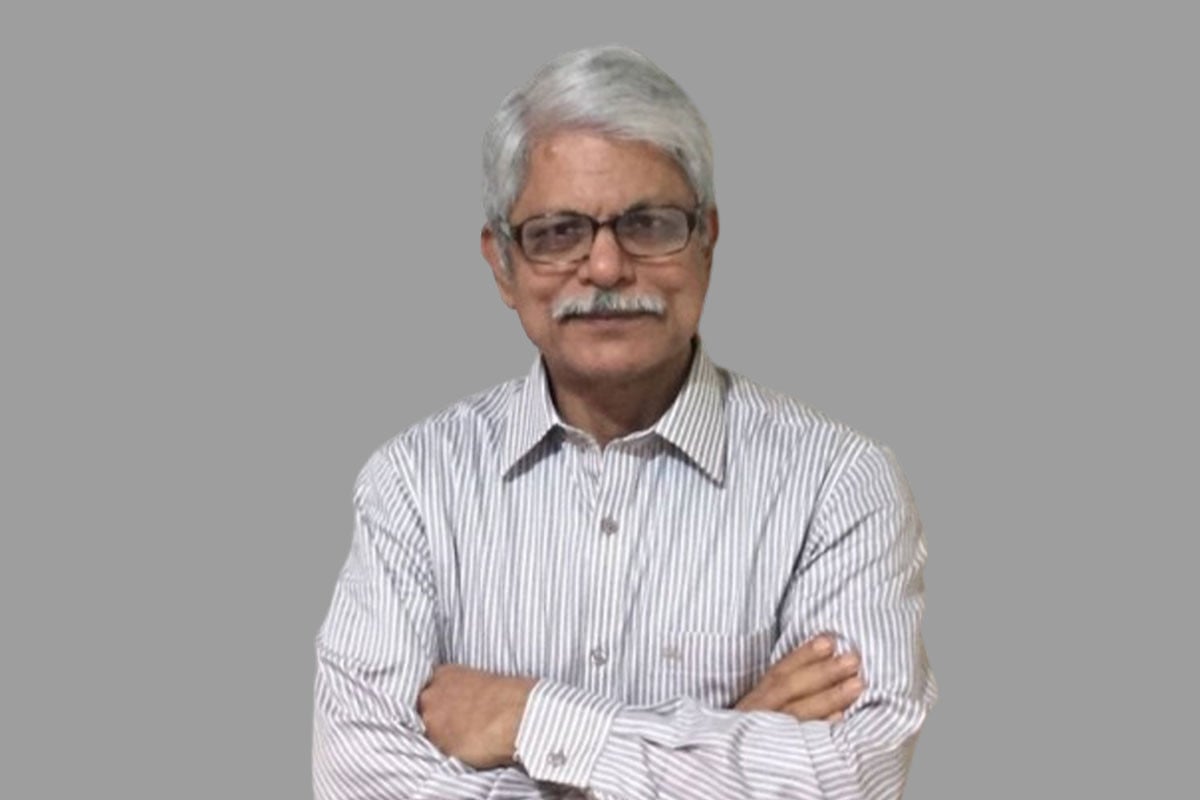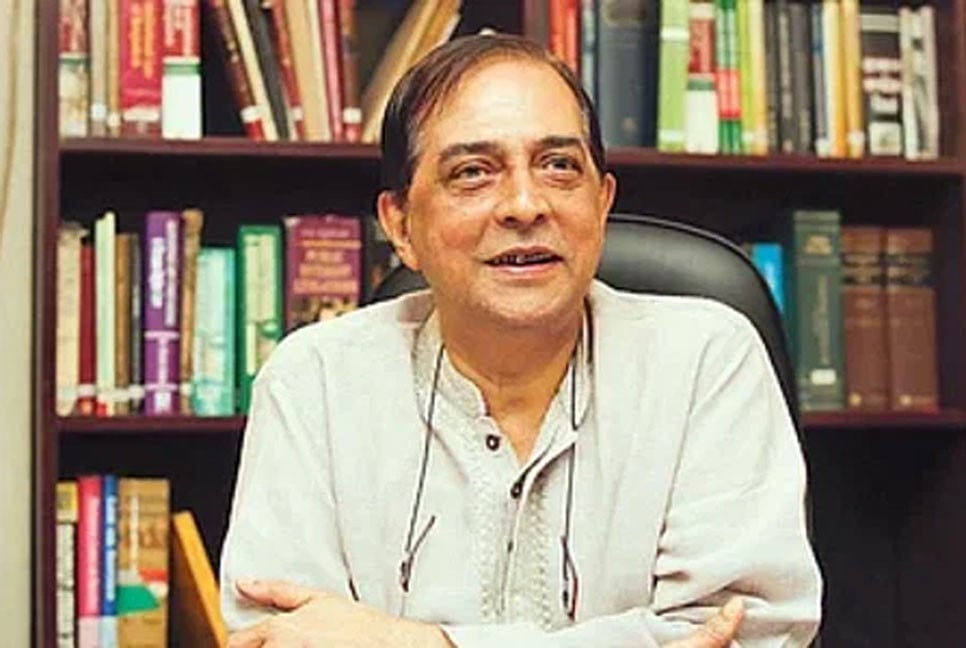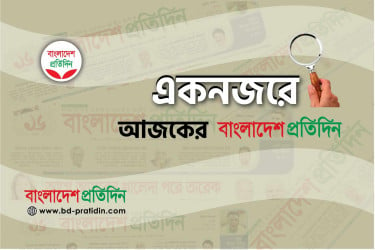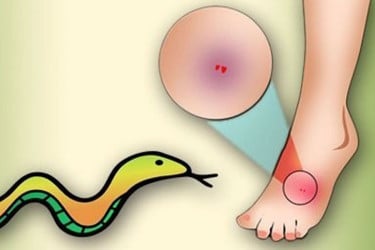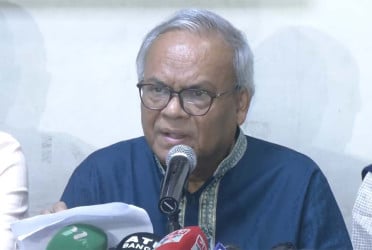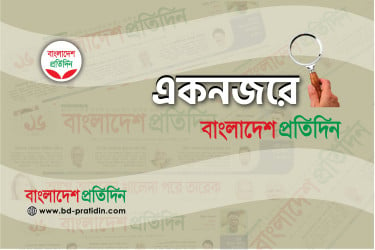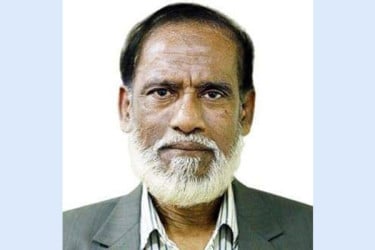বাংলাদেশের অগ্রাধিকার আজ পর্যন্ত স্থির করা সম্ভব হয়নি। যে রাজনীতিবিদদের ওপর জনগণ নির্ভর করেছে, তারা বিগত দিনগুলোতেও জনগণকে কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারেননি, এখনো পারছেন না। তাদের একমাত্র অগ্রাধিকার যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়া। নজিরবিহীন গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশকে উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত করে ভয়াবহ নিপীড়ন, বৈষম্য, বঞ্চনা চাপিয়ে দেওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার পর একটি বছর কেটে গেছে। এক বছর একেবারে কম সময় নয়।
কিন্তু অযাচিত ও অকল্পনীয় মুক্তির স্বাদ পেয়ে একশ্রেণির রাজনীতিবিদ দেশকে আরও তিমিরে ঠেলে দেওয়া ছাড়া সবার জন্য কল্যাণকর নতুন কোনো কিছু যোগ করার কথা ভাবতেও অক্ষম হয়ে পড়েছেন। দেড় দশকের রাজনীতিশূন্যতা রাজনীতিবিদদের মস্তিষ্কে মরিচার যে পুরু আবরণ সৃষ্টি করেছে, তারা অনেক ঘষামাজা করেও মরিচার সেই স্তর অপসারণ করতে পারছেন না। তাদের অনেকে দিশাহারার মতো অযৌক্তিক, দায়িত্বহীন আচরণ করছেন।
শুধু রাজনীতিবিদরাই যে দায়িত্বহীন আচরণ করছেন তা নয়, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারও একইভাবে দায়িত্বহীন আচরণ করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে সময় ক্ষেপণ করে দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির পথ অবারিত করে দিয়েছেন। প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা বিলম্ব ঘটিয়েছেন এবং এখনো ঘটিয়ে চলেছেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের প্রতিশ্রুতি ও অগ্রাধিকার কী ছিল? জুলাই গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় এনে দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন এবং জাতীয় সংসদের নির্বাচনের অনুষ্ঠান।
এসবের পাশাপাশি অভ্যুত্থানের চেতনা ও জন–আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সাড়ে পনেরো বছর ধরে যারা প্রশাসন, বিচার বিভাগকে কলুষিত করার জন্য দায়ী, তাদের অপসারণ করে প্রশাসনকে পরিশুদ্ধ করা। এসবের অনেক কিছু যে কোনো নতুন সরকারের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ। এজন্য নতুন কোনো আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা নেই, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই যথেষ্ট।
ফেলে আসা এক বছরের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে এসবের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সাবেক ফ্যাসিবাদী সরকারের লোকজনদেরই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রেখে নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করার মতো কাজ করেছে ড. ইউনূসের সরকার। জাতীয় জীবনের একটি বছর অর্থহীনভাবে কেটে গেছে বললে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। অন্তর্বর্তী সরকার যেহেতু রাজনৈতিক সরকার নয়, তাদের প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত ছিল দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সসম্মানে বিদায় নেওয়া। এটা খুব অসম্ভব ছিল না।
অনেকের মনে থাকার কথা অথবা মনে না থাকলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটালেই তারা দেখবেন যে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ‘লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার’ (এলএফও) বা ‘আইনগত কাঠামো আদেশ’ ঘোষণা করেছিল। এলএফও অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদকে প্রথম অগ্রাধিকার কোনটি : সংস্কার না নির্বাচন? অধিবেশন বসার পর পরিষদের ১২০ কর্মদিবসের মধ্যে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার শর্ত দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ কেন কার্যকর হয়নি সেটি ইতিহাসের ভিন্ন এক অধ্যায়। বাংলাদেশেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে ১৯৯৬ সাল থেকে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নবগঠিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণের।
এ দৃষ্টান্তগুলো উল্লেখ করার কারণ হলো, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সংবিধান প্রণয়নের মতো জটিল কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি অথবা তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই তাদের ওপর। কিন্তু দীর্ঘ এক বছরেও তারা কাজের কাজ কিছুই করতে পারবে না, তা রাজনীতিসচেতন কারও পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং কমিশনগুলো যথাসময়ে তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছে। প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) শুরু থেকেই বলে আসছে যে অনির্বাচিত সরকারের এ ধরনের সংস্কার করার কোনো সুযোগ নেই। আসলেও নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে এমন সুযোগ থাকতে পারত যদি তারা ‘সামরিক সরকার’ অথবা ‘বিপ্লবী সরকার’ হতো। এ দুই ধরনের অসাংবিধানিক সরকারব্যবস্থাায় দায়িত্ব গ্রহণের পরই সংবিধান বাতিল বা স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং এ ধরনের সরকারের নির্বাহী প্রধানই হন রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি তার সরকারের পক্ষে বিধিবিধান জারি করেন।
গত বছরের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী অরাজনৈতিক সরকার গঠনের পর সংবিধান বাতিল অথবা স্থগিত করা হয়নি এবং আওয়ামী লীগের সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিই রাষ্ট্রপ্রধান পদে বহাল রয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচনব্যবস্থাা সংস্কার কমিশন তাদের রিপোর্টে সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থাায় সংস্কার সাধনের যে প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করেছে, তার ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সমানুপাতিক বা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং জাতীয় সংসদকে উচ্চকক্ষভিত্তিক করার প্রস্তাব দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো এত দিন পর্যন্ত শুধু চটজলদি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর সরকারকে চাপ দিয়ে আসছিল।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও দুই কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদের প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলোকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে। ছোট ও নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো কস্মিনকালেও যাদের কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোটে বিজয়ী হয়ে সংসদে বসার সুযোগ নেই তারা এ প্রস্তাব লুফে নিয়েছে। কারণ এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভোটে না জিতেও সংসদে ঠাঁই করে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। ছোট দলগুলোর জন্য সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সংসদের ধারণা নিঃসন্দেহে লাভজনক। কিন্তু বড় দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী কী কারণে এ পদ্ধতির পক্ষে সোচ্চার হলো তা অনেকেরই বোধগম্য নয়।
তা ছাড়া জাতীয় নির্বাচনসংক্রান্ত যে কোনো বিষয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া কীভাবে এই দুটি মৌলিক প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব? দেশে সংবিধানের চেয়ে বড় আর কোনো আইন নেই। বিদ্যমান সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হবে। নির্বাচনে কোনো দল যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করে এমনকি অন্য দলের বা স্বতন্ত্র সদস্যদের প্রলুব্ধ করেও যদি সরকার গঠনকারী দল তাদের নিজেদের সদস্যসহ দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সমর্থন নিশ্চিত করতে না পারে, সে ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অথবা উচ্চকক্ষের কী ঘটবে?
বাংলাদেশ কি এখনো সাংবিধানিক রাজনীতি বিকাশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে অথবা সংবিধানে নতুন নতুন পদ্ধতি যোগ করলেই দেশ যে ভবিষ্যতে আর কখনো নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার পথে যাবে না তার গ্যারান্টি কি? কোনো গ্যারান্টি নেই। কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো ক্যারিশমেটিক নেতাও এ ধরনের কোনো গ্যারান্টি দিতে পারেননি বলে বাংলাদেশ বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং তথাকথিত ক্যারিশমেটিক নেতাদের দুঃখজনক পতন ঘটেছে। দেশকে আবার ‘বিসমিল্লাহ’ থেকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে।
বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান, যা ‘বাহাত্তরের সংবিধান’ হিসেবে বহুল পরিচিত, কিছু বিষয় ছাড়া সেটি ভারতের সংবিধানেরই ‘রেপ্লিকা’ বা প্রতিরূপ ছিল। ভারতে ১৯৫০ সালে বহুদলীয় ব্যবস্থাভিত্তিক একটি সংবিধান কার্যকর হয়। সেই সংবিধানের মৌলিক কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই বিগত ৭৫ বছর ধরে সেটির আওতায় ভারতের মতো বহু জাতি গোত্র, বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মবিশ্বাসী জনগণ এবং শত শত নৃগোষ্ঠীর রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব হলেও এক ভাষাভিত্তিক, বহুলাংশে এক ধর্মভিত্তিক ও গুটি কয়েক ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বাংলাদেশকে পরিচালনার জন্য কার্যকর বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাভিত্তিক ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে কার্যকর সংবিধানের অস্তিত্ব টিকেছিল ২ বছর ৪ মাসেরও কম সময়।
যারা বাহাত্তরের সংবিধানের প্রণেতা, যারা বাহাত্তরের সংবিধানের পিতা-মাতা, একচ্ছত্র ক্ষমতার দাপটে অথবা তাদের ‘বাহাত্তরে ধরায়’ (মতিভ্রম ঘটায়) তারাই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকার্যকর প্রমাণ করেন এবং বাহাত্তরের গণতান্ত্রিক সংবিধানকে দাফন করেন। বাহাত্তরের সংবিধানের খোলনলচে পাল্টে তারা জাতিকে উপহার দেন একদলীয় বাকশালী শাসনের সংবিধান।
বাংলাদেশের ওই সময়ের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাকশালের মাধ্যমে তার ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ তত্ত্বের সংস্কারের অংশ হিসেবে ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে তার নিজের, পরিবারের ও তার দল আওয়ামী লীগের মহাবিপদ ডেকে আনেন। সপরিবার শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার দলের অশুভ পরিণতি পরবর্তী সময়ের এবং এখন যারা সংস্কারের নামে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন তারা অতীত থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি।
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংস্কার হয়েছে, এরশাদের আমলে সংস্কার হয়েছে। তারা সবাই কোনো না কোনো উপায়ে নির্বাচিত ছিলেন; কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগ বা সংস্কার প্রস্তাবকদের কেউ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। কারও কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে না। দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করে সংস্কারকরা কেটে পড়বেন, দুর্ভোগ পোহাবে জনগণ। বাংলাদেশে অতীতে কখনো আরোপিত কোনো সংস্কার ছাত্রসমাজ, রাজনৈতিক দল, জনগণ এবং শ্রেণিপেশার লোকজন মেনে নেয়নি।
গত সাড়ে পাঁচ দশকের বাংলাদেশে ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে বিতর্কিত নির্বাচনের সংখ্যাই বেশি। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসনে বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে এ বিতর্কের শুরু। এরপর ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারির নির্বাচন), ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও সর্বশেষ ২০২৪-এ অনুষ্ঠানগুলো চরম বিতর্কিত ছিল। এসব নির্বাচনের কোনোটিই অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল না। কোনো না কোনো বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করেছে, কোনোটা ভোটারবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভোটারদের ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও ধারণা আছে যে কোনো প্রার্থীর জয়-পরাজয় কীভাবে নির্ণয় করা হয়। প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কিছু করতে গেলেই জনমনে সংশয় সৃষ্টি হবে এবং সংস্কারবিরোধী রাজনৈতিক মহল এ সংশয়কে কাজে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ নেবে। কারণ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বিশেষত যারা অতীতে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে তারা ‘ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুযোগ’ হাতছাড়া করবে না। সে জন্য সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও উচ্চকক্ষের ধারণা কেবল রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বুঝলেই হবে না, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকেও বুঝতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে এত দীর্ঘ সময় নেই।
ইতোমধ্যে অনেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে তাদের ‘সেইফ এক্সিট’ বা সসম্মানে বিদায় নেওয়ার উপায় ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন। সরকারের জন্য এটা বিব্রতকর। পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে স্পষ্ট যে যত দিন যাবে সরকারের চলার পথ আরও বিঘ্নসংকুল হয়ে উঠবে। সবকিছু সত্ত্বেও সরকারের ওপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পড়েছে সুষ্ঠুভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের। সংস্কারের নামে সময়ক্ষেপণ না করে সরকার যত দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেবে ততই মঙ্গল।
লেখক: যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক