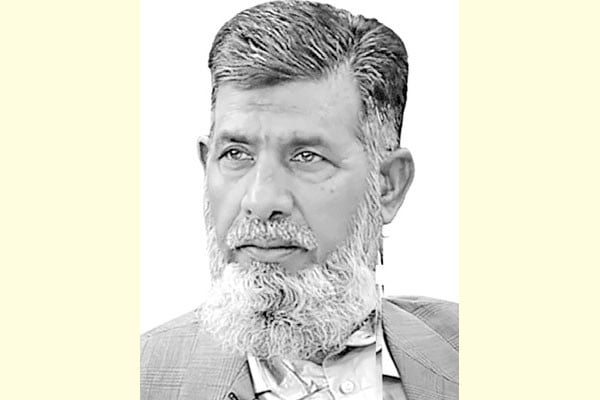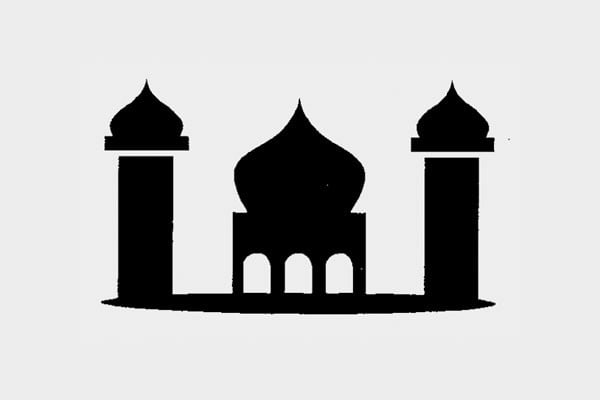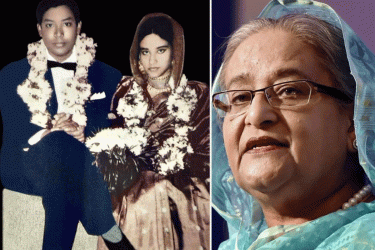’৫৭-এর ফেব্রুয়ারির ৬-১১ তারিখ কাগমারী মহাসম্মেলনের দেখতে দেখতে ৬০ বছর চলে গেল। আমাদের ভাষা, কৃষ্টি-সভ্যতার শক্তিশালী ভিত রচনা করেছিল ১৯৫৭ সালের কাগমারী মহাসম্মেলন। কী চমৎকার মিল। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মুর্শিদাবাদের ভাগিরথির তীরে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের হাতে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদ দৌলা স্বাধীনতা হারিয়ে ছিলেন। আমরা আবার সেই স্বাধীনতা দইয়ের স্বাদ ঘোলে মিটানোর মতো ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলাম। ১০ বছরে আমাদের সে স্বাদ মিটে গিয়েছিল। পাকিস্তানের বঞ্চনা ও অসংগতির বিরুদ্ধে ১৯৫৭ সালে হুজুর মওলানা ভাসানী কাগমারীতে আফ্রেশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার শান্তির সম্মেলন ডেকেছিলেন। সেখানে উপমহাদেশের কত নেতা, কত মনীষী এসেছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, আবদুল ওয়াদুদ, নরেন্দ্র দেব, বাংলাদেশের কবি জসীমউদ্দীন, অধ্যাপক ড. এবি হালিম, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, শাসুন্নাহারের মতো জগদ্বিখ্যাত লেখক-সাহিত্যিক। মহেশ্বেতা দেবীও সে সম্মেলনে পদধূলি দিয়েছিলেন। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফ্ফার খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, পীর পাগারুসহ আরও যোগ দিয়েছিলেন ইয়ার মামুদ, মো. ইদ্রিস, ফকির সাহাবুদ্দিন আহমেদ, খায়রুল কবির, খন্দকার মহাম্মদ ইলিয়াস, সদর ইস্পাহানী ও আবু জাফর শামসুদ্দিন। সে সময় পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার ছিল আওয়ামী লীগের। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতোয়ার রহমান খান। সেই সম্মেলনে ১০-১১ বছর বয়সে কতবার সমবয়সীদের সঙ্গে দৌড়ে গেছি, আবার ফিরেছি। ৬ দিনের সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল প্রায় ১৫-২০ দিন আগে থেকে। ছনের অসংখ্য কুঁড়েঘর বানানো হয়েছিল। তখন বেশ ঠাণ্ডা ছিল। রাস্তার পাশে শিশির ভেজা ঘাসে খালি পায় ছুটতে খুবই ভালো লাগত। সন্তোষ মহারাজার পুরনো বাড়িতে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়। জানালার ফাঁক দিয়ে আমরা সেসব দেখতাম। শেষদিন ছিল কাগমারী মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ মাঠে জনসভা। সে জনসভায় মাইকের আওয়াজ আর হুজুর মওলানা ভাসানীর দাড়ির নাচন আজও আমাকে উদ্বেল করে। আল্লাহ কখন কাকে কী দান করেন মানবের কল্পনার অতীত। কাগমারী সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রথম দেখেছিলাম, আবার কাগমারী কলেজ সরকারিকরণের অনুষ্ঠানে তাদের দুজনকে একত্রে শেষ দেখা দেখি। আল্লাহর কী দয়া, সে সভা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আমার। কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন হুজুরের সন্তোষের ভাঙা কুঁড়েঘরে। দরবার হলে খাবার খেয়ে তিনি সরাসরি খুলনা চলে যান। কারণ তার বাবা তখন সেখানে খুবই অসুস্থ। সেই ছিল তার টাঙ্গাইলে শেষ সফর। দরবার হলে পিতার মতো পুত্রের পাতে যখন রুই মাছের বিশাল মাথা তুলে দিচ্ছিলেন তখন খুবই অভিভূত হচ্ছিলাম। বঙ্গবন্ধু অত বড় বিশাল মাথা খেতে পারছিলেন না, একে ওকে দিচ্ছিলেন। যেই অন্যের পাতে তুলে দিচ্ছিলেন, অমনি হুজুর আরেকটা তার পাতে দিচ্ছিলেন। সে এক অপূর্ব দেখার মতো দৃশ্য। হুজুর সব সময় অভিনব কাণ্ড করতেন। সে যাত্রায় বঙ্গবন্ধুকে খাওয়াতে খরচ হয়েছিল ১৭-১৮ হাজার। মাছ, মাংস, তরি-তরকারি যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার জন্য কোঁচ থেকে ১৩৫ টাকা বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। অমনটাই ছিল তার সারা জীবনের স্বভাব। মহররম অথবা খাজা বাবার জন্মদিন কিংবা তার পীর নাসির উদ্দিন বোগদাদীর উরসে কাঁচা মরিচ ৫ মণ, পিয়াজ ১০ মণ, আলু ২০ মণ, চাল ১৫-২০ বস্তা, তেল ২ মণ, চিনি ২ বস্তা— এ রকম এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে টাকা গুঁজে দিতেন ১০০-১৫০ বা ২০০ যখন যা খুশি। কিন্তু কেন যেন তার কোনো কাজ ঠেকে থাকত না। যখন যাকে যা বলতেন সানন্দে তা করতেন। সেটা আমি কাদের সিদ্দিকীই হই, জননেতা আবদুল মান্নান, শামসুর রহমান খান শাজাহান, বদিউজ্জামান আর তার দলের আবদুর রহমান, বুলবুল খান মাহাবুব বা মোসলেম মিয়া। কাউকে তার দেওয়া দায়িত্ব মনে হয় আল্লাহর তরফ থেকে পালিত হতো।
কাগমারীর মহাসম্মেলন ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা বাঙালিদের চোখ খুলে দেওয়ার মতো। আমরা ’৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হয়েছি। কিন্তু হুজুর মওলানা ভাসানী কত দূরদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ কাগমারী মহাসম্মেলন। তিনি ’৫৭ সালে পাকিস্তানকে ‘আস্সালামু আলাইকুম’ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘বঞ্চনা বন্ধ না করলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের থাকা হবে না।’ হুজুর মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবেন, এটা সেই সময় থেকে বলে বলে ক্ষেত্র প্রস্তুত না করলে ৭ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর— ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’— বলার জন্যও তার গলা টিপে ধরা হতো। আজকাল অনেক পণ্ডিত ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি বলে সমালোচনা করেন। ‘রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।’ আমাদের কাছে ওটাই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। এরপর আমাদের আর কোনো ঘোষণার দরকার ছিল না। স্বার্থান্ধ যারা তারা নিজেদের স্বার্থে ওসব বলে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বলবে। বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে যেভাবে জাতিকে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করেছেন, আর কোনো নেতা হাজার বছর বেঁচে থেকেও পারতেন না। বাংলার স্বাধীনতার জন্য মওলানা ভাসানী হাল দিয়েছেন, মই দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু তাতে ফসল ফলিয়েছেন। জীবনের একটা সময় এই দুই নেতার মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করেছি, তাই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি শেষ জীবনে তারা দুজন ছিলেন এক ও অভিন্ন।
অতীত ভোলা বাঙালি, ’৫৭-কে ভুলতে বসেছি। ১৭৫৭-র পলাশীর পরাজয়ের দাগ যেমন আমাদের আলোড়িত করে না, তেমনি ১৯৫৭-এর কাগমারী সম্মেলনও আমাদের হৃদয়ে অনেকটা ম্রিয়মাণ-ম্লান। সামনের বিপদ থেকে দূরে থাকতে এবং আলোর পথে চলতে অতীতের ওপর চোখ রাখতে হয়। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হলে কল্যাণ হয়। অকল্যাণ থেকে দূরে থাকা বা তা প্রতিরোধ করা যায়। সেই অর্থে ১৯৫৭-র কাগমারী মহাসম্মেলন আমাদের সামনে এক দীপশিখা। যে শিখা কখনো নেভার নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সব সময় পথ দেখাবে। মানুষের অধিকার, আত্মসম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো প্রেরণা জোগাবে।
গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সোনারগাঁয় সীনহা আবুল মনসুরের ‘একজন মুক্তিযোদ্ধার না বলা কথা’ প্রকাশনী উৎসব ছিল। সোনারগাঁয়ে প্রকাশনী যেমন হওয়ার কথা তেমনই ছিল। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, প্রধান অতিথি সাংস্কৃতিক বিষয়কমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। লেখক বার বার অনুরোধ করায় টাঙ্গাইল থেকে ছুটে গিয়েছিলাম। ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তায় ইদানীং চলা যায় না। ৬০-৭০-৮০ কিলোমিটার লম্বা যানজট লেগে থাকে নিত্যদিন। সেদিন তেমন না থাকলেও সাড়ে ৩ ঘণ্টায় ঢাকা পৌঁছেছিলাম। যখন সেখানে পৌঁছি অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছিল। জনাব আনিসুল হক বই নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বইয়ের শুরুতেই ২-৩টি চিঠি ছিল, যা নিয়ে আনিসুল হক কথা বলছিলেন, চিঠি পড়ছিলেন। ভদ্রলোক দেখতে যেমন সুন্দর, কথা বলেন আরও ভালো, লেখেন তারচেয়েও চমৎকার। প্রথম অবস্থায় দর্শকদের মাঝে বসেছিলাম। কিন্তু উদ্যোক্তারা থাকতে দেননি। বলতে গেলে টেনেহিঁচড়ে মঞ্চে নিয়েছিলেন। ইদানীং অমন আদর খুব একটা পাওয়া যায় না। বই নিয়ে আমাকে কিছু বলতে হবে তেমন আগ্রহ ছিল না। বইটির মূল নায়ক আমারই দলের এক কাল্পনিক যোদ্ধা। উপন্যাসে অনেক রং মাখা যায়, বাস্তবে তেমন যায় না। লেখকের সঙ্গে আমার ৪-৫ বার কথা হয়েছে। তিনি আমার ‘স্বাধীনতা-৭১’ পড়েছেন। বইটা অনেক বড়। তাই হয়তো সবটুকু পড়েননি বা ভালো করে পড়েননি। কিন্তু পড়েছেন। লেখক সীনহা আবুল মনসুরের লেখার ক্ষমতা অসাধারণ, নিষ্ঠা আরও বেশি। তার ক্ষমতা ও নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ‘জীবন এতো ছোট কেন?’ পড়ে অভিভূত হয়েছি। তার ভ্রমণ কাহিনী পড়ে মনে হয়েছে আমিই যেন ভ্রমণ করছি। এসব দিক থেকে তাকে একজন ভালো লেখক বলতে হবে। আমেরিকায় থাকেন। শখ করে লেখেন। কর্মজীবনে একজন ডাক্তার। মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার আগ্রহের শেষ নেই। সে আগ্রহ থেকেই লেখকের এই প্রয়াস। বই সম্পর্কে তিনি বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ৬-৭ বছরের ছিলাম। তাই হয়তো আমার অনেক কথাই পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। সে জন্য অতি সম্প্রতি এক যোদ্ধার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
উপন্যাস আর ইতিহাস বা ঘটনা এক নয়। উপন্যাস উপন্যাসই। একজন লেখকের চিন্তা থেকে উপন্যাসের জন্ম। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা কড়কড়ে সত্য। লেখকের মুনশিয়ানায় কিছু বাস্তব, কিছু কল্পনা মিলেমিশে একাকার হয়ে মুক্তিযুদ্ধের কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু লেখকের দরদের কোনো ঘাটতি দেখিনি। কিন্তু প্রকাশনী সভায় প্রধান অতিথি আসাদুজ্জামান নূর বাস্তবের চেয়ে কল্পনাকে এত বেশি গুরুত্ব দিলেন যা দেখে বিস্মিত হয়েছি। কাদেরিয়া বাহিনীকে ঘিরে বইখানি রচনা করেছেন। কাদেরিয়া বাহিনীর কত জয়-পরাজয়ের ইতিহাস আছে, ঘটনা আছে, কত যোদ্ধা শহীদ হয়েছে। রকেট, আমির হানাদারদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করে জীবন দিয়েছে। দাইমার শামসু যমুনা নদীতে পাকিস্তানি হানাদারদের গুলিতে নিহত হয়েছিল। তার ভাগ্যে কবর জোটেনি। যমুনার পানির প্রবল টানে সে ভেসে গেছে। কদ্দুসনগরের কদ্দুস তার নিজের থানা স্বাধীন করতে গিয়ে বুকে গুলি খেয়ে শহীদ হয়েছিল। পাকিস্তানিদের মটরশেলে আনুর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। লেখক সেদিকে দৃষ্টি দেননি বা দিতে পারেননি। অর্নব নামে তার কল্পনায় সৃষ্ট নায়ক আমার সামনে দাঁড় করে দিয়েছেন। যে কথা তিনি তাকে দিয়ে বলিয়েছেন তাও যেমন সত্য নয়, আমাকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তারও কোনো সত্যতা নেই। তারপরও লেখার গুণে বইটি হয়তো পাড় পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি আসাদুজ্জামান নূরের বক্তৃতা শুনে। তার কল্পনার স্বপ্ন দেখা জাল বোনা দেখে। তিনি নিজেকে একজন মুক্তিযোদ্ধা দাবি করলেন। আমি জানি না তিনি কেমন মুক্তিযোদ্ধা, কোথায় কোন রণাঙ্গনে অথবা অন্য কোথাও কি করেছেন। তবে বলতে বলতে তিনি যখন বললেন, ১৪ মার্চ তারা ডিমলা, না ডোমর থানা দখল করেছিলেন। শুনে অবাক হয়েছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠেছিল। ১৪ মার্চ তাকে থানা দখল করতে হবে কেন? সব থানা তো আমাদের দখলেই ছিল। আওয়ামী লীগের পক্ষে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ যে ফরমান জারি করতেন, সেই ফরমানেই চলত। তাহলে কীভাবে তিনি দখল করলেন? সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন, ‘আমি ছাত্রলীগ করতাম না, ছাত্র ইউনিয়ন করতাম।’ আজ মন্ত্রী হলেও সেদিন ছাত্র ইউনিয়নের কেউ বঙ্গবন্ধুকে সহজভাবে নেয়নি। তাদের কথায় তিনি ছিলেন সিআইএ-এর চর বা দালাল। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যার পরও তারা তার বিরোধী ছিলেন। এখন জননেত্রী শেখ হাসিনার সামনে দাঁড়াতে না পেরে বঙ্গবন্ধুর চরম বিরোধীরাও জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ধরনা দিয়ে যে যতটা সুযোগ-সুবিধা লুফে নিতে পারছেন নেওয়ার চেষ্টা করছেন। বঙ্গবন্ধুকে কেউ সহায়তা করেনি আমাদের মতো কিছু উন্মাদ ছাড়া। কিন্তু সেই উন্মাদরাই আজ বেশি বঞ্চিত নির্যাতিত নিগৃহীত। আজকাল যত পেখমধারী বর্ণচোরাদের জয়-জয়কার।
সেদিন হতেয়ার নয়ন হাজী এসেছিলেন। তার মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট চাই। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন, আপনার সার্টিফিকেট নেই? ‘না স্যার, এখন পর্যন্ত কোনো সার্টিফিকেট পাইনি।’ কেন পাননি? ‘তা তো বলতে পারবো না।’ আবেদন ফরমে লেখা ‘কোথায় ভর্তি হয়েছেন? কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন? কমান্ডার কে? কোথায় যুদ্ধ করেছেন? কোথায় অস্ত্র জমা দিয়েছেন?’ হাজী মানুষ, তার সোজা জবাব, ‘স্যার, আমি কি ভর্তি হয়েছি? তা তো আপনিই ভালো জানেন। ইউনুস কমান্ডার সাহেবের সঙ্গে ছিলাম। আমার বাড়িতে একটানা ৬ মাস ক্যাম্প ছিল। আমার জমি-জমা ছিল। হাজার— দুই হাজার মণ ধান পেতাম। এখন আরও বেশি পাই। নিজেরটাও খাইয়েছি, অন্যের কাছ থেকে এনেও খাইয়েছি।’ তা ভালো কথা। কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন? ‘স্যার, ট্রেনিং আবার কী? সারা দিনই তো ট্রেনিংয়ের মধ্যেই থাকছি। সব সময়ই তো যুদ্ধের মধ্যে ছিলাম।’ আরে হাজী সাহেব, সরকারি মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম লেখাবেন, যুদ্ধ করবেন না? নিজেই বলছেন যুদ্ধ করেননি। এই ফরম অনুসারে আপনি মুক্তিযোদ্ধা না। বিস্মিত হয়ে বলেন, ‘কি বলেন স্যার? যুদ্ধের সময় কত কষ্ট করলাম। মুক্তিযোদ্ধারা এক রাইফেল কাঁধে নিয়ে হতেয়া থেকে পাথরঘাটা গেছে। আমি ৪টা গামছায় বেঁধে পৌঁছে দিয়েছি। না হলেও ১০ বার গুলির বাক্স নিয়ে কাচিনা গেছি, ফুলবাড়িয়া রাঙ্গামাটি গেছি। এমন কোনো দিন নেই নিজের ঘরে দুই-একশ রাইফেল, গোলাবারুদ পাহারা দিইনি। আগস্ট মাসে মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টার ভেঙে গেলে আহত কমান্ডার খোরশেদ আলমকে আমাদের কাছে দেওয়া হয়। আমরা দেড় মাস তাকে চাঙ্গারিতে করে পালিয়ে বেড়িয়েছি। আমজাদ মাস্টার, ১০-১২ জন গুলি খাওয়া মুক্তিযোদ্ধা দিয়েছিলেন। তাদের জান বাঁচিয়েছি। দেশ স্বাধীন হলে আমার হেফাজতে থাকা ১৬ গাড়ি অস্ত্র বাসাইল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে জমা দিয়েছি। তারপরও আমি মুক্তিযোদ্ধা না। চোখের সামনে কত মুক্তিযোদ্ধা ঘুরে। যারা আমার ক্যাম্পে ভাত রান্নার সময় ছাই-খোঁচানি হাতে চুলা খুঁচিয়েছে তারা মুক্তিযোদ্ধা আর আমি মুক্তিযোদ্ধা না। স্যার আপনিই বিচার করেন এটা কেমন কথা?’ হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু এখনকার হিসাবে নন। তবু তাকে বলেছিলাম, আপনি যান যাচাই বাছাই কমিটিকে বলবেন আমাদের সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন? এই যে কমিটির সভাপতি আবু হানিফ আজাদ, ওসমান গনি কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন? খোরশেদ আলম, আউয়াল সিদ্দিকী, সালাম সিদ্দিকী, নয়া মুন্সী, শওকত মোমেন শাজাহানের যে ট্রেনিং আমারও তো সেই ট্রেনিং। তারা মুক্তিযোদ্ধা হলে আমি কেন হবো না? পাহাড়ের বন্ধু হামিদুল হক বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছেন। তিনি তো কোনো ট্রেনিং নেননি, যুদ্ধ করেননি। আনোয়ার উল আলম, ফারুক আহমেদ, দাউদ খান, সোহরাব আলী খান আরজু তারা যা করেছে আমি তাদের চাইতে কম করিনি। তারপরও আমি মুক্তিযোদ্ধা না? আমি অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা।
কিছু মানুষ যুদ্ধের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল তারা কয়টা গুলি ছুড়েছে, কয়টা যুদ্ধ করেছে তার চেয়ে অনেক বড় যুদ্ধে জোগান দিয়েছি তাদের একজন উপলদিয়ার নুরুল ইসলাম নুরু মিয়া। তিনি জামালপুর সমবায়ে চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বাড়ি এসে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আর চাকরিতে যাননি। যখন যে কাজ দিয়েছি, চিলের মতো উড়ে গিয়ে করেছেন। ঘাটাইল থানা দখলের সব অস্ত্র তার জিম্মায় রাখা হয়েছিল। তিনি এখন মুক্তিযোদ্ধা না। নিয়মিত সেনাবাহিনীর গাড়ির চালক, ধোপা, নাপিত, রাঁধুনী, মিস্ত্রি, হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স যুদ্ধ করে না। কিন্তু তাদের ছাড়া যুদ্ধ চলে না। কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধে এমন কিছু মানুষ ছিলেন যাদের ছাড়া সব কিছু অচল। কিন্তু তাদের নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নেই, ‘কয়টা যুদ্ধ করেছেন? কয়টা হানাদার মেরেছেন?’ এসব কথা বলে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। দেওপাড়ার করিম মুন্সী সেও নাকি যাচাই বাছাইয়ে টিকছে না। অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা কোম্পানি যে কাজ করেছে তেমন কাজ তিনি একাই করেছেন। দেওপাড়ার এক যুদ্ধে কমান্ডার মফিজের ফেলে আসা ২ ইঞ্চি মর্টার উদ্ধার করেছিলেন। হাবিবুর রহমান বীরপ্রতীক আর আনছার একই সঙ্গে হানাদারদের মর্টারের একই গোলায় বাথুলীতে আহত হয়েছিল।
একই সঙ্গে ওদের চিকিৎসা হয়েছে। ওদের দুজনের নামই খেতাবের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। হাবিবুর রহমান খেতাব পেয়েছেন তাই মুক্তিযোদ্ধা তালিকাতেও নাম রয়েছে। কিন্তু আনছার যেমন খেতাব পায়নি, তেমনি তার মুক্তিযোদ্ধা তালিকাতে নাম নেই। এরা এখন কোথায় যাবে? কোথায় প্রতিকার পাবে?
লেখক : রাজনীতিক।