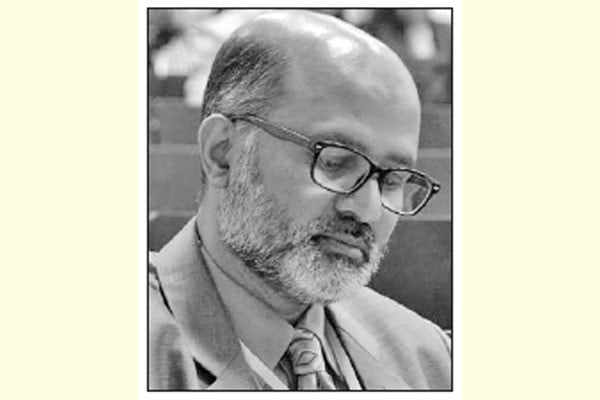১৭৫৬ সাল। সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলেন। কলকাতা আক্রমণের আগে তিনি কাশিমবাজার দখল করে নিয়েছিলেন মাঝপথেই। ইংরেজ সাহেবরা ভয় পেয়ে কাচুমাচু হয়ে নবাবের কাছে এসে ধরা দিল। বন্দী সাহেবদের হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মুর্শিদাবাদের গারদখানায়। সেই সাহেবদের মধ্যে বাংলার পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসও ছিলেন। কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠির সর্বেসর্বা ছিলেন ভিনেট। সেই ভিনেট গিয়ে নবাবকে ধরাধরি করতে লাগলেন- 'হুজুর হেস্টিংসকে ছেড়ে দিন। সে কোম্পানির সামান্য একজন কর্মচারী মাত্র। তার ছোবলও নেই, বিষও নেই।' হেস্টিংসকে ছেড়ে দিলেন নবাব। হেস্টিংস সোজা চলে এলেন কাশিমবাজারে।
ওদিকে সিরাজের আক্রমণের ভয়ে কলকাতা কুঠির সাহেব-সুবোরা সবাই গা-ঢাকা দিয়েছেন ফলতায়। এ সময় হেস্টিংস করলেন কী- নবাবী শাসনের যা কিছু গোপন খবর সব জোগাড়যন্ত্র করে পাঠাতে লাগলেন ফলতায়। কথায় আছে, 'ইজ্জত যায় না মইলে খাসলত যায় না ধুইলে।' হেস্টিংসের হয়েছে তখন সেই অবস্থা। তার গোপনে খবর পাঠানোর এ ব্যাপারটা বেশিদিন গোপন রাখা গেল না। সিরাজ সিদ্ধান্ত নিলেন হেস্টিংসকে আবার জেলে পুরবেন। খবর পেয়েই হেস্টিংস কাশিমবাজার ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। এখনই কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার। হেস্টিংস ভাবতে লাগলেন, কোথায় যাওয়া যায়? কার কাছে যাওয়া যায়? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল কান্তবাবুর নাম। অন্ধকারে চুপি চুপি তিনি হাজির হলেন কান্তবাবুর দোকানে। সেখান থেকে তার বাড়িতে। কান্তবাবুর ভালো নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। বাবা রাধাকৃষ্ণ নন্দী। আদি বাড়ি ছিল বর্ধমানের সিজনা গ্রামে। সেখান থেকে কান্তবাবু চলে এসেছিলেন কাশিমবাজারে। কেননা দেশজুড়ে কাশিমবাজারের তখন দারুণ নামডাক। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র তখন কাশিমবাজার। কাশিমবাজারে কান্তবাবুর ব্যবসা ছিল সুপুরি ও রেশমের। দোকানটা আবার ইংরেজদের কুঠি আর রেসিডেন্টের সঙ্গে একেবারে লাগোয়া। ফলে অচিরেই ইংরেজদের সঙ্গে বেশ একটা মাখামাখি ভাব হয়ে গেল কান্তবাবুর। ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা থেকে কান্তবাবু নাকি প্রায় দুই হাজারের মতো ইংরেজি শব্দ আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। ব্যবসাপত্রের হিসাব-নিকাশে হাত ছিল পাকা, তাই একদিন চাকরিও পেয়ে গেলেন ইংরেজ কুঠিতে। মহুরীর চাকরি, সেটা ছিল ১৭৫৩ সাল। সামান্য একটা চাকরি নিয়ে তখন হেস্টিংসও কাশিমবাজারে এসে হাজির। সেই থেকে কান্তবাবুর সঙ্গে হেস্টিংসের চেনাজানা। যাই হোক, কান্তবাবু হেস্টিংসকে দেখে তো স্তম্ভিত! কোথায়? কিভাবে লুকিয়ে রাখবেন তিনি হেস্টিংসকে? কান্তবাবু প্রথম কয়েকদিন তাকে লুকিয়ে রাখলেন তার মুদি দোকানে। তারপর গোপনে হেস্টিংসকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার বাড়িতে। দোকানে হাতের কাছে তেমন কিছু না পেয়ে কান্ত বাবু হেস্টিংসকে আপ্যায়ন করেছিলেন পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ দিয়ে। হেস্টিংসের পলায়নপর্বের খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। আর তখনই মানুষের মুখে মুখে জন্ম নিল এই ছড়া- বেচারা হেস্টিংসের এই পলায়নকে অমর করে রাখতে। হেস্টিংস সিরাজভয়ে হয়ে মহাভীত/কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত।/কোন স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়/হেস্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।/কান্তমুদী ছিল তাঁর পূর্ব পরিচিত/ তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত।/ মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়/হেস্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?/ ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ/ কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ।/সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে/হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে। সেই পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ খাবার পর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। হেস্টিংস যেদিন গভর্নর জেনারেল হলেন সামান্য কর্মচারী থেকে, সেদিনও তিনি ভোলেননি দুঃখের দিনের উপকারী বন্ধু কান্তবাবুকে। তাকে করে নিয়েছিলেন নিজের প্রিয়তম সাগরেদ। ক্রমেই কান্তবাবু হয়ে উঠেছিলেন হেস্টিংসেরই আরেকটি ছায়া।
ওয়ারেন হেস্টিংস না হয় বিপদে পড়ে পান্তা খেয়েছিলেন কিন্তু আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে পান্তা-ইলিশের চল কেন ও কীভাবে শুরু হলো তা একটি ভাবার বিষয়। ইলিশ-পান্তা খাওয়ার প্রচলন সম্ভবত শুরু ১৯৮২-'৮৩ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে পান্তা ও ইলিশ খাওয়ার ইতিহাস আমাদের সংস্কৃতিতে অতি প্রাচীন। রামায়ণে দেখা যায় যে, সীতা পোলাও রান্না করে রামকে খাওয়াচ্ছেন। ঠিক তেমনি সেই যুগের ঋষি-মুনিরা শুধু পোলাও কিংবা অষ্ট ব্যঞ্জন দিয়েই আহার করতেন না, পান্তাও খেতেন। তবে দুই, আড়াই হাজার বছর আগে যেহেতু কাঁচা লঙ্কাই ছিল না, সেহেতু পান্তা খাওয়া হতো চিংড়ি চচ্চড়ি, মৌরলা মাছের ঝোল অথবা বেগুন পোড়া দিয়ে। প্রাচীন যুগে মরিচের প্রচলন ছিল না বললাম এই অর্থে যে, আমাদের দেশে কাঁচা মরিচের আগমন ১৫০০ সালের দিকে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার হাত ধরে। সম্রাট শাহজাহানের আমলে মরিচের প্রচলন ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগ পর্যন্ত ব্যঞ্জনগুলোতে ঝালের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতো গোলমরিচ, পিপলু আর আদা। তবে বলে রাখা ভালো, মরিচের আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ায়। সে দেশের আদিবাসীরা মরিচ খেয়ে আসছে আনুমানিক চার হাজার বছর ধরে। স্পেনীয়, পর্তুগিজ ও ইতালিয়ান নাবিকদের কল্যাণে এই মরিচ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রথমে আসে ইউরোপে এবং পরবর্তীতে ভাস্কো-দা-গামার বদৌলতে চলে আসে আমাদের এই ভারতবর্ষে। ভাস্কো-দা-গামা আরও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন কামরাঙ্গা, আনারস, টমেটো প্রভৃতি ফল ও আনাজ।
পান্তাভাত বা পানি ঢালা ভাত খাওয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণত বাঙালির সাধারণ জীবনাচরণের সন্ধান ও অপচয়বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে জ্বালানি বাঁচানোর বিষয়টি তো রয়েছেই। গ্রামের পাঠশালায় গমনকারী ছাত্র বা কৃষিজীবী মানুষের পান্তা খেয়ে কাজ শুরু করার প্রথা এই তো বেশকিছু দিন আগে পর্যন্তও আমি দেখেছি। একটি শিশু ছড়া আছে এমন- 'পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে কাপড় দিয়ে গায়/গরু চড়াতে পাঁচন হাতে রাখাল ছেলে যায়।'
আমার জন্ম ঢাকায় হলেও আমার নাড়িটি মনে হয় পোঁতা আছে আমার বাপ-দাদার ভিটেয়। শৈশব থেকে অদ্যাবধি গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্কটি অত্যন্ত নিবিড়। আমার বাবা আমাকে সব সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন গ্রামে। ধান খেতের আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতাম দূর-বহুদূর অবধি। তখন দেখেছি গ্রামের অনেক দেহাতি কৃষক হয়তো অর্ধেক অর্ধকর্ষিত নাবাল জমির ওপর বসে গেছেন এক গামলা পান্তাভাত নিয়ে। সঙ্গে শুধু গোটাকয়েক পিয়াজ ও মরিচ। দু'একজনকে আবার দেখতাম শুধু প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মরিচ দিয়েই পান্তা খেতে। তাদের এই মরিচ খাওয়া দেখে আমি রীতিমতো অাঁতকে উঠতাম। জিজ্ঞাসা করতাম এত মরিচ তারা কেন খাচ্ছে? উত্তরে পাবনার আঞ্চলিক ভাষায় তারা বলতেন- 'এত মরিচ না খালি পরে চোইত মাসের এই রোদি গাও পুড়ি ছাই হয়য়া যাবিনি।' এই কথার অর্থ হলো- প্রচুর পরিমাণে মরিচ খেলে শরীরে রোদের অাঁচ কম অনুভূত হয়।
বাংলাদেশে আগের দিন রান্না করা ভাতে পানি ঢেলে পান্তা তৈরি করার বিশেষ রীতি আছে। বরিশাল জেলায় এই ভাতকে বলে 'পসুতি' ভাত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় গরম ভাতে পানি ঢেলে রাখলে তাকে বলা হয় 'পোষ্টাই' ভাত। এই ভাত খেলে নাকি পেট ঠাণ্ডা হয়। দুর্গাপূজার দশমীর দিন সকালে দেবী দুর্গাকে পান্তাভাত আর কচুর শাক নিবেদন করে বাঙালি হিন্দুরা তাদের প্রিয় দেবীকে বিদায় জানায়। এর পেছনে অবশ্য মজার একটি মিথ চালু আছে- দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেয়েরা সাধারণত তাদের পিতার গৃহে আসেন। তিনদিন ধরে বাপের বাড়িতে নানা স্বাদু ব্যঞ্জন দিয়ে তারা খাবার খান বটে কিন্তু সেই তথ্য স্বামীর কাছে গোপন রাখার জন্যই দেবী বিদায়ের দিনে কচুর শাক দিয়ে পান্তা খান। অথচ স্বামীর কাছে গিয়ে বলেন, দরিদ্র পিতা তার কন্যাকে এর চেয়ে বেশি কিছু আহার করাতে পারেননি। যাতে করে এই কথা শুনে তার স্বামী সারা বছর তাকে ভালো-মন্দ খাওয়ান। বড় বড় সাহিত্যিকদেরও দেখি আমোদ-আহ্লাদ করে কিংবা কখনো অভাবে পড়ে পান্তা খেতে। রবীন্দ্রনাথও পান্তা খেতে পছন্দ করতেন, বিশেষ করে তার নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর হাতের পান্তাভাত ও সঙ্গে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন- 'ইসকুল থেকে ফিরে এলেই রবির জন্য থাকে নতুন বউঠানের আপন হাতের প্রসাদ। আর যেদিন চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে নতুন বউঠান নিজে মেখে দেয় পান্তাভাত, অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে সেদিন আর কথা থাকে না।' কবি রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যেও টেনে এনেছেন পান্তাভাতের বিষয়টি। বিশেষ করে তার 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে আমরা দেখি পান্তাভাত খাওয়ার বর্ণনা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা আমাদের পল্লীকবি জসীমউদ্দীন ছাত্রাবস্থায়, তাদের পান্তা খেতে হয়েছে অভাব-অনটনের কারণে। কবি জসীমউদ্দীন ফরিদপুর থেকে পালিয়ে যখন কলকাতায় যান কবিযশ খ্যাতি পেতে, তখন সেখানে তিনি উঠেছিলেন তার এক দূর-সম্পর্কের বোনের ওখানে। তার ওই বোনটি এত অভাব-অনটনের মধ্যে ছিলেন যে, জসীমউদ্দীনকে তিনি দুবেলা ভালো করে খাওয়াতে পর্যন্ত পারতেন না। তাই হরহামেশাই জসীমউদ্দীনের ভাগ্যে জুটত শুধু পান্তাভাত ও কাঁচামরিচ।
আমার এক অনুজ- আব্দুল্লাহ ওমর সাইফ আমাকে একদিন বললেন- পহেলা বৈশাখে ইলিশ-পান্তা না খেয়ে আমাদের আসলে খাওয়া উচিত ডাল সহযোগে পান্তা। কারণ দামের দিক দিয়ে ইলিশ এখন একটি মহার্ঘ্য বস্তু। তা ছাড়া ডাল আমাদের অনেকদিনের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ভোজ্য। যদিও নানা বিষয়ে ওর জ্ঞান ও পড়াশোনা আমাকে বিস্মিত করে কিন্তু খাবার-দাবারের প্রতি সাইফ বেশ খানিকটা উদাসীন বলে ওর এমন আলপটকা মন্তব্যে আমি খানিকটা চুপসে গেলাম। ডাল ব্যঞ্জনটি আমাদের নিজস্ব একটি ভোজ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাতার, ফিরিঙ্গি ও মোগলরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে নানাবিধ ফল ও আনাজ আমদানি করলেও ডাল বস্তুটি বরং এ দেশ থেকেই তারা পৃথিবীর অন্যত্র জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। যদিও এখানে ডাল জন্মাত অতি প্রাচীনকাল থেকেই কিন্তু আমাদের কখনোই ডাল খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। আমাদের ডাল খাওয়া শিখিয়েছে পর্তুগিজরা- সম্ভবত ১৫০০ সালের দিকে। পরবর্তীকালে ডাল ব্যঞ্জনটি আমাদের এতই ভালো লেগে গেল যে, ডালের মধ্যেও এলো নানা বৈচিত্র্য- মসুর ডাল, মুগ ডাল, মটর ডাল, ছোলার ডাল, বিউলীর ডাল, অড়হর ডাল, খেসারি প্রভৃতি ডাল এ দেশে এখন সর্বত্র বেশ উপাদেয় ব্যঞ্জন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
এবার একটু ইলিশ মাছ সম্পর্কে বলি- এক কিলো ওজনের একটি ইলিশে কতগুলো কাঁটা থাকে বলতে পারেন? আমি বলছি- ১০ হাজার কাঁটা! তারপরও আমাদের অনেকের কাছে ইলিশ মাছ অনেকটা প্রসাদের মতো। আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে ইলিশ মাছ খাওয়া। ইলিশ মাছ শুধু বাংলাদেশেরই জনপ্রিয় মাছ নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লোকজনও সব সময় ইলিশের জন্য হাপিত্যেশ করে থাকে। ইলিশ মাছটি কিন্তু এমন কোনো মাছ নয়, যা শুধু পদ্মা কিংবা গঙ্গায় পাওয়া যায়। আমেরিকার পূর্ব উপকূলেও ইলিশ পাওয়া যায়। যেখানে এর নাম শ্যাড। ইরান-ইরাকে পর্যন্ত ইলিশের অস্তিত্ব আছে। সেখানে এর নাম সোউর কিংবা সোবুর, স্বাদ গন্ধ যাই হোক না কেন ইলিশকে প্রায় সর্বভারতীয় মাছই বলা চলে। কর্নাটকে ইলিশ মাছের নাম পালিয়া কিংবা পালাসা। গুজরাটে যে ইলিশ পাওয়া যায় তাকে বলে পান্না। আর আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে এই ইলিশ মাছের নামই ন-তা-লাউক্।
বাংলাদেশে বেশির ভাগ মানুষ যে কোনো মূল্যে পদ্মার ইলিশ এবং কলকাতার মানুষজন গঙ্গার ইলিশ খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু কেন? আমার মতে যে কোনো আহার্য বস্তু ও মাছের স্বাদের ব্যাপারে স্থানীয় জল-মাটির একটি প্রকট প্রভাব থাকে। নিজের মাটি ও জল থেকে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যগুলো যে অমৃতসুধা হবে সেটাই ন্যায়সঙ্গত নয় কী? তবে আমি পাঠকদের একটি বিষয় জানিয়ে দেই, ব্যক্তিগতভাবে ইলিশপ্রেমী হওয়ায় আমি নিজে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি যে, আমাদের এখানে পদ্মার ইলিশ হিসেবে যা প্রতিদিন বিক্রি হয় তাদের মধ্যে একাংশ আসলে মিয়ানমার থেকে আসা ইলিশ।
আমি এমন এক অবাঙালিকে চিনি, যিনি ইলিশ মাছ অসম্ভব পছন্দ করতেন। পাগলাটে সম্রাট মুহম্মদ বিন তুঘলক রোজার মাসে সারা দিন না খেয়ে সন্ধ্যায় ইলিশ খেয়েছিলেন বলে পেটের অসুখে মরেই গেলেন। অবশ্য বিখ্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, ইলিশ খাওয়ার জন্য তুঘলক বেহেশতেই নাকি গিয়েছিলেন।
এবার বাংলা সনের প্রচলন নিয়ে দুই-চার কথা বলা যাক। আমরা কমবেশি সবাই জানি, বাংলা সনের প্রবর্তক হচ্ছেন সম্রাট আকবর। কারণ হিসেবে ইতিহাসবিদরা বলেন, খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল থেকে খাজনা পরিশোধ করতে পারেন সে জন্যই আকবর বাংলা সন নামে নতুন একটি বর্ষ পঞ্জিকার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু বিশিষ্ট গবেষক ও ইতিহাসবিদ গোলাম মুরশিদ, ডক্টর আহমদ শরীফ ও জয়নাল আবেদীন খান প্রমুখের মতে, বাংলা সনটি আসলে আকবর প্রবর্তন করেননি। বাংলা সনের উদ্ভাবক আসলে ছিলেন মহারাজা বল্লাল সেন (ওরফে নবাব আবুল কাশেম ওরফে শাহজাদা মঙ্গৎ রায় ওরফে শ্রী ধরমসা) যিনি ছিলেন আরাকানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা মলহন ওরফে হুসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৬১২-২২)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। বল্লাল সেন ছিলেন ঢাকার নবাব এবং নিম্নবঙ্গের মোগল সুবেদার। ড. আহমদ শরীফের মতে সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে মোগলরা নামমাত্র বাংলার অধিকার লাভ করে। অধিকার লাভ করলেও আকবরের কোনো আগ্রহ ছিল না বাঙালির জীবন-জীবিকার প্রতি। অন্যভাবে বলা যায়, সম্রাট আকবর যদি সুবে বাংলার জন্য বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করতেন তাহলে মোগল সাম্রাজ্যের বাকি সুবাগুলোতেও বঙ্গাব্দের মতো সমান্তরাল উড়িষ্যাব্দ, বিহারাব্দ, গুজরাটাব্দ ইত্যাদি থাকার কথা ছিল, তাই নয় কী?
আমাদের প্রধান ফসল আমন ধান কৃষকের ঘরে উঠে অগ্রহায়ণ মাসে। বৈশাখ মাসে নয়। আর সেই জন্য ফসল তুলে খাজনা পরিশোধের ব্যাপারটাও স্পষ্ট নয়। অধুনা ইতিহাসবিদরা মনে করেন সম্রাট আকবরই যদি বাংলা সনটি চালু করে থাকেন তবে দলিল-দস্তাবেজগুলোতেও নিশ্চয়ই এর প্রমাণপত্র থাকাটি ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, দলিলপত্রে বাংলা সনের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে।
লেখক : গল্পকার ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী।
ই-মেইল : [email protected]