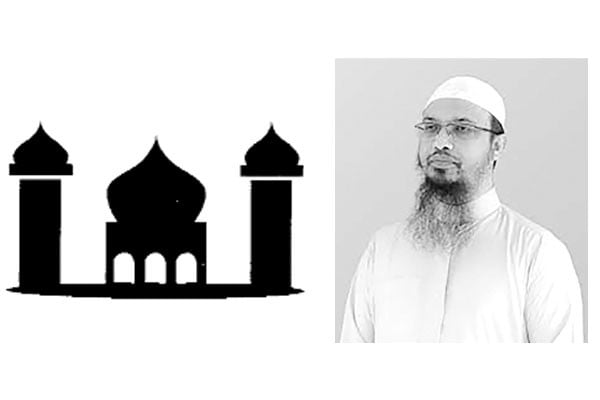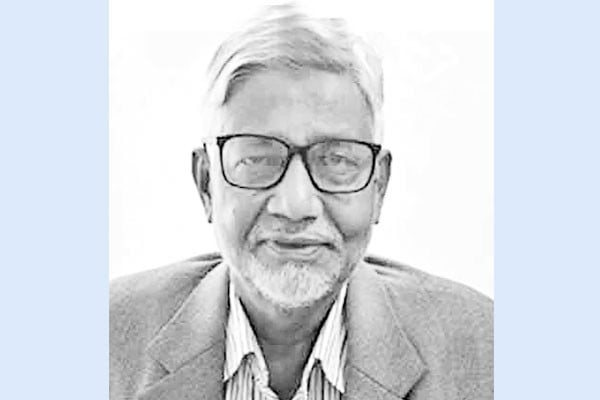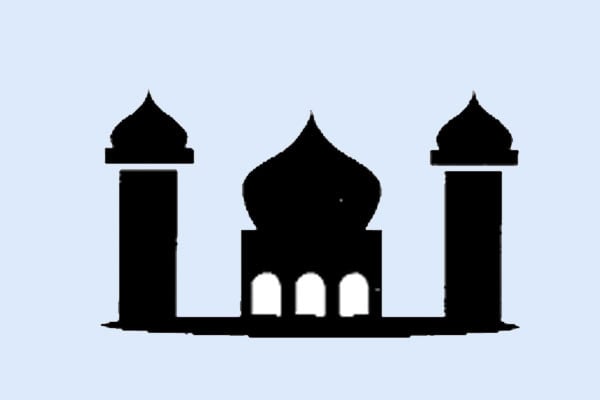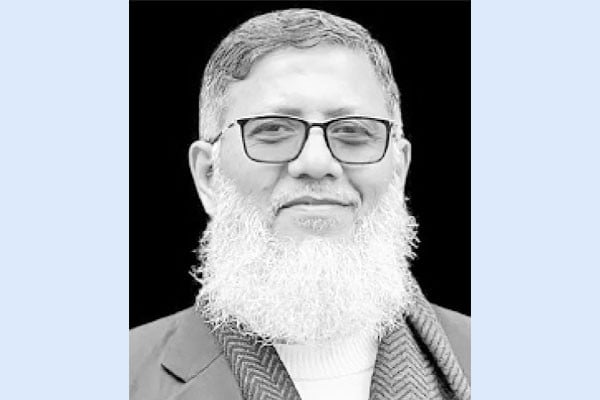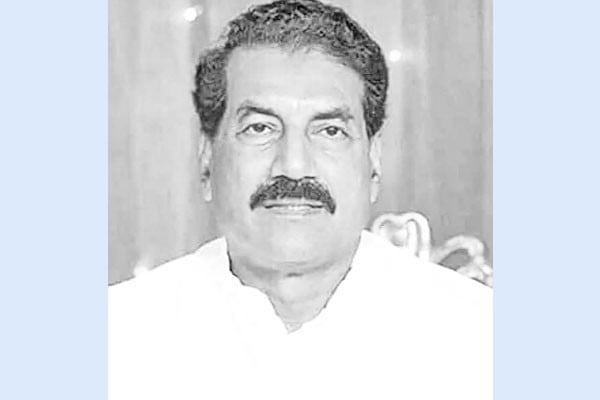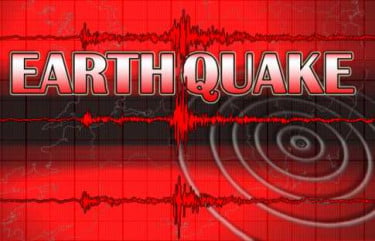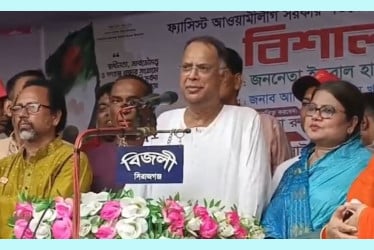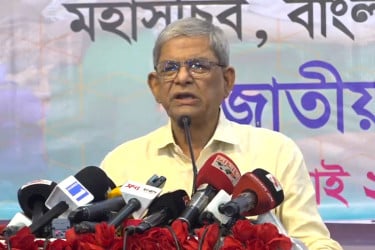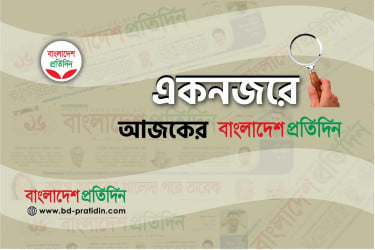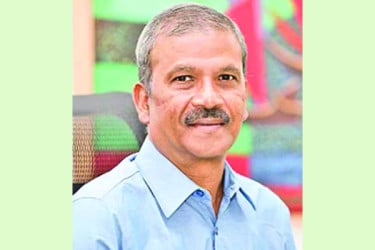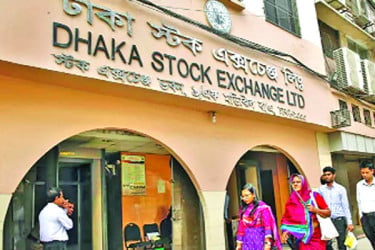২০২৩ ও ২০২৪ সালে যেসব শিক্ষার্থী মানসম্মত নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ৫৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৭ হাজার শূন্য আসনের বিপরীতে তিন লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। করোনা ভাইরাসের কারণে তাদের শর্ট সিলেবাসে পড়ানো হয় এবং সে অনুযায়ী বোর্ড পরীক্ষা নেওয়া হয়। যদিও ২০২৪ সালে পরীক্ষার্থীদের ৩-৪টি বিষয়ে পরীক্ষা না নিয়েই অটোপাস দেওয়া হয়। কলেজ ও কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরাও পরীক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হবে শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা দেয় ২০২৩ ও ২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। অথচ কৃষি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বইয়ের সমগ্র অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫-৬ নম্বর সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন করে, যা পরীক্ষার্থীদের কাছে তেমন অস্বাভাবিক ঠেকেনি। তবে কৃষি গুচ্ছের পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একধরনের প্রতারণা করা হয়েছে বলা যায়। এ বিষয়ে সরকারি কলেজের কয়েকজন শিক্ষক মন্তব্য করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নাকি প্রশ্নপত্র তৈরির সময় শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে কাক্সিক্ষত সমন্বয় করে না। আবার একেক বিশ্ববিদ্যালয় একেক নিয়মে পরীক্ষা নিয়েছে। যেমন- ঢাকা ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়; তন্মধ্যে ৪০ নম্বর লিখিত ও ৬০ নম্বর এমসিকিউ। কৃষি গুচ্ছের ১০০ নম্বরের পুরোটাই এমসিকিউ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ নম্বরের পরীক্ষায় পুরোটাই এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেওয়া হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট প্ল্যান থাকলেও জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট প্ল্যান ছিল না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে যে কোনো আসনে বসা যায়। ফলে একজন অভিজ্ঞ পরীক্ষার্থী পাশের জনকে বলে দেওয়ার সুযোগ নিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয়, তারা যেন সরকারের ভিতর আরেকটি সরকার। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের হয়রানির কথা বিবেচনা করে ২০১৯ সাল থেকে গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম চালু করে (দাবিটি প্রথম তোলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক। সে সময় কয়েকটি বামপন্থি ছাত্রসংগঠন তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল)। শুরু থেকেই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছের বাইরে থেকে যায় (কেউ কেউ মনে করেন, এসব বিশ্ববিদ্যালয় ব্রাহ্মণ্যবাদের গরিমায় ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজ গোত্রভুক্ত ভাবতে রাজি নয়)। তবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক কেন্দ্র স্থাপন করে অভিভাবকদের কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। ২০২৪ সালে বিভিন্ন কলেজ ও মাদরাসা থেকে এইচএসসি কিংবা সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছেন ১০ লাখ ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসনসংখ্যা ৫৭ হাজার ৯৯টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা ২ লাখ ২৫ হাজার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ৪ লাখ ৩৬ হাজার আসন রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৪ লাখ ছাত্রছাত্রী উচ্চতর শিক্ষার্জনের কোনো সুযোগ পাননি। এসব শিক্ষার্থী কেউ পাস কোর্সে, কেউ ছোটোখাটো কর্মে ঢুকে পড়েন। বহু অভিভাবক হতাশ হয়ে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা না দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। কলেজগুলোতে ঠিকমতো ক্লাস না হওয়াতে পরীক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারনির্ভর। কোচিং সেন্টারে ভর্তি ফি ২২-২৩ হাজার টাকা। যারা স্বল্প আয়ের লোক তাদের সন্তানরা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেন না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে গেলে ১৮-২০ লাখ টাকার প্রয়োজন পড়ে। সেখানেও প্রতিযোগিতা। সেগুলোর মধ্যে ১০-১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মানসম্মত ধরা যায়। আবার উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও বহু শিক্ষার্থী বেকার থাকছেন। প্রতিটি সরকার কর্মমুখী শিক্ষার কথা বলেন বটে; কিন্তু বাস্তবে কোনো পদক্ষেপ নেন না। বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার হার ১৭ দশমিক ৭৬ শতাংশ। অথচ জাপানে ৭৩ শতাংশ, জার্মানে ৭১ শতাংশ ও চীনে ৬৫ শতাংশ (চীনে মাধ্যমিক পর্যায়ে সব শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান নিতে হয়)। বিগত সরকারের আমলে শোনা যেত ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ করা হবে। বর্তমান সরকারের মুখে আরও চমকপ্রদ কথা শোনা যাচ্ছে, প্রতিটি হাসপাতালের সঙ্গে নার্সিং ইনস্টিটিউট খোলা হবে, যেন মেয়েদের স্বল্প বেতনে বিদেশে গিয়ে গৃহকর্মীর কাজ না করতে হয়। অতীতে সচ্ছল পরিবারের শিক্ষানুরাগী সন্তানরা স্বল্প বেতনে বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করতেন। তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন দেশে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের অধীন করায় এখন কেউ শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যান না। ভাবটা যেন এই- ‘শিক্ষার জন্য নয়, বেতনের জন্য চাকরি করি।’ স্কুল-কলেজগুলোতে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা ম্যানেজিং কমিটির হাতে থাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে ২০১৪ সাল থেকে নিবন্ধিত শিক্ষক নিয়োগ ‘এনটিআরসিএ’-এর হাতে চলে যাওয়ায় ম্যানেজিং কমিটির দৌরাত্ম্য কিছুটা কমেছে। হাতে গোনা কয়েকটি কলেজ ছাড়া কোথাও মানসম্মত লেখাপড়া হয় না। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের পোয়াবারো অবস্থা। তাদের বাড়িগুলো একেকটি মিনি কলেজ। অথচ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা টিউশনি অথবা কোচিং সেন্টারে যুক্ত থাকতে পারেন না।
লেখক : গণতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারবিষয়ক গবেষক