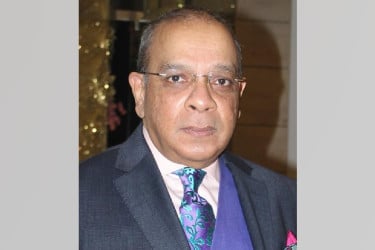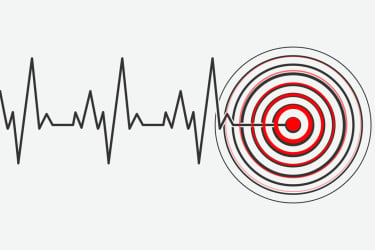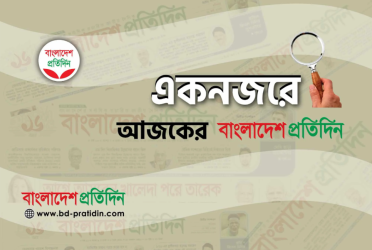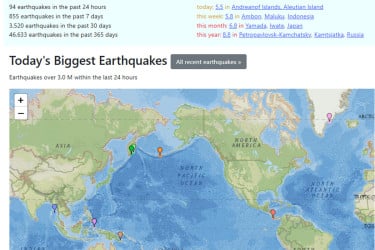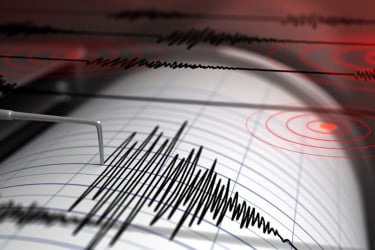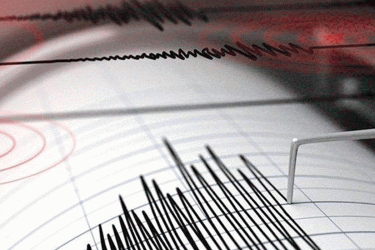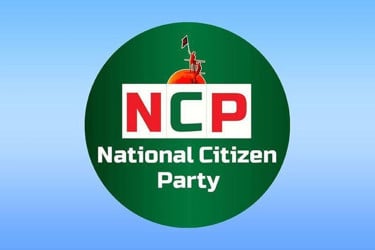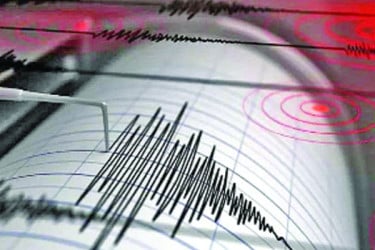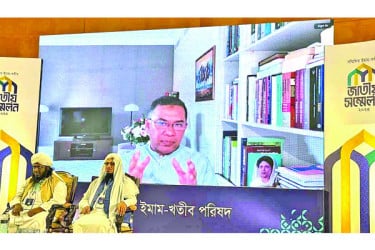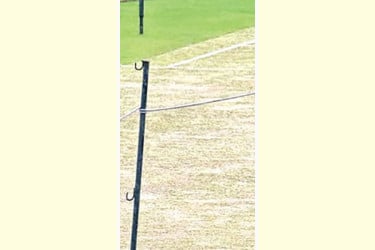বোধকরি ১৯৩০ সালের কথা। অ্যালবার্ট সেইন্ট জর্জ নামে জনৈক জৈবরসায়নবিদ হাঙ্গেরির সেজ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Szeged) ভিটামিন সি বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না তিনি। কাজের চাপে বেচারার নাওয়া-খাওয়া প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। দিন দিন উপোস থেকে থেকে বিজ্ঞানী মহাশয় তো শুকিয়ে একেবারে কাঠ। গবেষক বেচারার দয়ালু স্ত্রী একদিন নিজ হাতে পর্যাপ্ত প্যাপেরিকা (মরিচ) সহযোগে খাবার রান্না করে পাঠালেন স্বামীর জন্য। সেই ঝালযুক্ত রান্না খাবার মুখে তুলতেই বিজ্ঞানীর মাথায় বিদ্যুতের মতো এক বুদ্ধি খেলে গেল। পরদিনই জর্জ মহাশয় বস্তা বস্তা মরিচ কিনে আনলেন বাজার থেকে। কদিনের মধ্যেই চোখ জুড়ানো গাঢ় সবুজ রঙের সে মরিচগুলো থেকে তিনি হাফ লিটার ভিটামিন সি তৈরি করে ফেললেন গবেষণাগারে বসে। দুনিয়ার সব বিজ্ঞানী হইহই করে উঠলেন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন বিজ্ঞানী জর্জ। সে সময় বিষয়টি পৃথিবীতে এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করল যে অ্যালবার্ট জর্জকে নোবেল পুরস্কার না দিয়ে আর উপায় রইল না। ১৯৩৭ সালে তিনি মরিচ থেকে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড অর্থাৎ ভিটামিন সি আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। অনেক লোকের হয়তো এটি অজানা যে সমপরিমাণ কমলালেবু থেকে তিন গুণ ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড এ কাঁচা মরিচে বিদ্যমান। পরবর্তীকালে এই হাঙ্গেরিয়ান সায়েব কিন্তু লঙ্কানির্ভর এক নতুন ওষুধও বাজারে ছেড়ে ছিলেন। ভিটামিন স্টাইলে এর নাম দিয়েছিলেন তিনি প্রিটামিন।
এখানে এ ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এ কারণে যে মরিচ নিয়ে যেসব মানুষ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন এ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তারা অন্তত নিদেনপক্ষে এটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে মরিচ নিয়ে গবেষণা করেও নোবেল পুরস্কার জেতা যায়। অন্যদিকে প্রতি বছর আমাদের দেশে মরিচের ঝাঁজ টের পাওয়া যায় বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এবার মনে হচ্ছে মরিচের ঝাঁজটা যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। শ্রাবণের শেষ দিকে ঝালপ্রেমী বাংলাদেশিদের ২৫০ টাকা কেজি দরে মরিচ খেতে হয়েছিল। এখন অবশ্য লঙ্কার ঝাঁজ কিছুটা কমে এসেছে। ২৯ শ্রাবণ বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর ছাপা হয়েছে- ‘সীমান্ত পার হয়ে ঢাকায় এসেই তিন গুণ দাম কাঁচা মরিচের’।
অথচ ভারত থেকে দেশে কাঁচা মরিচ আসছে প্রতি কেজি ৫০ রুপিতে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর দাম পড়ছে ৬৫ টাকার মতো। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রতি কেজিতে ২২ টাকা শুল্ককর। প্রতি কেজিতে ফড়িয়াদের পেছনে খরচ হচ্ছে ৩ টাকা। বেনাপোল, সোনামসজিদ এসব স্থলবন্দর থেকে ঢাকার কারওয়ান বাজারে আসতে প্রতি কেজিতে খরচ পড়ছে আরও ১০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কেজিতে ভারতীয় কাঁচা মরিচের দাম পড়ছে ১০০ টাকা। অথচ এক মাস আগেও প্রতি কেজি কাঁচা মরিচের দাম ছিল ৪০ থেকে ৫০ টাকা। তবে ৬৫ টাকার কাঁচা মরিচ সব ধরনের খরচসহ ১০০ টাকা হলে খুচরা বাজারে তা ২০০ টাকা দরে কেন বিক্রি হবে তা মানতে পারছেন না কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ।
দেশের বাজারে কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে যাওয়ার পেছনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ উইং দায়ী বলে মনে করছেন কাঁচা মরিচ আমদানিকারকরা। হিলি স্থলবন্দর আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি হারুন উর রশীদ বলেন, ‘প্রতি বছর কোন সময় কাঁচা মরিচের ঘাটতি থাকে তা আমরা জানি। ১৫ দিন আগে আমদানি অনুমোদন (আইপি) চাইলে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ উইং এ অনুমোদন দেয়নি।’ এর কারণ হিসেবে তিনি ঘুষ দিতে না পারার কথা উল্লেখ করেন। তাহলে বোঝেন এই হচ্ছে দেশের অবস্থা।
পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক শংকরের একটি কথা আমার বেশ মনে ধরেছে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ নাকি ঝালপ্রেমী ও ঝালবিরোধী এ দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত। তবে আমার ধারণা মাঝেমধ্যে এই যে মরিচের মূল্য হঠাৎ এত বেড়ে যায় এর পেছনে ঝালবিরোধীদের কোনো হাত না থাকলেও মুনাফালোভীদের যে হাত আছে।
অনেকেই জেনে অবাক হবেন লঙ্কা কিংবা মরিচ যা-ই বলি না কেন এটা আমাদের দেশে ছিল না। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো দা গামা ভারত অভিযানের সময় আরও অনেক কিছুর মতো মরিচও নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে। এখন হয়তো অনেকেই বলবেন তাহলে কি ১৪৯৮ সালের আগে আমরা ঝাল খাবার খেতাম না। যদিও হিন্দুশাস্ত্র বেদসহ অন্যান্য পুরাণে লঙ্কার কথা উল্লেখ নেই। তবে সে সময় ঝালের জন্য বিভিন্ন ব্যঞ্জনে ব্যবহার হতো গোলমরিচ ও আদা। ষোল শতকের শেষ দিকে উত্তর ভারতে বসে আবুল ফজলের লেখা ‘আইন-ই-আকবরি’তে ৪০টি পদের রান্নার বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু তার কোনোটিতেই মরিচের নামগন্ধ নেই। সব পদেই গোলমরিচের ব্যবহারের কথা লেখা। কাঁচা মরিচ আসার আগে প্রাচীন ভারতে ধারণা ছিল অতিমাত্রায় ঝাল আমাদের সিস্টেমটাকে গরম করে দেয়। এজন্য মানুষ তখন ঝাল খাবার কমই খেত। ভাস্কো দা গামার হাত ধরে মরিচ ভারতে এলেও এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিন্তু তার নয়। বরং লঙ্কা আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তার আরেক সতীর্থ অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাসের। কলম্বাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমেরিকা আবিষ্কারের সময় ওখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন মরিচ। মধ্যযুগে ইউরোপে এক অদ্ভুত খাদ্য সমস্যা বিদ্যমান ছিল। মাছ-মাংস কোনো কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু সেসব খাদ্য মুখে তোলার জন্য দরকার গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা। আর সেসব মশলা আরব বণিকদের হাত ধরে ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়দ্বীপ থেকে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে পৌঁছাত মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে। পাঠক জেনে অবাক হবেন যে ইজিপ্টের ফারাওদের মমিতে ভারতবর্ষের অত্যাশ্চর্য সব মশলা ব্যবহার হচ্ছে অন্তত ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন! এ মরিচের সন্ধানে যুগযুগান্ত ধরে ফিনিশিয়ান, সিরিয়ান, ইজিপশিয়ান, গ্রিক, রোমান, আরব ও চাইনিজরা আমাদের দেশে হাজির হয়েছে। তো যে কথা বলছিলাম, আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর থেকে সেসব মশলা ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে পৌঁছাত ইতালির ভেনিসের বাজারে। খাবার দাবার ঝাল ও মুখরোচক করতে তখনো গোলমরিচের জুড়ি ছিল না। তাই আকাশছোঁয়া ছিল তার দাম, এতটাই যে গোলমরিচকে ‘কালো সোনা’ বলা হতো। রোমানরা গোলমরিচের পরিবর্তে ভারতবর্ষকে সোনা দিত। বহু শতাব্দী ধরে সোনা-রুপার মতো মূল্যবান ছিল এ গোলমরিচ। মরিচ দিয়ে ট্যাক্স দেওয়া যেত। দেনা শোধ করা যেত। ইংল্যান্ডে অর্ধকিলো গোলমরিচের বিনিময়ে বেশ কয়েকটি ভেড়া পাওয়া যেত। সেজন্য মাঝেমধ্যেই আরব বণিকেরা আজগুবি সব গল্প ফেঁদে মশলার বাজারে আগুন ধরিয়ে দিত। এসব গল্পের কিছু আপনারা পাবেন ইতিহাসে প্রথম ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের বইয়ে। পাঠক গোলমরিচ আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। প্রথম দেখাতেই মনে হবে যেন আগুনে ঝলসানো কোনো শস্যদানা।
ভেনিসের বেনেরা যখন আরব বেনেদের জিজ্ঞেস করত, এসব মশলা কোথায় পাওয়া যায়? আরব বণিকরা তখন নাকি বর্তুল চোখগুলো বড় বড় করে বলত এগুলো তো পাওয়া যায় ভারতবর্ষে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এসব মশলার বাগান পাহারায় থাকে বড় বড় সব ড্রাগন, সেগুলোর নাক দিয়ে আগুন বের হয় আর সে আগুনে পুড়েই তো গোলমরিচগুলো কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আমরা ওইসব ড্রাগন আর দৈত্যদানবের চোখ ফাঁকি দিয়ে, জীবন বাজি রেখে তবেই তো তোমাদের জন্য নিয়ে আসি এসব মশলা। সেজন্যই তো এগুলোর এত দাম!!! হেরোডোটাসের বইয়ে আরও মজার মজার সব গল্প আছে। আপনারা পড়লে সেসব পাবেন।
কিন্তু ইউরোপবাসীর সুখ চিরকাল টিকল না। অটোমান শাসনকালে এ প্রচলিত রুট বন্ধ হয়ে গেল। ইতালিয়ানরা দারুণ আর্থিক সংকটে পড়ল। কারণ ভেনিসের বাজার থেকেই দেশের সিংহভাগ রাজস্ব আসত। মশলাপাতির ঊর্ধ্বগতির প্রভাব বেশি করে পড়ল ইউরোপের অন্য দেশগুলোতেও। কলম্বাসও জাহাজে উঠেছিলেন ভারতবর্ষে গিয়ে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা নিয়ে এসে দেশের অর্থনীতি বাঁচাবেন বলে। একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের রাস্তা তৈরিরও ইচ্ছা ছিল তার।
তিনি নতুন দেশে পৌঁছে দেখলেন লোকে লঙ্কা দিয়ে বিভিন্ন ব্যঞ্জন রান্না করে হাপুসহুপুস খাচ্ছে। এই দেখে তার বিশ্বাস আরও পোক্ত হলো যে নিশ্চয়ই এটা ভারতবর্ষের কোনো দ্বীপ। প্রায় ৪ হাজার বছর ধরে সেখানকার লোক তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেত ‘আজি’ বলে এক রকম লঙ্কা।
মরিচের আদিনিবাস দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন টিয়াসহ অন্য অনেক পাখিরই পছন্দের খাবার হচ্ছে মরিচ। আর সেখান থেকে পাখিদের মলমূত্রের মাধ্যমে ও স্থানীয় বাসিন্দাদের হাত ধরে মরিচ একসময় উত্তর ও দক্ষিণ দুই আমেরিকাতেই ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যই বিজ্ঞানীরা প্রথমে ধারণা করেছিলেন মরিচের আদিনিবাস সম্ভবত মেক্সিকো। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে মরিচের আদিনিবাস বলিভিয়া।
স্পেন ও পর্তুগালের বেশ কাছাকাছি দেশ হয়েও ইংরেজদের ঝাল খাওয়া শিখতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। তারা ৪০০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেও ঝাল খাওয়া রপ্ত করতে পারেনি। পলাশীর যুদ্ধের পরই রবার্ট ক্লাইভ কী কী খাবার খেয়েছিলেন তা নিয়েও নাকি বিবিসি রিসার্চ করেছে। ক্লাইভ সাহেব নাকি খেয়েছিলেন চিকেন দোপিঁয়াজা মালাই চিংড়ি এবং বিরিয়ানি কিন্তু সেসব ব্যঞ্জনে কী পরিমাণ ঝাল ছিল তা জানা যায়নি। রবার্ট ক্লাইভের ঝাল খাওয়ার বিষয়ে কিছু খুঁজে না পাওয়া গেলেও ওয়ারেন্ট হেস্টিংসকে যে প্রাণ বাঁচাতে একবার কাঁচা মরিচ দিয়ে পান্তাভাত খেতে হয়েছিল সে ইতিহাস আছে।
একবার ওয়ারেন হেস্টিংসের এক কুকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিদ্ধান্ত নিলেন হেস্টিংসকে জেলে পুরবেন। খবর পেয়েই হেস্টিংস কাশিমবাজার ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। হেস্টিংস ভাবতে লাগলেন কোথায় যাওয়া যায়? কার কাছে যাওয়া যায়? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল কান্তবাবুর নাম। অন্ধকারে চুপি চুপি তিনি হাজির হলেন কান্তবাবুর দোকানে। সেখান থেকে তার বাড়িতে। কান্তবাবুর ভালো নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র তখন কাশিমবাজার। কাশিমবাজারে কান্তবাবুর ব্যবসা ছিল সুপারি ও রেশমের। দোকানটা আবার ইংরেজদের কুঠি আর রেসিডেন্টের সঙ্গে একেবারে লাগোয়া। ফলে অচিরেই ইংরেজদের সঙ্গে বেশ একটা মাখামাখি ভাব হয়ে গেল কান্তবাবুর। সেই থেকে কান্তবাবুর সঙ্গে হেস্টিংসের চেনাজানা। যা হোক, কান্তবাবু হেস্টিংসকে দেখে তো স্তম্ভিত! কোথায়? কীভাবে লুকিয়ে রাখবেন তিনি হেস্টিংসকে? কান্তবাবু প্রথম কয়েকদিন তাকে লুকিয়ে রাখলেন তার মুদি দোকানে। দোকানে হাতের কাছে তেমন কিছু না পেয়ে কান্তবাবু হেস্টিংসকে আপ্যায়ন করেছিলেন কাঁচা মরিচ দিয়ে পান্তাভাত আর সঙ্গে ছিল চিংড়ি মাছ।
স্বামী বিবেকানন্দের আগে মরিচ এবং ভারতীয় রান্নাকে বিদেশে প্রচারের জন্য তেমন কেউ একটা অবদান রাখেনি। ইচ্ছা করলে সে অবদান রাখতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু তিনি আদৌ ঝালাণুরাগী ছিলেন কি না সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।
বিবেকানন্দের মেজ ভাই মহিমবাবু লিখে গিয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দের ডাকনাম) মরিচ খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন, তীব্র ঝাল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মিষ্টান্ন একেবারে পছন্দ করতেন না; তবে পরবর্তী জীবনে স্বদেশে ও বিদেশে তাঁকে আইসক্রিমে আসক্ত হতে দেখা গিয়েছে।
এ মরিচপ্রীতি প্রচন্ড অভাবের সময় বিবেকানন্দকে শক্তি দিয়েছে। রামকৃষ্ণর মৃত্যুর পর বরানগরে সাধনভজনের সময় প্রবল অভাব-অনটন। দারিদ্র্য এমনভাবেই গ্রাস করেছিল যে মুষ্টিভিক্ষা করে এনে তা ফুটিয়ে একটা কাপড়ের ওপর ঢেলে দেওয়া হতো। একটা বাটিতে থাকত লবণ ও মরিচের পানি। একটু ঝালজল মুখে দিয়ে এক এক গ্রাস ভাত উদরস্থ করা হতো।
১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন বিলেতে গিয়েছিলেন সেখানে তখন মরিচের ভীষণ আকাল। স্বামীজি প্রায়ই ঝাল খাদ্যের জন্য হাপিত্যেশ করেন। একদিন এক সহযোগী বহু কষ্টে উইলিয়াম হোয়াইটের দোকান থেকে তিনটি কাঁচালঙ্কা কিনে আনলেন। ১০০ বছর আগে সেই ১৮৯৬ সালে সায়েবদের দেশে তিনটি কাঁচা লঙ্কার দাম ছিল ৩ শিলিং যা তখনকার ৩ টাকার মতন। বিবেকানন্দ মরিচের মোহমায়া সামলাতে পারলেন না, সব কটা লঙ্কা খেয়ে ফেললেন। লন্ডনে একদিন কচুরি ও আলুচচ্চড়ি রেঁধেছিলেন বিবেকানন্দ। কাজের মেয়েটি ভাগ না পেয়ে রেগে বলল, ‘আমার জন্য কিছু রাখনি।’
এক চামচ আলুচচ্চড়ি মুখে নিয়ে মিস কেমিরন লাফাতে লাগলেন। প্রবল ঝাল সামলাতে দুই হাতে দুই গাল চড়াতে লাগলেন এবং স্বামীজিকে উদ্দেশ করে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। ‘ও ইট্’স পয়জন, ও ইট্’স পয়জন!’ ১০০ বছর আগের সেই ইংরেজ এখন অন্য মানুষ, তারা এখন ঝাল কম হলে চটে যায়, কারিতে চাই ঝাল আরও ঝাল এই হলো এ যুগের স্লোগান এবং এ পরিবর্তনে বিবেকানন্দর ভূমিকা অবহেলার যোগ্য নয়।
পাঠকের অনেকের মনেই হয়তো এ প্রশ্ন আসতে পারে মরিচকে লঙ্কা নামে কেন সম্বোধন করা হয়? পর্তুগিজরা যখন এ দেশে লঙ্কা নিয়ে এলো তখন লঙ্কার নাম হলো গাছমরিচ। আর বঙ্গে লঙ্কা নামের পেছনের কারণটি হলো আসলে প্রাচীন ভারতে জলবেষ্টিত যে কোনো ভূখন্ডকেই লঙ্কা বলা হতো। এক অর্থে লঙ্কা শব্দের অর্থ বিদেশ। যেমন ওড়িশার মানুষ লঙ্কাকে বলে সোপারিয়া, সোপারিয়া অর্থ সাগরপাড়িয়া।
শুধু সাধারণ মানুষই নয়, পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লোক এখন মরিচে আসক্ত। যেমন একসময়ের বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা গ্রেগরি পেক, স্পেনের রাজা জুয়ান কার্লো এবং পাশ্চাত্য সংগীতের একসময়ের কিংবদন্তি পুরুষ জুবিন মেহতা। জুবিন যেখানেই যান সেখানেই পকেটে লঙ্কা নিয়ে যান। তেলআবিবে এক কনসার্টের সময় বিখ্যাত লঙ্কা গবেষক ও লেখক অমল নাজ মশাই তাকে পাকড়াও করলে জুবিন স্বীকার করলেন যে তাঁর দেশলাই বাক্সে তখনো দুটো লাল লঙ্কা রয়েছে। জুবিন অকপটে স্বীকার করলেন, ‘লঙ্কা ছাড়া মনে হয় যেন হাসপাতালে শুয়ে রোগীর পথ্য খাচ্ছি।’ রেস্তোরাঁয়ও যখন তিনি যান নিজের ম্যাচবক্সটি চুপিচুপি এগিয়ে দেন, ওয়েটার সেটি নিয়ে ছোটেন কিচেনে, সেখানে চিফ শেফ নিজেই জুবিন মেহতার খাবারে লঙ্কা ঢেলে দেন!
জুবিনের বাগানে তিন রকম লঙ্কা গাছের চাষ হয়- জালাপেলো, টাবাস্কো ও হাঙ্গেরিয়ান চেরি। তার দেখাদেখি চিত্রতারকা গ্রেগরি পেকও তাঁর বাগানে লঙ্কা লাগিয়েছেন। জুবিন মেহতা বেজায় খুশি- ‘ভালোই হয়েছে। এত দিন সব ভোজসভায় গ্রেগরি আমার লঙ্কায় ভাগ বসাত।’ ইংল্যান্ডের রানী একবার জুবিন মেহতাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেন। সেখানে জুবিনের সোনার ছোট্ট বক্স থেকে লঙ্কা বেরিয়ে এলো। ভদ্রতাবশত জুবিন তার লঙ্কার কৌটোটা রানীর দিকে এগিয়ে দিলেন। রানী অবশ্য লঙ্কা নিলেন না কিন্তু জুবিনের কৌটোটা অন্য অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিলেন। স্পেনের রাজা কার্লো তো একবার জুবিনের বাড়িতে ডিনার খেতে এসে তাঁর লঙ্কাবাগান দেখতে চাইলেন এবং সেখানে গিয়ে পটপট করে মরিচ তুলে নিয়ে পকেটে ফেলতে লাগলেন স্পেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
লেখক : গল্পকার ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ।
ইমেইল : [email protected]