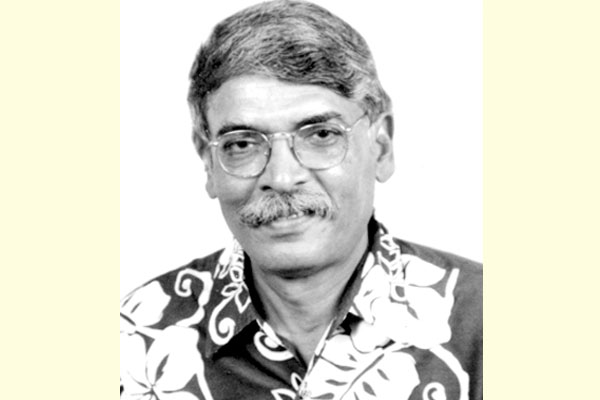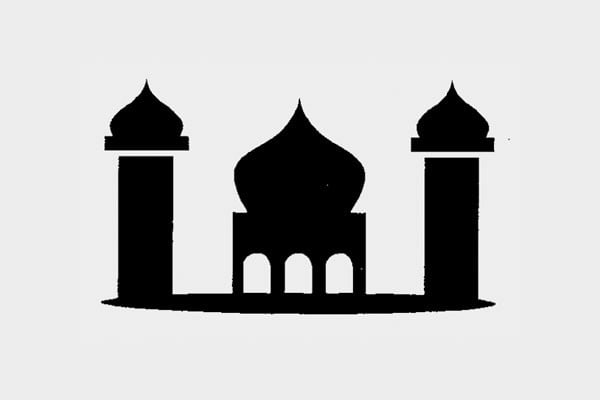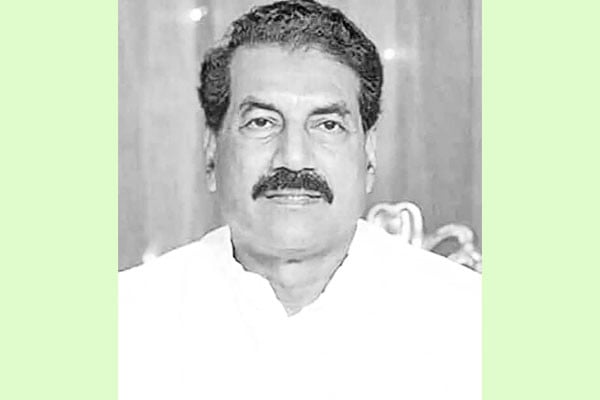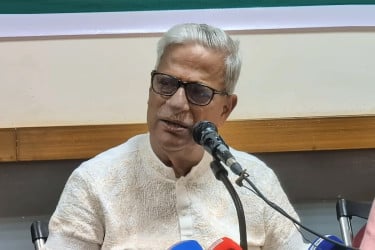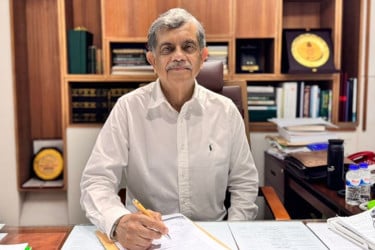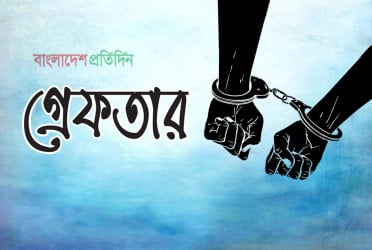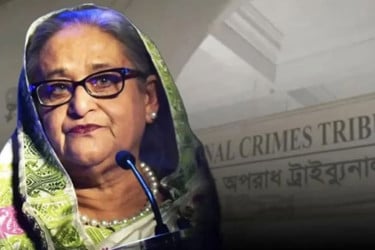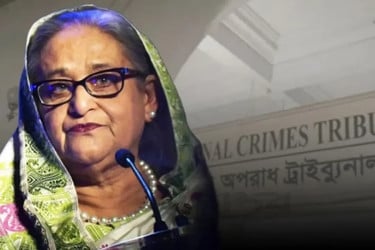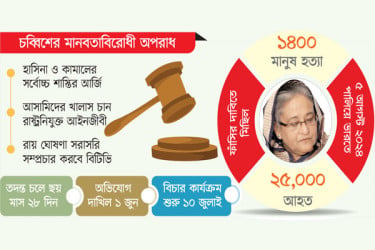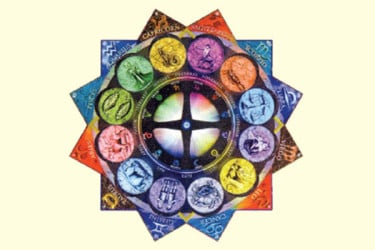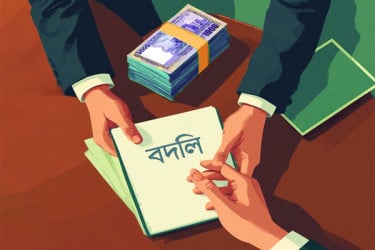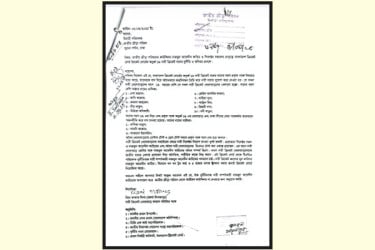পাবনা জেলার পূর্বদিকের যমুনা নদী-তীরবর্তী গ্রামে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করত। সেই গ্রামটির নাম তাঁতীবন্দ। আমার ধারণা ওই গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের লোকই তন্তুবায় ছিলেন বলেই নাম হয়েছে তাঁতীবন্দ।
তাঁতীবন্দের জমিদার ছিলেন অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী। তিনি কোনো দিনই প্রজাদের ওপর অনাচার, অত্যাচার করতেন না। তার যে সব প্রজা ঠিকমতো জমির খাজনা দিতে পারতেন না, তাদের ওপর অত্যাচার না করে বরং বলতেন এ বছর বর্ষা এবং খরা দুটোই প্রবল ছিল। আশা করি, আগামী মৌসুমে আমন ধান, আউশ ধান এবং পাট যখন উঠবে, তখন তোমাদের জমির খাজনা দিয়ে দেবে। তোমাদের টাকা পেলে দিতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে। জমিদার মহাশয় ছিলেন শিক্ষিত, কলকাতার স্কুল থেকে এনট্রান্স (মাধ্যমিক) পাস করে ফিরে এসেছিলেন তার জন্মভূমি তাঁতীবন্দে। তার পিতার মৃত্যুর পর তাকেই জমিদারির দায়ভার নিতে হয়েছিল।
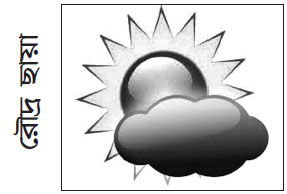 ১৮৯০ সালের কয়েক বছর আগে তিনি পাবনা শহরের গোপালপুর মহল্লায় ১৩ শতাংশ জমির ওপর বানিয়েছিলেন তার জমিদারির কাচারিবাড়ি। পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউটের পূর্ব দিকে। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় তাঁতীবন্দের জমিদারের প্রজারা শহরে আসতেন যমুনা এবং পদ্মা পাড়ি দিয়ে। শহরের দক্ষিণ দিকের পদ্মা নদীর শাখা, ইছামতী নদী দিয়ে। কখনো শীতলাই জমিদারের বাড়ির ঘাটে। আবার কেউ কেউ আসতেন সুজানগর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। প্রজারা জমির খাজনা দিয়ে ওইদিন ফিরে যেতেন তাঁতীবন্দে। জমিদার অন্নদা গোবিন্দ থাকতেন শহরে। মাঝে মাঝে তিনি যেতেন তার গ্রামের বাড়ি। গিয়ে প্রজাদের কুশলাদি জানতেন। দিন কয়েক থেকে ফিরতেন শহরের বাড়িতে। কাচারিবাড়িতে দুর্গাপূজার সময় আনন্দ উৎসবে কলকাতা থেকে শিল্পীরা আসতেন। বিসর্জনের পর শিল্পীদের ইছামতী, পদ্মা পাড়ি দিয়ে বজরা নিয়ে যেতেন তাঁতীবন্দে তার জমিদারিতে। শিল্পীদের প্রচুর সম্মানী দিয়ে পৌঁছে দিতেন স্টেটের ম্যানেজার প্রফুল্ল বাবুকে দিয়ে কলকাতায়।
১৮৯০ সালের কয়েক বছর আগে তিনি পাবনা শহরের গোপালপুর মহল্লায় ১৩ শতাংশ জমির ওপর বানিয়েছিলেন তার জমিদারির কাচারিবাড়ি। পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউটের পূর্ব দিকে। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় তাঁতীবন্দের জমিদারের প্রজারা শহরে আসতেন যমুনা এবং পদ্মা পাড়ি দিয়ে। শহরের দক্ষিণ দিকের পদ্মা নদীর শাখা, ইছামতী নদী দিয়ে। কখনো শীতলাই জমিদারের বাড়ির ঘাটে। আবার কেউ কেউ আসতেন সুজানগর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। প্রজারা জমির খাজনা দিয়ে ওইদিন ফিরে যেতেন তাঁতীবন্দে। জমিদার অন্নদা গোবিন্দ থাকতেন শহরে। মাঝে মাঝে তিনি যেতেন তার গ্রামের বাড়ি। গিয়ে প্রজাদের কুশলাদি জানতেন। দিন কয়েক থেকে ফিরতেন শহরের বাড়িতে। কাচারিবাড়িতে দুর্গাপূজার সময় আনন্দ উৎসবে কলকাতা থেকে শিল্পীরা আসতেন। বিসর্জনের পর শিল্পীদের ইছামতী, পদ্মা পাড়ি দিয়ে বজরা নিয়ে যেতেন তাঁতীবন্দে তার জমিদারিতে। শিল্পীদের প্রচুর সম্মানী দিয়ে পৌঁছে দিতেন স্টেটের ম্যানেজার প্রফুল্ল বাবুকে দিয়ে কলকাতায়।
জমিদার অন্নদা গোবিন্দ খুবই শৌখিন ছিলেন। নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। তিনি একদিন লক্ষ্য করলেন, পাবনা শহরে কোনো পাবলিক লাইব্রেরি নেই। স্থানীয় লোকজনের খবরের কাগজ পড়ার কোনো সুযোগ নেই। তক্ষুনি স্থির করলেন শহরের শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন করবেন। গোবিন্দ বাবুর বন্ধু ছিলেন রাধানগরের মোখতার ভবতোষ মজুমদার, কালাচাঁদ পাড়ার উকিল গণেশ দত্ত। গোপালপুরে একটি স্কুলের শিক্ষক প্রমথ লাহিড়ীসহ আরও জনাকয়েকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সবাই সহমত পোষণ করলেন একটি পাবলিক লাইব্রেরির প্রয়োজন আছে পত্রিকা পাঠকদের জন্য। কলকাতা থেকে পাবনায় পত্রিকা আসত কলকাতায় প্রকাশিত হওয়ার দুই দিন পর।
অন্নদা গোবিন্দর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোপাল চন্দ্র লাহিড়ীর সামনেই ঘোষণা দিলেন, আগামী মাস থেকে আমার কাচারিবাড়ি এখানে আর থাকবে না। যাবে তাঁতীবন্দে। আর শহরের এই ১৩ শতাংশ জমির ওপর বানানো হবে পাবলিক লাইব্রেরি। কাঁলাচাদ পাড়ার উকিল গণেশ দত্ত প্রস্তাব করলেন পাবলিক লাইব্রেরিটি আপনার নামেই হবে। উপস্থিত সবাই সমর্থন জানালেন এবং তক্ষুনি জমিদার জানালেন, কলকাতা থেকে নিজে গিয়ে বই আনবেন। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, ধর্মীয় গ্রন্থ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রথম আলোচনার সময় ছিলেন পাবনা গোপাল চন্দ্র ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী। কলকাতা যাওয়ার সময় লাহিড়ী বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দ বাবু অনেক টাকার বই কিনে এনেছিলেন পাবলিক লাইব্রেরির জন্য। লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হলো। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জমিদার অন্নদা বাবু না হয়ে অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপান্তে প্রথম সভাপতি বানিয়েছিলেন ইংরেজ সাহেবকে। সম্ভবত পাবনা জেলার প্রশাসক ছিলেন মি. ডব্লিউ প্রিডেন। তিনি সভাপতি পদে মাত্র দুই বছর ছিলেন। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক/লাইব্রেরিয়ান ছিলেন শিক্ষিত সীতানাথ অধিকারী। ১৮৯০ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত একটানা ৩৪ বছর ছিলেন ওই পদে। ১৯২৪ সালের পরে আরও দু-তিনজন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ইতোমধ্যে লড়কে লেঙ্গের গরম বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় আহত/নিহত হলেন দুই সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষগুলো ইংরেজদের কূটবুদ্ধিতেই। ভারতবর্ষ ভাগ হলো ১৯৪৭ সালে। পাকিস্তান নামক একটি দেশ পেলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। অপরদিকে ভারত নামক দেশটির জনক হলো- করমচাঁদ গান্ধী। মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা ভাগে পড়ল পাকিস্তানের। যার পরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার হিন্দু জন্মভূমি ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিলো ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। অনুরূপভাবে ভারত থেকে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে এবং করাচি পাড়ি দিলেন। এসবই হয়েছিল আমার জন্মের আগে। পিতার দোতলা বাড়ি ছিল শহরের জিলাপাড়া মহল্লায়। আমাদের বাড়ির সামনেই এখনো আছে পাবনা পলিটেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রাবাস, একটু দক্ষিণে জেলা জজের বাস ভবন, সেই বাস ভবন থেকে মিনিট তিনেক পুবের দিকে গেলেই মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়ি। মিসেস সেনের পিতা ছিলেন পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তা। আর আমাদের জিলাপাড়ার বাড়ি থেকে সুচিত্রা সেনের (রমা), বাড়ির দূরত্ব মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ।
যা হোক, আমার স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল পাবনা জিলা স্কুলে, ১৯৫৬ সালে। পাবনা জিলা স্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক মাওলানা জসিমউদ্দিন আহমদ প্রতিটি বাড়ি থেকে ছাত্র নিয়ে গিয়ে তার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করাতেন। বেতন ছিল এক টাকা আট আনা। আর সারা মাসের টিফিন ফি ছিল আট আনা। কয়েক বছর লেখাপড়া করেছিলাম জিলা স্কুলেই। একদিন পিতামহ মারা গেলেন আমাদের জিলাপাড়ার দোতলা বাড়িতেই। পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে। পিতার মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি জিলাপাড়ায় না থেকে শহরের পূর্ব দিকে দোহার পাড়ায় চলে এলেন, প্রচুর জমিজমা রক্ষার্থে। অপর দিকে শহরের দোতলা বাড়ি মাত্র ৪০ টাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ অফিসকে ভাড়া দিয়েছিলেন। গ্রামে এসে, আমি রবীন্দ্রনাথের ফটিক হয়ে গেলাম। একদিন সুপারি গাছ থেকে লাল সুপারি পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে দীর্ঘদিন পাবনা সদর হাসপাতালে থাকার ফলে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। ডাক্তারের নির্দেশে কোনো স্কুলেই ভর্তি করেননি পিতা। শেষে দুই বছর নষ্ট করে পাবনা গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়েছিলাম ৬০ দশকের গোড়ার দিকে। গোপাল চন্দ্র ইনস্টিটিউশন বা জিসিআই থেকে আমাদের অগ্রজ জিয়া হায়দার ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়েছিলেন। মেজো অগ্রজ রশিদ হায়দারও ওই স্কুল থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়েছিলেন। আমি মাধ্যমিক পাস করেছিলাম ১৯৬৫ সালে। জিয়া হায়দারই আমাদের বংশের প্রথম মাধ্যমিক পাস। ওই স্কুলে আমাদের ভাইয়েরা এবং আমাদের কাকাদের ছেলে ও গ্রামের অনেক ছেলে লেখাপড়া করেছে। মেজো কাকার ছেলে মোকলেসুর রহমান বাদশা, আনিসুর রহমান রাজা, ছোট কাকা আবুল কাসেমের ছেলে মোশাররফ হোসেন, হায়দার খোকন, জাহিদ হায়দার স্বপন, আবিদ হায়দার তপন। আমরা কয়েক ভাই পাড়ার জনাকয়েকের সঙ্গে যেতাম প্রায় ২ মাইল হেঁটে রাস্তায় বুনদে উড়িয়ে। শরৎচন্দ্রের ‘বিলাসী’ গল্পের দলনেতার মতো। আমাদের স্কুলের বাংলা শিক্ষক ছিলেন বিমল ভৌমিক। বিএ বিটি কলকাতা বিকালবেলায় তিনি ছিলেন পাবনা অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ওই দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ১৯৬৪ সালে পাবনায় দাঙ্গা বাধিয়ে ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এবং উসকানিদাতা ছিলেন পাবনার জেলা প্রশাসক। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। রাতারাতি অনেক মানুষ নিহত হলেন। থানাপাড়ার বিহারি এবং কসাইরা যুক্ত ছিল হত্যাকান্ডে। মেরেছিল পশ্চিম দিকের উকিল মোখতারদের মধ্যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন বিখ্যাত উকিল প্রভাত কুমার রায়, জগদীশ গুহ এবং দেবেন রায়সহ অনেকে। তবে শালগাড়িয়া এবং কালাচাঁদ পাড়ার অনেকেই নিহত হয়েছিলেন। দিলালপুরে নিহত হয়েছিলেন বলাই দে। আমাদের শিক্ষক জীতেন দের কলেজপড়ুয়া ছেলে। পূর্বদিকের আতাইকুলা এবং লক্ষ্মীপুর গ্রামে একাধিক পরিবার আহত-নিহত হয়েছিল। পোড়ানো হয়েছিল বাতিঘর। খুনোখুনিতে জড়িত ছিল পাবনা শহরের পশ্চিম দিকের মহল্লা কেষ্টপুরের গুন্ডারা এবং পূর্বদিকের আরিফপুর গ্রামের ইউনুস, সোহরাবসহ আরও অনেকেই। পরের বছর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান থেকে অধিকাংশ হিন্দু পরিবার রাতের অন্ধকারে পাড়ি জমিয়েছিল ভারতে। তাদের ভিতরে আমাদের শিক্ষক এবং অন্নদা গোবিন্দ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বিমল ভৌমিক এবং উকিল মোখতার, ব্যবসায়ীরা ছিলেন। অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি বন্ধ ছিল অনেক দিন। আমাদের গোপাল চন্দ্র ইনস্টিটিউশনের বাংলা শিক্ষক রশীদ ভাই আমাকে স্নেহ করতেন। রশীদ ভাই, অন্নদা গোবিন্দ লাইব্রেরির সভ্য হলেও আমি হইনি। ভারতে যাওয়ার আগে বিমল স্যার তথা লাইব্রেরিয়ান আমাকে তার স্বাক্ষরিত একটি বই লিখে দিয়েছিলেন স্নেহের মাকিদকে। সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে-বিদেশে’। ১৯৬৫ সালের পরে পাবনা অন্নদা গোবিন্দ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হয়েছেন আবদুল খালেক নামের এক সরকারি কর্মচারী। ১৯৭১ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময় পাকিস্তানি আর্মিরা শহরের টেলিফোন ভবনে ঘাঁটি বানিয়েছিল। পাবনা শহরের উকিল আমিন উদ্দিন, দাঁতের ডাক্তার দক্ষী এবং লাইব্রেরিয়ান আবদুল খালেকসহ সাতজনকে পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউটের মাঠে দাঁড় করিয়ে হত্যার আগে তাদের দিয়ে কবর খুঁড়িয়েছিল পাকিস্তানি দস্যুরা। গুলিতে ছয়জন নিহত হয়েছিলেন। আবদুল খালেককে মৃত ভেবে কবরে ফেলে সামান্য মাটি চাপা দিয়ে খুনিরা ফিরে গিয়েছিল টেলিফোন ভবনে। আবদুল খালেকের গায়ে গুলি না লাগায় বেঁচে গিয়েছিলেন। এবং রাত একটু গভীর হলে কবর থেকে উঠে গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। দেশে স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পুনরায় গোবিন্দ চন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান থাকার কয়েক বছর পর তিনি মারা যান। পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজের বাংলার অধ্যাপক কবি, প্রাবন্ধিক আমার বন্ধু মনোয়ার হোসেন জাহিদও দীর্ঘদিন লাইব্রেরিয়ান পদে থাকার পরে তিনি তার প্রিয়জন অধ্যাপক আবদুল মতিনকে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব দিয়ে কিছুদিন পর না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। অধ্যাপক মতিন বর্তমানে লাইব্রেরিয়ানের পাশাপাশি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। শহরের একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। আমার প্রিয় স্কুল শিক্ষক বিমল ভৌমিক ভারতে যাওয়ার আগে ‘দেশে-বিদেশে’ বইটি উপহার দিয়েছিলেন। সেটি এখনো সযতনে রেখেছি আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি রৌদ্র ছায়াতে। সৈয়দ মুজতবা আলীকে জীবনে একবারই দেখেছিলাম ঢাকার নিউমার্কেটের প্রগতি প্রকাশনীতে। প্রকাশনাটির মালিক ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় কবির খান। আমি সেই দিন গিয়েছিলাম প্রগতিতে কিছু বই কিনতে। এমন সময় এলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। কয়েকটি বই কিনলেন। যথারীতি দামও পরিশোধ করলেন। কবির ভাই বিনীতভাবে বললেন, স্যার আপনার নাম? তিনি মৃদু হেসে বললেন, আমি ‘দেশে-বিদেশে’র লেখক। আর না দাঁড়িয়ে দ্রুত চলে গেলেন। সে দিন আমার তাকে স্বচক্ষে দেখা। সৈয়দ মুজতবা আলীর খ্যাতি ভ্রমণ বিষয়ক ও রম্য রচনার জন্য। জনপ্রিয় উপন্যাস, ছোটগল্প, অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জানতেন ১৬টি ভাষা। কবি গুরু রবিঠাকুরের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে জার্মানির বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষে ভারতে ফিরে আসেন। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে যোগ দেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে লিখেন, ‘দেশে-বিদেশে’।
লেখক : কবি