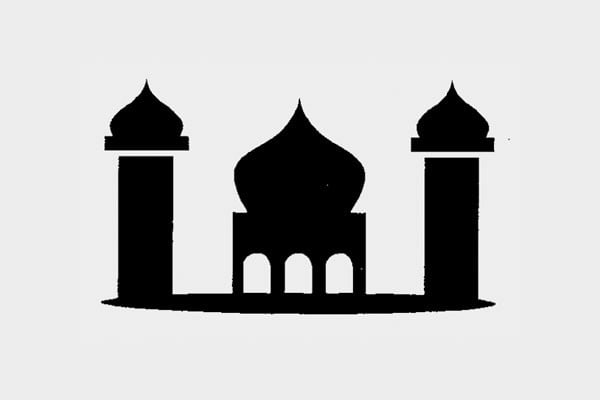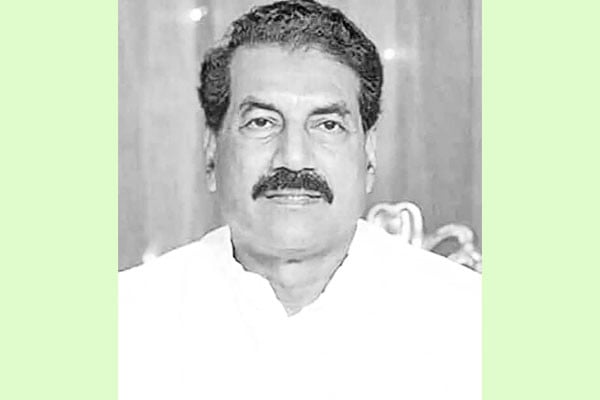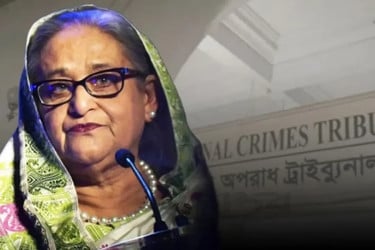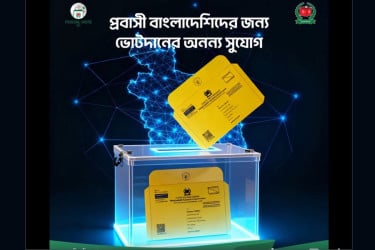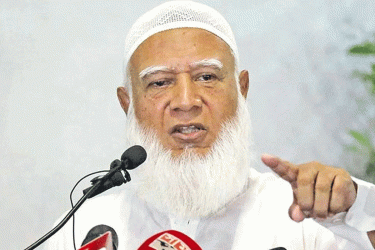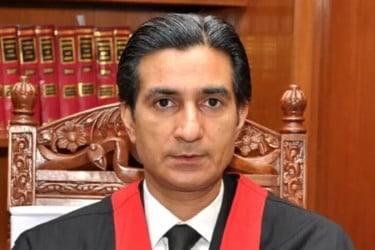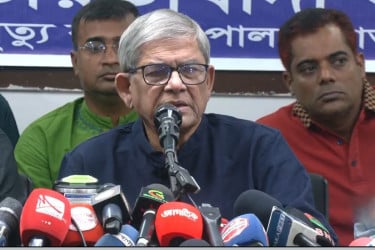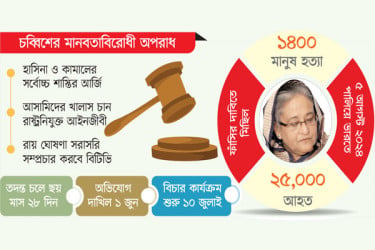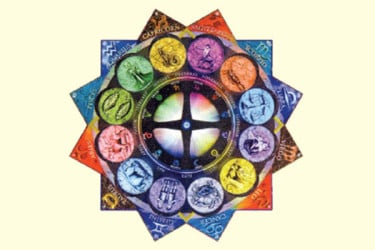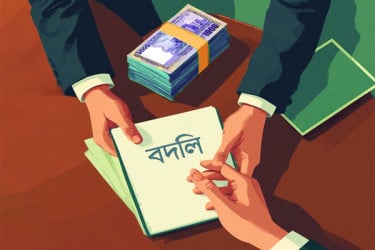বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সব নাগরিকের জন্য সর্বজনীন, গণমুখী, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার। অর্থাৎ, ধনীগরিবনির্বিশেষে সবাই একই মানের শিক্ষার সুযোগ পাবে। স্বাধীনতার পর থেকে যতগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, মুদী বোর্ড থেকে শুরু করে কুদরাত-ই-খুদা কমিশন, তারপর ২০১০ সালের শিক্ষানীতি- সবখানেই একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু চুয়ান্ন বছর পরও সেই একমুখী শিক্ষার ছায়াও বাস্তবে দেখা যায়নি। সংবিধানে আছে, বক্তৃতায় আছে, কিন্তু মাঠে নেই- এটাই নির্মম সত্য।
বর্তমানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যেন এক বিভক্ত নদী, পাঁচটি স্রোতধারায় চলছে পাঁচ ধরনের শিক্ষা : সাধারণ, মাদ্রাসা (আলিয়া ও কওমি), কারিগরি এবং ইংরেজি মাধ্যম। একেকটি ধারার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ একেক দিকে বয়ে যাচ্ছে। একদিকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে ‘সমতা’, ‘একতা’ আর ‘অধিকার’-এর বুলি, অন্যদিকে বাস্তবে ভয়াবহ বৈষম্য। এই বৈষম্য শুধু পাঠ্যক্রমে নয়, জীবনের নানা সুযোগের ক্ষেত্রেও। একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ৫০০ শিক্ষার্থীকে সামলাতে হয় দুই-তিনজন শিক্ষককে, সেখানে রাজধানীর নামিদামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয় করা হয় শতগুণ বেশি অর্থ। এই দুই শিশুই একদিন দেশের পরিণত নাগরিক হবে, কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে ব্যবধান থেকে যাচ্ছে আকাশপাতাল।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ শিক্ষার্থী পড়ে। কিন্তু তাদের শেখার মান কী অবস্থায়? জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলছে, তৃতীয় শ্রেণির মাত্র ৫১ শতাংশ শিশু বাংলা পাঠে প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করে, আর গণিতে এই হার মাত্র ৩৯ শতাংশ। এত কোটি টাকা ব্যয় করেও শিক্ষা মানের এই দীন হাল কেবল ব্যর্থতা নয়- রীতিমতো অপরাধ। কারণ শিক্ষার মান ঠিক না হলে পরবর্তী ধাপের সব অর্জনই অর্থহীন। অন্যদিকে রাজধানী, চট্টগ্রাম বা সিলেটের নামি বেসরকারি ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে ভর্তি হলে মাসে ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ফি দিতে হয়। কোথাও ভর্তি ফিই লাখ টাকার ওপরে। কোথাও আবার সুপারিশপত্র, গাড়ির নম্বর, এমনকি অভিভাবকের পদমর্যাদাও বিবেচনা করা হয়! শিক্ষা যেন পণ্য, আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান!
এই বাস্তবতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সন্তান আর নেই বললেই চলে। দুর্ভাগ্য যে সরকারি স্কুল এখন গরিব মানুষের স্কুল; যেখানে শিক্ষা নয়, বরং দারিদ্র্যের চক্রই প্রজন্মান্তরে ঘুরেফিরে টিকে থাকে। একদিকে বস্তিবাসী শিশু দুপুরে খিচুড়ি খেয়ে লেখাপড়া শিখছে, অন্যদিকে নামি ইংরেজি মাধ্যমের শিশুরা এয়ারকন্ডিশন ক্লাসরুমে ট্যাব হাতে আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রমে পড়ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুই শিশুর ভবিষ্যৎ কি একই দেশের ভবিষ্যৎ? এক দেশের মধ্যেই যেন দুটি জাতি তৈরি হচ্ছে- একটি সুবিধাভোগী, আরেকটি বঞ্চিত।
দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায়ও বৈষম্যের চিত্র কম নয়। সরকারি স্কুলগুলোতেও এখন পার্থক্য চোখে পড়ে। ঢাকার একটি সরকারি বালক বা বালিকা বিদ্যালয় ও কোনো জেলা শহরের সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য এতটাই যে তাদের ফলাফল, শিক্ষকসংখ্যা, এমনকি ভবনের অবস্থাও যেন ভিন্ন দেশের। আর ক্যাডেট কলেজের কথা বললে সেখানে ছাত্ররা মেধার পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত। স্বভাবতই রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী। তারা একদম অন্য এক বাস্তবতায় বড় হয়- শৃঙ্খলা, পরিবেশ, ক্রীড়া, নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব গঠনের অসাধারণ সুযোগ পায় তারা। তাই তারা উচ্চশিক্ষা ও চাকরির বাজারে সব সময় এগিয়ে যায়। অন্যদিকে গ্রামের একটি সাধারণ স্কুলের ছাত্রকে সেই একই পরীক্ষায় বসে প্রতিযোগিতা করতে হয়। ফলাফল অনুমান করা কঠিন নয়।
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, ‘সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।’ কিন্তু স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসেও আমরা এমন এক সমাজ তৈরি করেছি, যেখানে শিক্ষাই সবচেয়ে বড় বৈষম্যের ক্ষেত্র।
বাংলাদেশের উন্নয়ন সূচকে আমরা যতটা এগিয়েছি, শিক্ষার গুণমানে ততটাই পিছিয়ে আছি। সরকারি হিসাব বলছে, সাক্ষরতার হার এখন প্রায় ৭৬ শতাংশ। কিন্তু এ সাক্ষরতা কতটা কার্যকর? যারা স্কুলে যায়, তাদের বড় অংশই শেখে পরীক্ষার জন্য মুখস্থবিদ্যা, বাস্তবজীবনের দক্ষতা নয়। ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এখনো প্রায় ১৭ শতাংশ শিশু স্কুলের বাইরে- যেখানে শ্রীলঙ্কায় এই হার মাত্র ৪ শতাংশ। অর্থাৎ আমরা শুধু সংখ্যায় নয়, মান ও সুযোগে ভয়াবহভাবে পিছিয়ে।
লেখক : আইনজীবী