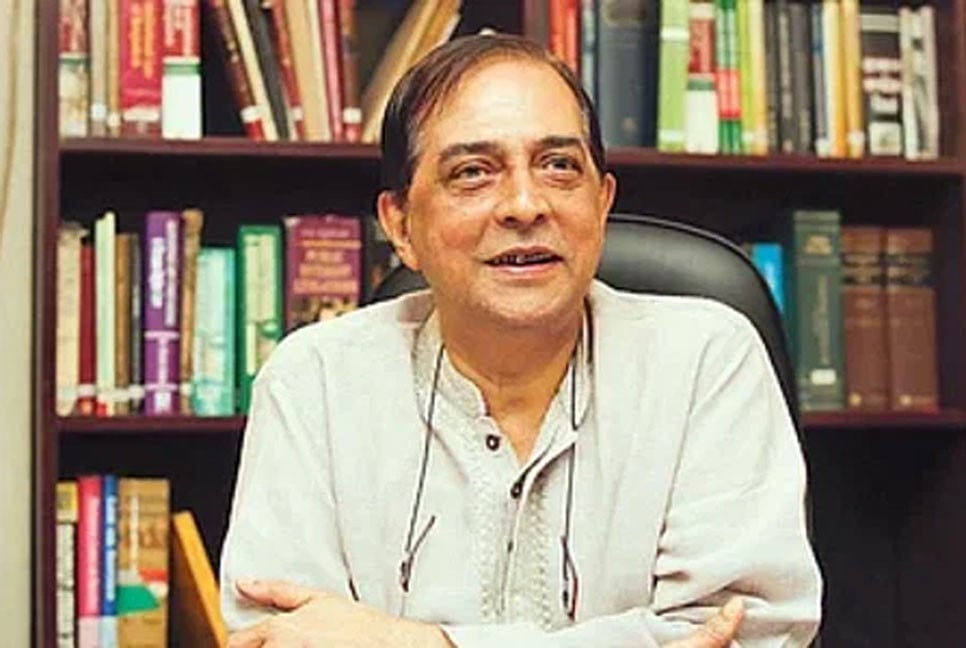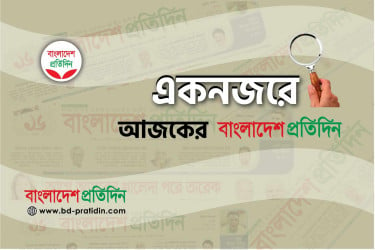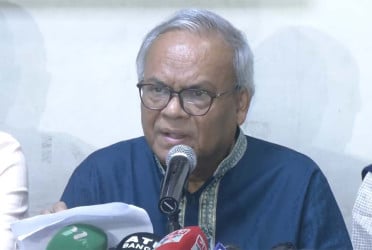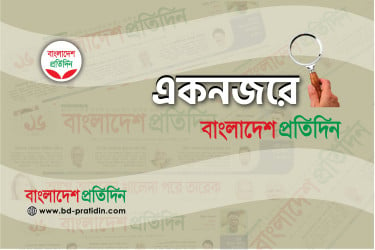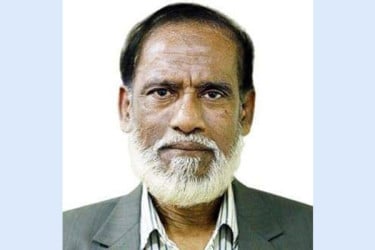চলছে বাজেটের মাস জুন। সমান্তরালে আছে বাঙালির মধু মাস। কিন্তু সেই মধুর নহরে সবকিছুই এখন নাকি বিষে বিষময়। আম, কাঁঠাল বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলের জন্য এখন অন্যতম একটি অর্থকরী ফসল। এটিকে বিষময়তার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বাজেটে কিছু করার আছে কিনা জানি না। তবে প্রাজ্ঞজনের মতে, বাজেট একটি রাষ্ট্রের জন্য চলার পথের দর্পণের সমতুল্য। তাই অর্থকরী এই খাতকে দুর্বৃত্তায়নের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য বাজেটে কী ধরনের দিকনির্দেশনা থাকতে পারে তা বলার জন্য অনেক পণ্ডিত আছেন। আমার দৌড়ের সীমানায় তা পড়ে না। আজকের আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রতিরক্ষা বাজেটের সঙ্গ-প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা বলা। কিন্তু তার আগে দু'য়েকটি কথা না বললেই নয়। বাজেট সংসদে পেশ করা হয়েছে। পেশের আগে ও পরে বাজেট নিয়ে সব ধরনের মিডিয়ায় এবং সুধী সমাজে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির অন্যতম প্রধান একটি অনুষঙ্গ হলো বাৎসরিক বাজেট। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজনীতিবিদরাই নেবেন। কিন্তু সেই রাজনৈতিক অঙ্গনে বাজেট প্রসঙ্গে তেমন একটা বিশ্লেষণ বা যুক্তিতর্ক নেই বললেই চলে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যনীতি ও তার বাজেট নিয়ে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে কি তুমুল যুদ্ধটাই না হলো ওবামার প্রথম মেয়াদে। শেষমেশ অনেক ঘর্মাক্ত দিন ও নির্ঘুম রাত পেরিয়ে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে তবেই ওমাবা তার প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যনীতির অনুমোদন পান। কোথায় কোন খাতে কত বরাদ্দ হবে, কোন খাত অগ্রাধিকার পাবে এবং বাজেট বাস্তবায়নের পথনির্দেশনা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন তুমুল বাকযুদ্ধে লিপ্ত থাকার কথা। কিন্তু কই! সরকারি দলের কথা না হয় বাদই দিলাম। তাদের কাজ তো শুধুই প্রশংসা করা! সংসদে বিরোধী দলের তেমন কোনো গলা মানুষ শুনতে পারছে না। সংসদ সদস্যরা বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে অন্যান্য প্রসঙ্গে কথা বলে সময় পার করছেন। বাজেটের খাতওয়ারী বরাদ্দ ও তার বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা নিয়ে খুব কমই বলেন। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বিএনপি এখন ঘরে-বাইরে কোথাও নেই। তারা দুটি পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় ছিল। বিএনপি এখন সবহারাদের মতো নীরব-নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে বাজেটের বিচার-বিশ্লেষণ তাদের কাছে কোনো বিষয়ই না। মাঝে-মধ্যে তারা যা বলেন তাতে মনে হয় বিএনপি ক্ষমতায় গেলেই বাংলাদেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই সব কিছু বাদ দিয়ে এখন ঘোরাফেরা করছেন শুধুই কূটনৈতিক পাড়ায়, ব্যাকুল হয়ে খুঁজছেন ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি।
১৯৭৫ সাল থেকে নব্বইয়ের শুরু পর্যন্ত দুই সামরিক শাসকের আমলে প্রতিরক্ষা বা সামরিক বিষয়াদি নিয়ে কেউ কোনো কথা বলতেন না। এখন এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। দেশের প্রতিরক্ষা এবং সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে এটিকে সবাই ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। এবারের অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর প্রতিরক্ষা বাজেট নিয়ে কিছু আলোচনা এবং দুয়েকটি লেখাও দেখেছি। আমি মনে করি এতটুকু যথেষ্ট নয়, আরও বেশি আলোচনা হওয়া উচিত। প্রতিরক্ষা বাজেট নিয়ে আলোচনায় দুটি বিষয় প্রধান্য পায়। প্রথমটি হলো প্রতিরক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ নিয়ে, আর দ্বিতীয়টি হলো বাজেট ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে। এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ১৬ হাজার ৪৬২ কোটি টাকা (২.২ বিলিয়ন ডলার)। গত বছর থেকে ৬.৬ শতাংশ বেশি। এই বরাদ্দ কি যথেষ্ট, নাকি কম, নাকি যথাযথ? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। প্রথম কথা হলো ৬.৬ শতাংশ বৃদ্ধি একেবারে গতানুগতিক। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সব সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নতুন বাজেটের প্রাক্কলন ও চাহিদা করার সময় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হলে সেটা স্বাভাবিক হিসেবে ধরা হয় এবং তার জন্য অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বৃদ্ধি কেবল ১০ শতাংশের ঊর্ধ্বে গেলেই সেই বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
কেউ কেউ বলেছেন, ১৯৮৮ পরবর্তী ২৩ বছরে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট প্রায় ১২ গুণ বেড়েছে। কথাটি আংশিক সত্য। ১৯৮৭ সালের ১৮ জুন ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরে মোট ১০ হাজার ৩০১.২৭ কোটি টাকার বাজেট উত্থাপন করেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাঈদুজ্জামান। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে মোট বাজেট ছিল ১১ হাজার ০৬০.২৯ কোটি টাকা, উত্থাপন করেছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মুনিম, ১৬ জুন ১৯৮৮। এ বছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট বাজেট প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকা। সে হিসেবে ১৯৮৮ সাল থেকে বর্তমান বছরের বাজেট প্রায় ২২ গুণ বেশি। সুতরাং ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিরক্ষা বাজেট ১২ গুণ বেশি হলে তাকে প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক হার বিচারে বেশি বলা যায় না। কিন্তু কথা সেখানে নয়। কথা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের সেনাবাহিনীর আকার ও কাঠামো কেমন হওয়া উচিত এবং ওই সময়ে তার কি কি সক্ষমতা থাকার দরকার, সেটা ঠিক থাকলে আমরা বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে যথার্থ আলোচনা করতে পারতাম। প্রতিরক্ষা নীতিমালা থাকলে এ বিষয়ে কিছু ধারণা পাওয়া যেত। কিন্তু প্রতিরক্ষা নীতিমালাই শেষ কথা নয়। রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থের নিরাপত্তা কীভাবে রক্ষিত হবে এবং সেই জায়গায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা কতখানি, সেটি যত সময়ে নিরূপণ না হচ্ছে, তত সময়ে এ ব্যাপারে কোনোরকম উপসংহারে পৌঁছানো যাবে না।
দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ধর্মান্ধতা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এখন বড় হুমকি। রাষ্ট্রের টেরিটোরি বা সীমান্ত রক্ষা করা সশস্ত্র বাহিনীর একটি অন্যতম কাজ হলেও এখন আর এই কাজকে মুখ্য কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এটা এখন গতানুগতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সেই ধ্রুপদি সংজ্ঞাও আজ সময়োপযোগিতা হারিয়েছে। এখন বিশ্বয়নের যুগ। ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিয়োগের এখন আর সীমানা নেই। এক দেশ আরেক দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এক দেশের হাজার-লাখো মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর্মে অন্য দেশে নিয়োজিত আছে। সুতরাং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পাখা এখন নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী অবাধ বিচরণের ফলে এক দেশের স্বার্থ অন্য দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। এক দেশের স্বার্থ যখন অন্য দেশের ভেতরে ঢুকে যায় তখন কোনো না কোনো সময়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বাধা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সেই দ্বন্দ্ব কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবে তা বহু ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভরশীল। দ্বন্দ্ব মেটাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সেটি যে সামরিক দ্বন্দ্বে রূপ নেবে না তা কিন্তু বলা যৌক্তিক হবে না। তবে নিজ দেশের সশস্ত্র বাহিনীর আকার ও সক্ষমতা যদি সময়োপযোগী হয় তাহলে অন্য দেশ যত বড় বা শক্তিশালীই হোক না কেন তারা সামরিক দ্বন্দ্বের পথ এড়িয়ে কূটনৈতিক পথে দুপক্ষের জন্য উইন উইন বা সমান সুযোগ প্রাপ্তির সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবে। একেই বলে নিজ দেশের ডেটারেন্ট ক্ষমতা বা নিবারক শক্তি। এই পয়েন্টে পৌঁছানোর পর প্রতিরক্ষা বাজেট বরাদ্দের যথার্থতা খুঁজলে তার যৌক্তিকতা পাওয়া সহজ হয়।
বাংলাদেশ এখন অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের মাথাপিছু আয় এখন প্রায় ১২০০ ডলার, তা ২০০০ ডলারে পৌঁছলে ১৬ কোটি মানুষের জন্য ভোগ্যপণ্যের যে বিশাল বাজারের সৃষ্টি হবে তা লুফে নেওয়ার জন্য বিশ্বের সব নামিদামি করপোরেট হাউস ঝাঁপিয়ে পড়বে। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা মীমাংসার পর প্রায় এক লাখ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রাঞ্চলের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক এখন বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে একই রকম মীমাংসা হলে এই সম্ভাবনার আরও বিশাল বিস্তার ঘটবে। সুতরাং বাংলাদেশ নেভির সক্ষমতা কতখানি হওয়া দরকার তা এখন সহজেই অনুমেয়। একটা প্রতিরক্ষা নীতিমালা থাকলে এবং সেই অনুসারে সশস্ত্র বাহিনীকে সময়োপযোগী করার পরিকল্পনা করলে মানুষের আস্থার জায়গা আরও জোরালো হয়। তবে ফোর্সেস গোল ২০৩০ নামের একটি রূপকল্প এখন প্রতিরক্ষা নীতিমালার স্থলে আছে। এই রূপকল্প অনুসারে সশস্ত্র বাহিনীর আকার, কাঠামো, অস্ত্র ও সমরসজ্জাকে সময়োপযোগী রাখার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে কাজ করছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীতে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আধুনিক ট্যাংক, গোলন্দাজ বাহিনীর কামান, ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল, হেলিকপ্টারসহ অন্যান্য উন্নতমানের সরঞ্জাম। কাঠামোগতভাবে পদ্মা সেতুর নিরাপত্তার জন্য গঠিত হয়েছে নতুন কম্পোজিট ব্রিগেড। সিলেটে আরও একটি নতুন পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে নতুন আধুনিক ফ্রিগেট, মিসাইল, হেলিকপ্টার। নৌবাহিনীকে একটি পরিপূর্ণ ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে, যা আমাদের সমুদ্র সম্পদের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। বিমান বাহিনীতে যোগ হয়েছে নতুন যুদ্ধবিমান ও আধুনিক রাডার। সামরিক শক্তি বিন্যাসে আঞ্চলিক ও বিশ্বের অন্য দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এখন সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন।
আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার, যাদের সঙ্গে আমাদের ২৪০ কিলোমিটারের মতো স্থলসীমান্ত এবং বিস্তীর্ণ সমুদ্র সীমান্ত রয়েছে, তাদের সেনাবাহিনীর আকার প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখের ঊর্ধ্বৈ। সংখ্যানুসারে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম সেনাবাহিনী। তাদের লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি, আমাদের এক-তৃতীয়াংশ, তবে আয়তনে আমাদের থেকে প্রায় ৬ গুণ বড় দেশ। এ বছরে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট মোট ব্যয়ের প্রায় ১৩ ভাগ। এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড প্রতিরক্ষা বাজেটে তাদের মোট ব্যয়ের ১২-১৪ ভাগ বরাদ্দ রাখছে। পাকিস্তান এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ১৮ ভাগ। চীন ও ভারতের কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার ছোট ও বাজেট কমানোর কথা বললেও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে তাদের সামরিক শক্তি আরও ১০ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। গত শতকের নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বের তাবৎ বিশ্লেষকরা ধারণা করেছিলেন ভবিষ্যতে হয়তো অস্ত্র ব্যবসা হ্রাস পাবে, প্রতিরক্ষা ব্যয় কমে যাবে এবং সেই টাকা মানবতার অভিশাপ দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যয় হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের দুই দশক পর সেই কথা এখন আর কেউ বলে না। সব দেশ সমানতালে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাবেক কর্মকর্তা রবার্ট কাগান কর্তৃক লিখিত- The Return of History and the end of Dreams@-বইটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মাত্র ১১৬ পৃষ্ঠার একটি বই। বাংলাদেশি মুদ্রায় মূল্য দুই হাজার টাকা। বইটি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর জন ম্যাককেইন এবং রিচার্ড হলব্রুক। বইটিতে লেখক বর্ণনা করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেও বিশ্ববাসীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, অস্ত্র ব্যবসা ও প্রতিরক্ষা ব্যয় না কমে বরং কেন তা আরও বৃদ্ধি পেল বা পাচ্ছে। যদিও রবার্ট কাগানের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ও চায়নার সমরসজ্জা বৃদ্ধিকে একতরফাভাবে দায়ী করতে চেয়েছেন, যার সঙ্গে বিশ্বের অনেক বিশ্লেষক হয়তো একমত হবেন না।
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড করতে চেয়েছিলেন। তার স্বপ্নের পরিস্ফুটন আমরা দেখতে পেলাম না। তবে তিনি মর্যাদাশীল ও একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। যার ফলে মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করলেন, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ট্যাংক, যুদ্ধবিমান আনলেন। মুক্তিযুদ্ধের পর সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করে ব্রিগেড পর্যায়ে উন্নত করলেন। সুইজারল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম নিরপেক্ষ দেশ। তাদের সশস্ত্র বাহিনী কনস্ক্রিপ্ট (বাধ্যতামূলক) নীতিমালা অনুসারে সংগঠিত। আপদকালীন শারীরিকভাবে সক্ষম পুরুষ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজন অনুসারে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। যার জন্য তাদের পর্যায়ক্রমে নিয়মিত বাৎসরিক প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হয়। সুইজারল্যান্ডের প্রতিরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী আপদকালীন প্রয়োজনীয় ফোর্সের যে আকার হতে পারে তার মাত্র ৫ ভাগ স্ট্যান্ডিং (নিয়মিত পেশাদার) ফোর্স হিসেবে থাকে। কিন্তু তাদের সশস্ত্র বাহিনীর কাঠামো বিন্যাস ও অস্ত্রশস্ত্র ইউরোপের অন্য রাষ্ট্র থেকে সামান্য কম নয়। সুতরাং আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী বিরাজমান পরিস্থিতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আমলে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষকেই ঠিক করতে হবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার, সক্ষমতা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাজেট কেমন হওয়া উচিত। তবে যৌক্তিক কথা হলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের চিন্তাচেতনা নিয়ে বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানো যাবে না।
এখন বাজেট ব্যয়ের স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে কিছু কথা। আমার ধারণা মতে, প্রতিরক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দের ৮০-৯০ ভাগ চলে যায় বেতন-ভাতা, পেনশন, পোশাক-পরিচ্ছদ, রেশন, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিবিধ খাতে। এই খাতের ব্যয়গুলো সংসদের স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপিত ও আলোচনা হলে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। এসব সাধারণ ক্রয়গুলো প্রতিরক্ষা ক্রয় অধিদফতরের (ডিজিডিপি) খোলা টেন্ডারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অস্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাহিনীর একাধিক কমিটি রয়েছে। এই কমিটিগুলো ক্রয়ের প্রতিস্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ অনুমোদনের পরেই সেটি চূড়ান্ত করা হয়। এক্ষেত্রে খোলা টেন্ডারের সীমাবদ্ধতা আছে। সব দেশ সব দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে না। সব দেশের অস্ত্র সরঞ্জমাদির স্পেসিফিকেশন এক নয়। আমাদের প্রয়োজনীয় স্পেসিফিকেশন সব দেশের সরঞ্জামাদিতে নাও থাকতে পারে। এখানে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার গোপনীয়তা রক্ষারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবার এখন বাংলাদেশ কিছু অস্ত্র সরঞ্জামাদি কিনছে জাতিসংঘের শান্তি মিশনের জন্য। এই কেনার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করতে হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কর্মপরিধি নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে একজন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর অধীনে আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম হয়েছিল। এদেশের সাধারণ মানুষের ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের রক্তের মেলবন্ধনে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশের মানুষকে এক ও অভিন্ন অবস্থান নিতে হবে।
লেখক : কলামিস্ট ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক।