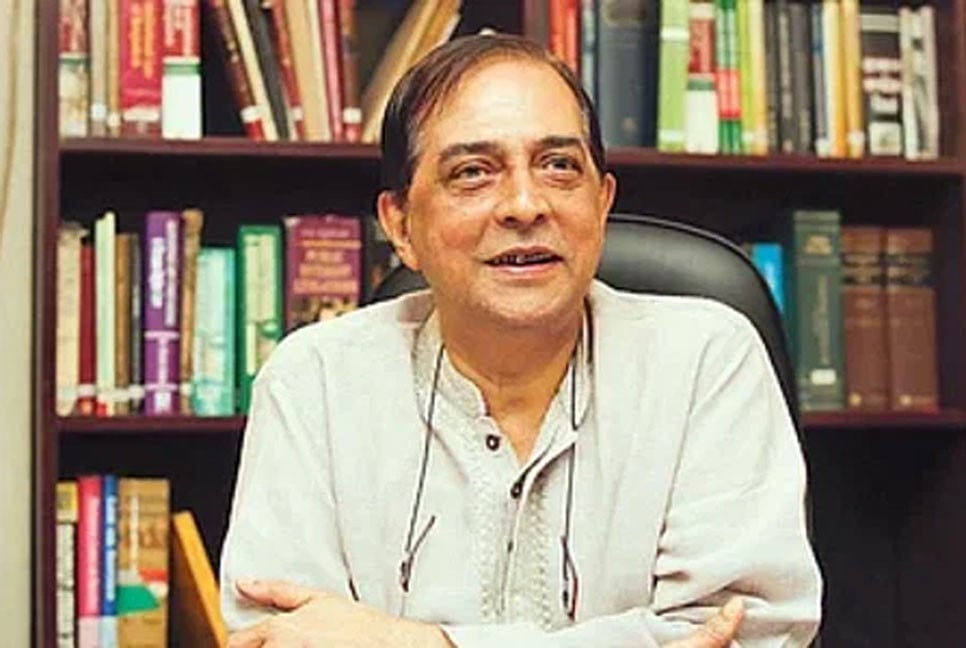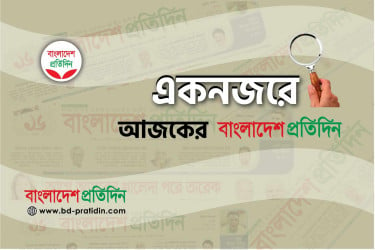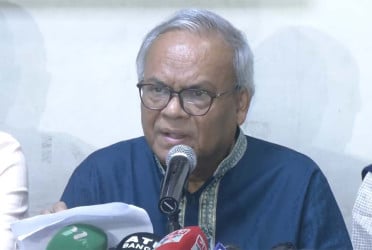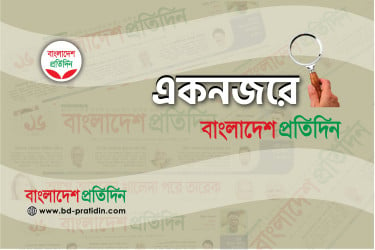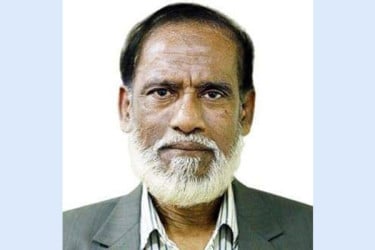ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার আন্দোলনে দুটি ধারা ছিল। একটি ধারা জাতীয়তাবাদী, অপরটি সমাজতান্ত্রিক। ব্রিটিশ বিতাড়নের অভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভেতর নৈকট্য যেমন ছিল তেমনি ছিল দূরত্বও; বলা যাবে বৈপরীত্যও। জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা পেলেই সন্তুষ্ট হবেন এই মনোভাব নিয়ে লড়েছেন; আর সমাজতন্ত্রীরা চেয়েছেন আরও অগ্রসর হয়ে সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে কেবল স্বাধীনতা নয়, জনগণের সব অংশের জন্য মুক্তি অর্জন করবেন। চূড়ান্ত লক্ষ্যের পার্থক্যের দরুন জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের বিরোধটাও ছিল অনিবার্য।
সমাজতন্ত্রীরা পরে এসেছেন এবং তাদের মূল ধারাটি কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হয়েছে বললে অন্যায় হবে না। দেখা গেছে যে, জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যারা অগ্রসর চিন্তার মানুষ এবং সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে আগ্রহী, যেমন জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু, তারাও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেননি। আর কংগ্রেসের ভেতরে থেকে নিজেদের যারা সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন তারাও আসলে কমিউনিস্টদের শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অনড় জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যথার্থরূপে সমাজতন্ত্রী হওয়াটা সহজ নয়।
জাতীয়তাবাদ শত্রু চায় এবং শত্রুকে সামনাসামনি পেলে তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। এই শত্রু সরাসরি বিদেশি বা অন্তত বিদেশাগত হবে এমনটাই স্বাভাবিক। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদীরা দেখতে পান যে, তাদের আত্দসম্মান বিপন্ন হচ্ছে, এমনকি অস্তিত্বই মনে হচ্ছে ঝুঁকির মুখে। তখন তারা আত্দরক্ষা ও আত্দপ্রতিষ্ঠার পথকে পরিষ্কার করার জন্য সংগ্রামে নামেন। এই জাতীয়তাবাদীরা হচ্ছেন সমাজের সচেতন অংশ। এরা শিক্ষিত ও স্পর্শকাতর। পরাধীনতা তাদের ভেতর ক্ষোভ ও যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। তারা নিজেদের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চান। এই যে তাদের আত্দজ্ঞান এখানে শ্রেণীগত অবস্থানটা চলে আসে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকেই জাতীয়তাবাদীরা বেরিয়ে আসেন; দেখা যায় পরোক্ষে নিজেদেরই তারা দেশ মনে করছেন এবং নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকেই দেশবাসীর অর্জন হিসেবে দেখছেন। এখানেই জাতীয়তাবাদের সীমাটা রচিত হয়ে যায়। এই সীমার শাসনের দরুন দেখা যায়, কিছুদূর একসঙ্গে গেলেও জাতীয়তাবাদীদের চোখে সহযোদ্ধা সমাজতন্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত আর মিত্র থাকেন না, শত্রুতে পরিণত হয়ে যান। কেননা জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সমাজতন্ত্রীদের লক্ষ্য যদি অর্জিত হয় তা হলে বিদ্যমান যে সমাজব্যবস্থার ওপর ভর করে তারা দাঁড়িয়ে আছেন সেটা ভেঙে পড়বে। তেমনটা ঘটলে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির আশা নিমর্ূল হয়ে যাবে, যেটুকু অর্জিত হয়েছে তাও অন্তর্হিত হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রম-শক্তি শোষণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। প্রকাশ্যে বলেন না, হয়তো-বা নিজেদের কাছে স্বীকার করতেও সংকোচবোধ করেন যে তারা চান জনগণ তাদের সঙ্গে থাকুক, থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটাকে শক্তিশালী করুক যাতে করে তাদের কায়েমি স্বার্থের সুবিধা হয় এবং পরিণামে দেশ শাসনের ক্ষমতা তাদের হাতে চলে আসে। সমাজতন্ত্রীরা যে জনগণকে ব্যবস্থাটা ভেঙে ফেলার জন্য উত্তেজিত করেন জাতীয়তাবাদীদের কাছে এ ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর এবং বিপজ্জনক। জাতীয়তাবাদীরা মোটামুটি সবাই হয় পুঁজিবাদে দীক্ষিত নয়তো পুঁজিবাদের কোনো বিকল্প আপাতত দেখা যাচ্ছে না এমন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত।
স্বার্থ সংরক্ষণের প্রণোদনায় এরা রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন। ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, আত্দপরিচয় তুলে ধরার ব্যাপারে ধর্ম একটি সুবিধাজনক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। কেননা এটা যদিও ঠিক যে জবরদখলকারী বিদেশিদের কেবল ধর্ম নয়, ভাষা ও গাত্রবর্ণ দিয়েও শনাক্ত করা সম্ভব, কিন্তু ধর্মের সাহায্যে আত্দপরিচয় ব্যক্ত করার একাধিক সুবিধা রয়েছে।
প্রথমত, ধর্মীয় পরিচয়টা হচ্ছে সর্বাধিক দুর্ভেদ্য। দ্বিতীয়ত, এই পরিচয় একাধারে অহমিকা ও আশ্রয় সরবরাহ করে। আমরা ধার্মিক, তোমরা বিধর্মী, অতএব তোমরা আমাদের তুলনায় নিকৃষ্ট, এই বোধ অহঙ্কার ও উচ্চমন্যতার জন্ম দেয়। সেই সঙ্গে এটাও তো সত্য যে, ধর্ম হচ্ছে উৎপীড়িতের জন্য নিজস্ব আবাস, সেখানে উৎপীড়নকারীর প্রবেশাধিকার নেই এবং ধর্মের চর্চার ভেতর প্রতিশ্রুতি আছে ইহকালের দুগর্্রহের বিনিময়ে পরকালে সুখপ্রাপ্তির। ধর্ম ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মেহনতি মানুষের শ্রম-শক্তি শোষণে আপত্তি করে না, পরোক্ষে ওই দুটি ব্যাপারকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা জোগায়। এটা মোটেই তাৎপর্যহীন নয়, আপতিকও নয় যে, ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাবাদীরা অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষ- ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য।
সাংস্কৃতিকভাবে ধর্ম মানুষকে নিয়ে যেতে চায় সামন্তবাদের কাছে। তার একটা কারণ সামন্তবাদ পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী। অপর কারণ সামন্তবাদ বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার সমর্থক। সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উভয় ঐতিহ্যের ভেতরই ধর্মের উপস্থিতি থাকে। [ চলবে ]