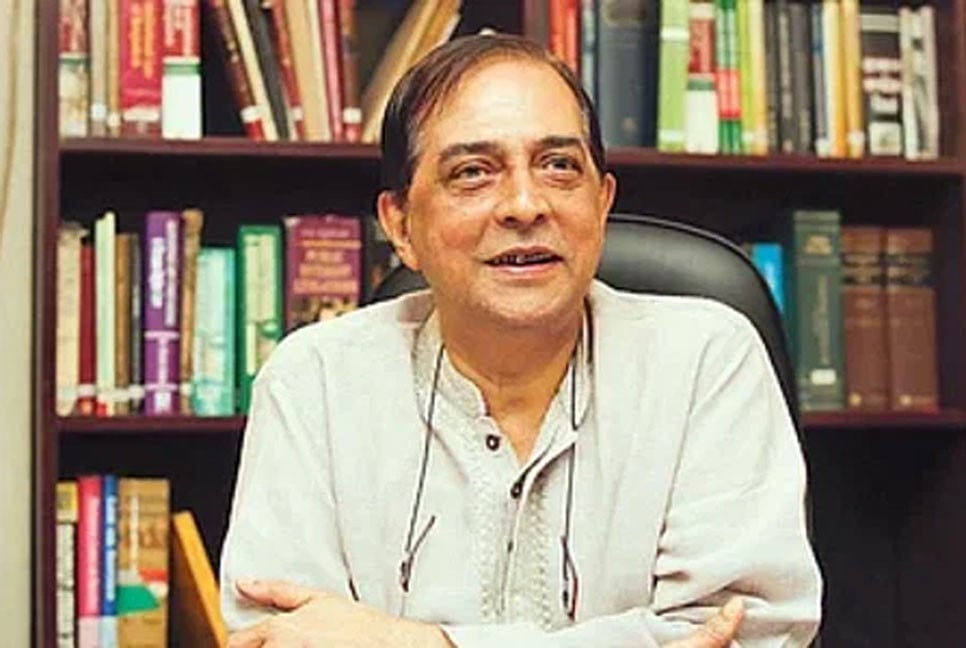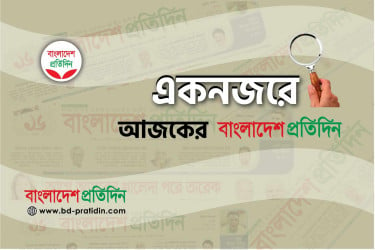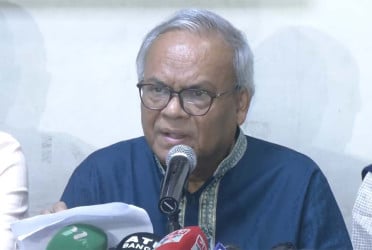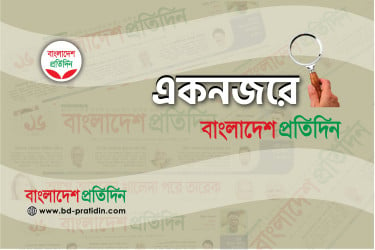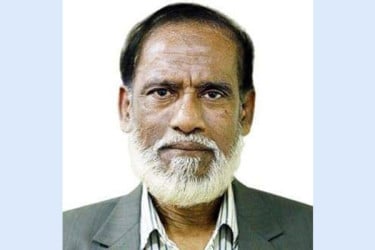এই যে ফোলানো ও দমানো এরা উভয়েই জাতীয়তাবাদকে অতীতমুখী হতে উৎসাহ জোগাল। আমাদের অতীত খুব সমৃদ্ধ, তাই আমরা পেছনের দিকেই তাকিয়ে থাকব; আমাদের অতীত খুব সামান্য, তাই আমরা অতীত নিয়ে লজ্জিত হব- এই দুই বোধের কোনোটাই স্বাস্থ্যকর নয়। অতীতের গর্ব এবং অতীতকে নিয়ে লজ্জা দুটোই জাতীয়তাবাদীদের প্ররোচিত করল বর্তমানের দুর্দশাকে অবজ্ঞা করতে। সেই সঙ্গে অতীতের গৌরব কার কত বেশি তা নিয়ে বড়াই করা এবং অতীতের ব্যর্থতার জন্য একে অপরকে দোষী করার প্রবণতা যে দেখা দিল না তাও নয়। মুচকি হাসল ইংরেজ, সবদিক দিয়েই তাদের অভিলাষ সফল হচ্ছে দেখে। শাসকরা চেয়েছে হিন্দু-মুসলমান মারামারি করুক এবং ফলশ্রুতিতে শাসকদের শাসন অক্ষুণ্ন থাকুক। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বে যে রক্ষণশীলরা ছিলেন তারা ব্রিটিশের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে আবার জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতার অভিমুখে পরিচালিত করে ব্রিটিশকে টিকে থাকতে এবং জনগণের মুক্তিকে বিঘি্নত করতে সহায়তা করেছেন। জনগণের মুক্তির প্রশ্নটি তাদের বিবেচ্য ছিল না, যদিও জনগণের হয়ে কথা বলার ব্যাপারে তারা কখনোই ক্লান্ত হননি। তারা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই লড়ছিলেন, কংগ্রেস নেতারা চাইছিলেন শাসন ক্ষমতা তাদের কাছে হস্তান্তরিত হোক, লীগ নেতাদের দাবি ছিল ক্ষমতার ভাগ তাদের অবশ্যই দিতে হবে। এই বিরোধে জনতা হয়েছে ভুক্তভোগী। দেশভাগ হয়ে গেছে, অসংখ্য মানুষ উৎপাটিত হয়েছে ও প্রাণ হারিয়েছে, যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে বহু নারীকে, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হয়নি। লাভ যেটুকু হওয়ার তা হয়েছে সুবিধাভোগীদের, তাদের সুবিধার বৃদ্ধি ঘটেছে। দুদিকেই জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন। তাদের ভয়ঙ্কর রকমের দরকষাকষির ভেতরে যা স্থির থেকেছে তা হলো তাদের ব্যবহৃত জাতীয়তাবাদের সীমা, যে জাতীয়তাবাদ জনগণের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করেনি, ব্যস্ত ছিল বিত্তবানদের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ নিয়ে। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের সীমা কীভাবে চিহ্নিত হচ্ছিল সে কাহিনীর দিকে তাকানোর বিভিন্ন উপায়ের একটি হচ্ছে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজ ও ভূমিকার ওপর দৃকপাত করা। শুরু করতে হয় রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩৩) দিয়েই। রামমোহনকে জাতীয়তাবাদী বলা যাবে না; কেননা জাতীয়তাবাদী ধারণার উদ্ভব তখনো ঘটেনি। তবে ঘটবে যে তার লক্ষণ কিন্তু দেখা যাচ্ছিল এবং সে লক্ষণ রামমোহনের নিজের কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। জাতীয়তাবাদ কোন পথ ধরে এগুবে তার একটি সাধারণ দিক-নির্দেশনাও এই অসাধারণ মানুষটির কর্মধারা ও বক্তব্যের ভেতর সংরক্ষিত রয়েছে।
রামমোহন দেশপ্রেমিক ছিলেন, যে জন্য সমাজ সংস্কারের জন্য তার অদম্য আগ্রহ ছিল। হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতাকে তার কাছে পুতুল খেলা বলে মনে হয়েছে, যে জন্য তিনি নিরাকারবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। নারী নির্যাতন দেখে তিনি পীড়িত হয়েছেন এবং নারী অধিকার রক্ষার পদক্ষেপ হিসেবে সতীদাহ নিবারণে ব্রতী হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনে তার উদযোগ ছিল অগ্রপথিকের। বাংলা গদ্যের প্রারম্ভিক নির্মাতা তিনি। সংবাদপত্রের প্রকাশ ও মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে রামমোহন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু সীমা ছিল, যে সীমা পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। প্রথমত তিনি ধর্মের বাইরে যেতে পারেননি এবং নিজের ব্রাহ্মণ্যত্বের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এর চেয়েও বড় ব্যাপার হলো সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তার আনুগত্য। অধিপতি ইংরেজদের আগমনকে তিনি ঈশ্বরের কৃপা বলে গণ্য করেছেন এবং তার নিজের শ্রেণীর মানুষদের সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের স্বার্থে ঔপনিবেশিক ইংরেজদের ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। বিলেতে গিয়ে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে রায়তের অধিকারের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু নিষ্পেষিত কৃষকের জন্য তার হৃদয় যে মমতায় ভরপুর ছিল এমনটা মনে হয় না; হলে নীলচাষে কৃষকের উপকার হচ্ছে এমন মত ব্যক্ত করতে পারতেন না। আর যে গদ্যরীতি তিনি প্রবর্তন করলেন তা জনমুখী হয়নি, সংস্কৃতভাষামুখী হয়েছে। জাতীয়তাবাদের আপসমুখিতা এবং কৃষকের প্রতি অবহেলাকে তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন এবং তুলে ধরেছেন। তবে জাতীয়তাবাদের শক্তি ও সীমা দুটোই অধিকতর স্বচ্ছ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) রচনাবলীতে। তার জন্ম রামমোহনের জন্মের ছেষট্টি বছর পরে। সাহিত্য প্রসঙ্গে যেমন, জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গেও তেমনি আমাদের বারবারই তার শরণাপন্ন হতে হয়। জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই তাকে ঋষি বলেন, সে-উপাধি অযথার্থ নয়। জাতীয়তাবাদের তিনি দার্শনিক উদ্গাতা এবং জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী ধারার পথপ্রদর্শক বটেন। এক্ষেত্রে তার 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও 'বন্দে মাতরম' গানটির প্রভাব ছিল অতুলনীয়। বিশেষ করে ওই গানটির ব্যাপারে বলা যেতে পারে, কেবল ভারতবর্ষে নয় তার বাইরেও অন্য কোনো গানের কথা আমরা জানি না সমসাময়িক রাজনীতির ওপর যা অতটা প্রভাব ফেলেছে।
কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গানটির প্রভাব আন্তর্জাতিক এবং তা এখনো প্রবহমান; কিন্তু সেটি তৈরি হয়েছে ঘটনার ভেতর থেকে, অন্যদিকে 'বন্দে মাতরম' ঘটনার জন্ম দিয়েছে। রণধ্বনি হিসেবে 'বন্দে মাতরম' অবশ্য আগেও ছিল। যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে 'আনন্দমঠ' রচিত সেই বিদ্রোহের সময়েও কোথাও কোথাও ওই ধ্বনি শোনা গেছে বলে জানা যায়। সুপ্রকাশ রায় তার 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' বইতে উল্লেখ করেছেন, ১৭৬৩ সালে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে মসলিন তৈরির কারিগররা ঢাকায় ইংরেজের কুঠি আক্রমণ করে। [ চলবে ]