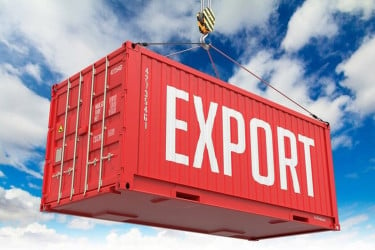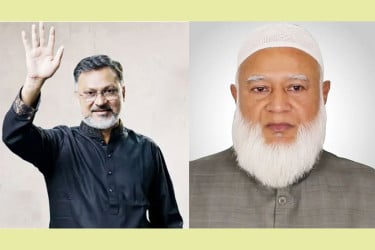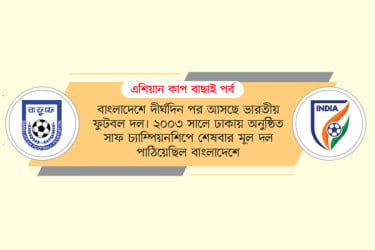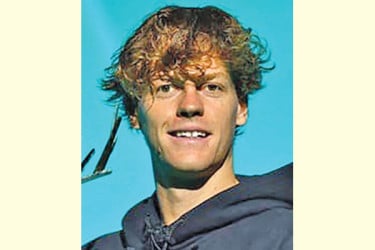বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি কিশোরসাহিত্য-গ্রন্থ ‘লাল নীল দীপাবলি’। লেখক ড. হুমায়ুন আজাদ। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে আগামী প্রকাশনী পুনঃপ্রকাশ করে। গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব পরম্পরা সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হলো।
বাঙলা সাহিত্যের তিন যুগ
প্রাচীন (৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ), মধ্য (১৩৫০-১৮০০), আধুনিক (১৮০০ থেকে বর্তমান)।
প্রথম প্রদীপ : চর্যাপদ
চর্যাপদ লিখিত হয় প্রাচীন যুগে। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন। ২৪ জন বৌদ্ধ মরমিয়া কবির মোট ৪৬টি কবিতা রয়েছে এতে। এর মধ্যে কাহ্নপাদ বারোটি, ভুসুকপাদ ছটি, সরহপাদ চারটি, কুক্কুরীপাদ তিনটি, লুইপাদ, শান্তপাদ, শবরপাদ দুটি এবং বাকিরা একটি করে কবিতা লিখেছেন।
অন্ধকারে দেড় শ বছর : ১২০০ থেকে ১৩৫০ অব্দের কোনো বাংলা রচনা পাওয়া যায় না। এ জন্য এই সময়কালকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ।
প্রদীপ জ্বাললো আবার মঙ্গলকাব্য। যেমন-অন্নদামঙ্গলকাব্য, ধর্মমঙ্গলকাব্য, কালিকামঙ্গলকাব্য, শীতলামঙ্গলকাব্য ইত্যাদি।
চণ্ডীমঙ্গলের সোনালি গল্প : চণ্ডীমঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। জনশ্রুতি অনুসারে কাব্যের আদি-কবি মানিক দত্ত।
মনসামঙ্গলের নীল দুঃখ
মনসামঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। এই কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত।
কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : মুকুন্দরাম আধুনিক যুগে জন্ম নিলে কবি না হয়ে ঔপন্যাসিক হতেন। হতেন শরৎচন্দ্র, তারাশংকর বা মানিকের মতো বাস্তবতার শিল্পী।
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র : ভারতচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি। অন্নদামঙ্গলকাব্য তার লেখা।
উজ্জ্বলতম আলো : বৈষ্ণব পদাবলি
দীনেশচন্দ্র সেন ১৬৫ জন বৈষ্ণব কবির নাম জানিয়েছেন। বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস। এ ছাড়া আছেন অনন্তদাস, উদ্ধবদাস, নরোত্তম দাস, নাসির মামুদ, বলরামদাস, বৈষ্ণবদাস, লোচনদাস, শ্যামদাস, সেখ জালাল, শেখর রায়, তুলসীদাস। বৈষ্ণব কবিতার মূল বিষয় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। রাধা ও কৃষ্ণ একে অন্যকে চায় কিন্তু মাঝখানে প্রবল বাধা। তেমনি সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একে অন্যকে চায় কিন্তু মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ বাধা- এ দুয়ের তুলনা করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। বৈষ্ণবদের মতে রস পাঁচ প্রকার- শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর।
বাবা আউল মনোহর দাস ষোড়শ শতকের শেষপ্রান্তে প্রথমবারের মতো বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করেন। প্রকাশ করেন পদসমুদ্র নামে এক বিশাল গ্রন্থ। এরপরের সংকলনের মধ্যে আছে রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু, গৌরীমোহন দাসের পদকল্পলতিকা, হরিবল্লভদাসের গীতিচিন্তামণি, প্রসাদদাসের পদচিন্তামণিমালা।
বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের মৈথিল কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় লিখতেন। বাঙলা, প্রাকৃত, হিন্দি থেকে শব্দ নিয়ে কেবল কবিতা লেখার জন্যই এই ভাষা তৈরি করা হয়েছিল। তার বই পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার। চৈতন্য ও বৈষ্ণবজীবনী শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনী বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। যেমন, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস। আর বেদব্যাসের মহাভারত অনুবাদ করেন কাশীরাম দাস। এরা দেবতুল্য মর্যাদা পান। এছাড়া আরও অনেকে খন্ড খন্ডভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।
ভিন্ন প্রদীপ : মুসলমান কবিরা
প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। তার মহাকাব্য ইউসুফ-জোলেখা। মুসলমান কবিরাই প্রথম কবিতায় দেবতার পরিবর্তে মানুষকে প্রাধান্য দেন। সাবিরিদ খান লেখেন হনিফা ও কয়রা পরী এবং বিদ্যাসুন্দর, বাহরাম খান লেখেন লাইলা-মজনু, মুহম্মদ কবির মধুমালতী।
ইতিহাস ও কল্পনা মিলিয়ে কয়েকজন কাব্য লিখেছিলেন। যেমন, আফজল আলীর নসিহৎনামা, জৈনুদ্দিনের রসুলবিজয়, শেখ ফয়জুল্লাহর গাজিবিজয় ও গোরক্ষবিজয়।
এরপর আসেন সপ্তদশ শতকের কবিরা- সৈয়দ সুলতান, শেখ পরাণ, হাজি মুহম্মদ, মুহম্মদ খান, সৈয়দ মুর্তজা, আবদুল হাকিম, দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন ঠাকুর এবং আরও অনেকে।
আলাওল মধ্যযুগের একজন বাঙালি কবি। তার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ পদ্মাবতী। এটা পড়ার সময় মনে হয় ‘যেন ক্রমশ একটি সযত্নে নির্মিত প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করছি।’
লোকসাহিত্য : বুকের বাঁশরি
সবচেয়ে বিখ্যাত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ময়মনসিংহের চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬)। তার সংগৃহীত গীতিকাগুলো ময়মনসিংহ গীতিকা নামে প্রকাশ করেন দীনেশচন্দ্র সেন। গীতিকা লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গীতিকা ছড়ার মতো ছোট নয়, অনেক বড়। বাঙলা সাহিত্যের বিখ্যাত গীতিকা প্রায় সবগুলোই ময়মনসিংহ থেকে পাওয়া।
রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার থলে), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (টুনটুনির বই)।
১৭৬০-এ মধ্যযুগের শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্র মারা যান। এরপর অর্ধ শতাব্দীব্যাপী আরেকটি অন্ধকার যুগ নেমে আসে। যাকে চিহ্নিত করা হয় দ্বিতীয় অন্ধকার। প্রথম অন্ধকার যুগের মতো এ যুগে যে কিছু লেখা হয়নি তা নয়। কিন্তু লেখাগুলো প্রায় সবই ছিল নিম্নমানের। এ সময় কবিগান প্রচলিত হয়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক কবি আরেক কবির সঙ্গে ছন্দে ছন্দে বিতর্ক করেন। এ ধরনের কবিদের বলা হয় কবিয়াল।
বিখ্যাত কবিয়ালদের মধ্যে আছেন : রাম বসু, রাসু, নৃসিংহ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হরু ঠাকুর, নিধু বাবু, কেষ্টা মুচি, ভবানী, রামানন্দ নন্দী এবং ভোলা ময়রা।
অভিনব আলোর ঝলক : ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। জন্ম হয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্য, নতুন কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সব কিছু।
গদ্য : নতুন সম্রাট
উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপহার বাঙলা গদ্য। মধ্যযুগেও গদ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো সাহিত্য নয় বরং চিঠিপত্র ও দলিলপত্র হিসেবে। যেমন- ১৫৫৫ অব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের অহমের রাজা স্বর্গদেবকে লেখা চিঠি।
বাঙলা গদ্যের বিকাশে বিদেশিদের (বিশেষ করে পর্তুগিজ) অবদান অসামান্য। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে রোমান অক্ষরে তিনটি বাঙলা গদ্যের বই বের হয়। একটি বইয়ের লেখক ঢাকা জেলার ভূষণা অঞ্চলের জমিদারের পুত্র দোম আনতোনিও। নাম ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ। অন্য দুটি বইয়ের লেখক পাদ্রি মনোএল দা আস্সুম্পসাঁউ। নাম কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবং বাঙলা-পর্তুগিজ অভিধান।
তবে প্রকৃত গদ্য উনিশ শতকেরই দান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তা পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। কলেজ থেকে প্রকাশিত বাঙলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম বই রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত।
গদ্যের জনক ও প্রধান পুরুষরা
উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আবির্ভূত হন রামমোহন রায়। বাঙলা গদ্যে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। তিনি সবার আগে বাঙলা গদ্যকে পাঠ্যবইয়ের বৃত্ত থেকে বিস্তৃততর অঙ্গনে নিয়ে যান।
‘বাঙলা গদ্যের জনক’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বাঙলা গদ্যের অস্থির রূপকে স্থির ক’রে দিয়ে গেছেন। মৌলিক বই লেখার পাশাপাশি তিনি অনুবাদ করেছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি অনন্য বই। বিদ্যাসাগরের সমকালে এবং একটু পরে যাঁরা উৎকৃষ্ট গদ্য লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এর আরও পরে আসেন আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ।