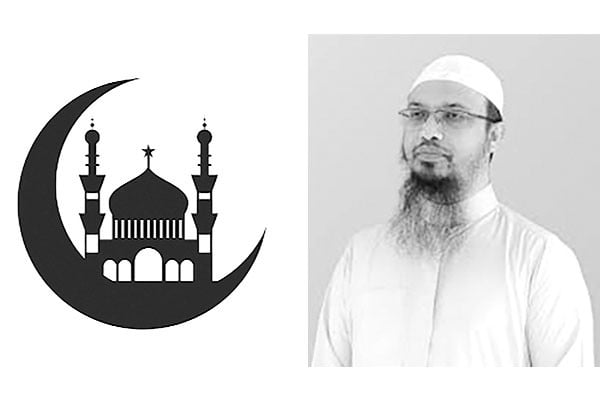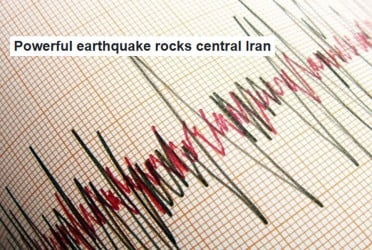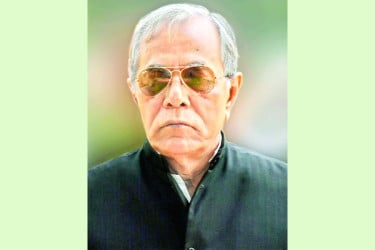সেটা সম্ভবত ১৯৮৮ কিংবা ৮৯ সালের কথা। আমার বাবা চাকরি করতেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তিনি ছিলেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সরকারি পরিদর্শক হিসেবে একবার বাবাকে পাঠানো হলো চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি উপজেলায়। এ ধরনের সরকারি ট্যুরগুলোতে বাবা সাধারণত আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বাবার সফরসঙ্গী হয়ে সেবার আমিও ঘুরেছিলাম চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, বাঁশখালী, লোহাগাড়া, পটিয়া ইত্যাদি উপজেলা। বাঁশখালী উপজেলায় গিয়ে একটি ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হলো। প্রত্যেক উপজেলাতেই আমাদের রাত্রিবাস সাধারণত হতো সরকারি সার্কিট হাউসে। কিন্তু বাঁশখালীতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন ওই অধিদফতরের একজন সহকারী প্রকৌশলী। অনেক পীড়াপীড়িতে বাবা তার আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। তার মাত্রাতিরিক্ত আদর আপ্যায়নে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম ওনার বইয়ের সংগ্রহশালাটি দেখে। বৃহৎ আকারের কাঠের আলমারিটি রাজ্যের সব বই দিয়ে ঠাসা। সবই পুরনো ধরনের বই। সহজাতভাবেই ছোটবেলা থেকে আমি একজন গ্রন্থপ্রেমিক মানুষ। আমার বয়স তখন ১০-১২ হলেও প্রায় শ’খানেক বই নিয়ে আমি গড়ে তুলেছিলাম ছোট্ট একটি গ্রন্থাগার। আমার চোখ গিয়ে পড়ল সেই লাইব্রেরিতে। থরে থরে সাজানো বইগুলোর মধ্যে দেখলাম সিল্কের কাপড়ে বাঁধানো শরত্চন্দ্রের বেশ কিছু উপন্যাস। সম্ভবত মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো রবীন্দ্র রচনাবলি। মোটা রেক্সিনের মলাটে কিছু পত্রিকার সংকলন- যেমন ‘প্রবাসী’, ‘শনিবারের চিঠি’ কিংবা ‘ভারতবর্ষ’। নজরুল কিংবা বঙ্কিমের রচনাবলিও শোভা পাচ্ছিল সেখানে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল কিংবা শরৎ এদের সাহিত্য কর্মের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকলেও প্রবাসী কিংবা ভারতবর্ষ পত্রিকাগুলো সম্পর্কে আমার আদৌ কোনো ধারণা ছিল না সেই বয়সে।
বাবাই প্রকৌশলী সাহেবকে প্রশ্ন করলেন- ‘আপনার সাহিত্যের প্রতিও বেশ অনুরাগ দেখছি।’ প্রকৌশলী মহাশয় এবার ভুল ভাঙালেন আমাদের, বললেন, ‘আরে না না ওগুলো আমার বই নয়। বইগুলো আমি পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার দাদার কাছ থেকে। দাদা চাকরি করতেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে। তিনিই ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমিক, সাহিত্যের আসল সমজদার। আরও অনেক বই ছিল তার সংগ্রহে। কালক্রমে অনেক বই-ই খোয়া গেছে। দেশ ভাগের পর দাদা বাবাকে নিয়ে ফিরে আসেন চট্টগ্রামে। আমার বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক- তারও বই পড়ার বাতিক ছিল বেশ ভালো রকমই বলতে হয়। কিন্তু আমি এই লোহা-লক্কড়, সিমেন্ট-সুরকি বিষয়ে লেখাপড়া করতে গিয়ে সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে উঠতে পারিনি কখনো।’
আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আমার এক বন্ধুপ্রতিমের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার বইগুলো একদিন নেড়েচেড়ে ও উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। ভারি আশ্চর্য হলাম একটি বিষয় লক্ষ্য করে। ওর পাঠাগারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই কেনা হয়েছে চল্লিশের দশকে। তাও আবার ঢাকার বাইরে থেকে। যেমন একটি বই দেখলাম- আন্দ্রে মরিস লিখিত ‘দ্য আর্ট অব লিভিং’ সেটি কেনা হয়েছিল ১৯৫০ সালে নবাবপুর রোডের কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি থেকে। ‘ফার্মা বুক অব আর্ট মাস্টারপিসেজ’ বইটি কেনা হয়েছিল ১৯৫৪ সালে, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে। ‘নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি সিলেক্টেড ইংলিশ শর্ট স্টোরিজ’ নামের বইটি কেনা হয়েছিল ১৯৫৫ সালে আইডিয়াল বুক ডিপো, বরিশাল থেকে।
ভাবতে অবাক লাগে এখন থেকে ৫০-৬০ বছর আগে কত ভালো ভালো বই পাওয়া যেত বাংলাদেশের মফস্বল জেলাগুলোতেও। তার মানে তখন মফস্বলের বেশিরভাগ শিক্ষিত লোকই সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এখন সেটা অবশ্য একেবারেই দেখা যায় না।
উপরোক্ত ঘটনা দুটির মাধ্যমে অনায়াসে ধারণা করা যায় যে, কীভাবে আমাদের দেশ থেকে সাহিত্য চর্চা ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯২৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে আমাদের সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ। আনন্দের বিষয় ছিল এই যে, ওই ১০-১২ ভাগ শিক্ষিত জনসমষ্টির সবাই কোনো না কোনোভাবে সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ শিক্ষিতের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি। কিন্তু সাহিত্য চর্চার হার বোধকরি ১০ ভাগ থেকে কমে ৩-৪ ভাগও হবে কিনা সন্দেহ। আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূর্ববঙ্গেও সাহিত্য চর্চা হতো নেহায়েত কম নয়। পূর্ববঙ্গের মাটি ও জল-হাওয়া সাহিত্যের জন্য এতটাই উর্বর ছিল যে, আজকের পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ প্রাতঃস্মরণীয় লেখক-সাহিত্যিকের জন্ম এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যে প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল এই বাংলাদেশেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (যশোর) থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী (পাবনা), বুদ্ধদেব বসু (ঢাকা), জীবনানন্দ দাশ (বরিশাল), শঙ্খ ঘোষ (চাঁদপুর), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (মাদারীপুর), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (খুলনা), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (ফরিদপুর), সৈয়দ মুজতবা আলী (সিলেট), দীনেশ চন্দ্র সেন (চট্টগ্রাম), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (ময়মনসিংহ), দেবেশ রায় (পাবনা), মনীশ ঘটক (পাবনা), ঋত্বিক ঘটক (পাবনা), মহাশ্বেতা দেবী (পাবনা), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (গাইবান্ধা), জরাসন্ধ (ফরিদপুর), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (ফরিদপুর), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (কুমিল্লা), সমরেশ বসু (বিক্রমপুর), নীরোদচন্দ্র চৌধুরী (ময়মনসিংহ)সহ আরও বহু লেখক সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ আমাদের এই বাংলাদেশে। বাংলা ভাষার শুদ্ধতম কবি জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতা ‘বর্ষা আবাহন’ (১৯১৯) ছাপা হয়েছিল বরিশালের একটি স্থানীয় ব্রহ্মবাদী পত্রিকায়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘নীরবিন্দু’ থেকে জানতে পারি জরাসন্ধের (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী) স্কুল-কলেজের সাহিত্য সাময়িকীর গণ্ডির বাইরে প্রথম গল্প ছাপা হয় পাবনার একটি স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকায়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কলকাতায় স্থায়ীভাবে থিতু হওয়ার পূর্ব থেকেই সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত ছিলেন এবং তার প্রথম গল্প কুমিল্লা থেকে ডাকযোগে পাঠিয়ে ছিলেন ঢাকার একটি পত্রিকায় এবং সেটি ছাপাও হয়েছিল পরবর্তীতে।
কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে দুটি কথা বলা আবশ্যক। এ সময়ে অনেকটা বিস্মৃত লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে ব্যতিক্রমধর্মী রচনাশৈলীর জন্য বেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিশেষ করে তার গল্প ‘গিরগিটি’ ও উপন্যাস ‘মিরার দুপুর’ বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ‘মিরার দুপুর’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। প্রাসঙ্গিকভাবেই বলতে হয়, মিরা চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম ‘এন্টি হিরোইন’ চরিত্র। ১৯২৭ সালে বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘প্রগতি’ পত্রিকাটি। বুদ্ধদেব বসু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ থেকে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ব্রিটিশ সরকার থেকে বৃত্তি পেতেন মাসে কুড়ি টাকার মতো। সেই টাকার সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তিনি প্রকাশ করতেন ‘প্রগতি’ পত্রিকাটি। ভাবতেও অবাক লাগে কী পরিমাণ জীবনীশক্তি ও সাহিত্যের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা থাকলে একজন তরুণতম কবির পক্ষে শুধু হাতে লিখে একটি পত্রিকা বের করা সম্ভব। প্রগতি পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ছিল ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। এ পত্রিকাটিতেই নিয়মিতভাবে ছাপা হতো জীবনানন্দ দাশ, নজরুল, মনীশ ঘটক, মনীশ ঘটকের ভাই সুরেশ ঘটকসহ আরও বিখ্যাত কবিদের কবিতা।
বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকপত্রগুলো উদীয়মান বাংলা ভাষাভাষী লেখক-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। আমার এ বক্তব্যের সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অন্তর্গূঢ় ও বলিষ্ঠ লেখক কবি ও কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র তার আত্মজীবনী ‘নানা রঙে বোনা’-তে লিখেছেন- ‘আর একটি যে নতুন জগতের সন্ধান তখন পেয়েছিলাম তা এক মুদ্রিত পত্রিকায়। বাড়িতে অনেক বাংলা পত্রপত্রিকা আসত, তার মধ্যে প্রথম যে পত্রিকাটি আমায় মুগ্ধ করে তার নাম ‘ভারত মহিলা’। সেটি কলকাতার কাগজও নয়। সে কাগজের প্রকাশ স্থান বলে যে দুটি শব্দ ছাপা থাকত আমার মনেও আপনা থেকেই তা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। শব্দ দুটি হলো উয়ারি, ঢাকা। বহুকাল বাদে ঢাকায় গিয়ে এই উয়ারি নামটি স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে পেয়ে একটা রোমাঞ্চই যেন অনুভব করেছিলাম। সুদূর উত্তর প্রদেশের একটি শহর থেকে অখণ্ড বাংলার সঙ্গে মনে মনে প্রথম যে ভৌগোলিক পরিচয় হয় তার মধ্যে কলকাতা বাদে ওই উয়ারি ঢাকাই প্রধান।
আমি একটি বিষয় বেশ গভীর দৃষ্টিপাত দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, চরমতম দারিদ্র্যের মধ্যেই সাধারণত মহানতম সাহিত্য সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয় অবশ্য। রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয় এই ব্যতিক্রমদের দলে। অন্যদিকে শেকসপিয়র থেকে শুরু করে দস্তয়ভস্কি, মার্কটোয়েন, অ্যালানপো, বদলেয়ার, এমিল জোলা, নজরুল, সুনীল, হুমায়ূন আহমেদ, আহমেদ ছফা, সুবোধ ঘোষ, শংকর, সমরেশ বসু, কমল কুমার মজুমদার এমন আরও শত-সহস্র লেখক দারিদ্র্যের কশাঘাতে পিষ্ট ও দগ্ধ হয়ে জীবনের সেই অভিজ্ঞতাগুলো লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। কয়লার খনিতে যেমন হীরার সন্ধান মেলে ঠিক তেমনি দারিদ্র্যের মধ্যেই সৃষ্টি হয় উত্কৃষ্ট সাহিত্য। নিজের অভাব অনটনের কথা বলতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, “একটি ডিমকে সুতা দিয়ে দুই ভাগ করার ক্ষেত্রে আমার মা ছিলেন একজন সুনিপুণ শিল্পী। বিভাজিত দুটি কুসুমের একটি থেকে এক বিন্দু কুসুমও কখনো স্খলিত হতো না।” কল্লোল পত্রিকাটির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এ পত্রিকারই আরেক লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজার আরেকটি বড় পরিচয় হলো উনি কবি কাজী নজরুল ইসলামের একেবারে ছোটবেলার বন্ধু। নজরুলের ওপর অসামান্য একটি জীবনী লিখেছেন শৈলজানন্দ। দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি সাহিত্যের মধ্যে কীভাবে মেতে থাকতেন সেই স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, ...“বাঁশরী’ পত্রিকায় গল্প লিখেছিলাম ‘আত্মঘাতীর ডায়রি’ নামে। দাদামশাই তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। গল্প কি কখনো আত্মকাহিনী হতে পারে। তবুও ভুল বুঝলেন দাদামশাই। বললেন, পথ দেখ।”
সে যাক লেখক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তার ‘কল্লোল যুগ’ বইটিতে লিখেছেন,— ‘মেসের সেই ঘরের চারপাশে তাকালাম আশ্চর্য হয়ে। শৈলজার মতো আরও অনেকে মেঝের ওপর বিছানা মেলে বসেছে। চারধারে জিনিসপত্র হাবজা-গোবজা। কারওবা ঠিক শিয়রে দেয়ালে-বেধা পেরেকের ওপর জুতো ঝোলানো। পাশ-বালিশের জায়গায় বাক্স-প্যাঁটরা। পোড়াবিড়ির জগন্নাথক্ষেত্র। দেখলেই মনে হয় কতগুলো যাত্রী ট্রেনের প্রতীক্ষায় প্লাটফর্মে বসে আছে। নিজেরা যদিও অভাবে তলিয়ে আছি, তবু শৈলজার দুস্থতায় মন নড়ে উঠল। কী উপায় আছে, সাহায্য করতে পারি বন্ধুকে? শৈলজাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, কী করে তবে চালাবে? সম্বল কী তোমার? সম্বল? শৈলজা হাসল, সম্বলের মধ্যে লেখনী, অপার সহিষ্ণুতা আর ভগবানে বিশ্বাস। তারপর গলা নামাল, আর স্ত্রীর কিছু অলঙ্কার, আর ‘হাসি’ আর ‘লক্ষ্মী’ নামে দু’খানা উপন্যাস বিক্রির তুচ্ছ ক’টা টাকা।’
সেকালে সাহিত্যচর্চার আরেকটি দিক ছিল- বিয়েশাদি কিংবা যে কোনো অনুষ্ঠানাদিতে প্রচুর বই পাওয়া যেত উপহার হিসেবে। কারণ সেকালে উপহার প্রদান কিংবা গ্রহণকারী উভয়ই বই দিতে কিংবা বই পেতে বেশ আনন্দবোধ করত। বর্তমান সময়ে সেই চল প্রায় উঠেই গেছে বলতে হয়। সেকালে ঢাকার একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সব্যসাচী লেখক বুদ্ধদেব বসু আমার ছেলেবেলায় লিখেছেন- ‘সেদিন ছিল ছানার পাকস্পর্শ, সন্ধে পেরিয়ে গেছে। দোতলায় রাস্তার দিকের চওড়া বারান্দায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে। সামনের সিঁড়ি দিয়ে একে-একে উঠে আসছেন সত্যেন্দ্রর বন্ধুরা ঢাকা কলেজে তার সহপাঠীর দল নববধূর হাতে দিয়ে যাচ্ছেন টুকটুকে লাল রিবনে বাঁধা বইয়ের প্যাকেট। এক-একবার দু’হাতে ধরা বইয়ের ভারে নুয়ে পড়েছে মেয়েটি, অন্য কেউ তার হাত থেকে নিয়ে তুলে রাখছেন।’
এ তো গেল বুদ্ধদেব বসুর কথা। এই মুহূর্তে আমার আরেকজন লেখকের কথা মনে পড়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শংকর তার ‘যেতে যেতে যেতে’ গ্রন্থটিতে লিখেছেন- ‘কলকাতায় এক সময় বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে প্রচুর বই দেয়ার রেওয়াজ ছিল।’ বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’ বইটি নাকি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, প্রায় সব বিয়ের অনুষ্ঠানেরই উপহার হিসেবে সেই বইখানা ছিল সবার পছন্দের। আর সে জন্যই নাকি অনেক বিয়েবাড়িতে যেখানে উপহারসামগ্রীগুলো সাধারণত যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয় তার পাশে বড় বড় অক্ষরে নোটিস ঝোলানো থাকত- ‘আর সাহেব বিবি গোলাম লওয়া হইবে না’।
এ তো গেল উপহার হিসেবে বইয়ের কথা। অনেক লেখক সাহিত্যিকের নিজেদের বিয়ের দিনেও বই পড়তে ও গান গাইতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বিয়ের রাতে তার নববধূকে গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। শরত্চন্দ্রকে দেখা যায় রেঙ্গুনে যেদিন তিনি বিয়ে করবেন সেদিনও বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে বাড়ি ফিরছেন, তারপর যাচ্ছেন বিয়ে করতে। অন্যদিকে একসময়ের বিখ্যাত লেখক রসরাজ অমৃতলাল বসুকে দেখি বিয়ের রাতে তিনি বই পড়ছেন। তার আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ ‘পুরাতন পঞ্জিকায়’ সে কথাই তিনি জানিয়েছেন আমাদের। তিনি লিখেছেন- “বিবাহের দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়; লালবিহারীর দোকান হইতে নাটক চাহিয়া পাঠাইলাম। দীনবন্ধু মিত্রের ‘লীলাবতী’ সেই প্রথম আমার হাতে পড়িল। তখনকার দিনে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের জন্য আমরা সবাই উদগ্রীব হইয়া থাকিতাম; বঙ্কিমের পুস্তকের জন্য তখনও জনসাধারণের সে রকম উৎকণ্ঠা হইত না। যখন বঙ্গদর্শনে ‘বিষবৃক্ষ’ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন হইতে বঙ্কিম সবার হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন; তাহার পূর্বে সবাই খোঁজ করিত- দীনবন্ধুর কোনো নতুন নাটক বাহির হইল কিনা। বিবাহের দিন ‘লীলাবতী’ আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম,- তাই তো, পত্নীটি আমার কি রকম হবেন! সারদা সুন্দরীর মতো হলেই ভালো হয়; আমার ঝোঁক লীলাবতীর চেয়ে সারদা সুন্দরীর দিকে। নিশ্চয়ই সারদা সুন্দরীর মতো হবে। যদি না হয়! লীলাবতীও মন্দ নয়, কিন্তু...। বিবাহ হইয়া গেল। দেখিলাম আমার পত্নীটি সারদা সুন্দরীও নন, লীলাবতীও নন,... একটি চেলির পুঁটলি!”
সেকালের সাহিত্যচর্চার আরেকটি বিশেষ দিক ছিল- মহিলারাও ঘরকন্না ও গৃহস্থালির কাজকর্মের পাশাপাশি সাহিত্য পাঠের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দেবীর কথা। তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন বলা যায় বেশ অল্প বয়স থেকেই। কুসুমকুমারী বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি কবিতা তো রীতিমতো বিখ্যাত- আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। জীবনানন্দ দাশের কবি হয়ে ওঠার পেছনেও ছিল কুসুমকুমারী দেবীর অসামান্য প্রেরণা ও উৎসাহ।
ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের মা-খালা কিংবা চাচিদের অবসরে বই পড়তে। তখনো পর্যন্ত আকাশ সংস্কৃতির হিংস্র আগ্রাসন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েনি। এখন মা-খালা, ফুফুদের সাহিত্যচর্চা আর প্রায় একটা দেখা যায় না বললেই চলে। বই পড়ার জায়গা বর্তমানে করে নিয়েছে ‘কিরণমালা’ নয় তো স্টার প্লাসের অন্য কোনো হিন্দি সিরিয়াল। আর অল্প বয়সের তরুণ-তরুণীরা ভয়ানকভাবে ঝুঁকে পড়েছে ফেসবুক নামক এক বস্তুতে। নিত্যনতুন আধুনিক সব প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত আমরা অবশ্যই হব। কিন্তু কোনো কিছুর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি থাকা উচিত নয়। তবে এ কথাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, নতুন যে কোনো প্রযুক্তির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার অভ্যাস মানুষের চিরন্তন।
সম্ভবত বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কোনো একটি লেখায় পড়েছিলাম- প্রথম প্রথম যখন বাংলাদেশে রেডিও চালু হয় তখন নাকি লোকজন মাঠে প্রাতঃকৃত সারতে গেলেও তার প্রিয় রেডিওটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। এ জন্যই বোধকরি ধনী লোকদের বাথরুমগুলোতে স্টেরিও সেট লাগানো থাকে। ১৯৬০-৬৫ সালের দিকে যখন বাংলাদেশে প্রথম টেলিভিশন চালু হয় তখন নাকি টিভিতে তেমন কোনো ভালো অনুষ্ঠান হতো না। মাঝে মাঝে দু-তিন ঘণ্টা লাগাতার শুধু যন্ত্রসংগীতই বাজত। প্রযুক্তিপ্রিয় মানুষজন নাকি সে সময় ঘণ্টা ধরে বসে বসে শুধু ওই যন্ত্রসংগীতই শুনত। আমারও কেন জানি মনে হয় মানুষের ফেসবুকের প্রতি এই আসক্তিও কমে আসবে একদিন। সাহিত্যচর্চার প্রতি এত প্রতিকূলতা ও বিরাগ থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে আশা জাগে যখন দেখি আমার একজন প্রিয় শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে বই তুলতে। নিভু নিভু সাঁঝবাতিটা যেন পুনরায় জ্বলতে দেখা যায়। আমার কেন জানি মনে হয় এই নিভু নিভু এক সাঁঝবাতির আলো ছড়িয়ে দেবে আরেক সাঁঝবাতিতে। এভাবে আলোয় আলোয় ভরে উঠবে সমগ্র বাংলাদেশ।
লেখক : গল্পকার ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী
ই-মেইল : [email protected]