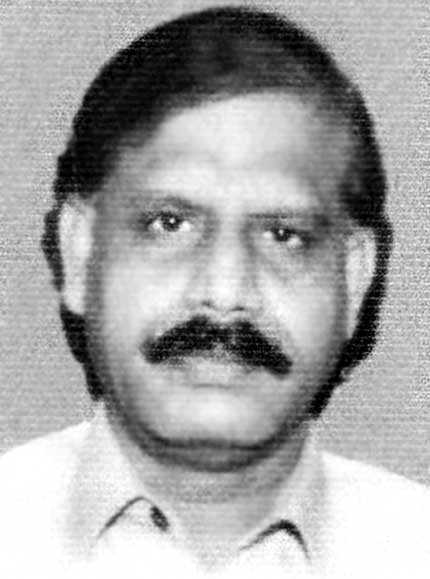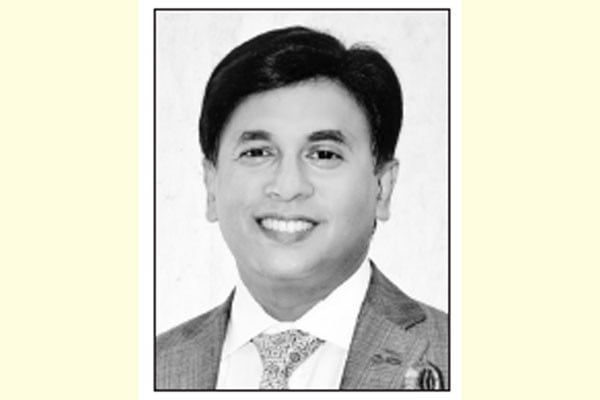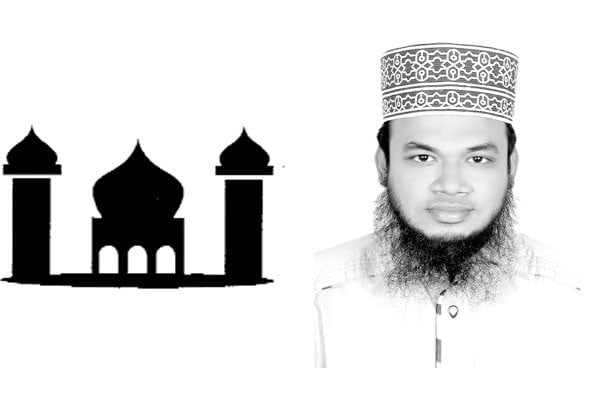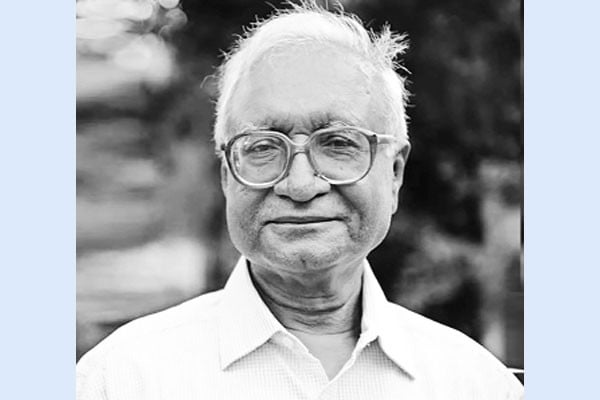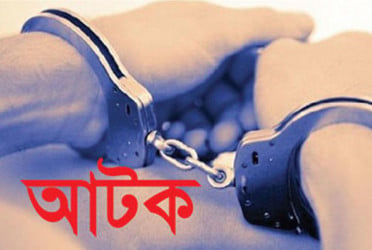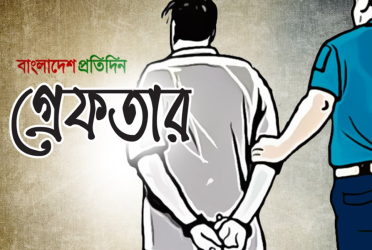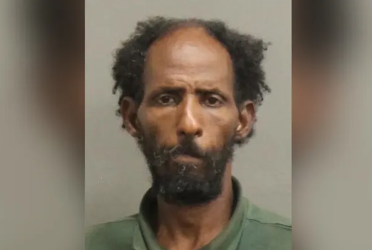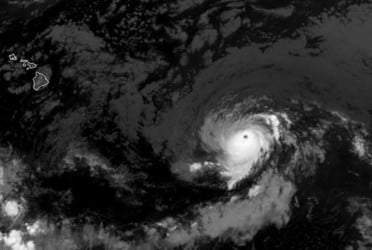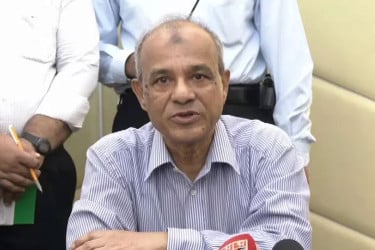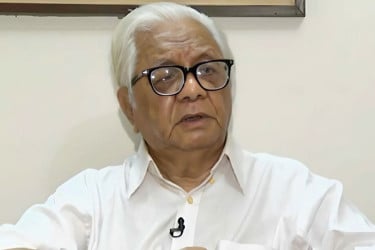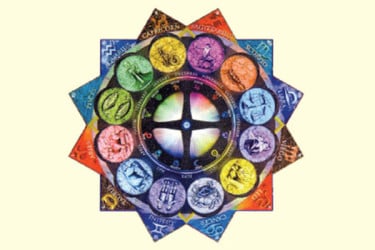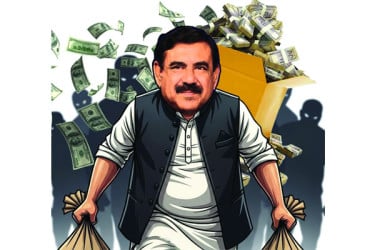এক. ডিকশনারির বাংলা প্রতিশব্দ অভিধান বা শব্দকোষ। কোনো ভাষার শব্দসমষ্টি, অভিধানে বর্ণমালা অনুযায়ী সাজিয়ে মুদ্রিত থাকে যাতে প্রয়োজনীয় শব্দের আদ্য অক্ষর ধরে খুঁজলে সহজে পাওয়া যায়। আসলে এটি ভাষান্তর অর্থাৎ একটি ভাষার আওতায় প্রার্থিত শব্দের বিপরীতে অন্য ভাষার কি শব্দার্থ, তা জানা যায়। আর এ প্রেক্ষাপটে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, একটি অভিধান হলো 'সার্বক্ষণিক একান্ত কাছের শিক্ষক'। সত্যি কথা বলতে কি, অভিধান বা শব্দকোষের চেয়ে Dictionary নামটি বহুল প্রচলিত। আর ইংরেজি Dictionary শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Dictonarium থেকে, যার অর্থ হলো শব্দের ভাণ্ডার। এদিকে Dictionary আর একটি পরিপূরক শব্দ হলো Lexicon, যা গ্রিক শব্দের আদলে সৃষ্ট। মূলত এটি শব্দার্থ বই, যা সবার জন্য একান্ত আবশ্যক ও জরুরি। কেননা এই বইটি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করে থাকে। উল্লেখ্য, ডিকশনারি বা অভিধানে কেবল শব্দের অর্থ থাকে না। একই সঙ্গে শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, অর্থ এবং ব্যবহারবিধি ইত্যাদি সনি্নবেশিত থাকে। দুই. এটা স্বীকৃত যে, হাজার হাজার বছর আগে জ্ঞান-গরিমাসহ অনেক সভ্যতার উন্মেষ হলেও ডিকশনারি বা অভিধানের ব্যবহার খুব বেশি দিন আগের নয়। যতদূর জানা যায়, বিশ্বে সর্বপ্রথম অভিধান লেখা হয় ইংরেজি ১২২৫ সালে। তাও আবার ল্যাটিন ভাষায়। আর এই অভিধান সংকলনের মহতী কাজটি করেছিলেন জন গারল্যান্ড (John Garland) নামে এক বিচক্ষণ পণ্ডিত। এদিকে ইংরেজি ভাষায় প্রথম ডিকশনারি প্রণয়ন ও প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৫৫২ সালে এবং এক্ষেত্রে সেই স্বনামধন্য উদ্যোগী, অভিজ্ঞ ও গুণী ব্যক্তিটি ছিলেন রিচার্ড হুলেট (Richard Huloet); এ ডিকশনারির শব্দ সংখ্যা ছিল প্রায় ২৬ হাজার এবং নামটি ছিল 'Abcdedarium Anglico-Latium Pro. Tyrunculis'. আর এই ডিকশনারিটি তৎকালে খুব জনপ্রিয় ছিল। আর এ সূত্র ধরে সবচেয়ে যে বিষয়টি প্রভাবিত করেছে, তা হলো এই অভিধানমূলক কনস্পেটটি প্রত্যেক দেশে তাদের ভাষার অভিধান প্রণয়নের আবশ্যকতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেই থেকে বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় ও আঙ্গিকে অভিধান সংকলনের রেনেসাঁ শুরু হয়। এদিকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম ডিকশনারি হলো অঙ্ফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি, যা ১২ খণ্ডে সংকলিত এবং এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫ হাজার ৪৫৭। উল্লেখ্য, আগে অভিধানে ছবি থাকত না। কিন্তু ইদানীং কিছু কিছু অভিধানে শব্দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ছবি সংযোজন করা হয়ে থাকে। তবে এ বিষয়টি নতুন প্রবর্তিত শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিন. এখন বলতে গেলে সারা বিশ্বে এমন কোনো লিখিত ভাষা নেই যে, তার ডিকশনারি নেই। সঙ্গত কারণেই আমাদের মাতৃভাষার প্রথম অভিধানের কথা না বললে কমতি থেকে যাবে। এক্ষেত্রে সেই মহান ব্যক্তির কথা এসে যায়, যিনি হলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনিই প্রথম অর্থাৎ ১৮১৭ সালে বাংলা ভাষায় (বাংলা থেকে বাংলা) প্রথম অভিধান প্রণয়ন ও সংকলন করেন। আর এর ঠিক শত বছর পর তথা ১৯১৭ সালে বড় কলেবরে প্রায় ৭৫ হাজার শব্দ সংবলিত 'বাংলা ভাষার অভিধান' নামে একটি বই সংকলন করেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং এর ২০ বছর পর এই অভিধানকে আরও ঢেলে সাজিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। আর এতে প্রায় এক লাখ ১৫ হাজার শব্দ সংকলিত করা হয়। ব্রিটিশ আমলে সারা বাংলায় এই ডিকশনারি দিয়ে কাজ চললেও, সাতচল্লিশে পাকিস্তান হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তাদের স্বকীয়তা নিয়ে নিজস্ব অভিধানের প্রয়োজন অনুভব করেন। এক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই মহতী কাজে হাত দেয় এবং ১৯৬১ সালে এর সংকলনের কাজ শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের নিয়ে একটি পর্ষদ গঠন করা হয়। যাতে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, অজিত কুমার গুহ, আহমদ শরীফ প্রমুখ। এর মধ্যে সময়ের পরিক্রমায় অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালে অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের আলোকে 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' নামে প্রকাশিত হয় এবং ২০০০ সালে পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়; তাতে প্রায় ৭৫ হাজার বাংলা শব্দ জায়গা করে নেয়। তৎপর বাংলা একাডেমি আরও বড় পরিসরে এগিয়ে যায়, যার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অধুনা প্রকাশিত হয়েছে, 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান'। আর এ কর্মকাণ্ডে সময় লাগে প্রায় সারে তিন বছর। এদিকে এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাপিডিয়া নামে ২০০ খণ্ডের বিশেষ ধরনের অভিধান সংকলন করে। ইদানীং ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এর তাৎক্ষণিক অভাব মিটলেও বই আকারে (হার্ড কপি) এর গুরুত্ব কোনো দিন কমবে না বলে বিশ্বাস করি।