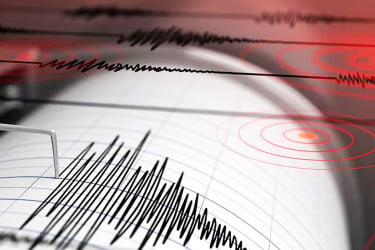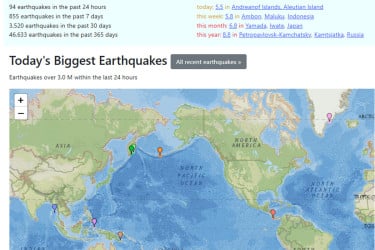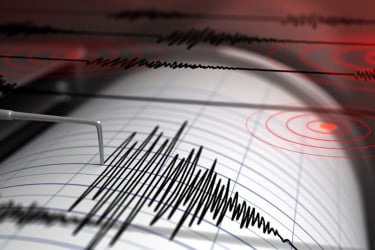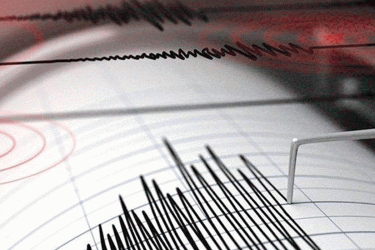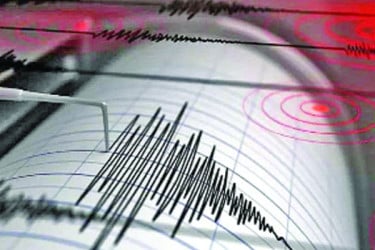১২ মে শুক্রবার মাকে দেখতে কুমিল্লায় যাচ্ছিলাম। মোবাইল ফোনে বিভিন্ন খবর পড়ার ফাঁকে লক্ষ্য করলাম এক দিন পর অর্থাৎ ১৪ মে ২০২৩ রবিবার পালিত হবে বিশ্ব মা দিবস। যাদের মা জীবিত নেই এ দিনটি তারা কী করে অতিবাহিত করেন এ প্রশ্ন আমাকে তাড়িত করেছে বছরের পর বছর। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এবার বিশ্ব মা দিবসের ঠিক আগের দিন ১৩ মে দুপুরে আমাদের ছেড়ে গেলেন আমাদের মমতাময়ী মা। যদিও ৮৪ বছর বয়সী শয্যাশায়ী মাকে যে কোনো সময় চলে যেতে হবে বলে ডাক্তাররা আগেই বলে রেখেছিলেন তবু কায়মনো বাক্যে চেয়েছিলাম আরও কটা দিন থাকুক না পরিবারের এ প্রাণভ্রমর! তাঁকে ঘিরেই পরিবারের মিলনমেলা হতো। অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে হলেও মাকে নেওয়া হতো নাতি-নাতনির বিয়েতে। আমরা পঞ্চাশোর্ধরা কেন জানি শরিয়ত-মারফত-বিদআতের ঊর্ধ্বে ওঠে পা ছুঁয়ে ময়-মুরুব্বিকে সালাম না করে তৃপ্তি পাই না। তবে পা ছুঁয়ে সালাম করা যায়, এমন মুরুব্বির সংখ্যা এখন হাতে গোনা কয়েকজন। তাই মাকে পাশে পেলে সালাম করার উৎসব শুরু হতো এসব অনুষ্ঠানে। না, তেমনটি আর হবে না। নাতি-নাতনিরা ঈদের সালামির জন্য বারবার আর ‘নানু- আমাকে!! দাদু আমাকে’ বলে হইচই বাধাবে না। কারণ সংসারের মধ্যমণি আর নেই। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া নাতনিকে চাহিবামাত্র আইসক্রিম, আচার আর চিপস কেনার টাকা দেওয়া ‘ম্যাজিক নানু’ কোন জাদুবলে যেন আকাশে মিলিয়ে গেলেন।
আমার নানা তৎকালীন ব্রিটিশ রেলওয়েতে চাকরি করতেন। থাকতেন কলকাতায়। সেখানেই ইংরেজি কনভেন্ট স্কুলে পড়তেন মা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর নানা সপরিবারে চলে আসেন এপারে। যোগ দেন ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে নানা তাঁর পীরের আদেশে মা-এর বিয়ে দেন। বাবা কাজ করতেন তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানে, যা বর্তমানে সোনালী ব্যাংক নামে পরিচিত। বাবাও ছিলেন একই পীরের মুরিদ। মাইজভান্ডারি তরিকায় বিশ্বাসী এ পীরসাহেবের দীক্ষায় হয়তোবা একরকম সংসার বিরাগী হয়ে যান আমার বাবা। চাকরি করে মাস শেষে মায়ের হাতে যৎসামান্য বেতনের টাকা তুলে দেওয়া ছাড়া সাংসারিক কোনো দায়দায়িত্ব পালনে বাবা মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর সব আগ্রহ ছিল প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর পীরভাই ও অন্য ফকির সন্ন্যাসীদের নিয়ে মোমের আলোতে আগরবাতি জ্বালিয়ে রাতভর জিকির করার দিকে। আর মায়ের কাজ ছিল বিশাল ডেকচিতে লাকড়ি পুড়িয়ে খিচুড়ি রান্না করা ও সবাইকে খাওয়ানো। এর বাইরে আরবি মাসের ১১ তারিখে ‘১১ শরিফ’, বড় পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর জন্মদিন, মিলাদুন্নবী, শবেবরাত ইত্যাদি উপলক্ষে ওরসের নামেও সারা রাত জিকির-আসকার হতো বাড়িতে। বাজার-সদাই, রান্না, বণ্টন সবই সামাল দিতেন মা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে মায়ের কোলজুড়ে আসে আমাদের বড় বোন। এরপর অল্প ব্যবধানে আরও তিন ভাই ও এক বোন। আমাদের বাসায় থেকে কলেজে পড়তেন আমাদের একমাত্র মামা। কদিন পর এক চাচাতো ভাইও যোগ দিলেন মামার সঙ্গে। আবার চিকিৎসা, চাকরির জন্য পরীক্ষা, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড অফিসে কাজ, ঢাকা-চট্টগ্রাম বা ঢাকা-নোয়াখালী যাওয়া-আসার পথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বিশ্রাম কিংবা হাওয়া বদল এমন নানাবিধ উপলক্ষ দেখিয়ে বছরব্যাপী মেহমান থাকত আমাদের বাসায়। পীরসাহেব বছরে অন্তত একবার একদল মুরিদ নিয়ে আস্তানা গাড়তেন। থাকতেন ৮-১০ দিন। বাবার ছিল স্বল্প বেতন। বাড়ি ভর্তি এত মানুষের থাকা-খাওয়া ঠিকই চালিয়ে নিতেন মা। বাবা নির্বিকার। জগৎ-সংসারে কোনো অভাব-অভিযোগ আছে বলে তিনি কখনো ভাবতেই পারতেন না। আমরা ভাইবোনরা কৌতুক করে বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম- আমরা কে কোন ক্লাসে পড়ি! বাবা স্বর্গীয় হাসি দিতেন- উত্তর দিতেন না। আমাদের ধারণা, বাবা নিশ্চিতভাবে জানতেন না আমরা কে কোন ক্লাসে পড়ি। অথচ পাঁচ সন্তানকে এক হাতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন মা। এর মধ্যে বড় বোনের বিষয়টি ছিল অবাক করার মতো। নাটকীয়ভাবে বড় বোনের বিয়ে হলো কলেজ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। মা তাঁর মেয়েকে তো সংসার করতে দিলেনই না, বরং জামাইকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। মার একটাই কথা- মেয়েকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, তারপর অন্য কথা। বড় বোন বিএসসি পড়া শুরু করলেন। চার বছর সময়ের মধ্যে তার কোলজুড়ে আসে দুই সন্তান। আমার মায়ের সে কী আনন্দ! দুই কোলে দুই নাতি- নাতনি নিয়ে সংসারের সব দিক দেখছেন। এক হাতে নাতনি আর অন্য হাতে রান্না। নাতির পেছনে দৌড়ে ও তাকে ধরে এনে কি টিউবওয়েলের নিচে গোসল করানো, এমন দৃশ্য নাটকের মনে হলেও সবই আমার নিজের চোখে দেখা। কী যে কর্মঠ ছিলেন মা! কখনো কুড়াল দিয়ে লাকড়ি কাটছেন আবার কখনো দা দিয়ে নারিকেল ছিলছেন, মাঝে গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-কবুতরকে খাবার দিচ্ছেন- সে এক এলাহি কা-।
এর মধ্যে বড় বোনের দেবর উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত হলেন। দুলাভাই এবার নতুন বাসায় যেতে চাইলেন ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার কথা বলে। বড় বোনের গ্র্যাজুয়েশন তখনো বাকি। মার একটাই কথা- আগে মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন। এ সমস্যার সমাধানও করলেন মা। এক দিন সেই বড় বোনের দেবর যোগ হলেন আমাদের সঙ্গে। এবার আমরা তিন ভাই, সঙ্গে আরেক বড় ভাই। এরই মধ্যে আচমকা বিয়ে ঠিক হলো বড় বোনের এক ননদের। তখন এত ডেকোরেটর সার্ভিস ছিল না। এ বাড়ি-ও বাড়ি থেকে চেয়ার, টেবিল, প্লেট, গ্লাস, জগ এনে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান হতো আর কলাগাছ ও দেবদারু পাতা দিয়ে গেট সাজানো হতো। হঠাৎ করে কে কোথায় কী আয়োজন করবে ভেবে ব্যাকুল। মা বললেন, আমাদের বাসায় বিয়ে হবে। কাউকে কোথাও যেতে হবে না। দিব্যি একটি বিয়েও সামাল দিলেন।
সত্তরের দশকে একজন সৎ ব্যাংক কর্মকর্তার বেতনে এতগুলো মানুষের বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন আমাদের মা। অভাব ছিল, তবে মা তা বুঝতে দেননি কাউকে। নিজের হাতে রান্না করা মাছ-গোস্ত সবই তুলে দিতেন অন্যের পাতে। ডেকচি বা কড়াইয়ের গায়ে লেগে থাকা ঝোলের ওপর ভাত ছিটিয়ে মেখে নিতেন আর পরম তৃপ্তিতে খেয়ে আল্লাহর শোকর গুজার করতেন। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় মিষ্টি আলু সেদ্ধ করে সবাইকে খাওয়াতেন ভাতের ওপর চাপ কমানোর জন্য, কিন্তু কাউকে বুঝতেও দিতেন না। কিস্তিতে হাতে ঘোরানো সিঙ্গার সেলাই মেশিন কিনলেন সবার জামা-কাপড় বানানোর জন্য। কিস্তির সেই ২০ টাকা শোধ করতেন ঘরে পালা মুরগির ডিম আর গাছের নারিকেল-সুপারি বিক্রি করে। একবার চুরি হলো বাড়িতে। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে সেলাই মেশিনও নিয়ে যায় চোরের দল। মা সবচেয়ে দুঃখ করলেন তাঁর সেলাই মেশিনটির জন্য। কদিন পর এ মেশিন উদ্ধার হলো এবং আমাদের বাসায় চলে এলো। আবার আমাদের জামা-কাপড় এমনকি প্রতিবেশীদের কাপড়ও সেলাই করা শুরু করলেন বিনা পারিশ্রমিকে। প্রতিবেশীদের বাচ্চা প্রসবের আগে অবধারিতভাবে মাকে ডাকা হতো। তাঁর হাতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং তাঁর যত্ন পেয়েছে এমন নবজাতক শিশুর সংখ্যা নিজেও জানতেন না তিনি। তাঁর হাতে বোনা সোয়েটার পেয়েছে তাঁর নাতি-নাতনিদের সবাই, এমনকি অনেক পাড়া-প্রতিবেশীও। ১৯৭১ সালে এই পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকেই বিশেষত সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মাঝপথে রাজাকারদের হাতে লুটপাটের ভয়ে মার কাছে তাদের মূল্যবান গয়না, টাকা-পয়সা, জমির দলিল ও অন্যান্য দামি সম্পদ রেখে সীমান্ত পাড়ি দেয় এবং শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযুদ্ধ শেষে মা যথারীতি যার যার কাছে তাদের গচ্ছিত সবকিছু ফিরিয়ে দেন। এ সময় আমাদের ছোট বোন পৃথিবীতে আসার অপেক্ষায় শেষ দিনগুলো গুনছিল। অন্যদিকে বড় বোন ছিলেন চোখে পড়ার মতো। যুদ্ধকালীন ৯ মাসে বড় বোনকে সব সময় লুকিয়ে রাখা আবার ছোট সন্তানের জন্মদান, এরই মধ্যে আমাদের সবার দেখভাল কেমন করে যে মা করেছেন তা আজ ভাবতেও অবাক লাগে।
এক ঈদের পর সবাই বেড়াতে গেলাম একমাত্র মামার বাড়ি। আমার নানি তখন প্যারালাইসিসের কারণে বিছানায় শয্যাশায়ী। তাঁর অবস্থা দেখে মার চোখে পানি। আমার বৈরাগী বাবা মনে হয় এই প্রথম আমার মায়ের মনের কথা পড়তে পারলেন। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বাবা নানিকে নিয়ে এলেন কুমিল্লার বাসায়। এবার শয্যাশায়ী আমাদের নানির সেবায় নিজেকে সঁপে দিলেন মা। প্রায় সাত বছর বিছানায় পড়ে থাকা ও নড়াচড়া করতে না পারা এ নানিকে পরিষ্কার রাখা, খাওয়ানো, নখ ও চুল কাটা, কাপড় বদলানো ও ধুয়ে দেওয়া সবই করেছেন আমাদের মা। এ বৃদ্ধা নানুর মৃত্যুর পর নিজের বাবাকেও অর্থাৎ আমাদের নানাকেও নিয়ে আসেন বাবার পরামর্শে। বাবা-মা হারানো আমাদের পিতৃ দেবতা হয়তো নানা-নানির মধ্যেই তাদের খুঁজে পেতেন। নানাও ছিলেন প্রায় অচল। মা তাঁকে সেবা করে গেছেন আরও ছয় বছর। নানার মৃত্যুর পর আমার বাবাও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে স্ট্রোকের কারণে তাঁরও শরীরের একটি অংশ অবশ হয়ে যায়। এ সময় তাঁকে প্লাস্টিকের নল দিয়ে খাওয়ানোসহ অকৃত্রিম সেবা করেছেন মা। বর্তমানে বহুল প্রচলিত ফিজিওথেরাপি তখন তেমন প্রসারিত হয়নি। কিন্তু মা কোন কবিরাজের কাছে কি শুনলেন জানি না, রসুন ও সরিষার তেল গরম করে অনবরত থেরাপি দিয়ে বাবাকে অনেকটাই সুস্থ করে তুললেন। এক সময় বাবা কথাও বলতে পারছিলেন না। অথচ বাবার ঠোঁট নাড়া দেখে এমনকি চোখ দেখেও মা ঠিকই বুঝে যেতেন বাবা কী চান। মাকে দেখলেই বাবা যেন সুস্থ হয়ে উঠতেন আর না দেখলে মৃতপ্রায়। ১-২-৩ অর্থাৎ ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখে বাবা চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। এরপর মা মনের জোর হারিয়ে ফেললেন এবং দ্রুতই দুর্বল হতে থাকলেন। এক সময় পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে গেলে মা নিজেই শয্যাশায়ী হন। এ সময় তাঁর দুই পুত্রই জীবন-সংগ্রামে দূরের দুই শহরে আর এক পুত্র বিদেশে। দুই কন্যা স্বামী-সন্তান নিয়ে ঢাকায়। ইতিহাস যেন পুনরাবৃত্তি ঘটাল আমাদের পরিবারে। দেশে থাকা এক পুত্র নিজের ক্যারিয়ারের মায়া ত্যাগ করে মায়ের কাছে কুমিল্লায় চলে এলেন। পুত্রবধূ পরম মমতায় মায়ের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিলেন। সেবা করার মতো একটি গ্রামের মেয়ে ও তার মা জুটে গেল। যে যুগে আপন মা-বাবার ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে, সেই যুগে এক পুত্রবধূ হাতে গ্লাভস পরে নিজের শাশুড়িকে পরিষ্কার করেছেন বছরের পর বছর। এই বছরগুলোতে এ পুত্রবধূ শাশুড়িকে ছেড়ে দূরে থাকেননি এক রাতের বেশি। কোনো অভাব-অভিযোগ করেননি। স্রষ্টা এ জগতে কষ্ট দিয়েই হয়তো মায়ের পরবর্তী জীবনের সুখের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আর শয্যাশায়ী মা-বাবা ও স্বামীকে সেবার বিনিময়ে এমন পুত্রবধূ দান করেছেন।
নাতি-নাতনিদের কাছে তিনি ছিলেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দৈত্যতুল্য। তাঁর বিছানায় এখানে-সেখানে ভাংতি টাকার খনি ছিল। নাতি-নাতনির যে কোনো আবদার মেটাতে এ ভাংতি ভান্ডারের তুলনা ছিল না। তিনি যেন এক জাদুর তোশকে থাকতেন গায়ে স্বর্গীয় চাদর জড়িয়ে। চুম্বকের মতো আমাদের সবাইকে টানত সেই জাদুর তোশক। কদিন পর পরই পাঁচ ভাইবোন মাকে ঘিরে সেই তোশকে শুয়ে থাকতাম। আমাদের ঈদ হতো মূলত ঈদের পরের দিন মাকে ঘিরে। যে যেখানেই ঈদ অতিবাহিত করুক, পরদিন ঠিকই হাজির হতো মায়ের চারপাশে। স্মৃতিতে ভেসে উঠত সেই দিনগুলোর কথা, যখন আমাদের কোনো ফ্রিজ ছিল না। মা ঈদের রাতে বেঁচে যাওয়া সব মিষ্টান্ন একসঙ্গে করে ঘন দুধ দিয়ে আবারও জ্বাল দিতেন পাঁচমিশালি সেই মিষ্টান্ন। আর পরদিন আমরা অপেক্ষা করতাম সেই অপূর্ব স্বাদের মিষ্টান্নের জন্য। বেশি পোলাও নতুন মাত্রা পেত মার হাতে। কোরবানি ঈদের পর গরুর মাংস দিনের পর দিন জ্বাল দিয়ে যখন ঝুড়া আকারে আমাদের চালের রুটির সঙ্গে দেওয়া হতো, মনে হতো এই পৃথিবীতে এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর কিছু নেই। পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনির বাইরে নাতবউ ও নাতজামাইরাও নানু বা দাদু বলতে যেন অজ্ঞান ছিল। পাঁচ সন্তান এবং ১২ নাতি-নাতনি ও তাদের স্বামী সন্তানদের সবাই তাঁর অনুপ্রেরণায় উচ্চশিক্ষিত, কর্মজীবী ও দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। তারা সবাই নানু বা দাদুকে উপহার এবং নগদ টাকা দিয়ে নিজেরা তৃপ্তি পেত। মা নিজের ইচ্ছামতো গরিবদের দান করতেন। বিছানায় শুয়েই তিনি এমন এক ভার্চুয়াল জগৎ তৈরি করেছিলেন যেখানে কোনো সন্তান বা নাতি বিদেশে বরফে কষ্ট পাচ্ছে, কার শরীর ভালো যাচ্ছে না, কোন নাতির পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশিত হবে- সবই তাঁর জানা ছিল। দূরদূরান্ত ও বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজন রোগী নয়, নিজেদের ভালোবাসার মানুষটিকে দেখতেই যেন বারবার ছুটে যেত সেই জাদুর বিছানায়।
১২ মে শুক্রবার ছিলাম মার সঙ্গে। ১৩ মে শনিবার সকালে মার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি মার চোখ বন্ধ। তাঁর পুত্রবধূ পায়ের কাছে বসা। ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে পুত্রবধূ (আমার ভাবি)-কে বললাম, আমার জরুরি কাজ আছে। আমি ঢাকা রওনা হচ্ছি। মার ঘুম ভাঙলে বলে দিও। ওমনি মা চোখ খুললেন। ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরলেন। মাথা ও মুখে হাত বুলালেন। আমার মাথাটা তুলে নিজের গালের সঙ্গে আমার গাল লাগালেন। মৃদুস্বরে বললেন, আমার জন্য খাস দিলে দোয়া করো বাবা। সবাইকে বলো খাস দিলে দোয়া করতে আর মাফ করে দিতে। আমিও মাফ চাইলাম। দোয়া চাইলাম। উত্তরে শুধু আমার মাথায় হাত বুলালেন মা। বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা করো। পথে ভাবছিলাম ফেলে আশা দিনগুলোর কথা। অভাবের মধ্যেও মা বই কিনে দিতেন। নিজেও বই পড়তেন। কোরআন পড়তেন। ইত্তেফাক পত্রিকা পড়তেন। আমাদের ‘কচিকাঁচার আসর’ পড়তে দিতেন। নিজের অজান্তে এভাবেই হয়তো মা আমার মধ্যে সৃজনশীল লেখার বীজ বুনেছিলেন।
আমি ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছেই ফোন দিলাম। কারণ যে কেউ যাত্রাপথে থাকলে তার নিরাপদে বাসায় না পৌঁছানো পর্যন্ত মা টেনশনে থাকতেন। কিন্তু ফোনের ওপার থেকে ভাবি জানালেন, ভাই, তুমি চলে আসো, মা আর নেই। দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে তাঁর চোখ স্থির হয়ে গেল। মুখে একটা স্বর্গীয় হাসিও ফুটে উঠল। কমতে থাকল তাঁর হৃদস্পন্দন। দৌড়ে এলো দুই ছেলে। কানের কাছে কলেমা পড়ে মুখে পানি দিল। পুত্রবধূরাও সুরা ইয়াসিন পড়তে থাকল। মা কলেমা পড়লেন। বলতে লাগলেন আল্লাহ...আল্লাহ...আল্লাহ...। এ স্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল। চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে গেল।
বাবার কবরের কাছেই নতুন কবর খোঁড়া হলো। তিন ভাই কবরে নেমে নিজ হাতে মাকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। মাটি দিয়ে এবং দোয়া করে ফেরার পথে দেখি একটি কবরের ওপর ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা- হে পথিক, একটু দাঁড়াও। একটু দোয়া করে যাও। আজ তোমরা যেখানে আছো, গতকালও আমরা সেখানে ছিলাম। আর আমরা আজ যেখানে আছি, আগামীকাল তোমরাও এখানে আসবে।
লেখক : গবেষক, বিশ্লেষক ও কলামিস্ট